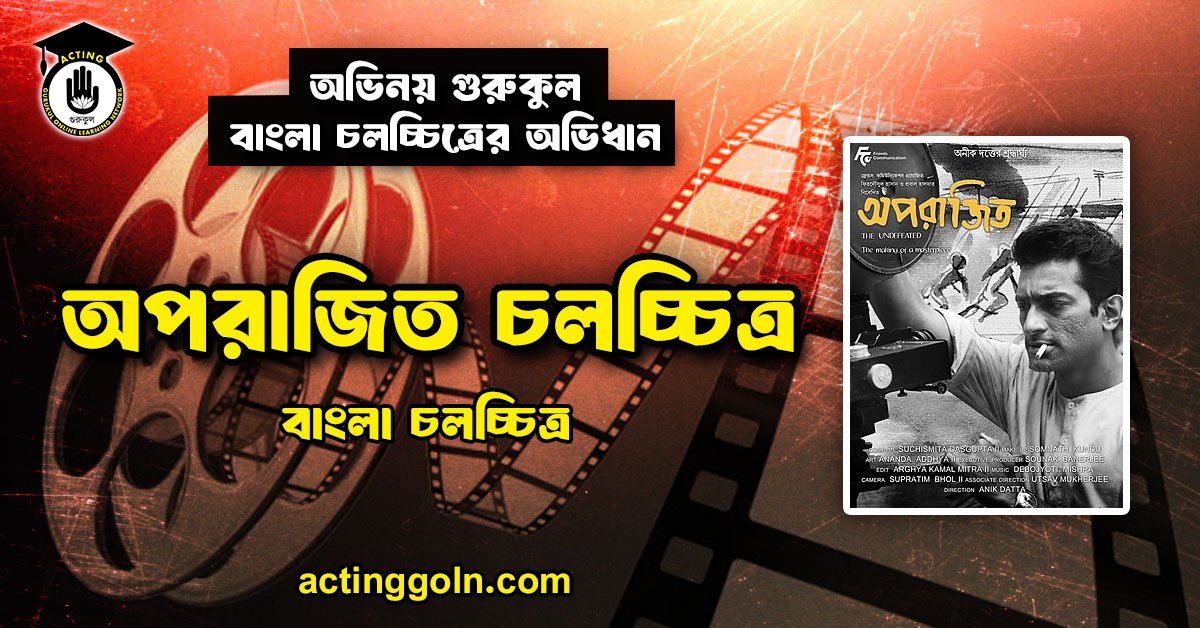অপরাজিত চলচ্চিত্রটি নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা- অপরাজিত অপু ত্রয়ীর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। এটি ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় মুক্তি পায়। এই চলচ্চিত্রটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পথের পাঁচালী উপন্যাসের শেষ এক-পঞ্চমাংশ এবং অপরাজিত উপন্যাসের প্রারম্ভিক এক-তৃতীয়াংশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
ছবিতে অপুর শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ এবং কলকাতায় কলেজে পড়ার সময়কার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটি ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জয় করে, যার মধ্যে আছে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের স্বর্ণ সিংহ পুরস্কার।
অপরাজিত চলচ্চিত্র
- প্রযোজক—এপিক ফিল্মস।
- প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা —সত্যজিৎ রায়।
- চিত্রগ্রহণ— সুব্রত মিত্র।
- সংগীত পরিচালনা —রবিশঙ্কর।
- শিল্প নির্দেশনা—বংশী চন্দ্রগুপ্ত।
- সম্পাদনা দুলাল দত্ত।
- শব্দগ্রহণ—দুর্গাদাস মিত্র।
অপরাজিত চলচ্চিত্রে যারা অভিনয় করেছেন —
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরণকুমার ঘোষাল, পিনাকী সেনগুপ্ত, অজয় মিত্র, রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, রাণীবালা, সুদীপ্তা রায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, মণি শ্রীমাণী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ রায়, কমলা অধিকারী, লালচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে. এস. পাণ্ডে, মীনাক্ষী দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অনিল মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ভাগনু পালোয়ান।
অপরাজিত চলচ্চিত্রের কাহিনি—
ভাগ্য বিড়ম্বিত হরিহর রায় (কানু), স্ত্রী সর্বজয়া (করুণা) এবং পুত্র অপুকে (স্মরণকুমার) নিয়ে কাশীতে থাকেন। কাশীর ঘাটে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করে সংসার চালান। সংসার আগের তুলনায় একটু সচ্ছল হয়েছে, অপু এখন দশ বছরের বালক। হঠাৎ একদিন স্নান করতে গিয়ে হরিহর অজ্ঞান হয়ে যান এবং চার দিন জ্বরে ভুগে হরিহরের মৃত্যু হয়। সংসার প্রতিপালনের জন্য সর্বজয়া লাহিড়ী বাড়িতে রাঁধুনির চাকরি নেন এবং ঐ পরিবারের সাথে বসবাসও করেন। লাহিড়ী মশায়ের ছোটখাট ফরমাশ খেটে অপুও কিছু পয়সা রোজগার করে। পুত্রের এই প্রবৃত্তিতে সর্বজয়া শঙ্কিত হন।
ঘটনাক্রমে সর্বজয়ার দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই ভবতারণ (রমণীরঞ্জন) তাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তাদের আর্থিক অবস্থা দেখে ভবতারণ তাদের নিজের গ্রামে বাংলাদেশের মনসাপোতায় নিয়ে আসেন। তাঁর ইচ্ছে অপু গ্রামের অন্যান্য বাড়ির সাথে তেলী বাড়ির পুজোর দায়িত্ব নিক, অপু পুজোর কাজ শিখে নিলে ভবতারণ কাশীতে অবসর জীবন কাটাতে পারেন। সর্বজয়া আবার একটি সংসার পেয়ে খুশি হন। তার বয়সি অন্য ছেলেদের দেখে অপুরও স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে হয়, সর্বজয়া আপত্তি করতে পারেন না, অপু সকালে পুরোহিতের কাজ করে বেলায় স্কুলে যায়।
অপু জেলায় দ্বিতীয় হয়ে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সর্বজয়া অপুর উচ্চশিক্ষায় মত দিতে বাধ্য হন। অপুর উচ্চশিক্ষায় মত দিলেও তাকে ছেড়ে থাকতে সর্বজয়ার কষ্ট হয়। ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়লেও নিজের অসুস্থতার কথা অপুর কাছে গোপন রাখেন। অপু মায়ের অসুস্থতার খবর চিঠিতে পায়। মায়ের মৃত্যু তার মধ্যে প্রাথমিক হতাশা সৃষ্টি করলেও সে আবার উঠে দাঁড়ায়। সে জীবনে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে।
অপু কাহিনি নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় ছবি অনেক পরিণত। এই ছবিও পথের পাঁচালীর মতোই বহু বিদেশি পুরস্কারে ভূষিত হয়। মাতা-পুত্রের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক আশ্চর্য মুনশিয়ানায় তুলে ধরা হয়েছে। মা সবসময় চান ছেলে বড় হোক, মানুষ হোক তা সত্ত্বেও মা ছেলেকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চান, আর পুত্রের বৃহত্তর জগতের টান তাকে ক্রমশ বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। সংলাপ ও দৃশ্য রচনার মধ্য দিয়ে এই জটিল মানসিক টানাপোড়েন ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পথের পাঁচালীর শেষ দৃশ্যে অপু বাবা মায়ের সাথে এক অজানা উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই ছবিতেও শেষ দৃশ্যে অপু মনসাপোতা ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে।

পুরস্কার—
ভেনিসে ১৯৫৭ সালে গোল্ডেন লায়ন, সিনেমা নোভো পুরস্কার, সমালোচকদের পুরস্কার। লন্ডনে ১৯৫৭ সালে FIPRCI পুরস্কার। সানফ্রানসিসকোয় ১৯৫৮ সালে সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ পরিচালক। ইউ এস এতে সেরা বিদেশি ছবি হিসাবে গোল্ডেন লরেল ১৯৫৮-৫৯। বার্লিনে ১৯৬০ সালে সেলঝেনিক গোল্ডেন লরেল। ডেনমার্কে ১৯৬৭ সালে এডিটরস’ এ্যসোসিয়েশনের দেওয়া বাদিল এ্যাওয়ার্ড।
প্রকাশনা ও সহযোগী গ্ৰন্থ
(১) ছবির চিত্রনাট্য এক্ষণ (অটাম ১৯৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
(২) অপুকাহিনি ভিত্তিক তিনটি ছবির চিত্রনাট্যর ইংরাজি অনুবাদ ১৯৮৫ সালে সীগাল বুকস থেকে প্রকাশিত হয়।
(৩) My Years with Apu, Satyajit Ray, N.D. Viking, 1994.
(৪) The Apu Trilogy, Robin Wood. London, Prager, 1971.