অভিনয়, অভিনয় দর্পণ পত্রিকা, নাট্যপত্র নিয়ে আশিস গোস্বামী লিখেছেন – ‘অভিনয় দর্পণ’ পত্রিকার সম্পাদক ঋত্বিক ঘটক পত্রিকার সম্পাদনার ভার ছেড়ে দেবার পর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘অভিনয়’ পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ১৯৭০ সালেই। পূর্ব-পত্রিকার অনেকেই এর সম্পাদকমণ্ডলীতে রইলেন এবং একই ভাবে নতুন পত্রিকা পুরাতনের প্রথানুসরণ করে চলতে শুরু করে। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যেই অর্থাৎ এক বছরেই বেশ কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।
[ অভিনয় দর্পণ নামে একটি বই রয়েছে, লেখক: অশোকনাথ শাস্ত্রী, বিষয়: কলকাতা। এই আর্টিকেলটি সেই বিষয়ে নয় ]
বাংলা নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি প্রযোজনার সমালোচনা ওই এক বছরের মধ্যেই পেয়েছিলাম। তবে মনে রাখতে হবে সত্তরের দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠে গেছে। থিয়েটারের অস্তিত্বের সংকট ততটা প্রকট না হলেও নিয়মিত থিয়েটার করা যাচ্ছিল না।

থিয়েটারে রাজনৈতিক নতুন চেহারা প্রতিফলিত হতে লাগল অবশ্যম্ভাবী রূপেই। শতাব্দীর ‘সাগিনা মাহাতো’ বা থিয়েটার ওয়ার্কশপের ‘রাজরক্ত’র মতো নাটক এ সময় অভিনয় হওয়াটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্য সমালোচনায় নাটকের সেই অস্থির রাজনৈতিক সত্তার প্রতি সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন শতাব্দীর ‘সাগিনা মাহাতো’ নাটকের সমালোচনায় লেখা হয় :
“১৯৭৩-এর অভিনয় সংখ্যার ১৯৮০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল, এর পরিবেশনার সুরটি বড়ো ধীর ঠাণ্ডা পর্দায় বাঁধা। তাই নিষ্প্রাণ খবরের কাগজ পড়ার মতো করে জানলাম যে, শহর থেকে দূরের এক কল্পিত শিল্পাঞ্চলে, গলায় ঢোল, মুখে চিও-জিওর বোল, গলা ভেজাবার জন্য ছেদির দিশী বোতল আর জুয়ার আড্ডা নিয়ে নিঃস্ব শ্রমজীবীর দল হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জ্বালা জুড়োয়।
খাটুনির জ্বালার সাথে সাথে, কারো আছে মেয়ে মানুষ হারাবার জ্বালা, কেউ বা শোষক মালিকের নানা উপদ্রবে জর্জরিত। বলিষ্ঠ জওয়ান সাগিনা ক্রমে ফুসমন্ত্রে হঠাৎ এদের অমানবিকতার মাঝে মনুষ্যত্ববোধের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে। জোটবদ্ধ শ্রমিকের শঠে শাঠ্যম্ নীতির মুখে মালিকপক্ষ শোষণের উগ্রতা কমাতে বাধ্য হয়। শ্রমিকের জীবনায়নে অবশ্য কোন পরিবর্তন আমরা দেখি না। হঠাৎ এই রামরাজত্বে কোলকাতার বাবু নেতারা আবির্ভূত।
ভোটের ভিত শক্ত করার জন্য সাগিনাকে দলে টেনে তারা লেবার ফ্রন্টে সাগিনার প্রভাবের বদলে দলীয় প্রভাব বাড়াতে বদ্ধ পরিকর। দলভুক্ত সাগিনার জনপ্রিয়তায় পার্টির জনপ্রিয়তা খর্ব হয়—এমনি একটা যুক্তি খাড়া করে আমাদের দেখানো হয় পার্টি আর মালিকপক্ষ গোপন চুক্তি করে সাগিনাকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদস্থ ধোঁকা দিচ্ছে।…এদিকে এক অলৌকিক কারণে শ্রমিক দল পার্টির হাতছাড়া হয়ে যায়।
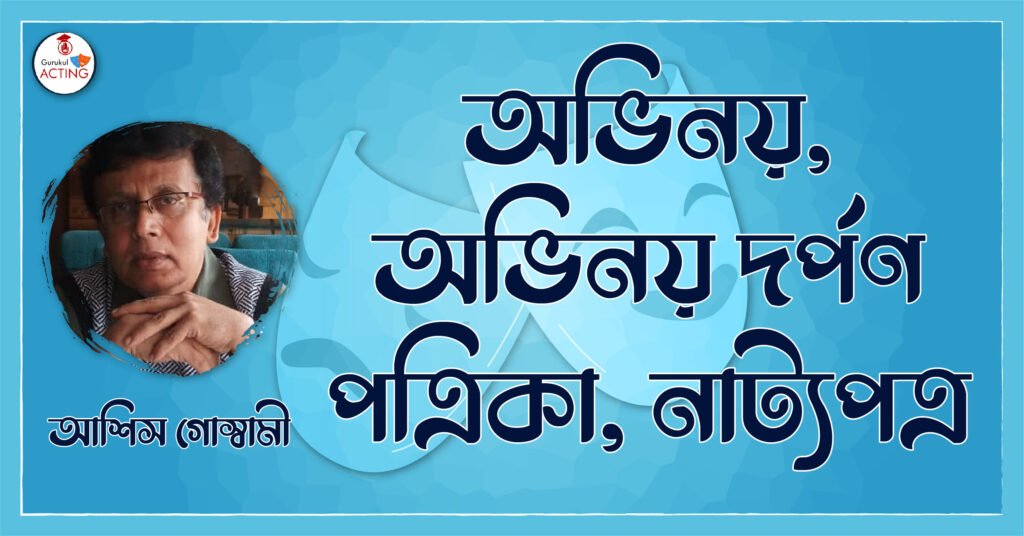
অভিনয় দর্পণ পত্রিকা
শ্রমিকদের দাবী দাওয়া উপেক্ষিত হতে থাকে; ওরা সংহতি হারিয়ে পরস্পর বিরোধী স্লোগানে মারমুখী হয়ে ওঠে।…দল-সাথী-শক্তি-নারী-নেতৃত্ব-বেইমানি সব খুইয়ে সাগিনা যখন হতাশা -জর্জর, তখন বাদলবাবু চুপিসারে তার এ্যাবসার্ড রাজ্যের দরজা দুটি একটুকু ফাঁক করে তাকে মদের মধ্য দিয়ে বাঁচতে বলে হয়তো দৃষ্টান্ত রাখতে চাইলেন যে, এ্যাবসার্ড নাটকে কেবল হতাশার কথা বলে না, বাঁচবার প্রেরণাও জোগায়।..
রাজনৈতিক দলের ভুল নীতি ও শোষকের ক্রমবর্ধমান পীড়ন নীতিতে শ্রমিক শ্রেণী আজ দিশাহারা মানি, কিন্তু এই তথ্যটিকে মাথায় রেখে গল্পকার-নাট্যকার কার্যকারণ ঘটনা-চরিত্রের যে বিন্যাস-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে কোন কৈশোরোত্তর মনের পরিচয় মেলেনি, তাই ওঁদের অজান্তেই ওঁরা প্রতিটি চরিত্রকেই উদ্দেশ্যহীনভাবে আক্রমণ করে বসেছেন।”
আবার অভিনয় ১৯৭০-এর ৭৪ পৃষ্ঠায় ‘রাজরক্ত’ নাটকের আলোচনায় নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতি সমালোচক সমর্থন জানিয়েছেন।
“রাজা সাহেবের এই জগতটাতে আমরা সকলে যেন একটা খেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তিনি কাউকে একেবারে মেরে ফেলতে চান না, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান না, তিনি সকলকে কাছে পেতে চান; একেবারে পোষা জানোয়ারের মতো বিনীত নম্রতায় মানুষগুলো তার নির্দেশে চলাফেরা করবে, গণ্ডী আঁকা সীমিত জমির মধ্যে, মানুষের উপর তিনি গিনিপিগের মতো এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাবেন।
… পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা তার শেষ মরণ কামড় দিচ্ছে শোষিত মানুষের বুকে, সর্বত্র তার ছুরির মতো বিষাক্ত দাঁতের দাগ বসিয়ে দিচ্ছে। সর্বত্র তার প্রাধান্য বিস্তার করছে, মানুষের শোষণের শেষ স্তরে নিয়ে যেতে বেতারে, ভাষণে, টেলিভিশানে, নিউজপ্রিন্ট, সিনেমায়, পোস্টারে, সব কিছুর পশ্চাতে উলংগ অত্যাচারের বিকৃত বিশাল জিহ্বার লালসা।
… নাটকের সূক্ষ্ম আধুনিক অলংকারিক রসতত্ত্ব মেনে নিয়েও বলতে পারি এখন অন্তত বাংলাদেশে সে সময়টা নিশ্চয়ই এসেছে যখন রসতত্ত্বের সত্তা সকল মেনে নিয়েও State machinary-কে আঘাত করার মতো কিছু তত্ত্ব চীৎকার করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন। শিল্পের মহান গাম্ভীর্যের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াও আমাদের রাজনৈতিক চতুরতার প্রতিক্রিয়াশীল বদমাইশিকে দর্শকের সামনে তুলিয়া ধরাই এখন বৃহত্তর উদ্দেশ্য।…
লক্ষ্যণীয় দুটি নাট্য সমালোচনাতেই বিষয়গত দিকটিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ‘অভিনয়’ পত্রিকার প্রায় সমস্ত আলোচনাতেই নাট্য বিষয়ের Political easthatic-টাই বড়ো করে দেখা হয়েছে। এর ফলে ওই এক বছরের সমালোচিত নাটকগুলির মধ্যে তৎকালের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ছাপ কতখানি ছিল তা যেমন ধরা যায়, অন্যদিক থেকে ভাবনার পরিমণ্ডলটাও জেনে নিতে পারি। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল।
যেমন ‘অভিনয়’ পত্রিকায় ১৯৭০ সালে ১৩১৩-১৩১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত থিয়েটার গিল্ডের ‘যদুবংশ’ প্রযোজনার উল্লেখ করা যেতে পারে। “যদুবংশের প্রেক্ষাপট এক মফস্বল শহরে বিস্তৃত।
চারটি যুবক–সূর্য, কৃপাময়, বুলি আর অভয় অমোঘ ধ্বংসের উপত্যকা দিয়ে যারা একটা অতলান্ত গভীর খাদের দিকে পা বাড়িয়ে চলেছে, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে এই উপমহাদেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতার যা কিছু গরল—অপ্রেম, অস্থিরতা, অর্থনৈতিক নিরাশ্রয় দু-হাতের মুঠোয় সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে চিরন্তন আক্রোশে তার আঘাত হানতে চেয়েছে সেই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণকে—যার কাছে শুধু বয়সের ঋণ শোধ করতে করতে তারা শুকিয়ে যাচ্ছে;
যে তাদের কিছুই দিতে পারে নি–যে যুদ্ধের আওতার বাইরে থাকলেও—অন্য এক ভয়ংকর যুদ্ধের প্রাঙ্গনে তারা ভীষণ ভাবে হেরে যাচ্ছে আর বারবার সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আরো একবার সেই ভাঙনকে চূড়ান্তভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলার ক্ষোভে চীৎকার করে উঠতে চেয়েছে।”
একই বছরে ২৭৯-২৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শৌভনিকের ‘হয়তো সেদিন’ “নাটকটির গল্পাংশ সরল। এক নির্জন দ্বীপে একটি কারখানাকে ঘিরে কিছু সংখ্যক highly skilled মানুষের বসবাস। বহু বছরের প্রচেষ্টায় এখন তারা রোবট (যন্ত্র মানব) তৈরী করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুসারে হাজারে হাজারে supply দিচ্ছে।

রোবটেরা আজ্ঞাবহ, একান্ত অনুগত। আকৃতি ও ব্যবহারে মরা মানুষেরই মতো কিন্তু প্রাকৃতিক মানুষের হৃদয় নামক অনুভূতির স্বাদ এদের অজানা। রোবটেরা ভালবাসা কাকে বলে জানে না। একে অপরকে ভালবাসে না। সকলেই বিচ্ছিন্ন, একক। তাই শোষিত হয়েও বিক্ষোভ নেই, দাবী নেই, … প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে দ্বান্দ্বিক সত্যটি সমগ্র, মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, সেটাই নাটকটির আলোচ্য বিষয়বস্তু।
…আজকের ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান স্পষ্ট তখন বিষয়টিকে সোজাসুজি উপস্থাপিত না করে রোবটের মতো এক কাল্পনিক রূপকথার ভেতর দিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম দেখান নাট্যকারের পলায়নী মনোবৃত্তি নয় তো? শ্রমিকেরা একে অপরকে ভালবাসে না (অবশ্য নাটকে ভালবাসা অর্থে নরনারীর ভালবাসা বোঝান হয়েছে) বলেই কি তারা সংঘবদ্ধ হতে অপারগ এবং সংগ্রাম বিমুখ?…
নাটকের মধ্যে রাজনৈতিক অস্তিরতার ছবি যেমন আছে, তেমনি সুস্থির একটা পথ অনুসন্ধানের চেষ্টাও বর্তমান, ‘অভিনয়’-এর সমালোচনায় তার প্রতি অধিক মনোনিবেশটা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বলা যায় ‘অভিনয়’ পত্রিকার নাট্য সমালোচনার বিশিষ্টতা এটাই। এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সেই সময়ের বাংলা নাট্য মঞ্চ অধিকার করেছিল ‘অ্যাবসার্ড’ নাটকের প্রযোজনা।
বহু দল ও মঞ্চ এই ‘কিমিতিবাদী নাট্য’ প্রযোজনা করেছে। ‘অভিনয়’ পত্রিকায় এ ধরনের বিখ্যাত কয়েকটি নাট্য সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন শতাব্দী-র ‘শেষ নেই’, নক্ষত্র-র ‘নয়ন কবিরের পালা। থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর ‘রাজরক্ত’ ইত্যাদি। এই ধরনের নাটকগুলি সম্পর্কে সমালোচকের মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য। নীচে কয়েকটি উদাহরণ পরপর তুলে দেয়া হল।
ওই বছরে ৩৬০-৩৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শতাব্দীর শেষ নেই’ : ‘শেষ নেই’এর গল্পাংশ একটা আছে বটে তবে গল্পের আকারে তা বলা নেই।… নাটকটি ‘ইউনিটি অব টাইম’ এবং ‘ইউনিটি অব প্লেস’কে খান খান করে ভেঙেছে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ দেখতে দেখতে যে ব্যাপারটা খুবই মনে হয়েছিলো। ধরে নেওয়া যেতে পারে আধুনিক পাশ্চাত্যের ‘ইউনিটি অব ইম্প্রেশানে তিনি বিশ্বাস রাখেন।
এই নাটকটির ব্যাপারে প্রশান্ত দাসের চরিত্রের যে ব্যাখ্যা তিনি রেখেছেন তা ভালো লাগেনি।…নাটকের শেষে লাল ঝান্ডার আগমন, অন্যথায় চলতে হবে চলাতেই শেষ অসহ্য হয়ে উঠেছে নাকি? অবশ্য মনস্তাপ করতে হয়নি, কারণ ‘শেষ নেই’, ‘শেষ নেই’ করতে করতে সবাই ‘ফ্রিজ’ হয়ে নাটকটি শেষ করেননি।”
২৮৩-২৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নক্ষত্রর ‘নয়ন কবীরের পালা’: “… ব্যর্থ হবার পর ক্লাউন দুজনের স্বীকারোক্তি ‘আসলে আমাদের জীবনে কোনো ঘটনাই ঘটে না’ । নাটকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে Symbolise করার চেষ্টা হয়েছে, এবং সাথে সাথে ক্লাউন দুজন
হোয়ে উঠেছেন সাচ্চা type symbol L… এ সমস্ত চমৎকার, image সৃষ্টি করেছে এবং নাটকের বক্তব্য (এরা বড় অভিনেতা, অথচ এদের জীবনে প্লট নেই, এবং বাধ্য হোয়ে বাহ্যিক জীবনকেই মানতে হবে) ভীষণ concentrated আর নাটক টির পক্ষে এটুকুই maxi অর্থাৎ কিনা যেমন বাঁটগুলো চেটে দেয় বাছুর তারপর দুধটুকু খাবে অন্যে, কিন্তু, তবুও নাটকটাকে নির্মমভাবে টানহ্যাঁচড়া করা হোলো— সে এক তুলকালাম কান্ড।
যেমন ধরুন ক্লাউন দুজন comatic হোয়ে বলেছে, নিলাম… ভালোবাসা এক, ভালোবাসা দুই… প্রতারণা এক, প্রতারণা দুই … আসলে আমরা নিজেদেরই বিকিয়ে দিচ্ছি, বৃত্ত পরিবর্তন করছে, মুখে চরম হতাশার স্লোগান, তারপর গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তাদের সময় নেই, ‘মাননীয় দর্শকদের কাছে মনের কথা আরো কিছু বললে তাদের হৃদযন্ত্রণা কিছুটা কমতো। এগুলোতে revealation মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে। এবং মনে হয়েছে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ব্যাপারটি একটি চটুল fancy |”
এগুলি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, শতাব্দীর শেষ নেই’ ও ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ শৌভনিকের হয়তো সেদিন’ ও ‘কারাগার’, গন্ধর্বর ‘ফুলওয়ালী’, ব্রেশট সোসাইটির ‘টিনের তলোয়ার’, রূপকারের ‘আলো দেখাও’ ইত্যাদি নাট্য সমালোচনা হিসেবে সবগুলিই যে অত্যন্ত উঁচুমানের তা নয়, তবে অভিনয় পত্রিকা গোষ্ঠী যে দল এবং তাদের প্রযোজনাগুলিকে সমালোচনার কলমে এনে হাজির করেছিল সেগুলি কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য।
মাত্র এক বছরের আয়ুষ্কালে নাট্য সমালোচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতি গুরুত্ববোধ তৈরি করতে এই সমালোচনাগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা আছেই। এই ধারাকেই পরবর্তীকালে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। ‘অভিনয়’ পত্রিকা এরপরেও বহু কাল এই দায়িত্ব পালন করেছিল। বিশেষত কলকাতার নাট্য প্রযোজনার পাশাপাশি গ্রাম ও মফস্সলের নাট্য প্রযোজনাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনার সম্মান দিয়েছিল এই পত্রিকা।
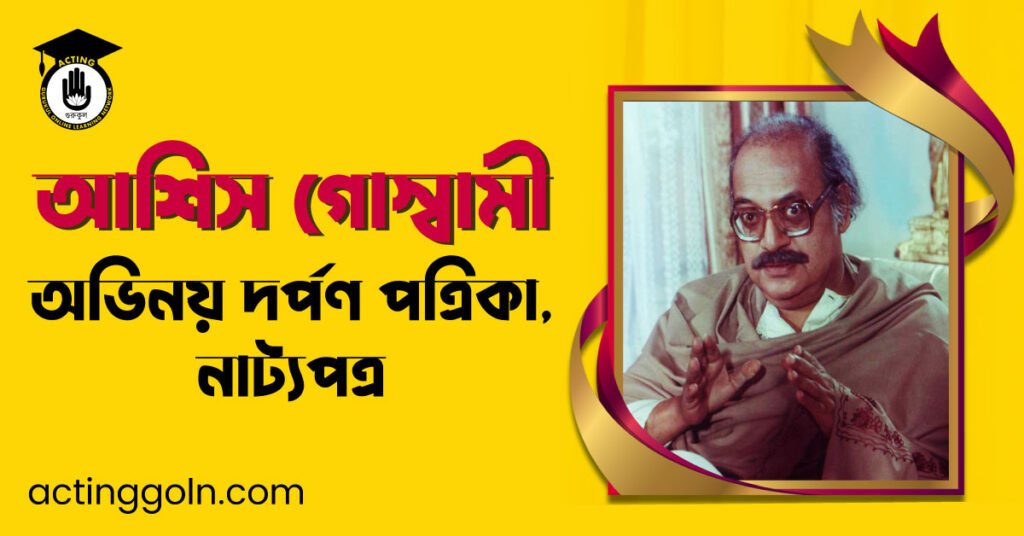
অভিনয় দর্পণ পত্রিকা , নাট্যপত্র [ আশিস গোস্বামী ] :
‘গন্ধর্ব’ এবং ‘থিয়েটার’ পত্রিকার নাট্য সমালোচনার মানকে পরবর্তী সময়ে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল ‘অভিনয় দর্পণ’ পত্রিকা। অসাধারণ কয়েকটি নাট্য সমালোচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষত পবিত্র সরকারের লেখা ‘মানুষের অধিকারে’র বাংলা নাট্য সমালোচনা একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরা যেতে পারে। যেমন ‘পাদপ্রদীপ’ এ ছিল উৎপল দত্ত কৃত বহুরূপীর ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার সমালোচনাটি। উৎপল দত্ত স্বয়ং তার প্রযোজনাগুলির নাট্য সমালোচনার মধ্যে মানুষের অধিকারে’র নাট্য সমালোচনাটিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে করতেন। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় এই উল্লেখযোগ্য আলোচনাটি প্রকাশিত হয়।
[ অভিনয় দর্পণ নামে একটি বই রয়েছে, লেখক: অশোকনাথ শাস্ত্রী, বিষয়: কলকাতা। এই আর্টিকেলটি সেই বিষয়ে নয় ]
“উৎপল দত্ত নাটকের ঘটনাকে কেবল আদালতে লিবোভিট্সের আতশবাজির খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রলোভনকে যে জয় করেছেন তাঁর জন্য তাঁর অজস্র ধন্যবাদ প্রাপ্য। তিনি কাছের ও দূরের পৃথিবীকে বিচারকক্ষের ঘটনার মধ্যে প্রক্ষেপ করে তাঁর নাটককে একটি আলাদা পরিসর দিয়েছেন, ফলে তাঁর নাটক কেবল রোমাঞ্চকর জবানবন্দীর ইতিবৃত্ত হয়ে থাকেনি, একটা প্রাসঙ্গিক ইতিহাসগত পটভূমি লাভ করেছেন।
… এবং যে মামলা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল, তাকে ১৯৬৭-র ‘নিগ্রো বিদ্রোহে’র সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সমকালীন ঘটনা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। নইলে ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকটি আঙ্কল টম্স কেবিন-এর মতো বড়ো জোর একটি করুণ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হয়ে থাকত, যা দেখে বা পড়ে আমরা দুঃখিত হতাম কিন্তু দেখা বা পড়া শেষ হয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতাম “উঃ কী ভয়াবহ দিনই না গেছে’.…… বহুদিন পরে এই প্রথম উৎপল দত্তের সম্বন্ধে এই অভিযোগ করা যাবে না যে,
তিনি মনোহর মঞ্চসজ্জার জন্য গল্প বেছেছেন, কিংবা চমকপ্রদ কিছু করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বক্তব্য প্রসঙ্গত এসেছে। এ নাটকে কয়লাখনির গহ্বর, অভাবনীয় জাহাজ বা বনস্পতি সংকুল অরণ্য নেই, মূলত দুটি মাত্র সেট, দুটিই পরিমিত এবং সুপ্রয়োগের জন্য নিখুঁত।…পরিচালনার ক্ষেত্রেই সযত্ন অধ্যবসায়ের পরিচয় আছে। মিনার্ভার সব নাটকেই যা লভ্য, …অসংখ্য টুকরো টুকরো কারুকার্য এ নাটকে রেখেছেন উৎপল দত্ত, সেগুলির দু’একটি ছাড়া বেশির ভাগই স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়।”
এই সমালোচনাটি ছাড়াও আর একটি নাটকের সমালোচনা এখানে আছে, যে নাটকটির আর কোথাও উল্লেখযোগ্য ভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি। উৎপল দত্তের এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তন-এর সাক্ষ্য বহনকারী ‘তীর’ নাটকটির এই সমালোচনা তাই অন্য মাত্রায় স্মরণযোগ্য, সমালোচনাটি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার ৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।
সমালোচক উৎপল দত্তের সেই রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থেকেই এই প্রযোজনাটির সমালোচনা করেছেন ‘তীর’ নাটকে প্রচার অবশ্যই আছে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দর্শন, যার মূল কথাগুলো বারবার নাটকের চরিত্রদের মুখে ঘুরে ফিরে এসেছে—‘অস্ত্র চাই; কান্না নয়, প্রার্থনা নয়, যন্ত্রণার প্রকাশ নয়, অস্ত্র চাই…. ‘মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা’ ইত্যাদি বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যে। এই প্রচার কোথাও লুকোবার চেষ্টা করাও হয়নি, বরং রাগ ও অভিযোগ সর্বত্রই অতিশয় স্পষ্ট।
নকশাল বাড়িতে আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণিতে কী রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা দেখানোর জন্য যে একটি বিজ্ঞপ্তি ধরণের দৃশ্য সাজানো হয়েছে – যে দৃশ্যটি প্রয়োগের দিক থেকে চমৎকার… নাট্যকার তাঁর নিজের বিশ্বাস মতো জানেন, কোন শ্রেণির সহজ অন্বয়, কাদের সঙ্গে কার স্বার্থ জড়িত, তাঁর ওই বিশ্বাসের স্পর্ধা বা তীব্রতা এই নাটকের সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।…
নাট্যকার নিশ্চয়ই শিল্পকে হাতিয়ার হিসেবে মানেন, কিন্তু তাঁর এই হাতিয়ার ওই অসমান ফলা তিরের মতো, উত্তেজনায় যার ধারগুলো বেয়াড়া আকৃতি পেয়েছে। এ অস্ত্র অব্যর্থ কিনা সন্দেহ, নইলে সত্যবান সিংকে আগাগোড়া কেন একটা ক্যারিকেচার হিসেবে খাড়া করা হবে?
পুলিশও তেমনি, অন্ততপক্ষে এই নাটকের পুলিশ অফিসার বিদ্রোহীদের জ্বালায় প্রায় স্নায়বিক বিকারে ভোগে, ফিকির বার করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে, অত্যাচারের মুহূর্তে দুর্বল হয়ে যায়, সোফাতে বসতে না গিয়ে প্রায়ই জোতদারের শায়িত পুত্রের পেটের ওপর বা উপবিষ্ট গৃহিণীর কোলের ওপর বসে পড়ে।
তাহলে শত্রুর আসল চেহারাটা কী শুধু মাত্র এই? যাদের ওপর দর্শক বেশ খানিকটা করুণা পরবশ হয়ে পড়ে তাদের আঘাত করতে উৎপল বাবু দর্শককে প্ররোচিত করবেন কী করে? অথচ নাটকে তো এই প্ররোচনাই দিতে চান।
এই প্ররোচনা সঞ্চারের ব্যাপার মঞ্চের যতটুকু কাজ তা সে করেছে। উৎপল দত্ত পরিচালক হিসেবে তাঁর চমৎকার এবং বিশাল উদ্ভাবনাকে সর্বত্র কাজে লাগিয়েছেন। ‘গন্ধর্ব’-র নাট্য সমালোচনার ধারাকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অভিনয় দর্পণ’
পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উৎপল দত্তের মতো মানুষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতার প্রকাশ নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল, তার প্রমাণ উপরোক্ত সমালোচনা। রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রবক্তা উৎপল দত্তের দুটি উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র প্রযোজনাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল এই পত্রিকায়।
এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষদের দিয়েই নাট্য সমালোচনা লেখার দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। উপরোক্ত দুটি আলোচনাই যেমন পবিত্র সরকার করেছেন, তেমনি এখানে সমালোচক হিসেবে পাচ্ছি অশোক মুখোপাধ্যায়কেও।
সরাসরি নাটকের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা নাটকের সমালোচনা করলে তা অন্য এক মাত্রা এনে দেয়। অন্য পত্রিকার সমালোচনাতে এর উদাহরণ যেমন রয়েছে, এখানেও তা সহজলভ্য। যেমন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অশোক মুখোপাধ্যায় কৃত বহুরূপীর ‘বাকি ইতিহাস’ আলোচনা, “গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে নাটক প্রযোজনার একটি অত্যন্ত দামী ঐতিহ্য বহুরূপী সম্প্রদায় নিজেদের নিষ্ঠা ও কৃতিত্বে তৈরী করে নিয়েছেন।
প্রত্যেক ভাল কবি যেমন একটু একটু করে আপন কবিতার পাঠক তৈরী করে নেন, তেমনি করে এই নাট্যগোষ্ঠী দর্শকদের রুচি ও বোধকে অনবরত পরিশীলিত করে নেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় থেকেছেন। বস্তুতঃ আজ তাঁদের যে কোন নাট্যকর্ম তাঁদেরই সৃষ্ট উচ্চমান ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা ছাড়া উপায়াত্তর নেই। এঁদের অধুনাতম নাট্যপ্রযোজনা ‘বাকি ইতিহাস’ বহুরূপীর শ্রেষ্ঠতম প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম।…
‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এবং ‘বাকি ইতিহাস’-এর রচয়িতা শ্রী বাদল সরকার বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কৃতিত্বের নিঃসংশয় অধিকারী হয়েছেন।… সাম্প্রতিক সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন নাট্যকর্মীদের আলোড়িত করছে তখন তার নাট্যরূপায়ণের জন্য তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন বারবার বিদেশী নাট্যসৃষ্টিকে দেশীয়করণের দুরূহ কাজে হাত দিতে। মৌলিক নাট্যরচনার এই দুর্বল ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী সরকারের কৃতিত্বের মূল্যায়ন সহজ হয়।
আধুনিক সভ্যতার অন্তর্লীন অবক্ষয় ও রক্তহীনতা আজ আর আমাদের আপনদেশেও কোন ধার করা অভিজ্ঞতা নয়। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এক অনির্দেশ্য ক্লান্তি ও অর্থহীনতায় আক্রান্ত হচ্ছে নিরন্তর। শ্রীবাদল সরকার-এর ‘বাকি ইতিহাস’-এ কেন্দ্রীয় দম্পতি শরদিন্দু ও বাসন্তী প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে প্রাণ ধারণের গ্লানিকে মেনে নিয়েছে।… আধুনিক জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা ও একঘেঁয়েমির এমন সাহিত্য গুণান্বিত বিশ্লেষণ বাংলা নাটকে এর আগে দেখিনি।…
নাটকটির প্রযোজনা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। প্রযোজকের পর্যবেক্ষণ শক্তির তীক্ষ্ণতা ও অনুভবের গাঢ় আন্তরিকতা অনায়াসেই সমগ্র প্রযোজনায় সংযম ও পারিপাট্য এনে দিয়েছে। তুচ্ছ কথা ও ঘটনার আড়ালে যা তুচ্ছ নয় তাকে ছুঁতে পারার বিরল ক্ষমতা প্রযোজককে সাহায্য করেছে বাস্তবতার একাধিক স্তরকে অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কোন রকমের সাহায্য না নিয়ে, আঙ্গিকের সস্তা চাতুরিকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিরলংকার সারল্যে প্রযোজক বিভিন্ন চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছেন অনায়াসে, বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন এবং পরিস্থিতির অন্তর্লীন তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণ ও সার্থকভাবে।”
এই অসাধারণ সমালোচনাটির পাশে যদি ভবেশ দাসের সমালোচিত বহুরূপীর ‘বর্বর বাঁশী’র কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে দেয়া যায় তাহলেই বোঝা যায় থিয়েটার মনস্ক ও থিয়েটারের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষের থিয়েটার দেখাবার পার্থক্যটা। সমালোচনাটি দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমালোচককে অশ্রদ্ধা না করেও এই তফাতটা মেনে নিতেই হবে। ‘
বর্বর বাঁশী’-র কিছুটা উদ্ধৃতি দেয়া হল, “নাটকের আগেই মুখবন্ধে ঘোষণা করা হয়েছে—’বর্বর বাঁশী’ তেমনই একটি আধুনিক কাহিনী, যার মধ্যেকার লোভ, স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার ছবির রেখায় রেখায় আমাদের সামাজিক ভাঁড়ামির ইতিহাস বিধৃত”, এই কথাতেই দর্শকদের উৎসাহ বেড়েছিলো। কিন্তু তার ফলে দর্শকরা দেখে এলো লারেলাপ্পা গোছের এক হৈ হল্লার আসর…..
প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই নাটক প্রযোজনার পর বহুরূপী তার নিজস্ব মেজাজ (যাকে আমি অরিজিন্যালিটিই বলব) পরিবর্তন করল। কেউ কেউ বলবেন বহুরূপীর নাটকের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে কবিতা কাজ করত, তা এ নাটকে অনুপস্থিত। আবার অনেকে বোলবেন বহুরূপী যেমন নতুন Content, নতুন অভিনেতা বেছে নিয়েছেন, তেমনি সে এত কালের দর্শক হারিয়ে নতুন এক শ্রেণির দর্শককে পাবেন।
এইখানেই নানা রকম প্রশ্ন উঠছে? দর্শক বহুরূপীর কাছে নতুন নাটক চাইছেন, প্রাক্তন নাটকের পুনরাভিনয় নয়। সুতরাং নতুন নাটক নিতে হবে, তা আবার সময়কে উপেক্ষা করে। নয়। কিন্তু এইখানেই কথা হল সেই নাটকে নির্বাচন করতে হবে বহুরূপীর পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। ‘বর্বর বাঁশী’ নাটক নির্বাচনে সেই ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হোয়েছে।
পূর্বোক্ত সমালোচক সমগ্র বাংলা থিয়েটারের প্রেক্ষাপটে দেখেছিলেন ‘বাকি ইতিহাস’ কে আর পরের সমালোচক নিছক একজন দর্শক হিসেবে বহুরূপীর প্রেক্ষাপটে দেখেছেন ‘বর্বর বাঁশী’র প্রযোজনাকে। দুটি সমালোচনার মধ্যে তাই সার্বিক পার্থক্য রয়েই গেছে। আবার এটাও লক্ষণীয়, কেবলমাত্র বহুরূপীর প্রযোজনার ক্ষেত্রেই অশোক মুখোপাধ্যায় এই সার্বিকতা খুঁজেছেন, তা নয়, অন্য প্রযোজনা সমালোচনাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি সজাগ ছিল।
যেমন মাইমেসিস নাট্যদলের ইফিজিনিয়া’ ও ‘ঈশ্বরবাবু আসছেন’-এর সমালোচনায় প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যার ১৯৩ পৃষ্ঠায় লেখেন— “…প্রথম দুটি নাটকের একটি অনুবাদ, অপরটি রূপান্তর। দুটি নাটকের জন্যই এরা দুটি বিদেশী নাট্য ঐতিহ্যের কাছে ঋণী। এরকম ঘটনা নতুন নয়। ঝাপসা ভাবে আমরা যাকে আধুনিক নাট্য আন্দোলন বলি তার অনেকটাই নাটক ও মদত পাচ্ছে বিদেশী নাট্য ঐতিহ্যগুলির কাছ থেকে।
এই অনুবাদ এবং রূপান্তর নিয়ে আজও বিতর্কের অবধি নেই, অথচ যারা এর বিরোধিতা করেন এবং ফ্যাশনের মোহে দেশী নাটক অবহেলিত হচ্ছে, এমন কথা সজোরে ঘোষণা করেন, তাঁরা একটি প্রচণ্ড এবং মর্মান্তিক সত্য সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে আছেন বলে মনে হয়। সেই সত্যটি হচ্ছে এই যে, বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেনি। দেশী নাটক লেখা হচ্ছে হয়ত রোজই বেশ কিছু কিন্তু তার মধ্যে মৌলিক ও আধুনিকতার কোন লক্ষণ প্রাণান্ত বিশ্লেষণেও আবিষ্কার করা শক্ত।”
একটি প্রযোজনার পজিটিভ দিককে বড়ো করে দেখিয়ে তারপর নাটকটির দোষগুণ বিচার করবার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আছে, সেই সঙ্গে সামগ্রিক নাটকের মৌলিকতার অভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা যে কতখানি সত্য ‘অভিনয় দর্পণ’-এর বেশ কিছু নাট্য সমালোচনায় তা সহজলভ্য।
যেমন অশোক মুখোপাধ্যায় কৃত থিয়েটার ইউনিটের ‘জন্মভূমি’, ‘‘থিয়েটার ইউনিট এর নবতম প্রযোজনা ‘জন্মভূমি’ আমাকে হতাশ করেছে। ….এর প্রধান কারণ অবশ্য নাটকটিরই মৌল দুর্বলতা। সহজ কথা সোজা করে বলার একটা ভঙ্গী নাটকটি জুড়ে আদ্যোপান্ত আছে। এবং কখনও কখনও তা ভালই লাগে।
কিন্তু যা সহজ নয় তাকেও সহজ করতে গেলে যে সরলীকরণের ঝোঁক এসে যায় তার থেকে নাট্যকার নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি।” এ ধরনের মৌলিক নাটকের কতদূর দুর্বল অবস্থা তখন ছিল, তার আর একটি উদাহরণ হল নাটুকে দলের ‘ক্রীতদাস’। সমালোচক দেবাশিস দাশগুপ্ত লিখেছেন, প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার ৬৭ পৃষ্ঠায় ‘অবশেষে আমি অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে বাধ্য।
বর্তমান বাংলাদেশে নাকি নাট্যচর্চার জোয়ার এসেছে।… আমার এ মন্তব্যে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবে কিন্তু আমি নাচার—বাস্তবকে স্বীকার করতেই হবে। এই ১০/১২টি সংস্থার প্রযোজনা যে রসোত্তীর্ণ অথবা সফল শিল্প প্রচেষ্টা এমন কথা বলছি না কিন্তু আকর্ষণী শক্তি এদের কাছে এবং লোকলক্ষ্মীর কিছুটা কৃপা (সব সময় নয়) এঁরা পান।….
এর কারণ কি? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রাচীন পন্থীরাই একটু ভোল পালটিয়ে এই কালে মঞ্চে হাজির। যে নাটক পঞ্চাশ বছর আগে রচিত বা অভিনীত হলে ক্ষতি ছিল না, সেই নাটক বা প্রযোজনা এরা আধুনিক কালে এনে হাজির করেন। সর্বতোভাবে প্রাচীন বর্জনীয় এমন আহাম্মুকি কথা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করি না—কিন্তু মধ্যযুগীয় সেই অচল ভাবলুতা আবেগ সর্বস্ব সংলাপ ব্যবহৃত ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হতে হতে ধার কমে এসেছে।
এরা সেই ভোঁতা জিনিষকেই আধুনিক নাটকের লেবেল মেরে উপস্থিত করেন; অথচ যুগ যে প্রতিনিয়তই পাল্টাচ্ছে সে খবর এদের অগোচরেই রয়ে গেল।”

মৌলিক নাটকের এহেন অবস্থার মধ্যে সে সময়ে নাট্যকার হিসেবে দুটি নামই ঘুরে ফিরে বাংলা নাট্যমঞ্চকে নাটক যোগান দিত। একজন বাদল সরকার, অন্যজন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বাদল সরকারের একটি নাটকের সমালোচনার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।
অন্য তিনটি নাটক ‘কবি কাহিনী’ ‘বাঘ’ এবং ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ নাটকের সমালোচনা করেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘শতাব্দীর তিনটি নাটক’ শিরোনামে “শতাব্দীর প্রযোজিত তিনটি নাটক ‘প্রলাপ-এর মত আঙ্গিকগত বা বিষয়গত অভিনবত্বে চিহ্নিত নয়।
আবার এগুলি বাদলবাবুর ‘বড়োপিসিমা’, ‘সলিউশন এক্স’ বা ‘রাম শ্যাম যদু’রও আত্মীয় নয়। ‘কবিকাহিনী’ (১৯৬৪-র প্রথমার্ধ) ও ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ (১৯৬৪-র দ্বিতীয়ার্ধ) রচনাকাল বিবেচনায় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’এর পরবর্তী। ইতিমধ্যে বাদলবাবুর হস্যরস আরো বুদ্ধিজারিত হয়েছে, বিশেষত ‘কবিকাহিনী’ নাটকে।
‘কবিকাহিনী’ নাটকের উপজীব্য নির্বাচন। বিষয় বলতে নির্বাচনী কৌশল। এতে হয়ত আমাদের প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতিহীনতাকে তিরস্কার করা হয়েছে। কিন্তু সেটা তিরস্কারই আক্রমণ বা ব্যঙ্গ নয়, হাস্যরস যে দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে। উপস্থিত হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই বিচারাধীন। তাই হাস্যরস কখনই সমালোচনার মনোভাব এড়াতে পারে না।
অথচ সেই সমালোচনাকে তার যোগ্য স্থান দিয়েও তাকে সংযত রাখার রীতিই বিশুদ্ধ হিউমারের রক্ষাকবচ। বাদলবাবুর এই কমেডিতে সেই পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়।… ‘বাঘ’ নাটকটির মধ্যে কিছু সমকালীন প্রশ্ন, কিছু জটিলতর প্রশ্ন উঁকি মারে, মুখ্যত শিক্ষা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রশ্ন ঘিরে।…‘বাঘ’-এর পরিস্থিতি পরিকল্পনার খানিকটা বিদেশীয়ানা আছে।
তাতেই কমেডি হিসেবে একটা নতুন ধাঁচ এসেছে।। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না পেয়েও যে মানুষটা নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে, তার মধ্যে একটা দানা বেঁধে থাকে, সে নিজেকে আরো বড়ো ভাবতে চায়, তাই কালি দিয়ে গোঁফ এঁকে বাঘ সাজে। খরগোসের জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে। বাদলবাবু এই চরিত্রে আয়রনির বহুমাত্রিকতা এনেছেন।…
১৯৬৪-র নাটক ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ এপিসোডিক। টুকরো টুকরো পরিস্থিতি বা ঘটনার মজায় এর মজা। দেখতে দেখতে পুরনো কমিক ছবির আদল মনে আসে। এই নাটকে সুবিন্যস্ত প্লট খুঁজতে যাওয়াই বোকামি। প্লটকে ভেঙে দিয়ে একটা শিথিল সূত্র বজায় রাখাই এই নাটকে বিশেষ লক্ষণ। এর মজাও তাই তাৎক্ষণিক। এই পরিকল্পনার মধ্যেও বাদলবাবুর অভিনয় তাঁকে কমিক অভিনেতার স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দিয়েছে।”
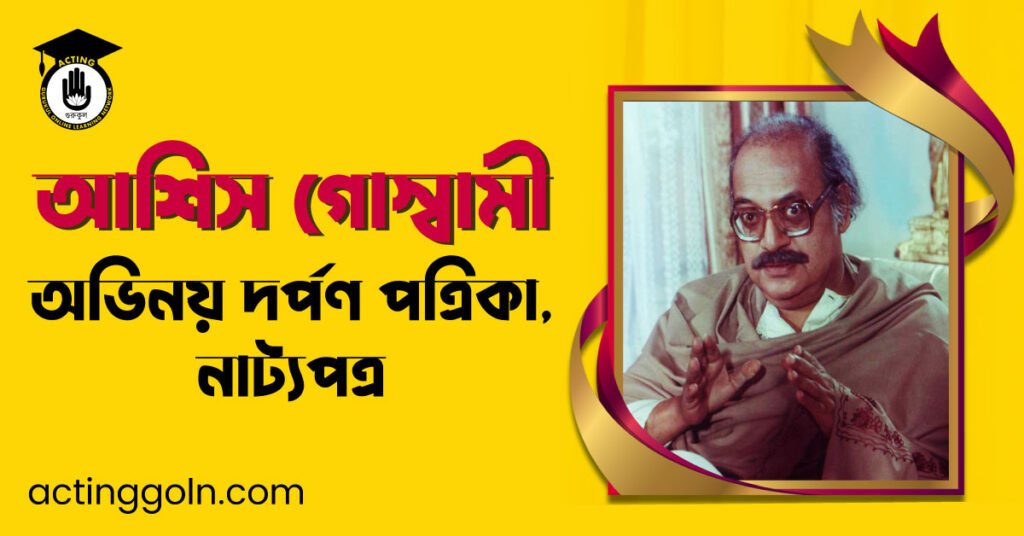
এই সমালোচনাটির বিশেষত্ব এই যে, বাদল সরকার নামক নাট্যকারের বিশিষ্টতাগুলির একটা রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা নাট্যমঞ্চে বাদল সরকারের সুগভীর বিশিষ্টতা ও প্রভাবের কথাটি জানিয়ে দেন নাট্যকার। বাদল সরকারের প্রভাব যে অন্য প্রযোজনাগুলিতেও পড়ছিল তাও জানতে পারি এই পত্রিকার দু-একটি নাট্য সমালোচনা থেকে। যেমন সুন্দরমের ‘শব্দরূপ ধাতুরূপ”, “সার্কাস পালানো ক্লাউন যদু মাস্টার ও একটি বাঘ (নাম তার বাবলু) নিয়ে কাহিনীর শুরু।
বাঘটা যদুকে তাড়া করেছে। তাড়া খেয়ে যদু উঠল গিয়ে এক শিল্পপতির বাড়ি, তার ড্রেসিং গাউন পরে আত্মগোপন করতে গিয়ে নকল শিল্পপতি সেজে সেখানেই রয়ে গেল। কিন্তু থাকতে পারল না। সমাজের লোভ, ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি তাকে তাড়া করল। এখানেও সেই বাঘ। যদু ফিরে এলো সার্কাসে।” অন্য একটি উদাহরণ রূপদক্ষর ‘রঙে রেখায় নির্বাসিত’ নাটকটি ।
সেই প্রযোজনাটির সমালোচনা লেখা হয়, “আঙ্গিকের চাইতে এ নাটকের বক্তব্য বেশী। বক্তব্য কখনো কখনো জটিলতায় অস্পষ্ট। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দুটি পরিচিত নাটকের (‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’ ও ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’) প্রভাব আছে। হয়তো নাট্যকারের অজ্ঞাতে, তবু এ দুটি নাটকের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।” সমালোচনাটি প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।
আর একজন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যার ১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত লোকায়নের ‘দ্বীপের রাজা’ প্রযোজনার সমালোচনায় নাট্যকার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি, “সাম্প্রতিক কালে যে ক’জন নাট্যকার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। মোহিতবাবু মূলতঃ কবি—একটা কাব্যময় পরিবেশ তাঁর নাটককে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কবিতার আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব তাঁর নাটকে স্পষ্ট।
এই প্রভাবই বহু ‘এ্যাবসার্ড’ মনন সৃষ্টি করে বাংলা নাটকে বিচিত্র সম্ভার এনে দিয়েছে সত্য কিন্তু সাধারণ বোধকে স্পর্শ করতে পারেনি। অন্ততঃ ‘দ্বীপের রাজা’ নাটকের পূর্বে মোহিতবাবুর বিরুদ্ধে এটি বহুসমর্থিত অভিযোগ। ‘দ্বীপের রাজা’ বক্তব্যের ঋজুতা ও চরিত্রের প্রতীক ধর্মিতা মিলে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য মৌল নাট্যসৃষ্টি।” অনুরূপ প্রশংসা খুঁজে পাই নক্ষত্রর চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’ প্রযোজনাটিরও।
“নক্ষত্র প্রযোজিত ও শ্যামল ঘোষ নির্দেশিত ‘চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’ বেশ কিছুদিন ধরেই নাট্যমোদীদের আশীর্বাদপুষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি আজকের বাংলা মঞ্চে যে ক’টি মুষ্টিমেয় গ্রুপ তথাকথিত এ্যাবসার্ড নাটক মঞ্চস্থ করে আপন সৃজন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন—নক্ষত্র নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এবং এ সুযোগ নক্ষত্রকে এনে দিয়েছে ‘চন্দ্ৰলোকে অকিও।”
এই দুই নাট্যকারের প্রভাব বাংলা মঞ্চে যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠেছিল–এর প্রমাণ আগেই দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ‘অ্যাবসার্ড প্লে’-র মতো ‘অ্যান্টি প্লে’র আমদানিও হয়েছিল এই সময়ে। হয়তো রাজনৈতিক অস্থিরতা এ ধরনের নাট্যের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ ছিল। কারণ পরবর্তীকালে এ ধরনের নাটকগুলি টিকে থাকতে পারেনি। তবু সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ও ধরনের নাটকের মঞ্চায়নকে স্বীকৃতি দিতেই হবে।
যেমন, গান্ধার-এর ‘তারারা শোনে না’ এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল, “আজকের কলকাতায় নাটকের প্লাবন এসেছে, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ভার। ‘আধুনিক নাটক’, ‘অত্যাধুনিক নাটক’, ‘এ্যাবসার্ড নাটক’, ‘কাব্য নাটক’, ‘অনুবাদ নাটক’, আরও কত কি! এবারে গান্ধার গোষ্ঠী উপহার দিলেন ‘এ্যান্টি প্লে’—এক ধরনের নাটক যাতে আপাত কোন কাহিনী নেই, সংঘাত নেই, সুর নেই, শেষ নেই, এক কথায় বলতে গেলে তথাকথিত ‘নাটক’ নেই।
তারারা শোনে না’ এমনই এক নাটক যেটা রচয়িতা চাণক্য সেনের মতে ‘এ্যান্টি প্লে’ (যে অর্থে সত্যজিৎ রায়ের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিটিকে এক বিদগ্ধ সমালোচক বলেছিলেন ‘এ্যান্টি ফিল্ম’) আমি ইদানীং বেশ কিছু বহুল প্রচারিত আধুনিক নাটক দেখতে গিয়ে ঠকে এসেছি। প্রতিবারেই মনে হয়েছে কিছু সস্তা আঙ্গিকের মারপ্যাচ দিয়ে অত্যন্ত জোলো বক্তব্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
নাটক নিয়ে বেশী এক্সপেরিমেন্ট করার মধ্যে একটা কুফল আছে। সেটা হোলো, প্রায়শই খুব বেশী এক্সপেরিমেন্টাল নাটক নিছক স্টান্টের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। অবশ্য চট্ করে খ্যাতি লাভ করার এটাই সহজতম উপায়। এই সব কারণেই বলতে দ্বিধা নেই ‘গান্ধার’ গোষ্ঠী সত্যিকারের নতুনত্বের নিদর্শন রাখতে পেরেছেন।
তারারা শোনে না’ নিঃসন্দেহে গতানুগতিক সাধারণ প্রযোজনাগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র। নাটকটির বক্তব্য ও বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন নাট্যানুরাগী দর্শকদের চিন্তার ও আলোচনার অশেষ খোরাক জোগাবে।”
আলোচ্য পত্রিকায় অন্য এক ধারার নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, উপন্যাস গল্প থেকে গড়ে ওঠা নাট্যের প্রযোজনাগুলি যে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো মানের ছিল সে কথাও সমালোচনাগুলিতে স্বীকার করা হয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি সমালোচনার কিছু অংশ তুলে দেয়া হল।
দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার ৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা থিয়েটারের ‘সূর্যচেতনা’: “গৰ্কীর প্রকাশিত প্রথম গল্প ‘মাকার চু’ অনুপ্রাণিত নাট্যপ্রয়াস ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের ‘সূর্যচেতনা’।…উপন্যাস বা ছোটগল্পে যেটা পড়ে পাঠক বারবার মুগ্ধ,
সেই বিষয়ই হয়তো নাট্যরূপে ক্লান্তি কর। গকীর প্রথম পর্বের গল্পগুলোর মধ্যে এ সমস্যা বর্তমান। সমালোচকদের মতে, এই গল্পগুলি ‘রোমান্টিক হেরোইসম’ স্বাধীনতা ও সংগ্রামে সাহসী মনের আহ্বান। ব্যক্তিগত চেতনার আন্দোলনকে ব্যক্তি জীবনের সমস্যায় রূপান্তরের চেষ্টায় উপরোক্ত সমস্যাটা থেকে যায়।
তাই লাইকো জোবারের স্বাধীন উদ্দাম, প্রাণোচ্ছ্বল চেতনার যে ছবি গল্পে আছে, অনুপ্রাণিত নাট্যরূপে তার স্থান অধিকার করেছে অন্তত গল্পে প্রচলিত Socislist realism-এর বঙ্গদেশীয় বাঁধা গতে প্রতিচ্ছবি। তাই Socialist realism-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকার লাইকো জোবার ও রাডার স্বাধীন, উদ্দাম চেতনার চিত্রায়নের চেয়ে জোর দেন জমির মালিক সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ও কৃষকদের সংগ্রামের ঘটনার দিকে।”
ওই একই সংখ্যায় সমালোচনা হিসেবে প্রকাশিত হয় চতুরঙ্গর ‘আবর্ত’ : “ ‘আবর্ত’ চতুরঙ্গের একটি সহজ সুন্দর অবদান। বাংলার ভূমি সংস্কারে জমিদার হয়তো গেছেন, কিন্তু জোতদার, ছোট বড় অথবা মেজো, সবাই আছেন বহাল তবিয়তে…. গ্রাম বাংলার এই যে চিরন্তন সমস্যা, একে সার্থক রূপদান করেছেন বরুণ দাশগুপ্ত, সমরেশ বসুর ছোট গল্প ‘আবর্ত’ অবলম্বনে। কাহিনী বিন্যাসে যদি নতুনত্বের আশা কেউ করেন, তিনি নিরাশ হবেন। যাদের নিয়ে এ কাহিনী তারা সবাই আমাদের পরিচিত। সেখানে নাটকীয় চমক সৃষ্টির আশা বৃথা।…’
এই সংখ্যার আর একটি সমালোচনা ‘নোনাজল মিঠে মাটি’ “একটা গোটা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা যায় না এটা স্বতঃসিদ্ধ। এই কারণে সেই সেই অংশও সেই সেই চরিত্র যা গোটা উপন্যাসের সামগ্রিক মানসিকতা ও বক্তব্যের প্রয়োজনকে একেবারে অবিচ্ছেদ্য, নাটকের মঞ্চরূপে তাকে গ্রহণ করাই রীতি। মুন্সিয়ানা যতটুকু, সেটুকু ঐ গ্রহণ-বর্জনের পরিমিতিতে…
প্রফুল্ল রায়-এর অসামান্য উপন্যাস ‘নোনা জল মিঠে মাটি’ মঞ্চরূপ কেমন হবে এ ভাবনা স্বভাবতই ছিল। এর বিশাল পটভূমি, অসংখ্য চরিত্র ও অপূর্ব মানবিক সব ছোট ছোট ঘটনা সংযোজন—একটা ছোট মঞ্চে আড়াই ঘণ্টায় কি করে সম্ভব ভাবতে অবাক লেগেছিল। মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে ‘শৌভনিক’ প্রযোজিত নাট্যরূপ দেখে একটা বিস্ময়কর পরীক্ষার আভাস পেলাম এ কথা বলতে বাধা নেই।”
এই নাট্য সমালোচনাগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি সমালোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় ‘ছায়ায় আলো’ ‘ছন্দকের টেরোডেকটিল ও মৃত্যুর স্বাদ’, ‘সুন্দরমের শব্দরূপ ধাতুরূপ’, ‘ঋতায়ণের নেকড়ে’, ‘অনুভবের শনিবারের বিকেল’, ‘শৌভনিকের আন্তিগোনে’, এবং ‘নান্দিকের নটী বিনোদিনী’।
এ ছাড়া একটি যাত্রাপালার সমালোচনা ‘নিউ আর্য অপেরার রাইফেল’ প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে ‘অভিনয় দর্পণ’ সামগ্রিক বাংলা থিয়েটারের ছবিই তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে মফসল বাংলার থিয়েটার-চর্চার কোনো সংবাদ ও সমালোচনা নেই। পরবর্তীকালে ‘অভিনয় দর্পণ’ বন্ধ হয়ে ‘অভিনয়’ প্রকাশিত হলে সেখানে মফস্সল চর্চাকে স্থান দেওয়া হয় কিন্তু তাও বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে।
