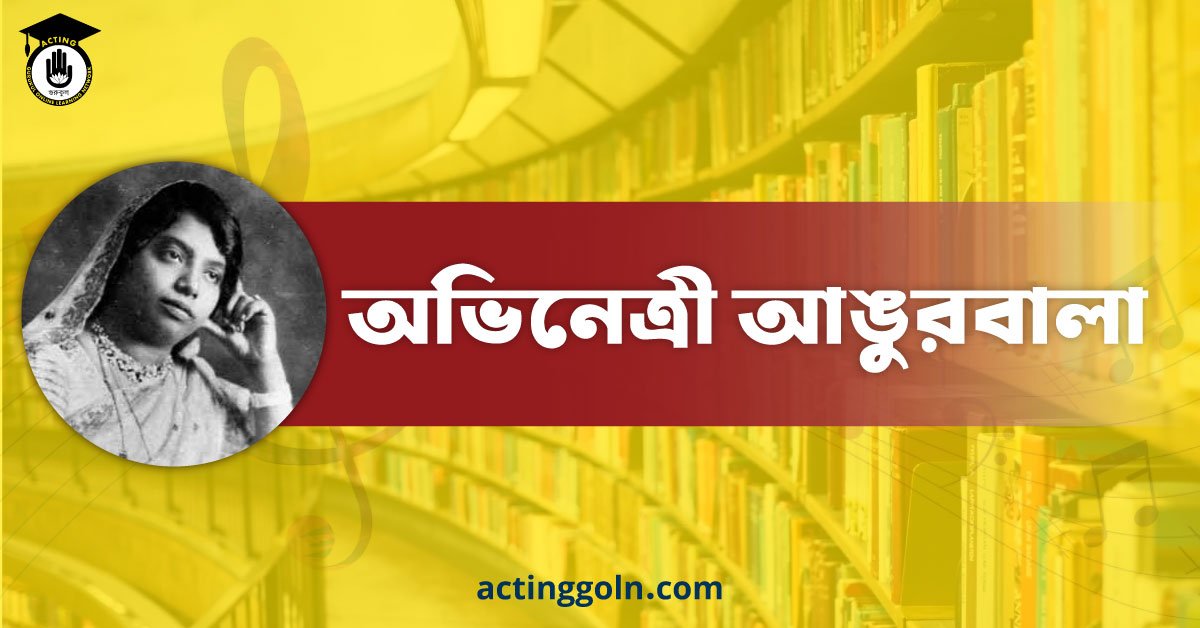বাংলা সঙ্গীত ও নাট্যজগতের ইতিহাসে যে ক’জন নারী শিল্পী একাধারে গায়িকা, অভিনেত্রী ও সাংস্কৃতিক প্রবর্তক হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আঙুরবালা (প্রকৃত নাম প্রভাবতী দেবী) অন্যতম। বিশ শতকের গোড়ার দিকের সমাজে যখন নারীদের জন্য শিল্পচর্চা ছিল কঠিন এক সাধনা, তখন তিনি নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা হয়ে উঠেছিলেন এক পথপ্রদর্শক নাম।
শৈশব, পারিবারিক জীবন ও শিক্ষার শুরু
আঙুরবালার জন্ম ২৩ জুলাই ১৯০৬ সালে কলকাতার কাশিপুরে। তাঁর পিতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বর্ধমান জেলার ইন্দাসের বাসিন্দা, ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী ও উদারমনা মানুষ। পরিবারটি সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ছিল, যা ছোটবেলা থেকেই প্রভাবতী দেবীর মানসিক জগতে গভীর ছাপ ফেলে।
শিক্ষাজীবনে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কৃত হন, কিন্তু পারিবারিক সীমাবদ্ধতার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। তবে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অদম্য ভালোবাসা ও কৌতূহল তাঁকে এক অনন্য পথে নিয়ে যায় — সঙ্গীত সাধনার পথে।
মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর প্রথম গুরুর নাম ছিল অমূল্য মজুমদার, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ। এই প্রাথমিক শিক্ষা-পর্বই তাঁর জীবনের ভিত গঠন করে দেয়।
সঙ্গীত সাধনা ও শিল্পী হিসেবে উত্থান
আঙুরবালার সঙ্গীতশিক্ষা ছিল বিস্তৃত ও বিচিত্র ধারার। তিনি শিখেছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন রীতি — খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, কীর্তন, ভজন, এমনকি গজল পর্যন্ত। তাঁর শিক্ষাগুরুদের তালিকা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ — জিতু ওস্তাদ, রামপ্রসাদ মিশ্র, ললিতমোহন গোস্বামী, জমিরুদ্দিন খাঁ, ঈষাণ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম।
বিশেষভাবে নজরুল ইসলামের কাছ থেকে গানের প্রশিক্ষণ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নজরুলের সংস্পর্শে এসে তিনি শুধু সুর নয়, গানের আবেগ, শব্দের অর্থ ও ছন্দের গভীরতা অনুধাবন করতে শেখেন। তাঁর কণ্ঠে নজরুলগীতি পেত এক নতুন প্রাণ, যেখানে ছিল অনুশাসিত সুরের সঙ্গে গভীর হৃদয়বোধের মিলন।
কিশোরী বয়সেই তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় — “বাঁধ না তরীখানি আমার এ নদীকূলে”। এরপর তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সংগীতজগতে এক উজ্জ্বল নাম হয়ে ওঠেন। তিনি বাংলা, হিন্দি ও উর্দু — তিন ভাষাতেই গান রেকর্ড করেন। প্রায় ৫০০টিরও বেশি গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছে, যার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, কীর্তন, গজল, এবং হিন্দি ফিল্মি সংগীত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল স্বচ্ছ, অনুরণনময় এবং আবেগপূর্ণ — যা একদিকে শ্রোতাকে শান্ত করত, অন্যদিকে ভাবাবেগে আলোড়িত করত। তাঁর গান শুনে কবি নজরুল একবার বলেছিলেন,
“আঙুরবালার কণ্ঠে আমার গান যেন নতুন রূপে জন্ম নেয় — ওর কণ্ঠের মাধুর্যই আমার কথায় প্রাণ দেয়।”
মঞ্চজীবন ও থিয়েটার সাফল্য
আঙুরবালার প্রতিভা শুধুমাত্র সঙ্গীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবেও অগ্রগণ্য। তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা হয় কলকাতার বিখ্যাত মিনার্ভা থিয়েটার-এ। সেসময়ের নারীশিল্পীদের জন্য মঞ্চে অভিনয় করা ছিল সামাজিকভাবে কঠিন এক সিদ্ধান্ত, কিন্তু আঙুরবালা সেই বাধাকে পরিণত করেছিলেন তাঁর সাহসের পরিচয়ে।
তিনি একাধিক নাটকে অভিনয় করেন — যেখানে তাঁর সংলাপ বলার ধরণ, মুখভঙ্গি ও গানের প্রকাশভঙ্গি মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের। তিনি ছিলেন এমন এক বিরল শিল্পী, যিনি একই নাটকে সংলাপের পাশাপাশি নেপথ্য সংগীতও পরিবেশন করতেন, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল।
চলচ্চিত্রজীবন: পর্দার আঙুরবালা
আঙুরবালা প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ১৯৩৩ সালে, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত যমুনা পুলিনে ছবিতে, যেখানে তিনি ‘জটিলা’ চরিত্রে অভিনয় করেন। পরবর্তীতে তিনি একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেন এবং বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের অন্যতম জনপ্রিয় মুখে পরিণত হন।
তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রসমূহ:
ধ্রুব (১৯৩৪)
অবর্তন, আমার দেশ, পণ্ডিতমশাই (১৯৩৬)
ইন্দিরা (১৯৩৭)
সৰ্ব্বজনীন বিবাহোৎসব, জগাপিসি, খনা, বেকার নাশন (১৯৩৮)
দেবযানী (১৯৩৯)
চলচ্চিত্রে তিনি শুধু অভিনয়ই করেননি, বরং অনেক ছবিতেই নিজের গলায় গান গেয়েছেন। এই দুই প্রতিভার সংমিশ্রণ তাঁকে করে তোলে বাংলা চলচ্চিত্রের এক বিরল নারী শিল্পী — একাধারে অভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী।
সঙ্গীত ও অভিনয়ে প্রভাব
আঙুরবালা ছিলেন নজরুলগীতির প্রথম দিকের অন্যতম প্রধান প্রচারক। তাঁর গাওয়া নজরুলগীতি রেডিওতে সম্প্রচারিত হতো, এবং বহু শ্রোতা প্রথম নজরুলের গান শুনতেন তাঁর কণ্ঠে। তাঁর গানের ভেতর ছিল সেই যুগের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসের ছোঁয়া — দেশপ্রেম, প্রেম, ভক্তি ও মানবতার সমন্বয়।
তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের এক সেতুবন্ধনকারী শিল্পী, যিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মাঝে তৈরি করেছিলেন সুরের সংলাপ।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি
তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৩ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। পরবর্তীতে তিনি ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন, যা ছিল তাঁর শিল্পজীবনের একটি গৌরবময় মাইলফলক।
তিনি আরও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানিত হন, এবং জীবনের শেষপর্যন্ত সঙ্গীতচর্চায় যুক্ত ছিলেন।
শেষ জীবন ও উত্তরাধিকার
আঙুরবালা ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁর গান, তাঁর সুর, তাঁর মঞ্চে সংবেদনশীল উপস্থিতি আজও বেঁচে আছে।
বাংলা সঙ্গীত ও নাট্যকলার ইতিহাসে তিনি শুধু একজন গায়িকা নন, বরং এক যুগসন্ধির নারী, যিনি নারীশিল্পীদের জন্য নতুন দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন প্রমাণ করে — প্রতিভা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস থাকলে সমাজের সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা সম্ভব।
চলচ্চিত্রপঞ্জি (নির্বাচিত)
১৯৩৩: যমুনা পুলিনে
১৯৩৪: ধ্রুব
১৯৩৬: আবর্তন, আমার দেশ, পণ্ডিতমশাই
১৯৩৭: ইন্দিরা
১৯৩৮: সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব, জগাপিসি, খনা, বেকার নাশন
১৯৩৯: দেবযানী
আঙুরবালার জীবন ছিল সংগ্রাম, সাধনা ও সাফল্যের এক অনন্য মেলবন্ধন। তিনি শুধু গানের শিল্পী ছিলেন না — তিনি ছিলেন এক যুগের নারীজাগরণের প্রতীক, যিনি কণ্ঠে ও চরিত্রে প্রকাশ করেছিলেন নারীর আত্মবিশ্বাস ও সৃষ্টিশক্তি।
বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে শ্রদ্ধা, অনুপ্রেরণা ও কৃতজ্ঞতায়। তাঁর গাওয়া প্রতিটি গান যেন স্মরণ করিয়ে দেয় —
“সত্যিকারের শিল্পী কখনো হারিয়ে যান না, তিনি রয়ে যান তাঁর সৃষ্টির সুরে।”