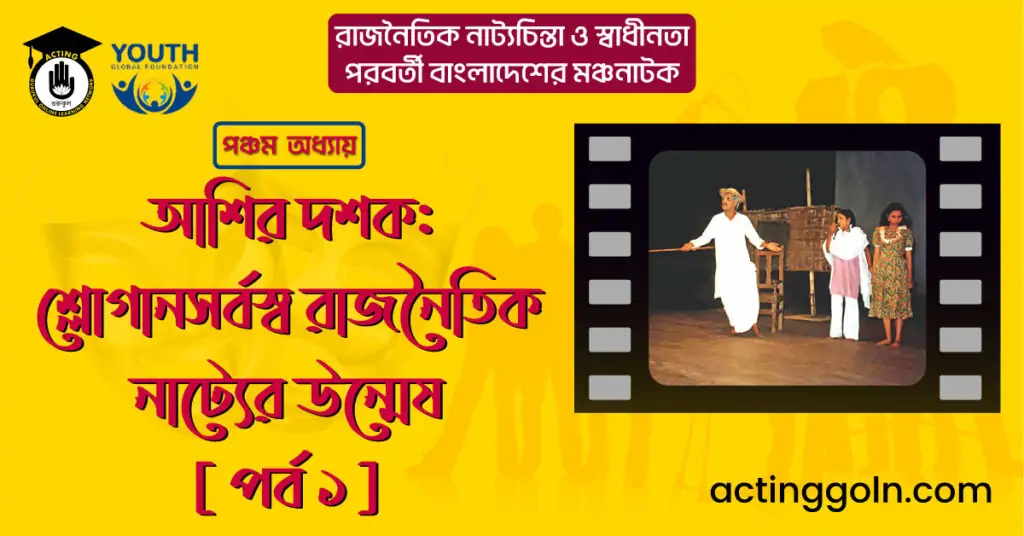আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ : – নাট্য আন্দোলনের এই পর্বের বেশিরভাগ সময়টা ছিলো, সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকাল। জিয়াউর রহমান নিহত হবার দশ মাস পর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। জিয়ার মৃত্যুর পর সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও সশস্ত্রবাহিনীর পরোক্ষ সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সাবেক উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার। রাষ্ট্রপতি সাত্তার তার স্বল্প সময়ের শাসনামলে চেষ্টা করেছিলেন প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে। জিয়াউর রহমান মন্ত্রীদের ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য দুটি গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, জিয়ার মৃত্যুর পর যা বন্ধ ছিলো।
আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 2 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/আশির-দশক-শ্লোগানসর্বস্ব-রাজনৈতিক-নাট্যের-উন্মেষ-পর্ব-১--1024x536.jpg)
রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই এই তদন্ত পুনরায় শুরু হয়। তিনি অর্থনীতিবিদ এম এন হুদাকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। সেই সাথে বিয়াল্লিশ সদস্যের একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়। খুব শীঘ্রই নবগঠিত এই মন্ত্রীসভার দেশপ্রেম, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেন। সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ নেন। বারোই ফেব্রুয়ারি তিনি শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে আঠারো সদস্যের মন্ত্রী সভা গঠন করেন। জেনারেল এরশাদ এসময় সরকার পরিচালনায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। কখনও কখনও সহায়তার নামে সরকারি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে থাকেন।
জেনারেল এরশাদ সে সময় সশস্ত্রবাহিনীর জন্য একটি সাংবিধানিক ভূমিকা নির্ধারণের দাবিও জানিয়ে আসছিলেন। এরশাদের এই দাবি এবং চাপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে না পেরে রাষ্ট্রপতি প্রথমে দশ ও পরে ছয় সদস্যর একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেন। সদস্যরা ছিলেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সশস্ত্র তিন বাহিনীর প্রধান। পরের বার চারজন মন্ত্রী সদস্যপদ থেকে বাদ পড়েন। এই সময় সরকার ও প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি, দলের ভিতরকার মারাত্মক অন্তর্দ্বন্দ্ব সরকারকে দুর্বল করে তোলে। বয়সের ভারে ন্যুজ, রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগে অনভ্যস্ত রাষ্ট্রপতি সাত্তার ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন। সেই সুযোগে জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।
ক্ষমতা দখলের সময় তিনি সেই পুরানো যুক্তি দাঁড় করালেন যা এতকাল সামরিক শাসকরা বলে আসছিলেন। তিনি সামাজিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নজীরবিহীন দুর্নীতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা, সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এই সব প্রশ্নগুলিই সামনে নিয়ে এসেছিলেন। এরশাদের এই ক্ষমতা দখলের পেছনে কয়েকজন বেসামরিক আমলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। সেই জন্যই এরশাদ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারেন।’
সামরিক সরকার সংসদ বাতিল এবং সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করে। সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে প্রচারিত ফরমানে সকল প্রকার মিছিল, ধর্মঘট, জনসভা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশের এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একজন আমলাও প্রতিবাদ করেননি। বরং কিছু কিছু আমলা এ সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক শাসনকে সমর্থন করার পেছনে ছিলো তাঁদের পেশাগত স্বার্থ। দীর্ঘদিনের আমলাতন্ত্রের সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি তাঁর ক্ষমতার শেষ দিকে কিছু কিছু সংস্কার সাধনও করেন। উনিশশো আটাত্তর থেকে আশি সালে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে একটি পুনর্বিন্যস্ত চাকরি কাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। মূল লক্ষ্য ছিলো অতীতের আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের অবসান করা।
মেধা, দক্ষতা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণকে প্রাধান্য দেয়া। সে চাকরি কাঠামোতে বেতনক্রমকেই পদমর্যাদার মানদণ্ড হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এরশাদ সরকার ক্ষমতায় এসে আমলাদের পুরানো ক্ষমতাকে বহাল রাখেন। জেনারেল এরশাদ বেসামরিক উচ্চপদস্থ আমলাশ্রেণীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে তিনি মন্ত্রীদের চেয়েও সচিবদেরকে অলিখিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন; এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় প্রশাসনে ব্যক্তিগত পছন্দের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। কোনো ধরনের নিয়ম-নীতি ছাড়াই এরশাদ ক্যাডার সার্ভিসের শতকরা দশভাগ পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেন। এসব পদে তিনি যে কাউকেই নিয়োগ দিতে পারতেন।
রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট ও ব্যাপক দুর্নীতি ছিলো এরশাদ সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে সময় বিদেশি গণমাধ্যমগুলোতে সরকারের দুর্নীতির তথ্য ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত অসততার কারণে তার শাসনামলে গুটিকয় ব্যক্তির ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে এবং অর্থ লুটপাটে পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়। জেনারেল এরশাদ খুব শীঘ্রই চরম গণবিরোধিতার মুখে পড়েন। ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে। সেইসব আন্দোলন ও মিছিল-সমাবেশ দমিয়ে রাখার জন্য তিনি সভা-সমাবেশে গুলি চালনা, রাজপথে ছাত্র হত্যা, পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে গোপন নির্যাতন চালানোর হুকুম দেন। তাঁর শাসনামলে নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় এবং ভ্রষ্ট ও তোষামোদকারী রাজনীতিবিদদের একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে।
প্রায় সব দল থেকেই স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরা যুক্ত হয়েছিলেন এরশাদের সঙ্গে। দলে যোগ দেয়া নিত্য-নতুন ব্যক্তিদের মন্ত্রী সভায় জায়গা দেয়ার জন্য এরশাদ নয় বছরে ষাটবারের মতো মন্ত্রীসভায় রদবদল ঘটান। তিনি দুর্নীতি উচ্ছেদের শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও তার শাসনামলে দুর্নীতির বিষবাষ্প পিরামিডের আকার ধারণ করে। জেনারেল এরশাদের আমলেই ব্যাপকভাবে স্বর্ণসহ বড় বড় চোরাচালানের ঘটনা ঘটে। মাদকদ্রব্যও দেশের ভিতর প্রবেশ করতে থাকে।”
ক্ষমতা দখলের পর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকলেও এরশাদকে বিদায় নিতে হয় বৈধতার সংকটের কারণেই। শেষদিন পর্যন্ত তাকে বৈধতার সংকট পোহাতে হয়েছে। মোকাবেলা করতে হয়েছে অব্যাহত সরকার বিরোধী আন্দোলন। হরতাল হয়েছে পৌনে চার হাজার ঘন্টা। আটাশি সালেই হরতাল হয়েছে সাতষট্টি দিন এবং উননব্বই সালে হরতাল হয়েছে দুশো উনচল্লিশ দিন। ব্যাপক গণআন্দোলনে নব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সামরিক শাসনের এ সময়কালটাই বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের একটি বিশেষ পর্ব। যার বেশির ভাগ সময়টাই আশির দশকের অন্তর্ভুক্ত। এই আশির দশককে এই গবেষণায় ভিন্ন পর্বে ভাগ করেছি বিভিন্ন কারণে।
সেই বিভাজনের পেছনে প্রধান কারণ, এই দশকেই নাটককে খুব জোরেসোরেই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির পক্ষে কাজে লাগানোর ঘোষণা দেয়া হয়। সত্তর দশকের নাট্যচর্চায় যা আমরা দেখি না। আশির দশকে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের জন্ম হয়। নাটককে রাজনীতির পক্ষে ব্যবহার করার শ্লোগান এবং সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের তৎপর হয়ে ওঠা এই দশককে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
নাট্য প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও এই সময়কালে ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময়কালে আমরা নাট্যচর্চার বেশ কিছু নতুন দিক লক্ষ্য করবো। এক দিকে রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে নাটককে ঘোষণা দেয়া, অন্যদিকে আবার পেশাদারিত্বের প্রশ্ন তোলা। মুক্তিযুদ্ধের মহিমা প্রচার করা এবং স্বাধীনতা-বিরোধীদের ঘৃণা করার ব্যাপারটিও এই সময়কালে প্রথম লক্ষ্য করা যায় নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে। বাংলাদেশের সত্তর দশকের নাট্যচর্চায় যেমন পশ্চিমবঙ্গের নবনাট্যধারা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিলো, আশির দশকে গণনাট্যের চিন্তা দ্বারা নাটকের দলগুলি কিছুটা প্রভাবিত হলো। আশির দশকের নাট্যচর্চার একটি বিশেষ দিক হলো এই, নাট্যদলগুলো বুঝতে পারলো রাজনীতির সাথে নাটকের কোনো বিরোধ নেই।
কিছু কিছু দল জোরেসোরেই ঘোষণা দিলো নাটককে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলতে হবে। সেজন্য আশির দশকে যে নাট্যদলগুলো জন্ম নিচ্ছিল্লো তাদের প্রায় সকলেরই ঘোষণায় নাটকের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিলো। দলগুলো এই প্রতিশ্রুতি কতোটা সমাজবিজ্ঞান সচেতন হয়ে দিয়েছিলো সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে নাটককে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা যে নাট্যদলের একটি দায়িত্ব সেটা তারা বুঝতে পেরেছিলো। সেজন্য দলগঠনের পেছনে সমাজ পরিবর্তন বা শ্রেণীসংগ্রাম খুব জোর পেয়েছিলো।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 3 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৫.jpg)
বাহাত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত আরণ্যক নাট্যদল আশির দশকে এসে তাদের নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু মতামত দেয়। এই দলটির নতুন ঘোষণায় বলা হয়, ‘আরণ্যক মনে করে, বর্তমান সমাজ সুস্থভাবে বসবাস করার অযোগ্য-তাই এর পরিবর্তন দরকার। নাটক সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সে কারণেই তাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা একজন নাট্যকর্মী হবেন প্রত্যাশিত সমাজ ব্যবস্থার দক্ষ রূপকার।
জনগণের মানস চেতনায় তিনি তুলে ধরবেন আগামী কালের ছবি। নাটক এই কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজ বিকাশের মূল যে চালিকা শক্তি শ্রেণী সংগ্রাম, সে সংগ্রামে নাটক শুধু বিনোদন নয়, শ্রেণী সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার।” নাট্যশিল্পকে শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে ব্যবহারের এই ঘোষণা কিন্তু সত্তর দশকে কিংবা মুক্তিযুদ্ধ পূর্বের তেইশ বছর সময়কালে দেখা যায় না। প্রথম আরণ্যক নাট্যদলই এ ধরনের একটি ঘোষণা দেয়। যদিও এ ঘোষণা প্রথম আরণ্যকই দিয়েছিলো, পরে আরো অনেক নাটদলই এই একই মতবাদ ব্যক্ত করে।
উনিশশো পঁচাত্তর সালে চট্টগ্রামে গণায়ন নাট্য সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। জন্ম মুহূর্তে নাটক মঞ্চায়নে যে লক্ষ্যের কথা তারা ঘোষণা করেছিলো, আশির দশকে এসে সেই লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে। নতুন লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়, নিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে আস্থাহীন গণায়ন বিশ্বাস করে নাটক শোষিতকে শ্রেণীচেতনা দান করে আর শ্রেণীচেতনার অধিকারীদের বিদ্রোহ, আন্দোলন, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মর্মবস্তু বুঝতে সহায়তা করে। শিল্পের জন্য শিল্পপূজার নামে জীবনচ্যুত পলায়নী স্ববিরোধিতা অথবা নৈরাজ্যবাদী অপসংস্কৃতির উলঙ্গ প্রকাশে গণায়ন বিশ্বাসী নয়। উনিশশো উনআশি সালে রাজশাহীর অনুশীলন নাট্যদলের যাত্রা শুরু। আশির দশকে এসে এরাও বিশ্বাস করতে শুরু করে নাট্য আন্দোলন সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের একটি অংশ।
বগুড়ার সংশপ্তক থিয়েটারের জন্ম উনিশশো আটাশি সালে। এদের ঘোষণায় বলা হয়েছিলো, নাটক শুধু জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার। উনিশশো আশি সালে সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় দুর্বার নাট্যদল। এরাও ঘোষণা দেয়, ‘নাটক হোক জীবনের প্রকাশিত সত্য। মঞ্চ আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র, নাটকের মাধ্যমে শ্রেণী যুদ্ধের চেতনাকে ত্বরান্বিত করে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের যুদ্ধ।’ উনিশশো তিরাশি সালে চট্টগ্রাম থিয়েটার-এর জন্ম। এই দলের ঘোষণার মধ্যে ছিলো ‘শ্রেণী বিপ্লবের আকাঙ্খা চট্টগ্রাম থিয়েটারের নাটক নির্মাণের মূল উপজীব্য। আজকের সমাজের দীনতা আমাদের বিক্ষুব্ধ করে তাই আমরা এর পরিবর্তন চাই। উনিশশো বিরাশি সালে রাজবাড়ি জেলার পাংশাতে থিয়েটার সেন্টারের জন্ম।
পরবর্তী সময় থিয়েটার সেন্টারের কার্যক্রম ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। থিয়েটার সেন্টারের ঘোষণায় বলা হয়, থিয়েটার সেন্টার দেশের চলমান নাট্য আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ করে সমাজ সচেতন করার মাধ্যমে দেশের সহায় সম্বলহীন ক্ষয়িষ্ণু শোষিত জনগণের মুক্তি অনিবার্য করতে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী। যা ধ্বংস করবে সামাজিক বৈষম্য এবং শ্রেণীস্বার্থের দেয়াল। উনিশশো ছিয়াশি সালে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জের জীবন সংকেত নাট্যগোষ্ঠীর শ্লোগান ছিলো, নাটক হোক গণচেতনার হাতিয়ার। উনিশশো তিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার মহাকাল নাট্যসম্প্রদায় ঘোষণা দেয়, ‘এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মজুর খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের জীবন হোক আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু’।
উনিশশো একাশি সালে প্রতিষ্ঠিত সিলেটের সন্ধানী নাট্যচক্রের বক্তব্য ছিলো, ‘আজকের সমাজের দীনতা আমাদের বিক্ষুব্ধ করে তাই আমরা এর পরিবর্তন চাই। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। সমাজের প্রতিটি স্তরকে ভেঙেচুরে আমরা এর নোংরা জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করতে চাই মানুষের সামনে।” সিলেটের কথাকলির বক্তব্যও ছিলো অনুরূপ, শিল্প এবং শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করেই আমরা আমাদের হাত উত্তোলিত করেছি। ঢাকার কুশীলব নাট্য সম্প্রদায়ের জন্ম উনিশশো আটাশি সালে। এদের ঘোষণা ছিলো, নাটক হবে সংগ্রামী মানুষের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার শক্তিশালী গণমাধ্যম।” উনিশশো চুরাশি সালে চট্টগ্রামের মঞ্চমুকুট নাট্যসম্প্রদায়-এর জন্ম।
এই দলের ঘোষণায় বলা হয়েছিলো, ‘নাটক হোক শ্রেণীচেতনা বিকাশের হাতিয়ার’। উনিশশো একাশি সালে প্রতিষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের রূপক নাট্যগোষ্ঠী ও ঢাকার দৃষ্টিপাত নাট্য সম্প্রদায়েরও বক্তব্যে বলা হয়েছিলো, নাটক শ্রেণীসংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। ঢাকার গণছায়া সাংস্কৃতিক সংগঠন, নরসিংদীর কল্লোল নাট্যগোষ্ঠী, কুষ্টিয়ার অনন্যা’ ৭৯, সিরাজগঞ্জের তরুণ সম্প্রদায়, ফেনীর সুবচন নাট্যদল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকাল নাট্যচক্র-এদেরও বক্তব্য ছিলো একইরকম। বিশ্বনাটকের ইতিহাসে নানারকমভাবে নাট্যকলায় ব্যবহৃত হয়েছে রাজনীতি।
কখনও প্রচার নাটকের প্রত্যক্ষ শ্লোগানে, কখনও সাংকেতিক কাব্যময়তায়, কখনও সমাজ বিশ্লেষণে, কখনও বা সরাসরি মার্কসীয় ব্যাখ্যায়। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের যে ঘোষণা দিয়েছিলো তা মূলত মার্কসীয় রাজনীতির কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পিসকাটর-ব্রেন্ট-উৎপল দত্ত প্রমুখ মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেন নিজ নিজ দলের নাট্যচর্চায় এবং সত্যিকারভাবেই তাঁদের নাট্য প্রযোজনা ছিলো শ্রেণীসংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলোর শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণার পর নাট্যদলগুলোর প্রযোজনায় সত্যিই কি শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছিলো, এ প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক।
সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনকে ভীষণভাবে আমরা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে জড়িয়ে পড়তে দেখি আশির দশক থেকে। সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় যেমন নাট্য দলগুলো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তেমনি সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামে। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের অপেক্ষাকৃত কম প্রতিষ্ঠিত দলগুলো নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টি তাদের চিন্তায় বা দলিলপত্রে স্থান দিতে থাকে। কিন্তু দলীয় কর্মকাণ্ডে বা নাট্য প্রযোজনায় শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারেই ধরা পড়ে না। বাংলাদেশের কিছু কিছু নাট্যদল যেভাবে তাদের ঘোষণায় শ্রেণীসগ্রামের কথা ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গের অনেক নাট্যদলের ঘোষণাতেও তা লক্ষ্য করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ প্রচার করেছিলো যা সেখানকার গ্রুপ থিয়েটারগুলি করেনি।
বাংলাদেশের নাট্যদলগুলির একাংশ সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে পাশাপাশি নিজেদের আবার গণনাট্য কর্মী না বলে গ্রুপ থিয়েটার কর্মী বলে দাবি করলো। নাট্যদল বা নাট্যকর্মীদের বিভ্রান্তি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা তথা ভারতে গণনাট্যই ছিলো মার্কসবাদী ধারায় পথিকৃত, গ্রুপ থিয়েটার নয়। এরুপ থিয়েটার কখনও কোথাও নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করেনি।
স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের নাট্য দলগুলোর শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণার পেছনে তৎকালীন কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব ছিলো। চারু মজুমদারের নকশাল বাড়ির রাজনীতি, সিরাজ সিকদারের গোপন রাজনীতি ও জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান যুবমানসে এবং ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদের পক্ষে একধরনের সহানুভূতিশীল মন গড়ে তুলেছিলো। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশকে সাহায্যদানও মার্কসবাদের প্রতি যুবসমাজের সমর্থন আদায় করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে স্থান দেয়া হয়। মার্কসবাদ সম্পর্কে এই প্রচার বা মার্কসবাদ নিয়ে ব্যাপক হৈ চৈ শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি নাট্যকর্মীদের আকৃষ্ট করে। মার্কসবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করে বা ভালোভাবে জেনে নাট্যকর্মীরা এ পথে আসেনি। বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তাটি তাই কোনো সুপরিকল্পিত চিন্তা নয়।
মার্কসবাদী চিন্তা থেকে যেমন এর জন্ম নয়, তেমনভাবে কোনো মার্কসবাদী দলও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না। নাট্যকর্মীদের এ ধরনের ঘোষণা ছিলো চমক সৃষ্টির প্রয়াস, নিজেদের অতিবিপ্লবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়া। নাট্যকর্মীদের শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেয়ার পিছনে বিশেষ একটি পটভূমিকা ছিলো। সত্তর দশকে বেশ কিছু সমালোচনাতেই স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্যচর্চাকে মধ্যবিত্তের থিয়েটার বলা হচ্ছিলো। সত্যিকার অর্থে তারা যে মধ্যবিত্তের থিয়েটার করছে না তা প্রমাণ করার জন্যই আরণ্যক নাট্যদলের পক্ষ থেকে নাটককে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার বলা হয়। বিভিন্ন দলগুলোকে এই শ্লোগান অনুপ্রাণিত করে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সত্তর দশকে যারা শিল্পকলা একাডেমীর বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের কোনো দলের লক্ষ্যের মধ্যেই ‘শ্রেণীসংগ্রাম’ ব্যাপারটি ছিলো না।
আরণ্যকের ঘোষণার পর থেকেই এই শ্লোগান ব্যাপকতা পেতে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বাংলাদেশের সবগুলো নাট্যদল শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেয়নি। শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন গড়ে ওঠা দলগুলি। পাশাপাশি যারা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নাটক করার ঘোষণা দেয়, তারা কোনো শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না। ব্যক্তিগতভাবে তারা যে সকলে মার্কসবাদী ছিলো এমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। মূলত মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের কোনোই সম্পর্ক ছিলো না। যারা এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছিলো, নাটকের অঙ্গনে তাদের বেশিরভাগের কোনো গুরুত্বও ছিলো না। নাটক রচনা, নাটক পরিচালনা, এমনকি নাট্যাভিনয়েও তারা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।
সর্বোপরি তাদের নাটকে শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়বস্তু ছিলো না বললেই চলে। সংগ্রামী বিষয়বস্তুও এসেছে খুবই কম। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদের যে-অংশ নিজেদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের বঞ্চনা দারিদ্র্য ও মুক্তির লড়াইকে নাটকের উপজীব্য করে তুলতে চান, কোনো সন্দেহ নেই তাঁরা একটি নতুন আন্দোলনের স্রষ্টা এবং তাদের এই প্রচেষ্টারও একটি গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই প্রশ্নটিও স্বাভাবিক সেই আন্দোলনকে কতদূর তাঁরা নিয়ে যেতে পারেন বা নিয়ে যেতে পেরেছেন।
বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সকলেই একমত হবেন এমন নয়। তবে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করলে সকলেই মেনে নেবেন যে বাংলাদেশের বিদ্যমান শাসন-শোষণের প্রধান রক্ষক ও প্রতিপালক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের এই সক্রিয়তা অভ্যন্তরীণ গণশত্রু কিংবা শ্রেণীশত্রু সমূহের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গেই সম্পর্কিত। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা তাই দেশীয় শোষক-শাসক শক্তিসমূহের বিরোধিতা ছাড়া যেমন সম্ভব না তেমনি আরেকদিকে এসব শক্তিসমূহের কার্যকর বিরোধিতা কখনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ছাড়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের নাটকে যাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম প্রচারের কথা বলেছিলেন, তাঁদের নাটকে তো নয়ই, কোনো নাটকেই এ বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়নি।
শ্রমিকশ্রেণীর সাথেও এসব দলগুলোর যেমন কোনো সম্পর্ক ছিলো না, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তারা নাটক করেনি এবং তৎকালীন শ্রমিক-আন্দোলনের কোনো ঘটনা তাদের নাটকের বিষয় হয়ে ওঠেনি। অথচ আশির দশকে নানা ধরনের শ্রমিক আন্দোলন চলছিলো নানা স্থানে। নানা ধরনের শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠছিলো নিজ নিজ দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য। নাট্যদলগুলোর শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করবার, তাদেরকে নাটকের বিষয়বস্তু করে তুলবার মতো বহু ঘটনা ছিলো, বহু সুযোগ ছিলো।
বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে, মাঠে-ঘাটে লাখ লাখ ভাসমান অসংগঠিত শ্রমিক কাজ করে। পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, কুলি, দিনমজুর, রিকশা- শ্রমিক ইত্যাদি প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক। শতকরা আটানব্বই ভাগ শ্রমিকই অসংগঠিত, কোনো সংগঠন করে না। এ সকল শ্রমিকদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই, কোনো আইনের স্বীকৃতি নেই। অর্ধাহার, অনাহার আর মানবেতর জীবন এদের নিত্য সঙ্গী। শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শোষণ পীড়ন চালাবার জন্য এই শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে রাখে। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করে তোলার জন্য গড়ে তুলেছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্ব-স্ব রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন।
বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে আছে এই সব দালাল সংগঠন ও নেতারা। এরা শ্রমিক দরদী সেজে লম্বা লম্বা বুলি আওড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে রাখে। শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যবহার করে এরা নিজেদের প্রতিপত্তি গড়ে তোলে। শ্রমিকশ্রেণীকে মূল সমস্যা ও মূল অর্থনৈতিক দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূল শ্রেণীচেতনা থেকে সরিয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা নিজেদের বাঁচা-মরার প্রশ্নে এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে সামরিক শাসনকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নানা ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলে আশির দশকে।
উনিশশো বিরাশি সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। সামরিক শাসন জারি করলে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ বন্ধ করা হয়। শ্রমিকসমাজ সামরিক শাসন মেনে নেয় না। তিরাশি সালের ছাব্বিশে মার্চ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রমিক সংগঠনগুলোর এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তিরাশি থেকে নব্বই সন জুড়ে শ্রমিক লীগ স্কপের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালায়। ধর্মঘট, সমাবেশ, মিটিং মিছিল, ঘেরাও প্রচারান্দোলনই ছিলো আন্দোলনের ধারা।সামরিক শাসনের প্রথম দিকেই, সামরিক শাসন জারি করার পর পঞ্চাশ হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ঢালাওভাবে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের কালে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবির প্রতি সরকার সীমাহীন উপেক্ষা প্রদর্শন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন ও সংগঠন ধ্বংস করার জন্য রাতারাতি পেটোয়াবাহিনী গড়ে তোলে এবং শত শত শ্রমিক ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করা হয়।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 4 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৪.jpeg)
চুরাশি সালে শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের দাবিদাওয়ার পক্ষে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ছেচল্লিশ ঘন্টা হরতাল পালন করে।বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই পাটকলগুলো নানা দৈন্যদশায় পড়ে এবং শ্রমিকরা ভীষণভাবে অবহেলিত হতে থাকে। আশির দশকে পাটকল শ্রমিকরাও তাদের নানা দাবি দাওয়ার প্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করে। বিশেষ করে তাদের পাওনা বোনাস ‘ও বকেয়া বেতনের জন্য। তিরাশি সালের আগস্ট মাসে সামরিক আইনের তোপের মুখে চটকল শ্রমিক ফেডারেশন ও সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন রাজপথে নামে। শ্রমিকরা সাত দফা দাবি প্রদান করে এবং দাবিগুলোর পক্ষে শ্রম দফতর প্রাঙ্গণে গণ-অনশন করে। পরবর্তী গণঅনশন চলে আদমজী জুট মিলে।
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হয় জুট মিল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ। চুরাশি সনের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জের এগারো হাজার শ্রমিক শতকরা তিরিশ ভাগ মহার্ঘভাতার দাবিতে বারো দিন ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে একজন শ্রমিক নিহত ও সাতজন আহত হয়। চুরাশি সালের নভেম্বর মাসে অর্থাভাবের অজুহাতে মোহিনী মিল বন্ধ করে দেয়া হলে বত্রিশ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে, তাদের চাকরির কোনো পূর্বশর্ত ছিলো না।
শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে, পতিত হয় নিদারুণ অর্থসংকটে। মিলটি চালু করা ও শ্রমিকদের পুনরায় চাকরিতে বহাল করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালায়।* চুরাশি সালের উনত্রিশে মার্চ রিকশা-শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ ট্রাক চালিয়ে দেয়, এতে চারজন রিকশাশ্রমিক নিহত হয় ও সতেরো জন আহত হয়। পুলিশ তাদের ওপর গুলিও চালায়। জহিরুল ইসলাম নামে এক রিকশাচালককে ছুরিকাঘাত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রিকশাচালকেরা পরপর দুদিন হরতাল পালন করে। ২৫ পঁচাশি সালে রংপুরে দুজন রিকশাচালককে মারধর করলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও রংপুর জেলা শহরকে অচল করে দেয়।
ঢাকায় জনৈক যাত্রী এক রিকশাচালককে ছুরিকাঘাত করলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে চল্লিশ হাজার রিকশাচালক ও অন্যান্য স্তরের জনগণ তাতে অংশ নেয়। প্রশাসন ও পৌর কর্পোরেশনের বিভিন্ন জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেও রিকশাওয়ালারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনে নামে। ছিয়াশি সালের তেরোই ডিসেম্বর এয়ারপোর্ট রোডকে ‘ভিআইপি রোড’ ঘোষণা করে সরকার রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা মেট্রোপলিটন রিকশাচালক সংগ্রাম পরিষদ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন রিকশাচালক-মালিক ঐক্য পরিষদ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।
স্কপ উনিশশো সাতাশি সালের বারোই জুলাই চব্বিশ ঘন্টার পূর্ণ দিবস হরতাল ডাকে, সুইপার সংগ্রাম পরিষদ তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। তারা ঢাকা পৌর কর্পোরেশানসহ মহানগরীর সকল অফিস-আদালত ও কল-কারাখানায় সুইপারদের চাকরিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে ঐদিন পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে।” বাংলাদেশের ঠেলাগাড়ি, টানাগাড়ি ও বুলগাড়ি মালিক সমিতি উনিশশো আটাশি সালের ছয়ই ডিসেম্বর চব্বিশ ঘন্টা তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেয়ার জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশ ঘটায়। গাড়ি চালানো বন্ধ রেখে ঐ দিনের সমাবেশে তারা সাত দফা দাবি প্রদান করে। উনিশশো আটাশি সালে ঢাকার শ্যামপুর ডায়মণ্ড স্টিল ও দি শামছির ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে মালিকদের গুলিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের দুজন কর্মী সুজন ও ফজলু নিহত হয়। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে।”
বাংলাদেশে এইভাবে যে-সকল শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে কোনো নাট্যদলই তার সাথে কখনও কোনো ধরনের সংহতি প্রকাশ করেনি। সে সকল শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাগুলোকে তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও স্থান দেয়া হয়নি, যা আমরা পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্যের নাটকে দেখতে পাই। গণনাট্য সংঘ যেমন শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনকে সাহস জোগাতে, তাদের সচেতন করে তুলতে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে নাটক মঞ্চায়ন করেছে, তাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাগুলোকে তাদের নাটকের বিষয় করে তুলেছে, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে কখনই তা ঘটেনি। শহরের মধ্যবিত্তের মঞ্চের মধ্যেই তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিলো। কথিত এই দশকে নাট্যকর্মীরা আসলে নানা ধরনের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।
কারোরই রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার ছিলো না। যে-সব দল শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছে, প্রথমেই প্রমাণ করা জরুরি হয়ে পড়ে এই দলগুলো, দলের প্রতিটি সদস্য মার্কসবাদ বা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মানেন কি না। বাংলাদেশে এমন দল আমরা পাই না যারা শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই দলের সকল কর্মী মার্কসবাদী। বরং উল্টোটাই সত্যি। নাট্যকর্মীদের অনেকে শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিলেও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবের জন্যই শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন।
শ্রমিক-কৃষকদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন বাদ দিয়ে নাট্যদলগুলো দর্শকদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করে, যা কোনো পরিণতি লাভ করে না। কোনো কোনো দল কালে ভদ্রে নাটক নিয়ে শ্রমজীবীদের মধ্যে যে যায়নি এমন নয়। তবে এদের মূল লক্ষ্য ছিলো অভিজাত মঞ্চ ও অভিজাত দর্শকদের স্বীকৃতি। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শম্ভু মিত্র পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চা সম্পর্কে লিখছেন, ‘নিম্ন মধ্যবিত্তদের মাঝেই আমাদের প্রচার। মজুরদের কথা অবশ্য সময়ে সময়ে আস্ফালন করে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা আস্ফালন মাত্র, সত্যিকার কাজ কিছু হয়নি।… সকলেরই ভিড় মধ্য পাড়ায়। এই মধ্যবিত্তদের অনেকেই কেরানি বা কেরানি-মনোভাবাপন্ন।
যে মধ্যবিত্ত একদিন নতুন সভ্যতা এনেছে, দিকে দিকে নিজের বল প্রসার করেছে, এরা তারা নয়।’ কলকাতার নবনাট্য চর্চা বা গ্রুপ থিয়েটার চর্চা সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্য, বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবেই প্রযোজ্য। নাট্য আন্দোলন নামক নাট্যচর্চা এবং তার ফলাফল যদি সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে বাকি কোটি কোটি নিরন্ন নিরক্ষর মানুষের কাছে এই নাট্য আন্দোলনের কোনো মূল্য নেই। পাশাপাশি একথাও সত্য, রাজধানী বা বিভিন্ন শহরে নাটক মধ্যবিত্তদের মধ্যেই মঞ্চস্থ হবে। কিন্তু মঞ্চস্থ নাটকের বিষয়বস্তু যদি মধ্যবিত্তদের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে লড়তে উদ্বুদ্ধ না করে সেক্ষেত্রে সেই নাট্যশিল্পের কোনো বৈপ্লবিক সত্তা তৈরি হয় না।
শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইকে সংঘবদ্ধ করতে যদি নাট্য আন্দোলন কোনো ভূমিকা রাখতে না পারে তাহলে তা ব্যর্থ। নাটকের দলগুলো নানাভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলো সন্দেহ নেই, তবে তারা কার পক্ষে এবং কী উদ্দেশ্যে নাটক করছিলো তা বোঝা যাচ্ছিলো না। কোন্ ধরনের সরকার বা শাসনপদ্ধতি তারা আশা করে এ ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য ছিলো না। সামরিক সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করলে মূলত সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে অংশ নেয়। নাট্যকর্মীরা কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত না করেই সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং মিছিলে, সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।
বিষয়টা খেয়াল করার মতো, সামরিক শাসক এরশাদের শাসনকালে প্রথম নাটকের লোকেরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করে যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। নাট্যকর্মীদের ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে রামেন্দু মজুমদার চুরাশি সালে থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখছেন, ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন জোরদার হয়েছে।… গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকল্প গণতন্ত্রই-সামরিক শাসন নয়। সংস্কৃতি কর্মীরা দেশের এই বৃহত্তর গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।’
সাতাশি সালে রামেন্দু মজুমদার পুনরায় থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখছেন, ‘দেশে এখন চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছে। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে দেশব্যাপী যে প্রবল গণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে সংস্কৃতিকর্মীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।… চলমান আন্দোলনে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীরা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।
এরশাদের শাসনামলের এই ব্যাপারটি খুবই লক্ষ্যণীয় যে, জনগণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা আবার রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। সত্তরের নির্বাচনে কিংবা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে ধরনের ঐক্যবদ্ধ হবার ঘটনা ঘটেছিলো, এ ক্ষেত্রেও প্রায় তাই হয়। যখন সমগ্র জাতি কোনো একটি লক্ষ্যে এক হয়, দেখা গেছে সাংস্কৃতিক কর্মীরাও সেখানে খুব সাহসী হয়ে ওঠে। জাতি যখন রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত নাট্য দলগুলো তখন আর রাজনীতির মাঠে ততোটা সক্রিয় থাকে না।
আশির দশকের শুরুতে নাট্যকর্মীরা এটা বুঝেছিলেন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বা সামরিক শাসককে উৎখাত করা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব। সে ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিকতারও অভাব ছিলো না। তবে মঞ্চের নাটককে সে কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁদের দুর্বলতা যথেষ্ট পরিমাণে ধরা পড়ে।
সামরিক শাসনামলে নাট্য দলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেল, তারা মঞ্চের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় রাজপথে। মঞ্চের নাটকে রাজনীতি যতোটা এসেছে তার চেয়ে তাদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ধরা পড়েছে মঞ্চের বাইরে, রাজপথে সভা-সমাবেশে। রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন বিপুল উৎসাহে, মঞ্চের নাটকে সেই ঘটনাবলীকে তাঁরা তুলে ধরতে পারেননি তেমনভাবে। যা নাট্যকর্মীদের যোগ্যতা ও নাট্য বিষয়ের ওপর তাঁদের পারদর্শিতা সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি করে। রামেন্দু মজুমদার নাট্যকর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে ঠিক এই সময়েই লিখেছিলেন, ‘আমরা কেবল দেখব তাঁর নাট্যকর্মে তিনি তাঁর দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছেন।
সামাজের শোষণ, বঞ্চনা ইত্যকার নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সোচ্চার কি না-এটা অবশ্যই আমরা বিবেচনায় আনব। শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করবেন নাটকের মধ্য দিয়ে, রাস্তায় মিছিল বার করে বা সভা-সমিতি করে নয়। তার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। ‘রামেন্দু মজুমদার এক অর্থে ঠিকই বলেছেন। নাট্যকর্মী বা নাট্যকারের মূল্যায়ন হবে প্রদর্শিত নাটকের ওপর।
নাট্যকর্মীরা যদি তাঁদের নাটকে ঠিকমতো রাজনীতি প্রচার করতে না পারেন তাহলে নাট্যকর্মী হিসাবে তিনি ব্যর্থ, যতোই তিনি রাজনৈতিক সভা বা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন না কেন। মঞ্চের দায়িত্ব সঠিকভাবে, সার্থকভাবে পালন না করে সারাদিন রাস্তায় সভা সমাবেশ করে বেড়ালে তিনি নিজের মূল দায়িত্বটিই পালন করলেন না। নাটকে তিনি রাজনীতি না এনে, নাটকের মাধ্যমে জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে না ধরে তিনি যদি রাস্তায় বা মাঠে রাজনীতি করে বেড়ান, তাহলে তাঁকে রাজনৈতিক কর্মী বলা গেলেও নাট্যকর্মী বলা যাবে না।
রামেন্দু মজুমদারের বক্তব্যে যেমন সত্য আছে, তেমনি আবার তাঁর বক্তব্য আমাদের বিভ্রান্তির মধ্যেও ফেলে দেয়। রামেন্দু মজুমদারের বক্তব্য থেকে মনে হয় নাট্যকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীর দায়িত্ব শুধু ভিন্নই নয়, একজন আর একজনের জায়গায় যেতে পারবেন না। অথচ রামেন্দু মজুমদার নিজে নাট্যকর্মীদের সাথে রাজপথের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। শুধু অংশ নেয়া নয়, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে নাট্যকর্মীদের নেতার ভূমিকা পালন করেছেন।
তারপরে তিনিই এ ধরনের একটি বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি যে কথা বলতে চান, রাস্তায় মিছিল সমাবেশ করা কিংবা সভা- সমিতি করার দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর সে বক্তব্য কি গ্রহণযোগ্য? জনগণের ব্যাপক একটা অংশ বহু সময়ই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন যাঁরা আদৌ রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো সদস্য নন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার সমস্ত মানুষেরই রয়েছে। একজন নাট্যকর্মী একই সাথে একজন রাজনৈতিক কর্মীও হতে পারেন কিংবা রাজনৈতিক কর্মী না হয়েও তিনি মিছিলে সমাবেশে অংশ নিতে পারেন।
বিশেষ করে একজন রাজনৈতিক নাট্যকর্মীর সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে অংশ নেয়া দায়িত্বের মধ্যেই পরে। রাজনৈতিক নাট্যকর্মীর মঞ্চে এবং রাজনীতিতে দু জায়গাতেই সময় দেয়া সম্ভব এবং দরকার। নাট্যকর্মী যদি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থাকেন তাহলে তিনি মঞ্চে রাজনীতিকে তুলে ধরবেন কী করে? রামেন্দু মজুমদারের দেয়া এ ধরনের বক্তব্য প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অমল রায়ের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো।
অমল রায় লিখছেন, ‘যাঁরা নাট্যকর্মীদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মাধ্যমে জড়িয়ে পড়ার বিরোধী, তাঁরা আসলে জলে নেমেও বেণী ভেজাতে রাজি নন। এঁদের প্রগতিশীলতার দৌড় মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার বাইরে বাস্তব জীবনে চলমান শ্রেণীযুদ্ধের রণাঙ্গনে সেই প্রগতিশীলতা কোনো সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে অস্বীকার করে।
কার্যত এই ধরনের বামপন্থীয়ানা একটা বিমূর্ত বায়বীয় শিল্পবিলাসিতামাত্র এবং তা নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।’ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম বলতে কিন্তু কখনই কোনো দলীয় বা উপদলীয় শক্তি প্রদর্শনকে বোঝায় না। কোনো দলের সদস্য না হয়েও একজন মানুষ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন। যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সারা দেশের ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করে কিংবা গুরুত্বের বিচারে যা সমসাময়িক কালে জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তা কিন্তু কখনই কোনো দলীয় গণ্ডিতে বাঁধা থাকতে পারে না। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাই প্রধান।
এবং একজন বিপ্লবী ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও সে দলের জন্য কাজ করতে পারেন বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে। রাজনৈতিক নাট্যকার ঠিক একইভাবে বিপ্লবের পক্ষে কাজ করতে পারেন, নাটকই সেখানে অস্ত্রের ভূমিকা নেয় বিপ্লবের পক্ষে প্রচার চালিয়ে। ৩৫ নাটকটা সেখানে বিপ্লবী কাজের বিশ্লেষণাত্মক প্রচার হয়ে উঠতে হবে।
বাংলাদেশের আশির দশকের নাট্যকর্মীরা রাজনীতি নিয়ে মাঠে যতোটা সক্রিয় ছিলেন, মঞ্চে ততোটা নয়। রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্ব বহন করে। নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবশ্যই রাজনীতি থাকতে হবে, শুধু মঞ্চের বাইরে সভা-সমাবেশ করলে হবে না। মঞ্চের নাটকেই তার রাজনৈতিক বক্তব্য স্পষ্ট হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা বেশ ব্যর্থতারই পরিচয় দেন। রাজনীতির মাঠে তাঁরা সোচ্চার হলেও মঞ্চে তারা রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। সামরিক সরকারের অভ্যুত্থান বা ক্ষমতায় আসবার কারণ নিয়ে শক্তিশালী কোনো নাটক কেউ রচনা করতে পারলেন না।
ঢাকার বাইরে তো নয়ই, ঢাকার মঞ্চেও নয়। সরাসরি এরশাদের শাসনকালকে নিয়ে ঢাকার বাইরে দু-একটি নাটক মঞ্চস্থ হলেও ঢাকায় কোনো নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। যে-সব নাটকে রূপকের মাধ্যমে বা আকারে-ইঙ্গিতে এরশাদকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছিলো, সে নাটকগুলোর বিষয়বস্তু ছিলো খুবই দুর্বল। ঢাকার বাইরের মঞ্চে বিশেষ করে জেলা শহরগুলোতে এসময় নাটক মঞ্চায়ন খুবই কমে এসেছিলো। আর যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হচ্ছিলো তার বেশির ভাগই পুরানো নাটক, সমকালীন রাজনীতির সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক ছিলো না বললেই চলে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মঞ্চে নতুন নতুন নাটক মঞ্চায়িত হলেও সেগুলোতে সমকালীন রাজনীতির চিহ্ন সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
ঢাকার মঞ্চে আশির দশকের প্রথম দিকে যে নাটকগুলো মঞ্চায়িত হয় তার একটা মোটামুটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। থিয়েটার এ সময় মঞ্চায়ন করে সৈয়দ শামসুল হকের এখানে এখন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে, আবদুল্লাহ আল-মামুনের অরক্ষিত মতিঝিল ও এখনও ক্রীতদাস। ঢাকা থিয়েটার মঞ্চায়ন করে সেলিম আল দীনের কীত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল। আরণ্যক মঞ্চায়ন করে মামুনুর রশীদের ইবলিশ, গিনিপিগ ও অবাহিকা, আবদুল্লাহ হেল মাহমুদের সাতপুরুষের ঋণ ও নানকার পালা।
ঢাকা পদাতিক মঞ্চায়ন করে এস এম সোলায়মানের ইংগিত। পদাতিক মঞ্চায়ন করে বের্টোল্ট ব্রেশটের মা। ঢাকা ড্রামা মঞ্চায়ন করে নভেন্দু সেনের ভাঙ্গা মানুষের পালা। নাট্যচক্র মঞ্চায়ন করে বাদল সরকারের রাজা রাজা খেল, ব্রেশটের ককেশিয়ান চক সার্কল। নাগরিক মঞ্চায়ন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন ও অচলায়তন, ব্রেশটের মোহনগরী, স্যামুয়েল বেকেটের গডোর প্রতীক্ষায়, সৈয়দ শামসুল হকের নুরুলদীনের সারাজীবন, কার্ল সুখমায়ারের কোপেনিকের ক্যাপ্টেন।
এই নাটকগুলির কোনোটিই সেই সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত নয়। নাগরিকের কোপেনিকের ক্যাপ্টেন-এ সামরিক বাহিনীর লোকরা নাটকের মূল চরিত্র হলেও রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বা বাংলাদেশে সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপট তাতে মোটেই ফুটে ওঠেনি। নাটকগুলোর অন্য গুরুত্ব হয়ত ছিলো তবে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এবং তাদের রাজনীতি, কিংবা সে সময়কার রাজনীতির কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসব নাটকগুলোতে ছিলো না।
ঢাকার বাইরের নাট্যচর্চায় এ সময় দেখা গেছে, প্রধানত ঢাকায় বা চট্টগ্রামে মঞ্চস্থ নাটকগুলোই তারা করছে, আবার স্থানীয় বা নিজস্ব নাট্যকারের নাটকও মঞ্চস্থ করছে। ঢাকার বাইরের দলগুলোর মঞ্চায়িত নাটকের তালিকায় প্রচুর নাট্যকারের নাম পাওয়া যাবে যাঁরা নাট্যকার হিসাবে যেমন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, তেমনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত জড়িত থাকেননি।
বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যে পাঁচজন নাট্যকার সারাদেশের নাট্যদলগুলোর কাছে এবং সুধীমহলে নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা সকলেই ঢাকার নাট্যচর্চার সাথে জড়িত। এই পাঁচজন নাট্যকার হলেন, মমতাজউদ্দীন আহমদ, সেলিম আল দীন, আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ ও সৈয়দ শামসুল হক।
পাঁচজন নাট্যকারের মধ্যে চারজনই বাহাত্তর সাল থেকে নাট্যকর্মের সাথে জড়িত হন। শামসুল হকের নাট্যকর্মের প্রথম সন্ধান পাই আমরা ছিয়াত্তর সালে। থিয়েটার প্রযোজিত পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম নাটক। পাঁচজনের পরেও আশির দশকে যাদের কমবেশি নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি ছিলো তাঁরা হলেন আবদুল্লাহেল মাহমুদ ও এস এম সোলায়মান। তাঁরাও ঢাকার নাট্যচর্চার সাথেই জড়িত ছিলেন। শেখ আকরাম আলী, রবিউল আলম, মিলন চৌধুরী, কাজী জাকির হাসান, প্রমুখের নাটক তখন বিভিন্নস্থানে মঞ্চস্থ হলেও নাট্যকার হিসাবে তাঁদের স্বীকৃতি সেভাবে আসেনি।
ফলে ঢাকার বাইরের নাট্যকারদের নাটক নিয়ে তেমন আলোচনার সুযোগ আমাদের এ অধ্যায়ে থাকবে না। সত্তর দশকের পরের নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি বুঝতে গিয়ে আমরা মূলত প্রথমে উল্লিখিত পাঁচজন নাট্যকারের নাটককেই গুরুত্ব দেবো। শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবো মামুনুর রশীদের নাটক ও আরণ্যকের প্রযোজনাগুলোকে।
ঢাকার আরণ্যক নাট্যদলের কিছু কিছু প্রযোজনা বিশেষ করে মামুনুর রশীদের কিছু কিছু নাটক নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করবো প্রাসঙ্গিকভাবে। এই দলটির মতে সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পকর্মের অবস্থান শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয় বটে। এই নাট্যদলটি ঘোষণা দিয়েছিলো, শিল্প বেনিয়ারা নিপাত যাক এবং জনগণ ফিরে পাক তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ। দলটির লক্ষ্য সম্পর্কে আরো বলা হয়, ‘নাটককে শুধু বৃহত্তর জনগণের কাছেই নিয়ে যাওয়া নয়, নাটকের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরা, যে দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে উজ্জীবিত করে।’
নিজেদের প্রচারপত্রে আরণ্যক আরো বলে, বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যুক্ত হলো নতুন অধ্যায় ওরা কদম আলী মঞ্চায়নের মাধ্যমে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় একটি বিশিষ্ট প্রতিবাদী ও শ্রেণীমনস্ক ধারার সূত্রপাত ঘটালো আরণ্যক যার ধারাবাহিকতায় এলো আরো দুটি নাটক ওরা আছে বলেই এবং ইবলিশ। কলকাতার নাট্যসমালোচক আশিস গোস্বামী লিখছেন, বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় আরণ্যক নাট্যদলের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।
তিনি লিখছেন, ‘বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যচর্চার অঙ্কুরিত বীজ থেকে মহীরূহে পরিণতি দানে আরণ্যকের ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য। তাই আরণ্যকের ইতিহাস বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাস। বাংলাদেশের অন্যান্য নাটদলের তুলনায় আরণ্যকের স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্যণীয়। ৩৯ আশিষ গোস্বামী আরণ্যকের ওরা কদম আলী থেকে ময়ূর সিংহাসন পর্যন্ত সেই ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করেছেন এবং লিখছেন, ‘বাংলাদেশের বহু নাট্যদল সাড়া জাগানো প্রযোজনা দিয়ে কাজ শুরু করলেও তারা এক জায়গায় থেমে গিয়েছে। কিন্তু আরণ্যকের চেষ্টা ছিলো ক্রমবিকশিত হবার এবং তারা তা করে দেখিয়েছে। ‘
সমালোচক গোস্বামীর পাশাপাশি আরণ্যকের নিজের বক্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। আরণ্যক তাদের দলিলপত্রে লিখছে, ওরা কদম আলী ও ওরা আছে বলেই নাটক দুটি মঞ্চস্থ করার পরই আরণ্যক আবিষ্কার করে নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণীসংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। দর্শকের সাথে যোগাযোগ ও তাদের চিন্তার প্রতিফলন থেকেই তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্মে। ওরা আছে বলেই মঞ্চস্থ হয় উনিশশো আশি সালে।
যার অর্থ দাঁড়ায় তাঁরা নাট্যচর্চায় শ্রেণীসংগ্রাম ও রাজনীতিকে স্থান দেয় স্বাধীনতার নয় বছর পর। কিন্তু থিয়েটার পত্রিকায় ছিয়াশি সালের এক লেখায় মামুনুর রশীদ বক্তব্য দেন যে, স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরেই যখন মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যাগত কিছু যুবক দেখলো স্বাধীনতার পরেও দেশের অর্থনীতি বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে এবং স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে একচেটিয়া মুনাফা লুটছে সংখ্যালঘু মুৎসুদ্দিরা, তখন তারা সত্যিকারের বিপ্লব ঘটাবার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য নাটককে বেছে নিলো আরণ্যক প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে।
দুটো বক্তব্যের মধ্যে গরমিল ধরা পড়ে। মামুনুর রশীদ এক জায়গায় বলছেন, রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য বা বিপ্লবের স্বার্থে স্বাধীনতার পরপরই তাঁরা আরণ্যক গঠন করেন। পরে আবার বলছেন ওরা কদম আলী ও ওরা আছে বলেই নাটক দুটি করার পর তাঁদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা জন্মায়।
মামুনুর রশীদ বা আরণ্যকের বক্তব্য ও কাজে এ ধরনের গরমিল আরো লক্ষ্য করা যায়। যারা শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিচ্ছে, এই দলটিই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মুক্ত নাটকের অনুষ্ঠান করে। মামুনুর রশীদ পূর্বোক্ত লেখায় মুক্তনাটক করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ঢাকা শহরের মধ্যে নাটক মঞ্চায়ন সীমাবদ্ধ রেখে শ্রেণীসংগ্রামকে লক্ষ্যে পৌছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।
অথচ বাংলাদেশ পল্লী একাডেমীর সাথে সম্পাদিত সেই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি ছিলো, নাটকে জাগরণের কথা বলা যাবে কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলা যাবে না। নাট্যদল আরণ্যক তা মেনে নিয়ে মুক্তনাটক-এর কার্যক্রম শুরু করেছিলো। দলটির বক্তব্যের আরো স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। উনিশশো পঁচাশি সালে আরণ্যকের তিনশো একতম অভিনয়ের প্রাক্কালে যে উপলব্ধি তাতে বলা হয়, জনগণের সংগ্রাম ও তার আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। “” রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আরণ্যক উপলব্ধি করলো মহিলা সমিতির মাত্র সাড়ে তিনশত দর্শককে আনন্দ যোগান দেয়ার কারণে তারা তাদের দুর্লভ অভিজ্ঞতা ও শ্রমকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়।
এই চিন্তাকে সামনে রেখেই আরণ্যকের চিন্তায় কর্মে এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন।” আরণ্যকের সেই বৈপ্লবিক চিন্তাটি কী সেটা বোঝা দুরূহ। কারণ আরণ্যক মহিলা সমিতি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করার পরও সেই মঞ্চেই প্রধানত তাদের নাটকগুলো মঞ্চস্থ করেছে, যা নাট্যদলটির বক্তব্যের স্বাবিরোধিতাই প্রমাণ করে। তা সত্ত্বেও আরণ্যক নাট্য মঞ্চায়নে যে শ্রেণীসংগ্রামের বক্তব্য প্রচারের কথা বলে আমরা তাদের মঞ্চায়িত নাটকের প্রেক্ষিতে, সেগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো। বিশেষ করে আশির দশকের প্রথম দিকের মঞ্চায়িত নাটকগুলোকে বিশ্লেষণ করবো তাদের শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা বোঝার জন্য।।
মামুনুর রশীদকে এ সময় অনেকেই শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত করেন। যেমন রামেন্দু মজুমদার লিখছেন, ‘মামুনুর রশীদ আমাদের বিবেচনায় সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন। তাঁর নাটকে শ্রেণী সংগ্রাম বার বার ফিরে এসেছে।… তাঁর প্রায় সব নাটকেই সামাজিক শোষণ দেখানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং সবশেষে বিজয়। শোষিতকে অধিকার সচেতন করতে তাঁর নাটক একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। ‘৪” আতাউর রহমান লিখছেন ‘মামুনুর রশীদ যাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য শ্রেণী সংগ্রাম, তাঁর ‘ওরা কদম আলী’ নাটকের নায়ক কদম আলী, সে বোবা।
এই চরিত্রটি অনেকাংশে প্রতীকী, সে সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের চেহারা দেখে বারুদ্ধ হয়ে গেছে। এই বোবা মানুষটিকে আমরা নাটকের শেষে প্রতিবাদী চেতনায় প্রদীপ্ত খেটে-খাওয়া মানুষের নেতা হিসেবে দেখতে পাই।'”” বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখছেন, নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের জন্য নাটক লিখেছেন মামুনুর রশীদ। মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে নাট্যরূপ দেয়াই তাঁর নাটক সমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়। শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে অধিকার-সচেতন ও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে তাঁর নাটক পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। মামুনুর রশীদ সম্পর্কে অরাত্রিকা রোজী লিখছেন, ‘মামুনুর রশীদ রাজনীতি সচেতন সমাজ সচেতন ও শ্রেণীসচেতন নাট্যকার। তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিশ্বাসের জগতকে অবলম্বন করে।
শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নে মামুনুর রশীদ সম্পর্কে বা আরণ্যক নাট্যদল সম্পর্কে যে ধরনের বক্তব্য দেয়া হয়েছে সে ধরনের বক্তব্য অন্য কোনো দল কিংবা নাট্যকারদের সম্পর্কে দেয়া হয়নি। সেই সব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবো দলটির নাটক কতোটা রাজনৈতিক বা শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে ছিলো বা শ্রেণীসংগ্রাম প্রচার করতে পেরেছিলো। শ্রেণীসংগ্রাম বা রাজনৈতিক নাটকের কাজ হলো রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করা, পরিপুষ্ট করা, রাজনৈতিক বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করা, দর্শককে তত্ত্ব ও প্রয়োগে শিক্ষিত করে তোলা।
নাট্যদল হিসাবে আরণ্যক বা শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকার হিসাবে মামুনুর রশীদ তা কতোটা সাফল্যের সাথে করতে পেরেছেন সেটাই আমরা এখানে মূল্যায়ন করবো। জ্যোতি ভট্টাচার্য আমাদের দেখাচ্ছেন যে, মার্কসবাদ শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকারদের অনুচর হিসাবে চায় না। চায় সহকর্মী রূপে, তার নিজ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক অগ্রণী নেতা রূপে। বহু মানুষের গতানুগতিক জীবনের অসাড় চিত্তকে তিনি নাড়া দেবেন, জাগিয়ে তুলবেন, মানুষ মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবে। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী হবে। আমরা দেখবো মামুনর রশীদের দল বা তিনি নিজে শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকার হিসাবে তা কতোটা পেরেছেন।
মামুনুর রশীদের ওরা আছে বলেই নাটকটি মফস্বল শহরের একটি রেলস্টেশনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে রচিত। সেই নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে দেখা যায়, দরিদ্র-ছিন্নমূল মানুষ যারা রাতে রেলস্টেশনে ঘুমাতে আসে তাদের সাথে রেলস্টেশনের নিম্নস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লড়াই। রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্টেশনমাস্টার ও স্টেশনের অন্যান্য কয়েকজন কর্মচারীর সাথে জোটবদ্ধ নিম্নবর্গের মানুষের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। ছিন্নমূল এক নারীকে নিয়ে নিম্নস্তরের রেলকর্মী পয়েন্টসম্যানের সাথে অন্যান্য ছিন্নমূল মানুষের বিরোধ থেকেই সে আন্দোলনের শুরু। নাট্যকার ব্যক্তিগত পর্যায়ের সামান্য সে বিরোধকে বিরাট আন্দোলনে রূপ দেন এবং সেটাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলতে চান। কিন্তু নাটকের ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টি কোনো কিছুর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের কোনো পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠেনি।
সমস্ত শোষণ পীড়নের মূল উৎসের প্রতি আলোকপাত না করে নাট্যকার ছিন্নমূল মানুষের তাৎক্ষণিক ক্ষোভকে ঘিরে মহাবিদ্রোহ ঘটাবার আয়োজন করেন। ফলে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো বিরোধ ছাড়াই নাটকটি শ্রেণীসংগ্রামের ভাববিলাসিতায় পরিণত হয়। গল্পের কাঠামো ধরে তাই অনুধাবনের চেষ্টা করা যায়, নাট্যকার যে ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের এ আন্দোলন গড়ে তোলেন তা কতোটা বাস্তবসম্মত।
নাট্যকার তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে সাদা এবং কালোতে ভাগ করে ফেলেছেন। স্টেশনমাস্টার, সেনিটারী ইন্সপেক্টর, পয়েন্টসম্যান এ নাটকে শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ। আবার সহকারী স্টেশনমাস্টার, স্টেশনের ওয়ার্কশপের ওয়েল্ডার সালাম মিস্ত্রি শোষিতদের পক্ষের লোক। স্টেশনে আরো আছে ছিন্নমূল মানুষ, জীবন যাদের প্রতিদিনই কাটে বেঁচে থাকার সংগ্রামে।
এদের মধ্যে আছে হকার আজি, কুলি কাওছার, কাওছারের বৃদ্ধা মা, গ্রাম থেকে সদ্য আসা বিধবা ও এক সন্তানের মা আসিয়া। রাতে এরা সবাই স্টেশনে ঘুমিয়েই রাত কাটায়। স্টেশনে আরো আছে গ্রাম থেকে আসা উদ্বাস্তু ও কুলির পেশায় নিয়োজিত কালা, আছে মেথর গঙ্গারাম। কালা অসীম শক্তির অধিকারী এবং স্টেশনমাস্টার বা তার সঙ্গীদের হকুমে যা খুশি করার জন্য তৈরি। গ্রাম থেকে সদ্য আসা আসিয়াকে নিয়েই শুরু হয় বিরোধ। পয়েন্টসম্যান আসিয়াকে শহরের এক বাসায় কাজ করতে দিয়েছিলো। মানুষ ভালো না দেখে আসিয়া সে কাজ ছেড়ে এসে রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। পয়েন্টসম্যান জোর করে আবার আসিয়াকে সেই লোকের কাছে নিয়ে যেতে চায়। এই নিয়ে পয়েন্টসম্যানের সাথে বিরোধ বাধে সালাম মিস্ত্রি, কাওছার, আজি ও কাওছারের বৃদ্ধা মায়ের।
পরদিন সকালে স্টেশনে রেলওয়ের একজন বড় কর্মকর্তা আসার কথা। সে কারণে স্টেশন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে রাতে ঘুমিয়ে থাকা লোকদের স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য পুলিশ অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে কাওছারের বৃদ্ধা মা মারা যায়। সকিছুই ঘটে হঠাৎ। কাওছারের মার এই আকস্মিক মৃত্যুতে স্টেশনমাস্টার, পয়েন্টসম্যান, সেনেটারী ইন্সপেক্টর কেউই অনুতপ্ত হয় না। এমনকি ভীতও হয় না। যে-কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু বা হত্যা নিয়ে হৈ চৈ পড়তে পারে বলে বড় বড় ক্ষমতাবানরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, সেখানে স্টেশনমাস্টারের তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই।
বরং আজি কাওছারের মাকে কবর দিতে চাইলে পয়েন্টসম্যান হাশেম বলে, ‘শালা গরীবের আবার ঘোড়ারোগ।’ একটি হত্যাকাণ্ডের পর সত্যিকার অর্থে একজন পয়েন্টসম্যান এ ধরনের বক্তব্য রাখতে পারে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিস্ত্রি সালাম এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। মৃতদেহ নিয়ে যাতে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সেজন্য স্টেশনমাস্টার তাঁর সহকারীকে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার হুকুম দেয়। বাস্তবে একজন স্টেশনমাস্টার এই ক্ষমতা রাখে কি না নাট্যকার সে বিবেচনায় যাননি, নিজের খুশি মতো সংলাপ রচনা করেছেন। একটি হত্যার পর লাশের ব্যাপারটা চলে যায় পুলিশের হাতে। বিশেষ করে যেখানে স্টেশনমাস্টারের হাতে খুনটি ঘটেনি সেখানে সে কেন লাশের দায় বহন করতে যাবে।
নাটকে এরপর দেখা যায়, লাশ সরাতে সালাম বাধা দিতে চাইলে পয়েন্টসম্যানের হুকুমে কালা সালামকে স্টেশন থেকে বের করে দিয়ে লাশ নিয়ে চলে যায়। সকলের মিলিত শক্তির চেয়েও কালার একার শক্তি সেখানে বড় হয়ে ওঠে। কাওছারের মায়ের আর কবর হয় না। লাশ কী করা হয় তাও নাটক থেকে আর জানা যায় না। প্রশ্ন দাঁড়ায় একজন ছিন্নমূল কুলি একটি খুনের লাশ গুম করার দায়িত্ব নেবে কি না। সে কি জানে না, এরপর তাকে নানাভাবে পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু নাটকে আমরা দেখি লাশ গুম করা সত্ত্বেও কালা গ্রেফতার হয় না কিংবা পুলিশ তাকে কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ করে না। মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হয় না।
পুলিশের হাতে অসহায় কাওছারের মার মৃত্যুতে পরদিন স্টেশনে বিরাট আন্দোলন বা বিক্ষোভ দেখা দেয়ার কথা, সারা স্টেশনে এবং শহরে হৈ চৈ পড়ে যাওয়ার কথা, সাংবাদিকদের ভিড় জমে যাওয়ার কথা। নাটকে তার কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। সবকিছুই স্বাভাবিক থাকে। মার লাশ ফিরিয়ে দেবার জন্য কাওছার বা তার বন্ধুদের ছুটাছুটি, কাকুতি- মিনতি কিংবা একটি দাবি উচ্চারণ করতেও দেখি না। কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা যায় না। লাশটির কী হলো, দাফন হলো-না মর্গে পাঠানো হলো, নাকি গুম করে ফেলা হলো এ ব্যাপারে নাটক থেকে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।
নাট্যকার দেখাচ্ছেন, ঘটনার পর কালা অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। রাতে সে মেথর গঙ্গার সাথে মদ খেতে বসে। সালাম মিস্ত্রি সেখানে আসে কালাকে সুপথে ফেরাবার জন্য। কালাকে সে লাশ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। কালাকে সে বোঝায় পয়েন্টসম্যানের কথা মতো সে সকালে যা কিছু করেছে সেটা অন্যায়। কালা তখন ভালো মানুষের মতো বলে, সে তার চাকরির স্বার্থেই উপরওয়ালাদের হুকুম মতো কাজ করেছে। কালা একজন কুলি, রেলস্টেশনের একজন কুলি কার চাকরি করছে তা বোধগম্য নয়। কালার সংলাপ, ‘অগো কত শক্তি, অগো লগে মানুষ আছে, পুলিশ আছে।’ সালাম বোঝায় কালার গতরেও তো শক্তি আছে।
সবাই মিলে উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই হয়। নাট্যকার বিপ্লবী সালামের যে চিত্র দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, প্রতিবাদের জন্য সালাম মানুষের গতরের শক্তিতে বিশ্বাস করে। একটা রেল স্টেশনে বহু শ্রমিক থাকে। কুলি-মজুর থাকে। সালাম কাওছারের মার মৃত্যু নিয়ে তাদের সাথে কথা বলে না বা তাদেরকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করে না। সালাম শুধু কালাকেই এসব বোঝাতে আসে। যেন এক কালাকে সাথে পেলেই তার পক্ষে উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। শোষকশ্রেণীর মতো সেও কালাকে পেশীশক্তি হিসাবেই ব্যবহার করতে চায়।
মার মৃত্যুতে এবং মার কবর না হওয়াতে কাওছার স্টেশন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। আজি তাকে বাধা দেয়। কাওছার আজি আর আসিয়া মিলে ঠিক করে তারা স্টেশনে ফুলুরির দোকান দেবে। কাওছারের মার হত্যাকাণ্ড নিয়ে, লাশ দাফন করতে না দেয়া নিয়ে তারা কোনো কথা বলে না। সেটা যেন কোনো আলোচনার বিষয়ই নয়। এভাবেই নাট্যকার একটি ঘটনার পরিণতি শেষ না করেই অন্য ঘটনায় হাজির হন। পরের দৃশ্যে দেখা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই আসিয়ার ছেলেটাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেকে হারাবার জন্য আসিয়ার যে কোনো দুঃখবোধ আছে তাও মনে হয় না। ছেলের জন্য কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা, আসিয়া ছেলেকে খোঁজাখুঁজি পর্যন্ত করে না।
ঠাণ্ডা মাথায় বসে সে কাওছার ও আজিকে তার স্বামী খুন হবার গল্প শোনায়। গল্প শোনার পর আজি ও কাওছার আসিয়াকে বোন হিসাবে গ্রহণ করে। মেথর গঙ্গাও আসিয়াকে বোন হিসাবে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চায়। যে গঙ্গা নিজের বউ ও ছেলের জন্য খাবার জোগাড় করতে পারে না বলে রাতের বেশিরভাগ সময় মদ খেয়ে বাইরে কাটায়, তার আসিয়াকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চাওয়াটা কতোটা বাস্তবসম্মত?
নাট্যকার এখানে গঙ্গা চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে বাস্তবতাকে বর্জন করেন। নিজের কল্পনার সাথে বাস্তবতার সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হন।কাওছার, আজি ও আসিয়া যেদিন ফুলুরির ব্যবসা শুরু করে সেদিনই পয়েন্টসম্যান ও সেনিটারী ইন্সপেক্টর এসে লাথি মেরে দোকানের সব জিনিসপত্র ফেলে দেয়। সেনেটারী ইন্সপেক্টর নিজেই এবার আসিয়াকে তার বাসায় কাজ করবার প্রস্তাব রাখে। তার প্রস্তাবে আসিয়া সাড়া দেয় না। পয়েন্টসম্যান ওদের হাঁড়িপাতিল জোর করে নিয়ে যেতে চায়।
এসময় সেখানে আসে কালা। কোনোরকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই সে পয়েন্টসম্যানের কলার চেপে ধরে এবং জানতে চায়, আসিয়ার ছেলেকে সে কোথায় রেখেছে। নাটকের কোথাও কখনও পূর্বে আসিয়ার সাথে কালার পরিচয় হয়নি এবং আসিয়ার ছেলে হারিয়ে যাবার খবরও কেউ তাকে দেয়নি। স্বভাবতই আসিয়ার ছেলেসম্পর্কে কালার কিছুই জানার কথা নয়। কিন্তু নাট্যকার আমাদেরকে দেখান, কালা পয়েন্টসম্যানকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয়, আসিয়ার ছেলেকে ফেরত না দেয়া হলে পয়েন্টসম্যানের ছেলেকে ধরে আনা হবে। কালা আসিয়ার সাথে চেনা-জানা ছাড়াইএমনকি আসিয়ার ছেলের হারিয়ে যাবার খবর না শুনেই কেন পয়েন্টসম্যানের কলার চেপে ধরে সেটা যেমন বোঝা যায় না, তেমনি বোঝা যায় না আসিয়ার ছেলেকে কোন্ স্বার্থে পয়েন্টসম্যান ধরে নিয়ে যাবে।
যেখানে আসিয়ারই ছেলে হারানো নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই, সেখানে কালার কিছু না জেনেই হম্বিতম্বি করাটা ঘটনার বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এ ধরনের নানা অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে নাটকের ঘটনা এগিয়ে যায়। আসিয়া কালাকে হঠাৎ তার পক্ষে লড়তে দেখে তাকে ভাই বলে সম্বোধন করে। গঙ্গারাম এ সময় সেখানে আসে মদের বোতল হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কালা দীর্ঘদিনের মদের সাথী গঙ্গার হাত থেকে মদের বোতল নিয়ে সব মদ ফেলে দেয়। গঙ্গা ক্ষেপে গেলে কালা বোঝায়, যার ঘরে স্ত্রী-সন্তান আছে তার এসব সাজে না। কালার এক কথায় গঙ্গা দীর্ঘদিনের মদ খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দেয়। বাস্তবে কী কোনো মাতালের পক্ষে মুখের কথায় মদ ছেড়ে দেয়া সম্ভব? গঙ্গা মদ ছেড়ে দেবে বলার পর কালা বলে সেও আর মদ খাবে না।
মদ খাওয়া হচ্ছে গঙ্গাদের সংস্কৃতি, মেথরদের জীবনের সাথে যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গঙ্গার সমাজে তাই মদ্যপান খাওয়া নিন্দনীয় তো নয়ই, সেটা তাদের ঐতিহ্য। কালা মুসলমান। তার ধর্মে, তার সমাজে মদ সংস্কৃতি নয়, ঐতিহ্য নয় বরং নিন্দনীয়। মদ ছাড়া না ছাড়ার ব্যাপারে তাই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক হওয়ার কথা নয়। মদ খাওয়া না খাওয়ার সাথে বিপ্লবের বা সমাজ আন্দোলনেরও কোনো সম্পর্ক নেই। সেই মদ ছেড়ে দেয়ার সাথে গঙ্গার ভালো হওয়া, মন্দ হওয়ার সম্পর্ক কোথায়? মদ ছেড়ে দিলেই কেউ একজন ভালো মানুষ হয়ে যায় না। সেটা কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস, মার্কসবাদীদের বিশ্বাস নয়।
মামুনুর রশীদের উল্লিখিত নাটকে দেখা যায়, কালা ও গঙ্গা মদ ছেড়ে দেবে বলার সাথে সাথে সেখানে আসে সালাম মিস্ত্রি। আর আজি তখন চিৎকার করে ঘোষণা দেয়, ‘মিস্ত্রি ভাই, কালা ভাই মানুষ অইয়া গেছে’। মদ খাওয়াটাই যেন ভালো হওয়া মন্দ হওয়ার প্রধান বিষয়। সালামের কাছে পূর্ব ঘটনার জন্য মাফ চায় কালা। কালাকে দলে পেয়ে সকলে নিজেদের একজোট মনে করে। নাট্যকারের বিশ্বাস, বিপ্লবের জন্য কালার মতো পেশীশক্তিই দরকার। নাটকে তাই কালাকে দলে টানার পরেই সকলে আশ্বস্ত হয়।
কালাকে সাথে পাবার পরই তারা বিজয় লাভের স্বপ্ন দেখে। মানব সভ্যতার বিকাশকে পেশীগত বিকাশ দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে মানুষের চিন্তা ও শ্রম। মামুনুর রশীদের ওরা আছে বলেই নাটকে সেখানে পেশীশক্তিকে খুবই মূল্য দেয়া হয়। সেজন্য কালা অতিরিক্ত গুরুত্ব পায় সারা নাটকে। কালাকে দলে পাবার পর সালাম বিপ্লবী নেতার মতো বলে, আমরা যদি আমাগো শত্রু চিনবার পারি, বন্ধু চিনবার পারি তাইলে আমাগো কোনো দুঃখ থাকে না।
সালাম মিস্ত্রি সকলকে এসব বিপ্লবের কথা বোঝাতে থাকে। মামুনুর রশীদের নাটকে ছিন্নমূল মানুষকে এসব বিপ্লবের কথা বোঝাতে কোনো শিক্ষিত মানুষের দরকার হয় না, সাধারণ একজন মিস্ত্রিই এর জন্য যথেষ্ট। যদিও মার্কসবাদীরা মনে করেন সমাজবিজ্ঞান সচেতন মানুষরাই শ্রমিকশ্রেণীকে বা শোষিতদের এই শিক্ষা দিতে পারে। সর্বহারাশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন, তার কাছে সমাজতান্ত্রিক চেতনা আসে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে। লেনিনের বক্তব্য ছিলো, ‘সমাজতান্ত্রিক চেতনা এমনই একটা বস্তু যাকে সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে বাইরে থেকে-এর ভেতর থেকে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠেনি।
লেনিন সুনির্দিষ্ট করেই বলেছেন, বিজ্ঞানের বাহন সর্বহারাশ্রেণী নয়, বিজ্ঞানের বাহন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য হলো সর্বহারাশ্রেণীর কাছে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দেয়া। যদি চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে আসতো তবে এর কোনো প্রয়োজন হতো না। শ্রমিকরা নিজে নিজে কখনও সচেতন হয় না। বাইরে থেকেই সে চেতনা তাদের পৌঁছে দিতে হয়। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরাই তাদের মধ্যে প্রকৃত শ্রেণীচেতনা দান করবে। সেখানে মামুনুর রশীদের নাটকে মিস্ত্রির সামান্য বক্তব্যেই কালা নিজেকে পাল্টে ফেলে যা মার্কসবাদী চেতনার বিরোধী। প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সঠিকভাবে জানা নির্ভর করে জ্ঞানের ওপর। সে জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারো মধ্যে আসে না।” মামুনুর রশীদ সেখানে শ্রমিকদের, শোষিতদের বিপ্লবী চেতনাকে স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা হিসাবে দেখাচ্ছেন।
কালাদের মতো শ্রমিকদের সম্পর্কে মাও সেতুঙ লিখছেন, জীবিকা অর্জনের যথাযথ উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের মধ্যে অনেকে অন্যায় উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এদের কতককে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো কিনে নিতে পারে, আর কতক বিপ্লবে যোগদান করে। এসব লোকদের গঠনমূলক গুণাবলী নেই এবং গঠনের চেয়ে ধ্বংসের দিকেই এদের প্রবণতা বেশি। বিপ্লবে যোগদান করার পর এরা নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মাও সেতুঙ যে কালাদের নৈরাজ্যবাদী মনে করছেন, মামুনুর রশীদের নাটকে সেই কালাই এক ধাক্কায় সচেতন মানুষ বনে যায়। গঠনমূলক মানুষে পরিণত হয় কোনোরকম সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ছাড়াই এবং বিপ্লবী কোনো প্রক্রিয়ার পূর্বেই।
সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্রোহ করে এবং গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন হয় না। অথচ লেনিন বলেছিলেন, সহজে, যাদুর প্রভাবে, ভার্জিন মেরীর উপদেশে, শ্লোগানের ধাক্কায় শ্রমিকশ্রেণী তাদের কুসংস্কার মুক্ত হয় না। দীর্ঘস্থায়ী কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাদের কুসংস্কার দূর হয়।” গুস্তাভ লা বোঁ দেখান যে, ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ জনতার মনে দৃঢ় হতে এক শতাব্দীর বেশি সময় নিয়েছিলো শুধু প্রস্তুতি পর্বে। জনতার মনে বদ্ধমূল হওয়ার পরেই তা দুর্দমনীয় রূপ লাভ করেছিলো।” মামুনুর রশীদের নাটকে সেখানে কালা সালাম মিস্ত্রির দু-একটি বক্তব্যেই সচেতন হয়, জনতাও সঙ্গে সঙ্গে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়।
কিন্তু ব্রেস্ট দেখাচ্ছেন, মানুষ য়দি মানব সমাজের ইতিহাসের অংশ হয় তাহলে মানুষের বিশ্লেষণে ইতিহাসের প্রভাব, নানা চিন্তা ও ঐতিহ্যের প্রভাব অস্বীকার করলে মানুষের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত হতে বাধ্য। মামুনুর রশীদ ইতিহাস ও সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের বিচার বিশ্লেষণে গোড়ায় গলদ করে বসে আছেন।
নাটকের ঘটনায় এরপর দেখা যায়, পয়েন্টসম্যানকে কালা ভয় দেখিয়েছে বলে স্টেশনমাস্টার, সহকারী স্টেশনমাস্টার ও পয়েন্টসম্যান আলোচনায় বসে, নানারকম ষড়যন্ত্র করে। স্টেশনে সে-রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও আসিয়া জেগে থাকে। এই সময় ইন্সপেক্টর এসে জোর করে আসিয়াকে তার বাসায় নিয়ে যেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে আসিয়ার ডাকে সকলে জেগে ওঠে, ইন্সপেক্টরকে মেরে ভাগিয়ে দেয়।
স্টেশনমাস্টার, সেনিটারী ইন্সপেক্টর ও পয়েন্টসম্যান এবার একজোট হয়ে পুলিশ ডেকে আনে। পুলিশের সাথে মেথর গঙ্গার দ্বন্দ্ব শুরু হলে পুলিশ গঙ্গার গায়ে হাত তোলে। গঙ্গা ক্রোধে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে পালাতে গেলে পুলিশের গুলিতে মারা পড়ে। ক্ষুদ্র একটা বিষয়কে অকারণে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন নাট্যকার। যেখানে কোনো আন্দোলন এখনো দানা বেঁধে ওঠেনি সেখানে গঙ্গার পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নেয়া এবং পুলিশের গুলিতে মারা পড়া দুটোই অস্বাভাবিক নাটকীয় ঘটনায় পর্যবসিত হয়।
নাট্যকার গঙ্গার এই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তার চরিত্রকে মহত্ত্ব দান করতে চান। ব্রেন্ট নাটক রচনায় এ ধরনের মিথ্যা আবেগ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিলেন। ব্রেশটের ‘সিদ্ধান্ত’ নাটকে দেখা যায় বিপ্লবী একটি চরিত্র অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে বারবার শাসকশ্রেণীর ওপর আক্রমণ চালালে দল তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে। কারণ বিপ্লবীর আবেগপ্রবণতায় বিপ্লব এগিয়ে না গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ইতালীয় নাট্যকার আন্তনিও গ্রামশি বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণী শুধু ব্যরিকেডে লড়াই করে জয়যুক্ত হবে না, তাকে লড়তে হবে চেতনার জগতেও। তবেই তার সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। নাটকে পুলিশের হাতে গঙ্গার মৃত্যুর ঘটনাটা স্টেশনমাস্টারের ভিতর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বিরাট কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির মতো সে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হুকুম দেয় দ্রুত গঙ্গার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার জন্য। সিনিয়র সব অফিসররা আসছে তাই স্টেশন পরিষ্কার রাখতে হবে। ব্যাপারটা কি বাস্তবে এমন হতে পারে? স্টেশনের ভিতরে মেথরদের একজনকে পুলিশ গুলি করে মারা সত্ত্বেও সেটা নিয়ে স্টেশনমাস্টার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, স্টেশনমাস্টার রেলওয়ের কতো বড় কর্মকর্তা? স্টেশনমাস্টার নিজেও তো ক্ষুদ্রলোক, যাকে বলে ছাপোষা। নাটকে সেই ছাপোষা মানুষের সত্যিকার চরিত্রটি ফুটে ওঠেনি।
ব্রেস্ট বলছেন, বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে নাট্য চরিত্রটির বিবরণ দেয়া অসম্ভব যদি না তাকে তার শ্রেণী ও যুগের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। নাট্যকার এখানে ইন্সপেক্টরকে শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পাননি বলেই তার প্রকৃত . চরিত্রটি তুলে ধরতে পারেননি। ব্রেশটের নাটকে প্রত্যেক অভিনেতাকেই সচেতন থাকতে হতো যে তিনি একটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন।
তাঁর নাটকের মহড়ায় অনেকটা সময় ব্যয় করা হতো প্রত্যেকটি চরিত্রের রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝার জন্য। ব্রেস্ট মনে করেন, বৈজ্ঞানিক থিয়েটারের নাটকে চরিত্রকে কঠোরতম পরীক্ষা- নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগুতে হবে। চরিত্রগুলো দ্বন্দ্বসংকুল বাস্তবকে প্রতিফলিত করবে এবং তাকে অবশ্যই সংগ্রামজর্জর হতে হবে। তিনি কেন মার্কসবাদকে নাটক লেখার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে লিখছেন, ‘মার্কসবাদ এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জগতকে দেখতে শেখায়।
মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ বিশেষ পন্থার সূত্রপাত করে। বাস্তব চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ এক সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।’ তিনি আরো লিখছেন, ‘থিয়েটারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আচরণ নিয়ে আমাদের অধিকাংশ কাজ কারবার এবং মার্কসবাদের মূল নীতিগুলি ব্যক্তির বিচারের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। ‘৬২ মানুষের সামাজিক জীবনের সব ঘটনা যার ব্যাখ্যা দরকার, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসরণের মধ্য দিয়েই তার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব বলে পিসকাটর ও ব্রেন্ট মনে করতেন।
নাটকে এরপর লক্ষ্য করা যায় শোষিতদের মিলিত শক্তির লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। পয়েন্টসম্যান এসে স্টেশনমাস্টারকে খবর দেয়, কালা সব কুলি মজুর খালাসিদের নিয়ে গণ্ডগোল শুরু করেছে, সালাম মিস্ত্রিও কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। বড় সাহেবরা একটু পরই এসে পড়বে, স্টেশনমাস্টার ঘটনাকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ধাংগর পাড়া থেকেও শয়ে শয়ে লোক দা-ছুরি নিয়ে ছুটে আসে। সিগন্যাল রুম তারা দখল করে নেয়। যে ট্রেনে বড় কর্মকর্তার আসার কথা সে ট্রেনকে তারা স্টেশনের বাইরে দাঁড় করিয়ে দেয়। বড় কর্মকর্তা এ ঘটনায় ক্ষেপে যায়।
সবকিছু শোনার পর বড়কর্তা পুলিশকে জনতার ওপর গুলি চালাতে বলে। নাট্যকার নাটকে যা দেখান, বড়কর্তা আলোচনায় না বসে জনতার ওপর গুলি চালাতে বলে, সেটা কি কোনো বাস্তবসম্মত ঘটনা? জনতার মিছিলে গুলি চালাবার আগে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বহুবার চিন্তা করেন। রেলের বড় কর্মকর্তার কোনো পরিচয় দেননি নাট্যকার। শুধু বলা হয়েছে সিনিয়র অফিসার। সে অফিসারের গুলি চালাতে হুকুম দেয়ার ক্ষমতা আছে কি না সেটাও তো বিবেচনার ব্যাপার। একটি রাষ্ট্রে জনতার মিছিলে গুলি চালাবার হুকুম দেয়ার ক্ষমতা যেমন সবার থাকে না, তেমনি যার-তার হুকুমে পুলিশও জনতার মিছিলে গুলি চালায় না।
নাট্যকার এখানে বাস্তবতার চেয়ে নিজের খেয়ালকে প্রাধান্য দেন। সমাজবিজ্ঞানের চেতনার দ্বারা নয়, নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের দ্বারা ঘটনাকে সাজান। তিনি দর্শককে সচেতন করে তোলার চেয়ে, দর্শকের সামনে সমাজসত্য তুলে ধরার চেয়ে দর্শকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রেস্ট বলছেন, মানব সমাজের হাজারো দুঃখ দুর্দশার মধ্য থেকে সংগ্রহ করতে হবে আসল বিষয়বস্তুকে। সেই সাথে শিল্পীরও স্বাধীনতা থাকবে কল্পনা বিস্তারের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েই কল্পনার বিস্তার ঘটাতে হবে। নাট্যকারের স্বকীয়তা, রসবোধ, তার নিত্যনতুন আবিষ্কার তাঁর রচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
রচনার উদ্দেশ্য যদি কোনও না কোনভাবে শুধুই উত্তেজনার খোরাক হয় তবে তা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সমাজের অন্তর্গত যে দ্বন্দ্বের চাপে সমাজ বদলে যায় তার যথাযথ প্রতিফলন তাই মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে তুলে ধরতে পারেননি। নাট্যকার যে স্টেশনমাস্টার, পয়েন্টসম্যান কিংবা সেনিটারী ইন্সপেক্টরকে শোষকের দলে ফেলার চেষ্টা করছেন, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে তারাও শোষিতশ্রেণীর লোক।
বড়কর্তা যখন পুলিশকে গুলি চালাবার হুকুম দেয়, বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো তখন বলে, ‘কয়জনকে তোমরা শেষ করবা, আমরা হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি’। মঞ্চের সাদা পর্দা লাল হয়ে আসে। নাটকের শেষে এসে নাট্যকার যে কথা বলছেন, আমরা হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি-সেটা শ্রমিক আন্দোলনের কথা, গণ অভ্যুত্থানের কথা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে, সমাজ পাল্টাবার আন্দোলনে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনতা অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু ওরা আছে বলেই নাটকে কি সেরকম কোনো আন্দোলন মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়? সমাজ পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ বা কোনো গণ-অভ্যুত্থানের চেষ্টা কি সেখানে ছিলো?
নাটকের দ্বন্দ্বটি মোটেই রেলশ্রমিকদের সাথে রেল কর্মকর্তাদের নয় বা কোনো শ্রম শোষণ থেকে নয়। সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবার কিংবা রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের লড়াইও সেটা নয়। নয় তা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন। কিছু মানুষের ক্ষোভের জায়গা থেকে এই আন্দোলন বা নৈরাজ্যের শুরু। মামুনুর রশীদ এই নাটকে যে চরিত্রগুলোকে বিরাট আন্দোলনের সামনে নিয়ে এলেন, বিপ্লব বা সংগঠন করার কোনো পূর্ব ধারণাই নেই তাদের।
কোনো সংগঠন পর্যন্ত নেই। নাট্যকার তাদের হাতেই দিয়েছেন একটি বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব। মার্কসবাদ কখনো এ ধরনের ব্যক্তিদের হাতে নেতৃত্ব দেয়া সমর্থন করে না। একটি অভ্যুত্থান সফল করার পশ্চাতে নেতা এবং কর্মীদের যে শ্রম ও ত্যাগ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তার কিছুই দেখা যায় না। নাট্যকার আন্দোলন ব্যাপারটাকেই নাটকে খুব লঘু করে দেখিয়েছেন।
মামুনুর রশীদ ওরা আছে বলেই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ‘শ্রমিক শ্রেণী ও তার সাথে ছিন্নমূল মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের যে ইঙ্গিত এ নাটকে রয়েছে সমসাময়িককালের ঘটনাপ্রবাহেও সেই দিনের আগমন-ধ্বনি স্পষ্টতর হচ্ছে আমাদের কাছে। ‘৬৫ ব্যাপরটি কি সত্যিই তাই ছিলো? রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে দেশ ও সমাজ এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে ছিলো। মামুনুর রশীদ নাটক লেখার বিশ বছর পরেও বাংলাদেশে বিপ্লবের কোনো লক্ষণ দৃষ্টিগোচর নয়। দর্শন চৌধুরী লিখেছিলেন, জীবনে যার প্রস্তুতি নেই নাটকে সেটাকেই এতো সহজভাবে নিয়ে এলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। অতি-বিপ্লবীয়ানার ফানুস ব্যাপারটাকে একেবারে রূপকথার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।
মামুনুর রশীদ তার নাটকে শোষিতদের যে বিচ্ছিন্ন লড়াইকে দেখিয়েছেন মার্কসবাদীরা সে ধরনের কোনো লড়াইয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বা শোষিতদের একত্র করে না। মার্কসবাদীরা জানে সেটা কোনো চূড়ান্ত সফলতা দেয় না। মার্কসের দান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তার আগেই সমাজে এ ধরনের বহু গড়াইয়ে শ্রমিকদের অংশ নিতে মার্কস নিজেই দেখেছেন।
মার্কস শ্রমিকদের সে লড়াইকে সমাজবিজ্ঞানের চেতনা দ্বারা পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা বিছিন্নভাবে নয়, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অধীনে। রাজনৈতিক সংগঠন বাদ দিয়ে মার্কস এধরনের কোনো লড়াইয়ের কথা ভাবেননি। মার্কসীয় বিপ্লবে অংশ নেয়ার জন্য শ্রমিককে আগে সত্যিকার শ্রমিক হয়ে উঠতে হয়, শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। যে শ্রমিক সচেতন নয় মার্কস সে শ্রমিককে বিপ্লবী শ্রমিক মনে করেননি। লেনিন বলেছিলেন, সর্বহারাশ্রেণীর শক্তিকে তার সংখ্যা দিয়ে বিচার করা চলবে না। সর্বহারাশ্রেণীর ভূমিকায় নির্ধারক উপাদান তার সংখ্যাগত শক্তি নয়, বরং তার রাজনৈতিক শক্তি।
মামুনুর রশীদের সব নাটকেই এটা লক্ষ্য করা যায়, চিন্তা পড়ে থাকে বাস্তবের পিছনে। বাস্তবের সাথে সুসামঞ্জস্য রক্ষা না করেই তাঁর চিন্তা খেয়ালের বশে আগাতে থাকে। পরবর্তী সবগুলো নাটকেই তাঁর এই প্রবণতা লক্ষণীয়। মামুনুর রশীদ-এর অববাহিকা নাটকের ঘটনার কাঠামোও একই রকম। ওরা আছে বলেই নাটকের মতো সেখানে রয়েছে কিছু শোষিত মানুষ যারা শোষক জামান ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এসে শেষ দৃশ্যে শক্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।
সর্বহারার দল যে আগামীকালের রাজনৈতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, নাট্যকার তার ইঙ্গিত রেখেছেন সন্দেহ নেই, তবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য দিয়ে সত্যিকার বিপ্লবের উপলব্ধি দর্শকের কাছে পৌছায়নি। নাটকে শ্রেণীসংগ্রামের যে ভিত রচিত হবার কথা ছিলো তার সার্থক চিত্র অঙ্কনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পূর্বের নাটকটির মতো এখানেও চরিত্রগুলো সাদা-কালো দুভাগে বিভক্ত। যদিও মার্কসবাদ আমাদের শেখায় মানুষ নায়ক বা খলনায়ক কোনোটাই নয়। মানুষ হচ্ছে মানুষ। একটা বিশেষ অবস্থায় সে নায়ক হয়, আবার একটা বিশেষ অবস্থায় সেই লোকটাই খলনায়ক হয়। জীবনে নায়ক বলে কিছু নেই, খলনায়ক বলে কিছু নেই। যাকে আমরা হিরো বা নায়ক বলে থাকি, এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বে তার কোনো উল্লেখ নেই। নায়ক চরিত্র সম্বন্ধে ভাবনা পরবর্তীকালে উদ্ভূত।
প্রাচীন গ্রীক নাটকে নায়ক-খলনায়ক বানাবার ধারা না থাকলেও বুর্জোয়া থিয়েটার কাউকে নায়ক, কাউকে খলনায়ক বানাবার ধারা তৈরি করেছে। মানুষকে ভালো-মন্দ দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। চরিত্রগুলো সেখানে সূত্রবদ্ধ, নায়ক মানেই সাচ্চা কিংবা সৎ, খলনায়ক মানেই নিষ্ঠুর এবং কুটিল, সেখানে যেটা থাকে না তাহলো গুণ-দুর্বলতা- দ্বন্দ্ব সমেত মানুষ।
মার্কসবাদী নাট্যকার ব্রেন্ট সেই ধারা ভেঙে একই মানুষকে দোষ ও গুণের আধার করে দেখিয়েছেন, কোনো মানুষই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ভালো বা খারাপ নয়, সকলেই দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। প্রত্যেক মানুষ বা বস্তুর মধ্যেই একটা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকের যে সামগ্রিক প্রকাশ সেটাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্বের শিক্ষা। মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে বুর্জোয়াদের চিন্তাকেই ধারণ করেছেন। তিনি তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে নায়ক খলনায়ক বানিয়ে ভালো-মন্দ দুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন। তবে বুর্জোয়া মহৎ নাট্যকারদের মতো তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেননি।
মামুনুর রশীদের অববাহিকা নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে দ্বীপ অঞ্চলকে নিয়ে। জামান আন্দারমানিক দ্বীপের বনেদী পরিবারের সদস্য, শহরে থাকে। প্রয়োজন মতো সে দ্বীপেও আসে। দ্বীপটি মাঝে-মধ্যেই বন্যায় ভেসে যায়। বাঁধ দিয়ে এ বন্যাকে রোধ করা সম্ভব, অথচ জামান চায় না সে দ্বীপে কোনো বাঁধ দেয়া হোক। বন্যা হলে দ্বীপের অসহায় লোকজন জামানের কাছ থেকে ধারকর্জ নেয়, যার মধ্য দিয়ে তার পক্ষে সাধারণ দ্বীপবাসীর জমি দখল করা সম্ভব হয়। জামানের বিরুদ্ধে মানু গ্রামবাসীকে একত্রিত করে বাঁধ দেয়ার জন্য। মানুকে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য জামান ফাঁদ পাতে। মানুকে নিজ খরচে আরবদেশে পাঠিয়ে দিতে চায়, যাতে মানু বাঁধ দেয়ার ব্যাপারে দ্বীপবাসীকে একত্রিত করতে না পারে।
মানু বিদেশ যেতে রাজি হয় না। অন্যদেরকেও সে নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে বলে। মানু কোনো সংগঠন ছাড়া, কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়াই এ সব কাজ করে একক উদ্যোগে। কোনো অর্থনৈতিক সমর্থনও নেই তার পেছনে, নেই রাজনৈতিক কোনো দীক্ষা। মানুর পারিবারিক প্রতিপত্তি নেই, শিক্ষা-দীক্ষা নেই, সংগঠন নেই, টাকা-পয়সা নেই, তবুও সে কিসের ভিত্তিতে নেতা হলো বুঝে ওঠা কঠিন।
গুস্তাভ লা বোঁ আমাদের দেখান যে জনগণের নেতা হওয়া এতো সহজ নয়। জনগণ নেতা হিসাবে মেনে নেয় একজন দৃঢ় চিত্তের মানুষকে এবং যে দেবতুল্য। নেতার নানা গুণ থাকতে হয়। মানুর নেই নেতা হবার যোগ্যতা, তবু মামুনুর রশীদের নাটকে সে-ই বহু মানুষের নেতা।
নাটকে এরপর দেখা যায়, হঠাৎ বন্যা এসে দ্বীপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তখন সর্বস্বান্ত। টাকা-পয়সা নেই, খাদ্য নেই, পানি নেই, থাকার আশ্রয় নেই।
বন্যার পর সবাই যখন সর্বস্বান্ত সেই অবস্থায় রিলিফের ব্যবস্থা করে জামান। কেউ কেউ রিলিফ নিলেও মানুর পরামর্শে একদল রিলিফ না নিয়ে বাঁধ দেয়ার জন্য তৈরি হয়। বন্যা থেমে যাবার দুদিন পর, মানুষ তখনো না খেয়ে আছে, সেই অবস্থায় তারা বাঁধ তৈরি করতে যাবে কি-না নাট্যকার সে বিবেচনায় যাননি। তিনি সর্বহারাদের দিয়ে যেনতেন প্রকারে বিদ্রোহ করানোটাকেই ভেবেছেন রাজনৈতিক নাটক। ব্রেস্ট এই ধরনের নাট্যকার বা ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, ‘বহু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বিপ্লব বলতে বোঝে বাড়ীর জানালার কাচ ভাঙা। ‘
নাটকে এরপর দ্বীপবাসীরা মারমুখী হয়ে বাঁধ দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলে জামান বাধা দেয়। জামান সংঘবদ্ধ মানুষের কৌশলের কাছে প্রথম হেরে গেলেও, পরে এর প্রতিশোধ নেয়। সারাটা গ্রাম সে তছনছ করে ফেলে। রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে আন্দারমানিক দ্বীপে। মামুনুর রশীদ নাটকের শেষে এসে দেখান যে, দ্বীপের অধিবাসীরা প্রকৃতিসৃষ্ট প্রলয় ও মানুষের সৃষ্ট মহাপ্রলয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তবুও বেঁচে থাকে।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 5 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৩.jpg)
মামুনুর রশীদের এই বক্তব্যের মধ্যে একটি সত্যতা আছে। কিন্তু ব্রেস্ট দেখাচ্ছেন, মানুষ নিজের সম্পর্কে এতোই অজ্ঞ যে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের চিন্তা কোনো কাজেই আসে না। মানুষ ভূমিকম্পের মোকাবেলা করতে পারে, কিন্তু শাসকদের বিরুদ্ধে খুব সহজে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। লক্ষলক্ষ লোক যারা সামাজিকভাবে বিপদ আর দুর্দশায় ভুগছে তারা জানে না সে বিপদ কেন, দুর্দশা কিসের জন্য। অত্যাচারীর হাত থেকে কী করে তারা মুক্তি পাবে সে সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই।
মামুনুর রশীদ নাটকে সংগ্রামশীল মানুষের যে চিত্র তুলে ধরেন তা বাস্তব, তবে মানুষ কথায় কথায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা আর শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক কথা নয়, তার জন্য অবস্থা সৃষ্টি হতে হয়। জনতার চিন্তা বা ধারণা সুগভীর হয়ে বিশ্বাস বা মতবাদে পরিণত হলে তার শক্তি অপ্রতিহত হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ করে কোনো ঘটনা সংগ্রামের পথে আগায় না।
বন্যার পর মানুষের প্রথম যে লড়াই সেটা ঘর-গৃহস্থালী সামলানো এবং খাদ্য-পানীয় জোগাড় করা। সেসব বাদ দিয়ে দুদিনের না খাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষরা বাঁধ দেয়ার জন্য চলে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। বাঁধ দেয়ার শক্তি কোথায় তখন তাদের? মানু যতো সহজে নাটকে সকলকে জোট বাঁধতে উদ্দীপ্ত করে কিংবা মানুর কথায় যতো সহজে শোষিতরা জোট বাঁধে তাই যদি সত্যি হতো তাহলে তো বিপ্লব সহজ হয়ে যেতো। বিপ্লবের জন্য মানুষকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হতো না।
শোষিতদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা অতো সহজ নয়, শাসকরাই তাদের মধ্যে নানা ধরনের বিভেদ তৈরি করে রাখে। মার্কসবাদী একজন নাট্যকার অবশ্যই এ ব্যাপারে সচেতন হবেন। নাট্যকার নিজেই যদি রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন না হোন, তিনি দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবেন কী করে?
রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী যেমন শোষিতদের ওপর তাদের শ্রেণীশোষণ বজায় রাখে, তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাধান্যের দ্বারা শোষিত মানুষগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সেই ঘুম অকস্মাৎ ভাঙে না। মুখের এক বুলিতে তাই কোনো সংগ্রাম বা বিপ্লব সংঘটিত হয় না। মার্কসবাদীদের মতে তাই সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ হবে শোষকশ্রেণীর প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা। সেজন্যই দরকার বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করা। মনগড়া কোনো তাৎক্ষণিক বিপ্লব নাটকে না ঘটিয়ে বরং কঠিন বাস্তবের রূঢ়তাকে তাদের কাছে প্রকাশ করা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে-কোনো শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফলতা লাভ করাটা যে কতোটা কঠিন সেটা দর্শকদের বুঝিয়ে দেয়া।
শোষিতরা শোষকদের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কতোটা অন্ধ হয়ে আছে সেটা দেখানো। সর্বোপরি ব্যক্তিগত টানাপোড়েনে শোষিতদের মধ্যে লড়াইয়ের যে অনীহা তা ফুটিয়ে তোলা। শোষিতদের মধ্যকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দো- মনা স্বভাবসহ তাদের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারার মধ্যেই রয়েছে মার্কসীয় নাট্যচিন্তার প্রতিফলন। ব্রেন্ট-এর সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তাই দাবি করে। শোষিতরা যখন নিজেদের চরিত্রের সে-সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখবে তখনি নিজেদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবে, নিজেদেরকে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে তারা কীভাবে অবচেতনে সরকারিযন্ত্রের সাথে, বর্তমান সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা-রক্ষণশীলতা-কুসংস্কারের সাথে বাঁধা পড়ে আছে। সেগুলো দেখেই তারা সচেতন হবে। যদি নাটকে শোষিতদের খুব সংগ্রামী এবং ভালো মানুষ দেখানো হয়, তাহলে তো শোষিতরা নিজেদের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হবে না এবং নিজেদের দোষগুলি কাটিয়ে সত্যিকার বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে পারবে না।
শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির একটি বড় কারণ, সত্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা গভীর সত্যটাকে বের করে আনা। নাটক সম্পূর্ণ বাস্তবভাবে কখনই আগাতে পারে না বলেই দরকার হয় বাস্তবের উত্তরণ। বাস্তব জীবনে নায়ক-নায়িকা থাকে না, সেখানে খলনায়কও থাকে না। যে মুহূর্তে মানুষ নাটকে গুছিয়ে গল্প সাজায়, সে মুহূর্তে নাটকের চরিত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, সে মুহূর্তে নাটক দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে তৈরি করে নতুন বাস্তবতা। কল্পনার সাহায্য নিয়ে এই নতুন যে বাস্তব তৈরি হয় সেটাকেই বলা হয় বাস্তবোত্তর। নাটকে কেন বাস্তব থেকে বাস্তবোত্তরে যেতে হয়? তার প্রধান কারণটাই এই, দৈনন্দিন বাস্তবতা সামগ্রিক বাস্তবতার খণ্ডিতরূপ। সেজন্য সেখানে সব সত্য ধরা পড়ে না। বাস্তব থেকে বাস্তবোত্তরে যাওয়া হয় নতুন চিন্তাকে, নতুন সত্যকে ধারণ করার জন্য।

সত্যের ভিতরের যে সত্যের নির্যাস থাকে তাকে বের করে আনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই সত্য যা রচিবে তুমি যা ঘটে তার সব সত্য নয়। সেই সত্যটাকে ধরার উপায় নাটককে বাস্তবোত্তরে নিয়ে যাওয়া। সংগ্রামশীলতা নিঃসন্দেহে সর্বহারাশ্রেণীর, শোষিতদের বৈশিষ্ট্য। তবে বাস্তব অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত না থাকলে চরিত্রগুলো নাট্যকারের ইচ্ছাকে বহন করার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ে।
সেজন্য সর্বহারাশ্রেণীর বা বৃহত্তর জনগণের জীবন নিয়ে আলেখ্য রচনা করলেই বা তাদের বর্তমান জীবনকে প্রতিফলিত করলেই বৈপ্লবিক সংস্কৃতি হয় না। মামুনুর রশীদের নাটকের দ্বীপবাসীর যে সমস্যা, জীবন সংগ্রাম সেসবই সত্য। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে আরো বহু সত্য। শ্রেণীসমাজের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তাদের মধ্যেও হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, গোলামির মনোভাব সবই আছে। আছে নানারকম নীচতা, আছে নিজেদের মধ্যেই নানারকম স্বার্থের লড়াই। সমাজ বিশ্লেষণের মাধমে তাদের সেই চরিত্র নাটকে ফুটিয়ে তোলা দরকার বলেই মার্কসবাদীরা মনে করেন। রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য দাঁড়ায় যে, শ্রেণীশোষণ বা শ্রেণীসংগ্রামের সীমাবদ্ধতাকে, ছাড়িয়ে বৃহত্তর জায়গা থেকে মানুষ ও বিশ্বকে দেখতে হবে। সেই সত্যগুলো মামুনুর রশীদের নাটকে পাওয়া যায় না।
মামুনুর রশীদের ইবলিশ নাটকেও শোষিত মানুষের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবনযাত্রার কিছু কিছু চমৎকার চিত্র ফুটে উঠলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার অস্পষ্টতা এখানেও ধরা পড়ে।” নাটকের ঘটনার একদিকে রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, তার আভিজাত্য; অন্যদিকে তারই ভগ্নস্তূপে গড়ে উঠেছে যন্ত্রশিল্পের সৌধ, নতুন যুগের সভ্যতা।
এই দুয়ের সংঘাতময়তাকে নাটকের বিষয়বস্তু করতে চেয়েছেন নাট্যকার। ইবলিশ নাটকে গ্রাম্য মাতবর ফজল সিকদার, একাব্বর মেম্বর ও মুন্সি শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি। মুন্সি নিজে সরাসরি শোষক না হলেও সে শোষকদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের পক্ষেই তার মতামত। মুন্সি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানবিরোধী মানুষ। তার তালবেলেম মিয়া আবদুল গোফরান তার খুবই অনুগত ও বিশ্বস্ত।
কিন্তু মাতবর ও মুন্সির ছেলেরা শোষিতশ্রেণীর পক্ষে। মুন্সির মেয়েরও সহানুভূতি শোষিতদের দিকে। মুন্সির ছেলে রফিক মাদ্রাসা থেকে পাশ করে শহরে যায় কলেজে পড়াশুনা করার জন্য। রফিক পিতার আদর্শে বিশ্বাসী নয়। সে কুসংস্কারমুক্ত, গ্রামের সাধারণ মানুষদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে চায়। মুন্সি রফিককে ধর্ম-কর্ম, ইমামতী করার কথা বললেও রফিক সে পথে যায় না। কলেজে পড়াশুনা শেষ করে সে সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামেই থেকে যাবে।
ফজল সিকদারের সাথে রফিক ও গ্রামের একদল যুবকের বিরোধ শুরু হয় বিলের মাছ ধরা নিয়ে। বিলটি দশ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে ফজল সিকদার। রফিক- মজনু-মেরাজুল সেখানে মাছ ধরতে গেলে ফজল সিকদারের লোকরা বাধা দেয়। নিজের ইজারা নেয়া বিলে বাধা দেয়াটা ফজল সিকদারের জন্য স্বাভাবিক। নাট্যকার কিন্তু এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের পক্ষ নেন এবং ফজল সিকদারকে খলনায়ক বানান।
স্বাভাবিকভাবেই নাটকের কাহিনীতে এরপর যা ঘটে তাহলো, রফিকরা সিকাদারের কথা না শুনলে পুলিশ এসে তাদের মারধর করে ও অনেককে ধরে নিয়ে যায়। রফিককেও থানায় নিয়ে মারধর করা হয়। পরে গ্রামের মেম্বার রফিককে ছাড়িয়ে আনে। মজনু ছাড়া পায় টাকার বিনিময়ে। মজনুর হাতে তখন টাকা ছিলো না, তাই সামান্য কিছু টাকা ধার নেয় সে ফজল সিকদারের কাছ থেকে কাগজে টিপসই দিয়ে। ফজল সিকদার সেই কাগজের জোরে কিছুদিন পরই মজনুর বাড়ি-ঘর দখল করে। মজনু স্বকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়।
আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 7 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/আশির-দশক-শ্লোগানসর্বস্ব-রাজনৈতিক-নাট্যের-উন্মেষ-পর্ব-২--1024x536.jpg)
রফিকের বন্ধু আবদুল্লাহ, সে অনেকগুলো তাঁত ও দুটি পাওয়ার লুমের মালিক। পিতার সাথে বিরোধ করে রফিক বন্ধুর তাঁতের কারখানায় চাকরি নেয়। গ্রামের লোকজনকেও সে এনে তাঁতের কাজে লাগায়। যখন মজনুর সব সম্পত্তি জোচ্চুরি করে সিকদার দখল করে, তখন মজনুর কান্না ও আহাজারি শুনে রফিক বলে, ‘চুপ করো, শিখছো খালি কানবার, কানবার শিখছো? মইষের মত গতরডা নিয়া কান্দো খালি, শরমও করে না?’
রফিক মানুষের মোষের মতো শরীরটাকে অন্যের শ্রমদানে কাজে লাগাতে উৎসাহ জোগায়, সে সকলকে জোলা বা তাঁতী হতে বলে। শ্রমদানে বা শ্রম বিক্রিতে তার আপত্তি নেই। জমির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়, যেন জমির প্রয়োজন নেই। বন্ধুদের সে বলে, ‘জমি লইয়া কাইজা করতে চাও তোমরা? মারামারি করো তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে, মেম্বর আর খালাসির পায়ের তলায় থাকো। ‘৭৬ জমি ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নিয়ে যেন ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি হয় না।
নাট্যকারের দৃষ্টিতে জমিতে শ্রমদানের চেয়ে ভালো তাঁতী হওয়া। রফিকের পরামর্শে সকলে একযোগে, সারা গ্রামের মজুররা আবদুল্লাহর তাঁতশিল্পে জোলার কাজ নেয়, যার জন্য গ্রামের কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। মাতবর ও মেম্বার এ ঘটনায় ক্ষেপে যায়। সামন্ত- মহাজনদের সাথে ব্যবসায়ীর এই যে বিরোধ মামুনুর রশীদের নাটকে দেখা যায়, বাংলাদেশের এটা কোনো স্বাভাবিক চিত্র নয়। বাংলাদেশে সামন্ত-সমাজের সাথে ব্যবসায়ীদের মূলগতভাবে কোনো বিরোধ কখনও ছিলো না। বাংলাদেশের শিল্প- কারখানা সৃষ্টির ইতিহাস তো এরকম নয়, যা ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, কারখানার শ্রমিক জোগাতে গিয়ে মাঠের কৃষকের অভাব ঘটেছে। বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যার কারণেই অসংখ্য লোক বেকার।
কৃষিকাজ ছেড়ে সবাই এসে কারখানায় চাকরি খুঁজলেই সবাই চাকরি পাবে বাংলাদেশে এতো চাকরির সুযোগ কখনও কোথাও ছিলো না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে অফুরন্ত লোককে চাকরি দেয়া যায় না। তেমনি একজন শিল্প উদ্যোক্তা চাইলেই বহু লোককে চাকরি দেয়ার জন্য তার কারখানাকে বড় করতে পারে না। সেজন্য পুঁজির যেমন দরকার, তেমনি দরকার পণ্যের বাজার।নাট্যকার বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে সামান্য সচেতন হয়ে নাটক লিখলে কখনই এটা দেখাতে পারতেন না যে, চরকা-শিল্পে চাকরি করার কারণে গ্রামে কৃষিকাজের লোকের অভাব দেখা দিয়েছে।
ফলে নাটকের যে মূল প্রেক্ষাপট কারখানার মালিকের সাথে ভূস্বামীদের বিরোধ, সেটাই অন্তঃসারশূন্য হয়ে দাঁড়ায়, যার ওপর ভিত্তি করে নাটকের অন্যান্য প্রধান দ্বন্দ্বগুলি তৈরি করা হয়েছে। ইবলিশ নাটকে মূল বিরোধ শ্রমিক-মালিকের নয়, মালিকের সাথে শ্রমিকদের এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বিরোধ এখানে গ্রামের মাতবরের সাথে তাঁতশিল্পের। ইবলিশ নাটকে শোষিতদের মুক্তি ঘটে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁত শিল্পে শ্রমিকের চাকরি নেয়ায়। সমস্যার এভাবেই সমাধান টেনেছেন নাট্যকার রফিক চরিত্রটি সৃষ্টি এবং অন্যান্যদের রফিককে সমর্থন দেয়ায় মাধ্যমে। নাটকের কোনো চরিত্রই একথা বলে না যে, তারা এক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শোষণের অঙ্গনে পা রাখছে।
বরং মনে হয় জোলার চাকরি নেয়ার পর দীর্ঘদিনের শোষণ থেকেই তারা মুক্তি পেলো। নাটকে সিকদার বা মেম্বারকে খারাপ চরিত্র হিসাবে দেখানো হলেও তাদের সাথে শ্রমজীবীদের মূল বিরোধের কারণটা স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি তাঁতশিল্পের মালিক আবদুল্লাহ যে শ্রম শোষণ করছে সে বক্তব্য নাটকের কোথাও নেই, এখানে আবদুল্লাহ শ্রমিকদের বন্ধু। শ্রমিকরা তাই আবদুল্লাহর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে। মার্কসবাদী চিন্তার সবচেয়ে বড় বিষয় ‘শ্রম-শোষণ’ প্রশ্নটিকেই এভাবে এড়িয়ে যান নাট্যকার।
ইবলিশ নাটকে যাতে তাঁতশিল্প দাঁড়াতে না পারে তার জন্য সামন্ত সমাজের প্রতিভূ সিকদার ও মেম্বার মিলে ব্যবসায়ী আবদুল্লাহর সুতার যোগান বন্ধ রাখে, গ্রামে বিদ্যুৎ আসতে দেশ না। বিদ্যুৎ আসার পরও ষড়যন্ত্র করে আবদুল্লাহর কারখানায় তার সরবরাহ বন্ধ রাখে। সহজ প্রশ্ন দাঁড়ায়, সুতার যোগান বন্ধ রাখা বা বিদ্যুৎ বন্ধ রাখার কোনো এখতিয়ার গ্রামের একজন মেম্বারের থাকে কি না। মেম্বার তাঁত থেকে শুল্ক আদায় করার জন্যও আবদুল্লাহকে চাপ দেয়, শেষ পর্যন্ত তাঁত ধ্বংস করার জন্য কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। গরীবুল্লাহ নামে সিকদার ও মেম্বারের যে সহযোগী আগুন লাগায় সে রফিকদের হাতে ধরা পড়ে। রফিকরা তখন মেম্বারকে ধরে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়। সিকদার কিছুদিনের জন্য গ্রাম থেকে গা ঢাকা দেয়।
রফিক, মজনু ও তার দলবল তখন গ্রামটাকে তাদের রাজত্ব মনে করতে শুরু করে। সিকদার ও মেম্বারের সহযোগীদের ধরে ধরে তারা শাস্তি দিতে থাকে। সিকদার পূর্বে মজনুর ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছিলো কারচুপি করে, মজনু গায়ের জোরে দলিল-দস্তাবেজ ছাড়াই এখন তার সে জমি ফেরত নিয়ে নেয় আইন-কানুনকে তোয়াক্কা না করে। মজনু-রফিকরা গ্রামে সংঘবদ্ধ হওয়াতে কি সারাদেশের আইন-কানুন পাল্টে যায়? কিংবা গ্রাম্য মহাজনদের ক্ষমতা কি এতোই ক্ষণস্থায়ী যে জমিটা দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া দখল করে নিলেই দখলে রাখা যাবে?
পূর্বে গ্রামে জমিদার, মহাজন ও দাদন কারবারিদের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিলো, তার বদলে বর্তমানে জোতদার-মহাজন-মজুতদারদের এক মিলিত শক্তিশালী চক্র গড়ে উঠেছে। তাদের শোষণ আরো অনেক তীব্র, গভীর ও নির্মম। গ্রাম্য জীবনে এদের প্রভাব ও প্রাধান্য বিরাট অভিশাপের মতো চেপে আছে। জোতদার-মহাজন ও মজুতদারী চক্র গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জীবনকে কুক্ষিগত করেছে।
এরাই গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমলাতন্ত্র ও পুলিশের সঙ্গে এদের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ।মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে এই শোষকশ্রেণীর শক্তিকে ক্ষুদ্র করে দেখান। গ্রামের কিছু দরিদ্র লোকের বিচ্ছিন্নভাবে জোটবদ্ধ হওয়াতে শোষকরা ভয় পাবে, পালিয়ে যাবে সেটা খুবই অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের কোনো গ্রামে এখনো এ ধরনের কোনো বাস্তবতার সাথে পরিচিত হওয়া যায় না, যেখানে সাধারণ মানুষের জোটবদ্ধ হওয়ার কারণে শাসকচক্র পালিয়ে গেছে কিংবা পরাজিত হয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কখনও সেটা ঘটা সম্ভব নয়। সশস্ত্র বিপ্লবীরা কখনও কখনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কিছু কিছু গ্রাম নিজেদের দখলে নিতে পারে বা দখলে রাখতে পারে; তবে রফিক- মজনুরা তো সশস্ত্র বিপ্লবী নয়। কোন ভরসায় তাহলে মজনু মাতবরদের দখল থেকে নিজের জমি ফেরত নেয়?
নাটকের শেষে দেখা যায়, শোষিতদের বিরাট বিজয়ের পর সিকদার ও মেম্বার দুই-তিন ট্রাক পুলিশ নিয়ে হাজির হয়। বিদ্রোহীরা সবাই তখন রফিককে পালাবার পরামর্শ দেয়। রফিক তখন সকল বিদ্রোহীদের নিয়েই পালায় এবং আবদুল্লাহকে বলে যায় কারখানা চালু রাখতে। বিদ্রোহীরা পালালে সিকদার, মেম্বার ও মুন্সি তাদের সন্ধান লাভের জন্য আতশী নামের বিদ্রোহী দলের একজন মহিলাকে ধরে আনে।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 8 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-১.jpg)
আতশী কারো সন্ধান না দিলে তার শয়তান দূর করার জন্য মুন্সি গরম লোহা দিয়ে আতশীর পিঠে ছ্যাঁকা দেয় এবং গোফরানকে আজান দিতে বলে। মুন্সির এতোদিনকার অনুগত ভক্ত তালবেলেম গোফরান আজান না দিয়ে এই ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে বসে এবং সিকদার ও মেম্বারের সামনে দাঁড়িয়েই মুন্সির হুকুম মতো আজান দিতে অস্বীকার করে।
মুন্সির আশ্রিত গোফরান বিদ্রোহ করার এই চেতনা কোথায় পেল নাটক দেখে তা বুঝতে পারা যায় না। গোফরানের সকল শিক্ষা-দীক্ষা মুন্সির কাছ থেকে পাওয়া। যে গোফরান মনে করে মুন্সির বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই পাপ, হুজুর গোস্বা হলে আল্লাও তাকে মাফ করবে না, সেই গোফরানের দ্বারা হঠাৎ এক লাফে এই বিদ্রোহ কোনো সমাজবাস্তবতা নয়। বিশেষ করে সিকদার ও মেম্বারের মতো সমাজশক্তির সামনে দাঁড়িয়ে গোফরানের এ বিদ্রোহ করাটা নাট্যকারের খুবই অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতিফলন। গোফরান এখানে পশ্চাদপদ চিন্তার অধিকারী ও ছিন্নমূল মানুষ। তার পেছনে কোনো বন্ধু নেই, কোনো জনতা নেই। সে এ অবস্থায় সিকদার ও মেম্বারকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বসবে তা হতে পারে না।
যদি মুন্সির কার্যক্রম তার পছন্দ না হয় বড়জোর সে পালিয়ে যেতে পারে। গোফরানের সাথে আতশীর কোনো ধরনের স্বার্থের বন্ধন নেই, নেই কোনো মানসিক বন্ধন যে ব্যক্তিগত আবেগ থেকে সে এই বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করার কোনো কারণই তার নেই। মামুনুর রশীদের নাটকের চরিত্ররা এভাবেই কার্যকারণ ছাড়া খেয়ালের বশেই বিদ্রোহ করে বসে।
সিকদার ও মেম্বারের ডাকে গ্রামে পুলিশ আসে আবার চলে যায়। পুলিশ চলে গেলে রফিক, মেরাজুল ও মজনু ফিরে আসে। সিকদার ও মেম্বার পুনরায় পালাতে গেলে মজনু তাদের ধরে ফেলে। মজনু তাদের বলে, ‘পালাবি কই তরা? গেরামে পুলিশ আহে পুলিশ যায়, পুলিশ কতক্ষণ থাকে?’ রফিক বলে, ‘সিকদার সাব যুদ্ধ শুরু অইছে, কোন সময় যুদ্ধে আপনারা জিতবেন, কোন সময় আমরা, এইবার আমরা জিতছি তার একটা চিহ্ন থাকা দরকার…।’
সিকদারের গালে সে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেয়। নতুন তাঁতের আওয়াজ ভেসে আসে।” মামুনুর রশীদের নাটকে যতোই তাঁতের আওয়াজ ভেসে আসুক, সমস্ত রাষ্ট্রে বিপ্লব না ঘটিয়ে একটি গ্রাম দখলের ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে? সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের চাপে তারা ছত্রভঙ্গ হবে, রাষ্ট্রের সুসজ্জিত পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতেই পারবে না। বিদ্রোহের নামে মামুনুর রশীদ এ নাটকে যে বক্তব্য তুলে ধরেন তা এক ধরনের সাময়িক উত্তেজনা বা নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কসবাদীরা আন্দোলনের নামে যে-কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে।
দ্বান্দ্বিক বা শ্রেণীসংগ্রামের নাটক সম্পর্কে ব্রেস্ট বলেছিলেন, নাটকের মাধ্যমে জীবন্ত বাস্তবকে এমন জীবন্তভাবে জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে যেন তারা কঠিন বাস্তবকে আয়ত্ত করতে পারে। বাস্তবকে জীবন্ত করে তুলে ধরার জন্য তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হলো সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো। নাটকের ঘটনা ও চরিত্রকে ঐতিহাসিক, পরিবর্তনশীল এবং দ্বন্দ্বসহ উপস্থিত করা। সমাজ পরিবর্তন করার শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব দ্বারা প্রতিদিনের ঘটনাকে ব্রেস্ট তাঁর নাটকে আরো বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। ঘটনার সম্প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, ‘ধরুন, আপনারা একটা খুনের দৃশ্য সুন্দরভাবে দেখালেন। আমার সমালোচনার ঝোঁক হবে খুনটাকে ঘিরে এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যায়। ‘
ব্রেন্ট খুনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যায় যেতে চান কেন? কারণ খুনের পেছনে খুনীর স্বার্থ কোথায় সেটা যেমন তিনি ব্যাখ্যা করতে চান, তেমনি এই খুনটির সাথে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্কটিও তুলে ধরতে চান। তিনি চান দর্শকরা হয়ে উঠুক সাংসদের মতো। তিনি দর্শকদের বিচারকের আসনে বসিয়ে দিতে চান। দর্শকদের কাছে ব্রেশটের চাওয়া হলো, নাটকের সকল বিতর্কই তারা মন দিয়ে শুনুক এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করুক। তিনি বলেন, মার্কসবাদী চিন্তায় দর্শককে অভ্যস্ত করে তুলতে হলে দু-একজন ব্যক্তিকে খলনায়ক বানানোর চেয়ে পুঁজিবাদ-সৃষ্ট বীভৎসতার স্বরূপ উন্মোচন করাটা জরুরি এবং ব্যক্তির ভূমিকার বাইরে সমাজ ও অর্থনীতির ভূমিকা দর্শকের কাছে স্পষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলাটা অধিকতর দরকার।
ইবলিশ নাটকের মধ্যে নানা ধরনের স্ববিরোধিতা আছে, সেগুলো বাদ দিলেও রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে এই নাটক যেমন অস্বচ্ছ, তেমনি নানা বিভ্রান্তিতে ভরা। ইবলিশ নাটক সম্পর্কে ‘আরণ্যকের বিশ বছর’ শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করা হয়, ইবলিশ সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে আসে। ইবলিশ নাটকের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ধারায় সুস্পষ্টভাবে সূচিত হলো একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ।
যে মতাদর্শ এই প্রাচীন জনপদের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরতে সক্ষম। ইবলিশ নাটকে প্রতিফলিত হলো হাজার বছরের নিস্পন্দ গ্রাম বাংলার সমাজ কাঠামোর একটি স্থির চিত্র। যদিও আমরা জানি বাংলার গ্রাম ব্রিটিশ শক্তির আগমনের পর আর নিস্তব্ধ-নিস্পন্দ গ্রাম নয়। মামুনুর রশীদের নাটকেও যে গ্রাম আমরা দেখতে পাই, সে গ্রামও নিস্পন্দ গ্রাম নয়। যে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, নানা ধরনের বিদ্রোহ ও লড়াইয়ে যে গ্রাম মুখরিত, আরণ্যক নিজেই সে গ্রামকে নিস্পন্দ বলছে কিসের ভিত্তিতে বোঝা দুঃসাধ্য। পাশাপাশি তারা দাবি করছে, ইবলিশ নাটকে শ্রেণীসংগ্রাম ও গ্রামীণ জনপদের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। দেখা যাক সেটা কতোটা সত্য।
আরণ্যকের দুই হাজার সালের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান সম্পাদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, পুরানো দুটি প্রযোজনা জয়জয়ন্তী ও ইবলিশ-এর মধ্যে ইবলিশের ধার এখন কমে এসেছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এই নাটক আর অভিনয় করা ঠিক হবে না। মামুনুর রশীদ নিজেই প্রধান সম্পাদক হিসাবে এই বক্তব্য রাখেন। ধার কমে যাওয়া মানে কি? মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। বাংলাদেশে কি শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে? যদি শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে শ্রেণীসংগ্রামের নাটকের ধার কমে যায় কী করে? মামুনুর রশীদের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম বা রাজনীতি প্রচারে ইবলিশ নাটকের দুর্বলতাই ফুটে উঠেছে।
মামুনুর রশীদ যা বলতে চান তাহলো, শহরে এসব নাটক মঞ্চায়ন করে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না।সে-কথা বলার পরও মামুনুর রশীদ নাটককে গ্রামে নিয়ে যাননি। মামুনুর রশীদ কেন কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রেন্ট মনে করতেন, নাটক তখনই হাতিয়ার হয়ে ওঠে যখন তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির আগুনে ঝলসানো হয়। মামুনুর রশীদের নাটক সেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই তা রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারেনি।
মামুনুর রশীদের উল্লিখিত নাটকগুলোতে শোষিতদের হাতে শোষকদের পতন দেখিয়ে নাটক শেষ করা হয়। মনে করা হয় এই সত্য দেখেই মানুষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবে। এ চিন্তাটা যে ভুল মামুনুর রশীদের অভিজ্ঞতাই সেটা প্রমাণ করেছে। ব্রেস্ট বলেছেন, বৈজ্ঞানিক থিয়েটার দর্শককে তার বাস্তব দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সেখানে মামুনুর রশীদ নিজেই স্বীকার করছেন ধার কমে যাওয়ায় তার নাটক দেখে দর্শকদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।
মামুনুর রশীদ তাঁর উল্লিখিত নাটকগুলোতে বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি নাটকগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ফর্মুলার মধ্যে বেঁধেছেন। তাঁর তিনখানা নাটক পরপর দেখলেই বোঝা যায় ঐ একই সূত্রবদ্ধতায় গতানুগতিক হয়ে পড়ছে তাঁর নাটকের বিষয় ও বিস্তার। তিনি গ্রামবাংলার শোষণ কিংবা কৃষক ও পল্লীর বিভিন্ন জীবিকার মানুষের জীবন ও প্রতিরোধের বিষয়কে একটা কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখতে চাইছেন।
শোষিতরা অত্যাচারিত হতে হতে হঠাৎ করে জোট বাঁধে এবং শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। সাধারণভাবে হয়তো ঘটনাটা তাই। সেই শোষণ হওয়া, জোট বাঁধা এবং শোষিতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার থাকে নানা স্তর। সেই প্রতিটি স্তরের পেছনেই থাকে নানা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ এবং শ্রেণীঘৃণা। সেই কার্যকারণের ব্যাখ্যা ছাড়া শ্রেণীসংগ্রামের নাটক দাঁড়ায় না। যে-কোনো উপায়ে একটা অত্যাচারের দৃশ্য, তারপরেই প্রতিবাদের শপথ এবং শেষে লাল আলো জ্বালিয়ে কিংবা প্রচণ্ড চিৎকার করে অত্যাচারী চরিত্রটিকে খতম করে দেয়া মানেই রাজনৈতিক বা বিপ্লবী নাটক নয়।
শ্রমিকশ্রেণীর জয়গানকারী রচনা হলেই তা অতি অবশ্য মহৎ হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা তো প্রায় সকলেই জানে মানুষ শোষিত হয় এবং বিদ্রোহ করে। রাজনৈতিক নাটকে এ কথাটা জানানোই কি একজন নাট্যকারের কাছে জরুরি হবে? যদি তাই হয় সব নাটকে কি এই একই কথা বারবার বলতে হবে? সব নাটকে এই একই সূত্র বা ফর্মুলা প্রচার করলে তার ফল কী দাঁড়াবে? মার্কসবাদীদের এ সম্পর্কে নিজস্ব উত্তর রয়েছে। মাও সেতুঙ এর বক্তব্য হলো, কোনো এক ধরনের ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাই যেন নাট্য রচনার আদর্শ না হয়ে ওঠে। তাহলে নাটকে দেখা যাবে শুধু নির্দিষ্ট কিছু প্রথা বা অকারণ আনুগত্য। কোনো প্রগতিশীল রচনায় সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।
সে-সব নাটক দর্শকের হৃদয়ে স্থান পাবে না। এ ব্যাপারে মামুনুর রশীদের নিজস্ব বক্তব্যই এখানে তুলে ধরছি। তিনি লিখছেন, ‘সত্তর দশকে আরণ্যক তাদের প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে শহর এলাকায়। দর্শকরা নাটক দেখতে দেখতে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেও নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যকার আবেগজাত সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সক্রিয় হয়ে উঠবার তাগিদ সব হারিয়ে যেত।
ফলতঃ এই নাটকগুলো নাটক হিসাবে সাফল্য লাভ করলেও প্রত্যাশিত রাজনৈতিক অভিঘাত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। ‘ মামুনুর রশীদ সাফল্য বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা এখানে পরিষ্কার নয়। তবে দর্শকের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের চেতনা সৃষ্টিতে যে নাটকগুলো ব্যর্থ হয়েছে, মামুনুর রশীদের বক্তব্য থেকেই তা বোঝা যায়। আর যে নাটক মানুষের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের চেতনা পৌঁছে দিতে পারে না, তা রাজনৈতিক নাটক হিসাবে ব্যর্থ বলেই মার্কসবাদীরা মনে করেন। মামুনুর রশীদকে তাই যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তাদের বক্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করে। দুই বাংলার নাট্য বোদ্ধারাই স্বীকার করেন, সবচেয়ে বড়ো অভাবের মধ্যে একটা যেমন ভালো নাটক খুঁজে পাওয়া, অন্যটা তেমনি বড় মাপের সমালোচকের অভাব।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে সত্য। যিনি নাটক নিয়ে সমালোচনা করবেন, নাট্য কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক মূল্যায়ন করবেন তার মূল ভিত্তি হতে হবে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান রহিত সমালোচনা বা মূল্যায়নে নিন্দা কিংবা প্রশংসা যাই করা হোক তা মূল্যহীন। সমাজবিজ্ঞানের এই চেতনা জনন্ম নেয় ইতিহাস বোধ থেকে। কিন্তু দেখা গেছে, বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের প্রধান ব্যক্তিত্বরা যখন কোনো কিছু সমালোচনা করেন বা নাট্যচর্চার ইতিহাস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন তা হয়ে দাঁড়ায় বিভ্রান্তিতে পূর্ণ। বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্বদের বিভ্রান্তি ধরা পড়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে; স্বাধীনতা-পূর্ব নাট্যচর্চার আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং মামুনুর রশীদ সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে তাদের মূল্যায়ন। শ্রেণীসংগ্রাম কী, কীভাবে শ্রেণীসংগ্রামের নাটক রচিত হতে পারে এ বিষয়ে কোনো চুলচেরা বিশ্লেষণ ছাড়াই মামুনুর রশীদকে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকারের খেতাব দিয়ে দেন।
মামুনুর রশীদের নাটক ছাড়াও আরণ্যক আশির দশকে আবদুল্লাহ হেল মাহমুদের দুটি নাটক মঞ্চায়ন করে। আরণ্যকের সপ্তম প্রযোজনা ছিলো আবদুল্লাহেল মাহমুদ রচিত সাত পুরুষের ঋণ। সুবর্ণপুরের গফুর মাঝির আত্মহত্যা দিয়ে নাটকের শুরু, তারপর ঘটনা আগাতে থাকে অন্য খাতে। সুবর্ণপুরে আসে নাট্যকর্মী সাইফুল, ঠিক গফুর মাঝির আত্মহত্যার পরদিন। সেই সময় সুবর্ণপুরে একটি যাত্রার মহড়া চলছিলো। সে যাত্রার কাহিনী ছিলো ঐতিহাসিক।
রাজা-বাদশাদের নিয়ে। নাট্যকর্মী সাইফুল তাদেরকে বোঝায় রাজা-বাদশাদের নিয়ে নাটক করতে হবে কেন, তাদের নিজেদের জীবন নিয়েই তো নাটক হতে পারে।” নাট্যকারের বক্তব্যে মনে হয়, রাজা- বাদশাদের নিয়ে নাটক করাটা যেন প্রতিক্রিয়াশীল কোনো ব্যাপার। সে বিচারে প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলোতো বর্জনীয়ই, বর্জনীয় হয়ে যায় মার্কসের প্রিয় নাট্যকার শেক্সপিয়ার। গ্যাটে, শিলারকে পর্যন্ত বর্জন করতে হয়। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস- লেলিন-স্তালিন সকলেই ধ্রুপদী সাহিত্যের পক্ষে কথা বলেছেন।
দেখা যাবে পৃথিবীর বেশির ভাগ ধ্রুপদী নাটকগুলো রচিত হয়েছে রাজা-বাদশাদের নিয়ে। বহু বিপ্লবী নাটকেও রাজা-বাদশারা এসেছে প্রধান চরিত্র হয়ে। নবাব সিরাজদৌলা নাটক তো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই প্রতিচ্ছবি। নাট্যকার আবদুল্লাহহেল মাহমুদ সেখানে রাজা-বাদশাদের নিয়ে নাটক করার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন কেন বোঝা যায় না। রাজনৈতিক নাট্যকার ব্রেন্ট মনে করেন, সকল ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রগতিশীল চিন্তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি লিখছেন, মানুষ সব ধ্রুপদী সাহিত্যকে রক্ষা করে এসেছে এবং তার বলিষ্ঠ অগ্রগতি সর্বদা মানবিক শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণা দিয়েছে।**
রাজা-বাদশারা তো সমাজ বিবর্তনের বাস্তবতা এবং ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। সেজন্য নাটক থেকে তাদের পরিপূর্ণভাবে বাদ দেয়ার তো কোনো পথই খোলা নেই। সারা বিশ্বের জনগণকে হাজার হাজার বছর ধরে যাদের শাসনাধীনে থাকতে হয়েছে, যে রাজা-বাদশারা দরিদ্র মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল ভোগ করেছে, নাটক থেকে তাদের বাদ দেয়ার প্রশ্নই বা আসবে কেন? শাসককে বাদ দিয়ে তো শোষিত হতে পারে না। রাজনৈতিক নাটকের প্রবক্তা পিসকাটর তো জার-কাইজার এবং রাসপুটিনকে নিয়ে নাটক করেছেন, বাংলাদেশে শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা নাট্যদল আরণ্যকের একজন নাট্যকারের এ কথা না জানার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে, দরিদ্র মানুষকে নিয়েও নাটক হতে পারে এবং হচ্ছেও।
ভবিষ্যতে যারা শাসন ক্ষমতায় আসবে বহু নাটকের তারাই হবে নায়ক। মার্কসবাদীদের এ নিয়েও কোনো আপত্তি বা নিষেধ নেই। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, সর্বহারা চরিত্ররা খুব একটা চিত্তাকর্ষক এবং রংচঙে হয়েতো বিকশিত হয় না এই সমাজ ব্যবস্থায়। সে লিখতে পড়তে শেখেনি-সুতরাং মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়ে চৌকষ হয়ে উঠবে তার পথ বন্ধ। সারাদিন শ্রমক্লান্ত উদয়াস্ত মেশিনের তলায় বিধ্বস্ত, নিজবৃত্তি, নিজ চেতনা, অন্য মানুষ, সব থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক যখন রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে, সে প্রথম প্রাণের স্পর্শ অন্তরে অনুভব করে। শ্রমিকের ঘরোয়া জীবনের কিছু কি বাকি রেখেছে পুঁজিপতি ও মেশিন, যে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে ট্র্যাজেডির নায়ক?
যাই হোক, সাত পুরুষের ঋণ নাটকে দেখা যায়, সাইফুলের কথায় উৎসাহ পায় গ্রামের লোকজন। রাজা-বাদশা বাদ দিয়ে মৃত গফুরের স্ত্রী জয়মনের কাহিনী নিয়ে নাটক করার জন্য মহড়া শুরু করে তারা। নাটকটা কে লিখলো, কতোদিনে লিখলো তা নাটকের গল্পে উল্লেখ নেই। ধরে নেয়া যায়, বাংলাদেশের তথাকথিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় বহুজন মিলে দুদিনে যেভাবে নাটক লেখে এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।
বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষকে সচেতন করার জন্য একধরনের নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। কোনো একটি গ্রামের বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নাটকের পাত্রপাত্রীরাই বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু-তিনদিনে নাটকটি রচনা ও মহড়ার কাজ সম্পন্ন করে। নাটক তৈরি করা তাদের কাছে খুবই সহজ কাজ; সামান্য কিছু আলাপচারিতার দরকার হয় তার জন্য। মুক্ত নাটকের নামে গ্রামে গিয়ে উন্নয়ন সংস্থার অর্থে বিভিন্ন সময় আরণ্যক নাট্যদলও এ ধরনের নাটক করেছে। মাহমুদের সাত পুরুষের ঋণ নাটকের গল্পে তারই প্রতিফলন ঘটে। দরিদ্র মানুষের একত্রে বসে নিজের গ্রামের ঘটনা নিয়ে মিলিতভাবে নাটক লেখাটাকে এই নাটকে নাট্যকার বিপ্লবী কাজ হিসাবেই প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছে এসব উদ্ভট চিন্তা।
পৃথিবীর বড় বড় নাট্যকাররা কেউই উন্নয়ন সংস্থার মতো সামান্য কিছু তথ্য জোগাড় করে যৌথ উদ্যোগে নাটক লেখেননি। নাটক লেখার ব্যাপারে তাদের সবচেয়ে বড় উপাদান ছিলো মানুষ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন ধরনের অধ্যয়ন ও বছরের পর বছর দেখা নানা ঘটনা থেকে একজন নাট্যকার যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তিনদিনের সংগৃহীত তাৎক্ষণিক তথ্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি।
মহৎ নাটক লেখবার জন্য যা দরকার তা হলো ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, কিছু তথ্য জোগাড় করে দু-চারজন একসাথে বসে এবং যুক্তি- পরামর্শ-আলোচনা করে নাটক লেখা যায় না। পৃথিবীর কোনো মহৎ নাটকই সেভাবে লেখা হয়নি। কারণ নাটক লেখা কোনো করণিকের কাজ নয়। নাটক একটি শিল্প মাধ্যম। ভিতরে শিল্পবোধ না থাকলে, নাটক কী সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে শুধু কিছু তথ্য জোগাড় করে নাটক লেখা পাগলামির শামিল। পৃথিবীর সকল মহৎ নাট্যকাররা এককভাবেই নাটক লিখেছেন নিজেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে। নাটক বা সাহিত্যচর্চা একটি সৃষ্টিশীল কাজ। ভিতরের তাড়নায় তা জন্ম নেয়।
নাট্যকারের কিছু বলবার থাকলে ভিতর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বেরিয়ে আসবে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়ে এসব কাজ হয় না। নাট্যকার আবদুল্লাহেল মাহমুদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো; বিপ্লবী নাটক লিখতে হবে বহুজন মিলে। রাজা-বাদশা নয়, স্থানীয় কোনো ঘটনার বাস্তব চরিত্ররাই হবে নাটকের পাত্রপাত্রী। সাত পুরুষের ঋণ নাটকের গল্পে তাই জয়মনের কাহিনীর সাথে জড়িয়ে যায় স্থানীয় চেয়ারম্যান ও হেডমাস্টার, যারা জয়মনকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে চেয়েছিলো। গ্রামের অনেকের ধারণা গফুরকে খুন করা হয়েছে। গ্রামের লোকরা নাটক মঞ্চায়ন করে সেটা ফাঁস করে দিতে চাইলে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও তার সহযোগী হেডমাস্টার তাতে বাধা দিতে চায়।
চেয়ারম্যানের লোকেরা মহড়ায় এসে গণ্ডগোল পাকালে আহত হয় অভিনেতা রঞ্জু। এ ঘটনায় মজিদসহ অনেকেই ভয় পেয়ে নাটক ছেড়ে চলে যেতে চায়। নাট্যকর্মী মনে করে মজিদ খামোখাই ভয় পাচ্ছে। মজিদ তখন বলে, ‘খামাখা? চেয়ারম্যান যদি কেইস দেয়, বাড়ি-ঘর জ্বালায়া দেয়, রাইতের বেলা কাউরে জবাই করে আপনে কিছু করতে পারবেন? পারবেন না, আমরা অইলাম গরীব মানুষ। গরীব মানুষ অইলো কুত্তার মত।’ নাট্যকর্মী মজিদের সাথে একমত হয় না। সে মজিদকে বুকে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে বলে। সে সময় পাগল চরিত্র বৃদ্ধ মাখন, এক সময়ের স্কুল শিক্ষক এসে শেক্সপিয়ারের নাটকের একটি সংলাপ বলে, কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগে মরে বহুবার।
সে আরো বলে, ইতিহাস কি বলে জানো? ইতিহাস বলে মানুষ সামনের দিকে যায়, পিছনের দিকে নয়। গ্রাম্য যুবক কেরামত নাটক করার ব্যাপারে একমত। সে নাট্যকর্মীকে বলে, ‘পুরুষের পর পুরুষ কুলুর বলদের মত জোয়াল কান্দে লইয়া ঘুরতে আছিলাম। আপনি আমাগো ভিতরডা কাঁপাইয়া দিছেন… আইজ আমরা বুঝবার পারছি আমরাও মানুষ সবার মত আমাগো শরীলের রক্তও লাল।’ এই দৃশ্যের আগেই জানা যায় সুবর্ণপুর, হারাগাছির মানুষ গফুরের নেতৃত্বে একত্র হয়ে জলমহল দখলের জন্য লড়াই করে। তাহলে গফুর কি আগেই তাদের ভিতরটা কাঁপিয়ে দেয়নি?
নাট্যকারের বক্তব্য মতো গ্রামের লোকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে নাটক করার পক্ষে।
অন্যদিকে নাটক বানচাল করার জন্য চেয়ারম্যান ও হেডমাস্টার একই জায়গায় ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল ডাকে। নাট্যকর্মীকেও চেয়ারম্যান ভয় দেখায়। তাতে কাজ হয় না, দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়ায়। সেই সময় পাগল চরিত্র মাখন এসে বলে, ‘যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু কখনও ভালোবেসে কথা বলে না যুদ্ধ যুদ্ধই, যুদ্ধের ময়দানে মুখে কোন কথা হয় না তখন জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় শাণিত তরবারির ভাষায়। এটাই ঐতিহাসিক নিয়ম। ডু অর ডাই।’
মাখন যতোই জ্ঞানী হোক, একজন মানসিকভাবে অসুস্থ লোক রাজনৈতিক শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে না, যা আবদুল্লাহহেল মাহমুদের এই নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যেতো না, রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতো না, শোনা গেছে তখন নাট্যকাররা কৌশলগত কারণে পাগল চরিত্রের মুখ দিয়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক বা প্রতিবাদমূলক সংলাপ বলাতেন। যা একদা রাজনৈতিক কৌশল হলেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা হিসাবে বিবেচিত নয়। সে কৌশল আজ গ্রহণ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। পাগলরা সবসময় মূল্যবান কথা বলে এইরকম ভাবনা নিয়ে অনেকে আজও তাঁদের নাটকে জ্ঞানী-পাগলের একটি চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন। মাহমুদও নিজের নাটকে তাই করেছেন। বিচ্যুতি দিয়ে যার শুরু তাকে স্খলন থেকে স্খলনান্তরে ক্রমশই নেমে যেতে হয়। মাহমুদের নাটকে এরপর তাই ঘটতে থাকে।
মাহমুদের নাটকে মাখন বিরাট বিপ্লবী ও সমাজবিজ্ঞানী হয়ে দেখা দেয়। মাখনের কথায় চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে তাকে চলে যেতে বলে। মাখন চলে যেতে অস্বীকার করলে চেয়ারম্যান তার গলা টিপে ধরে। জয়গুন তখন মঞ্চ তৈরির শাবল দিয়ে চেয়ারম্যানের মাথায় আঘাত করলে চেয়ারম্যান মারা যায়। ইতিহাসে শোষকরা যে পরাজিত শক্তি তা বোঝানোর জন্য শোষককে যেন-তেন প্রকারে নাট্যকার হত্যা করার চেষ্টা করেন। সেজন্য চেয়ারম্যানের দ্বারা মাখনের গলা টিপে ধরা এবং জয়গুনের দ্বারা চেয়ারম্যানকে আঘাত করার গল্প নাট্যকারকে সাজাতে হয়। মনগড়া এসব গল্প সংগ্রাম সম্পর্কে দর্শকদের কোনো ধারণা দেয় না। বিপ্লবে শোষকশ্রেণীর পরাজয় ঘটে সন্দেহ নেই, তবে তার পূর্বে বহু শোষিত-বুদ্ধিজীবীকে প্রাণ দিতে হয়।
শোষিতদের বহু রক্ত ঝরার পরই সংগ্রামে সাফল্য আসে। ইউরোপে নবজাগৃতির সাফল্য ছিলো ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সাফল্য। সে সাফল্য লাভের আগে ব্রুনো, কপারনিকাসসহ বহু বিজ্ঞানীকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। দীর্ঘকাল গীর্জার হাতে নিগৃহীত হবার পর, রক্তাক্ত হবার পর বিজ্ঞান সাফল্য লাভ করে। তারপরেও গীর্জাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা আজও সম্ভব হয়নি। যাজকরা আজও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। হাজার হাজার বছরের মানুষের বিশ্বাসকে একদিনে কেন, শত বছরেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। শাসকশ্রেণীকেও তাই কথায় কথায় উৎপাটিত করা যায় না। শ্রেণীসংগ্রাম তাই দিবাস্বপ্ন নয়। দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করার ব্যাপার।সাত পুরুষের ঋণ নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে নাট্যকর্মী বলে, ‘নাটক শুরু হবার আগেই মঞ্চস্থ হয়ে গেল নাটকের শেষ দৃশ্য।
শেষ দৃশ্য কি হবে এ নিয়ে আমরা সবাই ছিলাম শঙ্কিত কিন্তু জয়মনই তার সিদ্ধান্ত দিয়ে টেনে দিল যবনিকা, তারপর কি হয়েছিলো জানি না, শুধু এইটুকুই জানি সেদিন হাজার মানুষের সামনে মঞ্চস্থ হয়েছিলো নাটক আর সেখানে আমার ভূমিকা ছিলো গৌণ। কতো সহজে আবদুল্লাহহেল মাহমুদ ইতিহাসের শেষ দৃশ্য তৈরি করে ফেলেন। কোনো রক্তপাত ছাড়াই শোষিতের হাতে শোষকের মৃত্যু। যে-কোনো নাটকে অবশ্যই রূপকের ব্যবহার চলতে পারে। সেই রূপক হতে হবে আবেগাশ্রয়ী কোনো মিথ্যাচার নয়, বিজ্ঞানসম্মত সত্যকেই শুধু সেখানে উদ্ঘাটিত করতে হবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে জয়মনের দ্বারা চেয়ারম্যানকে হত্যা এটা এক ব্যক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র।
শোষিতশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম এটা নয়। শ্রেণীসংগ্রাম হবে সুসংবদ্ধ, পরিকল্পিত। তাৎক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশের চেয়ে পরিকল্পিত আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে এক ধাপ এগিয়ে নেবে, চূড়ান্ত বিপ্লবের জন্যই লড়বে শ্রমিকশ্রেণী। তাৎক্ষণিক এইসব ক্ষোভ হঠকারী সিদ্ধান্তেরই নামান্তর, তা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতিই করে থাকে।
মার্কসবাদীরা তাৎক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশ বা বিছিন্ন আন্দোলনকে সমর্থন করে না, তারা শত্রুর ওপর সুসংগঠিত আক্রমণ চালাতে চায় শত্রুকে ভালোভাবে ঘায়েল করার জন্য। জয়মনের এই তাৎক্ষণিক বিদ্রোহে শত্রুপক্ষ পরাজিত হয় না, কোনো এক ব্যক্তি নিহত হয় মাত্র। আর তার পরিণামে এ নাটকে জয়মন জেলখানায় বসে মৃত্যুর প্রহর গোনে। জয়মনের দ্বারা চেয়ারম্যানকে হত্যা সেখানে কোনো বিপ্লবী চিন্তার ইঙ্গিত দেয় না। মার্কসবাদীদের কাছে প্রাণ দেয়া-নেয়াটাই বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্দেশ্য সাধন করা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সবকিছুকে দেখতে হবে। মার্কসবাদীদের প্রথম কাজ মানুষকে সমাজবিজ্ঞান সচেতন করা। যে-কোনো আক্রমণ করার আগে জানা কেন সে আক্রমণ করছে, তারপরের পরিণতিটি কী।
পরবর্তী পদক্ষেপ, চূড়ান্ত পদক্ষেপ না জেনে মার্কসাবাদীরা কোনো আক্রমণ চালায় না। রাজনৈতিক নাটকও সে ধরনের উস্কানিকে প্রশ্রয় দেয় না। সাত পুরুষের ঋণ নাটকে যে নাট্যকর্মী গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হবার, লড়াই করবার উস্কানি দেয় সে তার পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। সেজন্য নাটকের শেষে এসে সে বলে তারপর কী ঘটেছিলো সে জানে না। ঘটনার পর সে তার পূর্বের আশ্রয়ে ফিরে এসেছিলো।
মার্কসবাদী আন্দোলন এক দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপার, সেখানে যে-কোনো আক্রমণ, যে-কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হবে, দীর্ঘ ও চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। সেখানে একটি ছোট গ্রাম্য আন্দোলনও হবে সারাদেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের যে পরিকল্পনা তারই অংশ হিসাবে। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কর্মসূচিকে মাথায় রেখেই সেখানে সব পরিকল্পনা নেয়া হবে। মার্কসবাদী নাট্যকারের দায়িত্বই হচ্ছে মানুষের অসংলগ্ন নানা সংগ্রামকে দ্বান্দ্বিকতার আলোতে আনা, তাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা এবং তার ভিতরকার নানাক্রটিগুলোকে চিহ্নিত করা। শুধু ঘটনার বিবরণ দেয়া তার কাজ নয়।
সাত পুরুষের ঋণ নাটকের শুরুতে শহরের এক যুবক বিপ্লবের বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামে। শহরের শিক্ষিত সচেতন ছেলেরাই বিপ্লবের বার্তা গ্রামে পৌঁছে দেবে সেটা ঠিকই আছে। কিন্তু সেখানকার মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রথম কাজ স্থানীয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকে উস্কে দেয়া নয়, প্রথম কাজ শোষিত মানুষের চিন্তার জগৎটাকে গড়ে দেয়া। সারা পৃথিবীব্যাপী যে শোষণ চলছে সেটা কেন, তার সমস্ত নাড়ি-নক্ষত্র তাদেরকে চিনিয়ে দেয়া।
যখন শোষিতরা সমাজবিজ্ঞানের গতিপথ আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে, তখন সে নিজেই তার শ্রেণীর ভাগ্য পাল্টাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। সেজন্য মার্কসবাদী বা রাজনৈতিক নাটকের কাজ প্রথম লড়াইয়ের কথা বলা নয়, যাদের বিরুদ্ধে লড়বে বা যে সমাজে তার বাস, সেই সমাজ এবং শত্রুর সত্যিকার পরিচয়টা পরিষ্কার করা। তা আরণ্যকের কোনো নাটকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে দেখতে পাওয়া যায় শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তেই উস্কে দেয়া হচ্ছে ইতিহাসের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও না দিয়েই এবং বিচ্ছিন্ন তাৎক্ষণিক ঘটনাগুলোকেই মনে করা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম। পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ছাড়া সর্বহারারা প্রকৃত সর্বহারাশ্রেণী হয়ে উঠতে পারে না। সর্বহারাশ্রেণী প্রকৃত সর্বহারাশ্রেণী হয়ে ওঠার পরেই আসে শ্রেণীসংগ্রামে অংশ নেয়ার প্রশ্ন। আরণ্যকের সব নাটকেই সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত।
মূলত আশির দশকে মঞ্চস্থ আরণ্যকের আলোচ্য নাটকগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় পঞ্চাশের দশকে মঞ্চস্থ আসকার ইবনে শাইখের নাটকগুলোর। স্বাধীনতার পূর্বে পঞ্চাশের দশকে শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা না দিয়ে শাইখের নাটকে গ্রাম বাংলার শোষক-শোষিতের প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিলো, স্বাধীনতার পর আরণ্যক শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে সেই একই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করে।
পার্থক্য শুধু এই যে, আরণ্যক নিজেকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রচারক হিসাবে আখ্যা দিয়ে নাটকগুলো মঞ্চায়ন করে, শাইখ তেমন কোনো ঘোষণা দেননি। বিষয়বস্তুর তুলনামূলক বিচারে শাইখের নাটকের বক্তব্য আরণ্যকের উল্লিখিত নাটকগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জল ছিলো। শাইখের নাটকে যেমন বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব ছিলো, শিল্পমান দুর্বল ছিলো, আরণ্যকের নাটকও তাই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাই যতোই রাজনীতি, সমাজ পরিবর্তন আর শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেয়া হোক স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কোনো পার্থক্য দেখা যায় না, বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় মেলে না। সত্তর দশকে যা দেখতে পাই, আশির দশকেও তাই-কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নাটক সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ধারণ করতে পারছে না। এবং একথাও সত্যি, সমাজবিজ্ঞানের চেতনা না থাকলে শ্রেণীসংগ্রামের নাটক হয় না।
বিস্তারিত গবেষণায় দেখা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে স্বাধীনতা পূর্বকালের নাটকের বিষয়বস্তু নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ ছিলো। নাটকীয়তা ছাড়া নাটক হয় না; কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেখা যায় সমাজ পরিবর্তনের নামে, শ্রেণীসংগ্রামের নামে নাটকগুলো নাট্যগুণ হারিয়ে ফেলে মোটাদাগের গল্পে পরিণত হয়। নাটকীয়তাপূর্ণ বিরাট বিরাট চরিত্র সৃষ্টি কিংবা কল্পনার কোনো স্থান সেখানে নেই। রূঢ় বাস্তবতারও কোনো প্রতিফলন সেখানে পাওয়া যায় না; এমনকি স্বভাববাদের যে ফটোগ্রাফিক সত্য, তার দেখাও মেলে না। নাট্য রচনার সাফল্য নির্ধারিত হয় দুভাবে-একদিকে বিষয়মুখিতা এবং অন্যদিকে কল্পনা। রাজনৈতিক নাটকে সে কল্পনা সম্প্রসারিত হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্যচর্চায় সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা গঠনমূলক কল্পনার জায়গায়টাই তৈরি হয় না; মোটাদাগের কিছু সংলাপে নাটকগুলো হয়ে ওঠে শ্লোগান।
বহু নাট্য-ব্যক্তিত্বই বলে গেছেন মোটা দাগের গল্প মানে নাটক নয়, সে গল্পে যতই বিপ্লবী বুলি থাক না কেন। আলবেয়ার কামু বলেছিলেন, মানুষের ভিতরে যে সত্য লুকানো থাকে, তার অন্তরে যে রহস্য থাকে, সে সম্বন্ধে যার ঔৎসুক্য আছে সে যেন থিয়েটারে আসে। বাংলাদেশের শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকারদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই দেখা গেছে মানুষের অন্তরের জগৎকে বাদ দিয়ে তাঁরা বাহ্যিক দিকটাকেই নাটকের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।
আবদুল্লাহহেল মাহমুদের নানকার পালা নাটকে তাইই দেখা যায়। নানকার পালা আরণ্যকের দশম প্রয়োজনা। এ নাটক সম্পর্কে ‘আরণ্যকের বিশ বছর’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলো, নানকার পালা হলো এই বাংলার অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের একটি নানকার বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। আরণ্যকের নাট্যচর্চায় আর একটি সচেতন রাজনৈতিক বক্তব্য সমৃদ্ধ এ নাটক দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সকল শ্রেণীর দর্শকের। দেখা যাক, আরণ্যক যে নাটক নিয়ে এতো আপ্লুত সে নাটকটিতে রাজনীতি এসেছে কীভাবে।
নাটকের শুরুতে দেখা যায়, হাওড় এলাকায় কাজ করতে এসেছে একদল ক্ষেতমজুর, স্থানীয়ভাবে যারা জিরাতী নামে পরিচিত। বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা কাজ করতে আসে গেন্দু মিয়ার বাড়ি। কাজের শেষে মজুরি হিসাবে ধান নিয়ে ফিরে যাবে। সেই ধানে তাদের চারপাঁচ মাস খোরাকি চলে, কারো কম কারো বা বেশি। সেই জিরাতীরা সারাদিন কাজের শেষে রাতে কাশেমের কাছে নানকার বিদ্রোহের গল্প শোনে।
নানকার বিদ্রোহের ঘটনা শুনতে শুনতে তারা খবর পায় গেন্দু মিয়া এবার তাদের ধান কম দেবে। গেন্দু মিয়া ধান কম দিতে চাইলে কাশেমের কাছে নানকার বিদ্রোহের গল্প শুনে শুনে তারাও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। নিজেরাই নিজেদের ধান হিসাব মতো গোলা থেকে বুঝে নিতে চায়। গেন্দু মিয়া তখন পুলিশ নিয়ে এসে সবাইকে ধরিয়ে দেয় এবং সকলেই অনেকদিন ধরে জেল খাটে। এটাই হলো নাটকের সারমর্ম।
নাটকটির এই বক্তব্য সঠিক যে, খণ্ডিত এসব বিদ্রোহ কখনো সার্থকতা পায় না। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের চাপের কাছে তা নতি স্বীকার করে। তবে নানকার বিদ্রোহের সঠিক চিত্রটি এ নাটকে ধরা পড়ে না। বাস্তবের দুই শ্রেণীর লড়াইটা দেখালেই নাটক সত্যিকারের রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠে না, সেই লড়াইয়ের প্রতিটি কানাগলিও সেখানে দেখিয়ে দিতে হয়। ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণ থাকতে হয়, মানব মনের জটিলতাগুলোকেও সেই সাথে স্থান দিতে হয়। নাট্যকার ব্রেস্ট দেখাচ্ছেন, রাজনৈতিক থিয়েটার তৈরির জন্য একটি ঐতিহাসিক নাটককে যুগের সমগ্র বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে হবে এবং মঞ্চে তাকে জীবন্ত হয়ে উঠতে হবে। যুগের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা ঐতিহাসিক নাটকের অবশ্যই দায়িত্ব। যে-কোনো বিদ্রোহই একটি ঘটনাবহুল ব্যাপার।
তার থাকে নানা দিক, নানা প্রসঙ্গ, নানা অনুসঙ্গ। যেমন দেখা যায় উৎপল দত্তের তিতুমীর নাটকে, মহাবিদ্রোহ নাটকে, কল্লোল নাটকে, তীর নাটকে। বিদ্রোহের পাশাপাশি তার চারদিকের ঘটনাবলী, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুকিছুই ধরা পড়ে সে-সব নাটকে, বিদ্রোহের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। নানকার পালা নাটকে তা নেই। নীরস সব ঘটনা সেখানে নাটককে শুধু ভারাক্রান্তই করে। সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও গ্লানি থেকে নানকার বিদ্রোহের উৎপত্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি বিদ্রোহের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক কারণ নিহিত আছে নাট্যকার তা পরিহার করেছেন। শুধুমাত্র সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সময় ও ঘটনাটিকে তিনি পর্যালোচনা করেছেন।
উৎপল দত্ত বলেন, বাস্তবে যা ঘটতে দশ বছর লাগে নাটকে তাকে তিন ঘণ্টার পরিসরে বাঁধতে গেলে নাট্যকারের ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। বাস্তবের বিক্ষিপ্ততা, অসংলগ্নতা ও আকস্মিকতাকে বর্জন করে নতুন করে গল্প সাজাতে হয়, নতুন চরিত্র আঁকতে হয়। দশবছরের ঘটনাকে তিন ঘণ্টার পরিসরে বাঁধতে গেলে তাকে সুসংগঠিত করতে হয়।** আবদুল্লাহহেল মাহমুদের নাটকে সেই দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
পৃথিবীতে কোনো বিদ্রোহই তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হয় না। দীর্ঘদিনের একটি প্রস্তুতি থাকে তার পশ্চাতে। মানুষের ক্রোধই শুধু বিদ্রোহের কারণ নয়। আরো নানান কারণ থাকে। আপোষহীন বা গোঁয়ার মনোভাবই যদি আন্দোলনকারীদের চরিত্রের প্রধানতম গুণ হয় তাহলে তার বৈপ্লবিক চেতনা বুদ্ধি নির্ভর না হয়ে পুরোটাই আবেগ নির্ভর হয়ে পড়ে। নাট্যকার তাঁর এ নাটকের দুটি বিদ্রোহকেই তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠিত করেন। নাট্যকার দেখান, নানকার বিদ্রোহ ঘটে জমিদার কর্তৃক মতি নামে একজন পাহারাদারকে মেরে ফেলার পর। মতির স্ত্রী এ ঘটনায় তার গোত্রের লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। নানকাররা সংগঠিত হয়।
একটি মৃত্যুকে ঘিরে কখনও একটি বিদ্রোহ সংগঠিত হয় না, যদি সেই বিদ্রোহীদের মনে আগে থেকেই কোনো ঘৃণা জমে না থাকে। বিদ্রোহের সেই দিকটা যেমন এ নাটকে অনুপস্থিত, তেমনি যে সাম্যবাদীরা এই বিদ্রোহ সংগঠিত করতে প্রেরণা দেয় তাদের বিষয়ও নাটকে সেইভাবে আসেনি। বিশেষ করে বামপন্থী সচেতনতার পর্বটুকু নাটকে একেবারেই নেই। এবং এই অস্পষ্টতা অনেক বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছে।
নানকার বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত কেন পরাজিত হয়েছিলো সে প্রশ্নও এখানে অমীমাংসিত। শ্রমিকদের, শোষিতদের সংঘটিত যে-কোনো বিদ্রোহকেই মার্কসবাদীরা গুরুত্ব দেয়। বিদ্রোহীরা যদি পরাজিত হয় তার কারণও ব্যাখ্যা করে। মার্কসবাদীরা যখন কোনো সত্য ঘটনাকে নাটকের কাহিনী হিসাবে বেছে নেয়, তখন তাদের মূল লক্ষ্য হয় শুধু তার মাহাত্ম্য প্রচার নয়, শুধু ঘটনার বিবরণ দেয়া নয়, ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে নির্মোহভাবে তার মূল্যায়ন করা। ঘটনার সত্যতাই শুধু বড় কথা নয় বরং কীভাবে সেটাকে দর্শকদের মানসপটে তুলে ধরা হচ্ছে সেটাই বড় ব্যাপার। নানকার পালা নাটকটিতে শুধু বিদ্রোহীদের মাহাত্ম্যই প্রচার করা হয়েছে, বিদ্রোহীদের বা বিদ্রোহের ভুলত্রুটিগুলোকে তুলে ধরা হয়নি।
মার্কসবাদীরা মনে করেন, জনগণের নিজেরও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যেগুলিকে জনগণের নিজেদের মধ্যেই সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দূর করতে হবে এবং এ ধরনের সমালোচনা-আত্মসমালোচনায় রাজনৈতিক নাট্যেরও এগিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। জনসাধারণের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা দরকার। কিন্তু এটা করার সময় যথার্থভাবে জনগণের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে এবং জনগণকে রক্ষা করার ও শিক্ষিত করে তোলার একান্ত আন্তরিক আগ্রহ থেকেই কথা বলতে হবে। শোষিতদের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করার অর্থ হলো শত্রুর পক্ষ নেওয়া। মাও বলেন, মানব ইতিহাসের স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর আমরা জয়গান করবো না কেন?
কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকেও তুলে ধরতে হবে এবং তাদের একজন বন্ধু হিসেবেই।* বুর্জোয়া মহৎ নাট্যকারদের রচনার মধ্যে যতোই বুর্জোয়া ভাবধারা থাক, যতোই তাঁরা বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের জয়গান করুক, বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবনের অন্ধকার দিকটিও তাঁদের রচনায় ভাস্বর। সেজন্যই নাটকগুলো বিশেষ যুগের না হয়ে চিরকালীন সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এককালীন সাধারণ সম্পাদক গণনাট্যের কিছু কিছু নাটক সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের নেতাদের গণনাট্যের নাটকে এতো ভালো মানুষ হিসাবে দেখানো হয় যে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। নাট্যকাররা শোষিত মানুষের পক্ষাবলম্বন করে নাটক রচনা করবেন ঠিকই, কিন্তু এই পক্ষাবলম্বনের অর্থ এই নয় যে নাট্যকার তাঁর মতামতের নিতান্ত তল্পিবাহক কিছু চরিত্র মঞ্চে এনে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নাট্যকারের মত ও উদ্দেশ্য অতি স্থূলভাবে দর্শকদের উপর চাপিয়ে দেবেন।** হীরেন ভট্টাচার্য সেসব নাটক সম্পর্কে লিখেছিলেন, মোট সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাদের নায়করা এতো ভালো মানুষ যে সে আর রক্তমাংসের, দোষগুণ মিশ্রিত, বৈপরীত্য সমন্বিত মানুষ হয়ে ওঠে না।
এরা ভালো ভালো বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলে, মঞ্চে বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে চায়।** এই সব নাটকে জমিদারদের নারীলোলুপ চেহারা, নারীর উপর বলাৎকার করার দৃশ্য যতো থাকে, শোষিতদের বেলায় তা আর থাকে না। শহরের সাধারণ বেশ্যালয়গুলো যে তৈরি হয় শ্রমিকদের জন্যই, নাটক লিখবার সময় বিপ্লবী এসব নাট্যকাররা তা অনেক সময়ই ভুলে যান। আরণ্যকের নাটকগুলোতে তাই দেখতে পাওয়া যায়, কোনো নাটকেই শোষিতদের কোনোরকম দোষত্রুটি ধরা পড়েনি। শোষকদের চরিত্রের কোনো ভালো গুণ যেমন এসব নাটকে নেই, তেমনি শোষিতদের চরিত্রের মধ্যেও বীরত্ব ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া কোনো ধরনের দোষ লক্ষ্য করা যায় না।
এসব নাটকে শ্রমিক-কৃষক বা শোষিতদের চেহারা হয়ে ওঠে মহান। মূল সত্যিটা কী তাই? চাষী ঢের বেশি সংগ্রামী সন্দেহ নেই, লড়াইয়ে সে নির্মম-কিন্তু তার বাইরে কৃষক সংকীর্ণমনা, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, জমি-লোভী। সে নিজের সন্তান ও স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয় নিজ ইচ্ছাকে। কৃষক চরিত্রের থাকে আরো নানাধরনের নীচতা। ক্ষমতাবানদের সে তোয়াজ করতে পছন্দ করে, সুযোগ নিতে পছন্দ করে। নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস রাখে। শ্রমিকরাও একই রকম। যে শ্রমিক রাজনীতি সচেতন নয়, সে মোটেই মহান নয়। সে অনেক ব্যাপারে জঘন্য রকম পশ্চাদপদ। অথচ উল্লিখিত নাটকগুলোতে শ্রমিকদের চরিত্রের নানা দ্বন্দ্বগুলোকে নাট্যকাররা বাদ দিয়ে তাদের একপেশে ছবি এঁকেছেন।

শ্রমিক-কৃষক বলতে উল্লিখিত নাটকে দেখা যায় সংঘবদ্ধ কিছু মানুষকে, যারা নানাভাবে শোষিত এবং শেষ পর্যন্ত যারা বিদ্রোহ করে। দোদুল্যমান কোনো শ্রমিক- কৃষকের চেহারা এসব নাটকে নেই। যে-কোনো শ্রেণীসংগ্রামের নাটকে লড়াইটাই হতে পারে প্রধান বিষয়বস্তু। সেটাই পটভূমিকা। তবে শুধু সেখানে ঘুরলেই চলবে না। দুই পক্ষের মানুষগুলোর যে দ্বিধা-সংশয় দ্বন্দ্বের মানসিক জগৎ-সেগুলোও তুলে ধরতে হবে। উৎপল দত্ত লিখছেন, ‘দুই শ্রেণীর সংঘর্ষ বা দুই জাতির সংঘর্ষ হচ্ছে বাস্তব স্থূল ঘটনা। নাট্যকার কি করেন? তিনি ঐ সংঘর্ষের পেছনে যে তীব্র ঘৃণা কাজ করছে, অর্থাৎ দুই পক্ষের মনের মধ্যে যে বিষ জমা হচ্ছে সেটাকে আশ্রয় করেন। তিনি তারপর একটা পক্ষ নেন।’
দুই পক্ষেরই দৃঢ় ও দোদুল্যমান চরিত্রগুলোর মানস, ঘটনার সাথে সাথে ফুটে উঠবে নাটকে। সেভাবেই তো নাটকে চরিত্র সৃষ্টি হবে-চরিত্রগুলো দর্শক টানবে, তার চিন্তার জগতে নাড়া দেবে। বিপ্লবী নাট্যকার কতগুলো বাঁধা বুলি দিয়ে তার নাটককে করে রাখবেন একটা সন্তা প্রবন্ধের মতো কিংবা চরিত্রগুলোকে একটা সূত্রের মধ্যে ফেলে শোষক আর শোষিতদের বোঝাতে চাইবেন, সেটা রাজনৈতিক নাটকের কাম্য নয়।
নাট্যকার মামুনুর রশীদ ও আবদুল্লাহেল মাহমুদ তাঁদের নাটকে শোষক- শোষিতদের দ্বন্দ্ব তুলে ধরে এ কথা বোঝাতে চান, সংঘশক্তি মানব মুক্তি অর্জনের হাতিয়ার। তাঁরা দুজনেই শোষিতদের এক হওয়ার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মার্কসবাদীরা শুধু শোষিতদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাকেই মানব মুক্তির কারণ বলে মনে করেন না। মার্কসবাদীরা মনে করেন, শোষিতদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সচেতনভাবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা গেলে শোষিতদের এক হয়ে কোনো লাভ নেই। সেই জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বা শোষিতদের শ্রেণীচৈতন্য অর্জন করাটাও সেখানে একটা প্রধান দিক।
রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্তের ‘জপেন দা জপেন যা’ গ্রন্থের জপেনদার ভাষায়, ‘বিপ্লবের জন্য উন্নত শির মানুষ লাগে না, লাগে হস্তীযুখ পালবদ্ধ চিন্তাশক্তিহীন জানোয়ার এসব কথা কয় সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে প্রচারকরা। মামুনুর রশীদ বা আবদুল্লাহহেল মাহমুদের নাটকে যে ধরনের শোষিতদের চরিত্র সৃষ্টি করা হয়, কিংবা বিভিন্ন নাটকে ঐ ধরনের যে শ্রমিকদের চরিত্র সৃষ্টি করা হয়, সেই সব শোষিত চরিত্রদের ব্যঙ্গ করে উৎপল দত্ত জপেনদাকে দিয়ে বলিয়েছেন, ‘কাল্পনিক বস্তির কাল্পনিক বিপ্লবী শ্রমিক তৈরি ক’রে তোরা তাকে ফুল বেলাপাতা দিয়ে পূজো করিস।
বাস্তবের ভয়ংকর বস্তির বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের সংগে তার কোন সম্পর্কই নেই। মামুনুর রশীদ ও আবদুল্লাহহেল মাহমুদের চরিত্ররাও ঠিক তেমনি, বাস্তবের চরিত্র থেকে বহু দূরে তাদের অবস্থান। দুজনেই কল্পনায় রং মিশিয়ে শোষিতদের যেমন সৃষ্টি করেন, তেমনি শোষকদের-ঠিক তেমনি শ্রেণীসংঘর্ষগুলো। দুজনের নাটকেই দেখতে পাই, যে করেই হোক একটা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক নাটক সেভাবে হয় না। রম্যা রলাঁ বলেছিলেন, জনগণের ওপর সাজানো ফর্মুলা চাপিয়ে দেওয়ার মতো দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই।
মামুনুর রশীদের পরবর্তী নাটক গিনিপিগ। নাটকের প্রধান খলচরিত্র সরকারি মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব। তার নাম আহমেদ আলী। সে গ্রামের ছেলে, যার বাপ- দাদা গ্রামের সামান্য চাষী। প্রথমে সে গ্রামেই বিয়ে করেছিলো। সেই ঘরে তার রাজা নামে একটি ছেলেও আছে। পরবর্তী সময় আহমেদ আলী সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি পেয়ে আর একটি বিয়ে করে এবং পূর্বের স্ত্রী ও পুত্রের সাথে আর কোনো যোগাযোগই রাখে না। দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার কন্যা আহমেদ আলীর আগের বিয়ে সম্পর্কে কিছু জানে না। আহমেদ আলী তার এক অধস্তন মোঃ আলীকে চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে। এই অধস্তন আহমেদ আলীর বাড়িতে যখন যা কিছু দরকার যোগান দিয়ে যায়। মোঃ আলী ও আহমেদ আলী দুজনেই ভিতরে ভিতরে পাকিস্তানপন্থী।
সরকারি ক্ষমতার শীর্ষে বসে লুটপাট করে খুব ভালোই দিন কাটছিলো আহমেদ আলীর। হঠাৎ সে সময় একদিন তার প্রথম স্ত্রী জুলেখা ছেলে রাজাকে নিয়ে গ্রাম থেকে হাজির হয় তার অফিসে। ধুরন্ধর মোঃ আলী রাজা ও তার বোরখা পরিহিত মাকে আহমেদ আলীর সাথে দেখা করতে দেয় না। মানুষ দুজন আহমেদ আলীর গ্রাম থেকে এসেছে জেনে তার সন্দেহ হয়। জুলেখা কিংবা তার ছেলে এর আগে কখনো আহমেদ আলীর অফিসে আসেনি, মোঃ আলী তাদেরকে আগে কখনো দেখেওনি; তাহলে তার হঠাৎ এ ধরনের সন্দেহ হবার কারণ দর্শকের কাছে বোধগম্য নয়। সচিবের গ্রাম থেকে কেউ দেখা করতে এলে তাকে সন্দেহ করতে হবে কেন?
নিজগ্রাম থেকে বহু লোকজন সচিবের সাথে দেখা করতে আসবে সেটাই তো স্বাভাবিক। নাটকের ঘটনা অনুযায়ী জুলেখা ও রাজার আসল পরিচয় না জেনেই মোঃ আলী তাদের নিজের বাসায় নিয়ে যায়। গ্রাম থেকে আসা রাজা ও তার পর্দানসীন মা জুলেখাও কোনোরকম পরিচয় ছাড়াই এক কথায় অপরিচিত একজন মানুষের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র আপত্তি করে না।
রাজা ও তার মাকে নিজ বাড়িতে রেখে আসার পর মোঃ আলী সচিবকে জানায় গ্রাম থেকে দুজন লোক তার সাথে দেখা করতে এসেছে। আহমেদ আলী ঠিক বুঝতে পারে না গ্রাম থেকে কারা তার সাথে দেখা করতে আসতে পারে। সে এ নিয়ে কৌতূহলও বোধ করে না। বিদেশে যাবার ব্যস্ততার জন্য তাদের সাথে সে দেখা করে না।
রাজা পরদিন একা এসে হাজির হয় আহমেদ আলীর বাসার ঠিকানায়। কীভাবে সে বাসার ঠিকানা পেল নাটক দেখে জানতে পারা যায় না। রাজার এখানে আসবার উদ্দেশ্যও রোঝা যায় না। রাজা তার মায়ের সাথে ঢাকা এসেছে কিন্তু সে তখনো জানে না তার মা কেন আহমেদ আলীর সাথে দেখা করতে এসেছে এবং আহমেদ আলীর সাথে তার মায়ের সম্পর্ক কী। রাজা ভিতরে ঢুকতে গেলে নিরাপত্তা প্রহরীরা তাকে বাধা দেয়। গ্রাম থেকে আসা রাজা নিরাপত্তা প্রহরীদের বাধা উপেক্ষা করে সচিবের বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চায়। কীসের জোরে রাজার মতো সাধারণ এক গ্রামের ছেলে নিরাপত্তা প্রহরীদের অবজ্ঞা করে তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। সে সময় সচিবের শিক্ষিত মেয়ে পপি আসে সেখানে তার বন্ধু রুবেলকে নিয়ে।
রাজা আহমেদ আলীর সাথে দেখা করতে এসেছে জেনেই পপি গ্রাম্য এ লোকটাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় সম্মানের সাথে। আহমেদ আলী তখন বাসায় নেই, কখন ফিরবে তা না জেনেই পপি রাজাকে বাসার ভিতরে অপেক্ষা করতে বলে। বাস্তবে কি এমন ঘটতে পারে, একজন সচিবের মেয়ে বাবা বাড়িতে না থাকা সত্ত্বেও অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবে?
বড় জোর সে তাকে অফিসে যাবার পরামর্শ দিতে পারে। রাজা আহমেদ আলীর জন্য তার বাসায় অপেক্ষা করে। আহমেদ আলীর কাছে রাজার কোনো কাজ নেই, তবে কোন্ কাজে বা কী কথা বলার জন্য সে আহমেদ আলীর অপেক্ষা করে দর্শক তা বুঝতে পারে না। পপি গ্রাম্য এই ছেলের সাথে খুবই আন্তরিকভাবে আলাপ জমায়। রাজার বোকা বোকা অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় সে খুব আগ্রহের সাথে। রাজা ও পপি প্রথম আলাপেই পরস্পরকে তুমি বলে সম্বোধন করতে থাকে। গ্রাম্য একটি ছেলের সাথে সচিবের মেয়ের এই ঘনিষ্ঠ সখ্য গড়ে ওঠা বাস্তব সম্মত কি-না সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
রাজার সাথে গল্পে গল্পে যখন পপি রাজার মায়ের কথা জানতে পারে, পরদিন রাজার মাকেও সে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে বলে। যার সাথে পূর্ব জানাশোনা নেই, গ্রামের সেইরকম একজন লোকের জন্য পপির এই আন্তরিকতার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের নানা বিভ্রান্তি রয়েছে নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। পরদিন যখন রাজা তার মাকে সঙ্গে করে পপিদের বাড়িতে আসে, পপির মা রাজিয়া তাদের ভিক্ষুক মনে করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়। রাজা ও তার মায়ের পক্ষে পপি তখন নিজের মায়ের সাথে ঝগড়া বাধায়। মা অফিসে আহমেদ আলীকে ফোন করে।
আহমেদ আলী এসে নিরাপত্তা প্রহরীদের দিয়ে তাদের বের করে দেয়। ধরে নেয়া যেতে পারে আহমেদ আলী বোরখা পরিহিত জুলেখাকে চিনতে পারে না। কিন্তু জুলেখা ঢাকাতে আহমেদ আলীর সাথে দেখা করতে এসেও কেন নিজের পরিচয় দেয় না, সেটার কোনো ব্যাখ্যা নাটকে নেই। দেখা করার সুযোগ পেয়ে জুলেখা পরিচয় না দিয়ে চলে যাবে কেন? নাট্যকার এখানে বাংলাদেশের এক সচিবের মেয়েকে কতোটা মহত্ত্ব দিতে চায় তা দেখা যায় পরের ঘটনাবলীতে। পপি জুলেখা ও রাজার পরিচয় না জেনেও তাদের হয়ে বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। বাবা পপির কথার কোনো গুরুত্ব দেয় না।
নাটকের এখানে এসে হঠাৎ বোঝা যায়, আহমেদ আলী আসলে বিদেশে যাচ্ছিলো পপিকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো স্কুল-কলেজে ভর্তি করে দেবার জন্য। পপির ইচ্ছাতেই বাবা তা করতে যাচ্ছিলো। রাজা ও রাজার মায়ের সাথে তার বাবার আচরণের জন্য শেষ মুহূর্তে পপি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় সে বিদেশে যাবে না। গ্রামের দুজন মানুষের জন্য সে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বিসর্জন দেয় যাদের সাথে তার কোনো পূর্ব সম্পর্ক নেই।
বাংলাদেশের একজন সচিবের মেয়ের বিদেশে পড়তে যাওয়ার চেয়েও গ্রামের দুজন মানুষকে উপকার করতে না পারার যন্ত্রণাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বাবা পপিকে রেখে বিদেশে চলে যায়। বাবার তো পপির জন্যই বিদেশে যাবার কথা, সেই পপি বিদেশে যাওয়া বাতিল করলেও বাবা কেন বিদেশে চলে গেলো তার কোনো ব্যাখ্যা নাট্যকার দেন না। সচিব কন্যা পপি সিদ্ধান্ত নেয় সে রাজা আর রাজার মাকে খুঁজে বের করবে। পপির কাছে ওদের কোনো ঠিকানা ছিলো না। তা সত্ত্বেও পপি ঠিকই ওদের খুঁজে বের করে।
কীভাবে খুঁজে পেলো সে ব্যপারে দর্শকরা কিছুই জানতে পারে না। পপির সাথে রাজা এবং রাজার মা ফিরে আসে এবং পপিদের বাড়িতেই থাকতে শুরু করে, যে বাড়ি থেকে কয়েকদিন আগে তারা অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে। পপির মা রাজিয়া এ সময় বাড়িতে ছিলো না, বয়স্কা মেয়ে পপিকে বাড়িতে একা রেখে নিজে বাবার বাড়িতে বেড়াতে চলে গিয়েছিলো। গৃহকত্রীর অবর্তমানে রাজার মা জুলেখার সাথে এবং রাজার সাথে পপির খুব খাতির জমে ওঠে। সে ওদের কাছ থেকে গ্রামের গল্প শোনে, মনোযোগ দিয়ে রাজার গান শোনে। রাজার বাঁশী বাজানো শুনে তো পপি রাজার প্রেমেই পড়ে যায়। সে রাজাদের গ্রামে যেতে চায় যেখানে থাকবে শুধু রাজা আর পপি।
রাজা অবশ্য তার প্রতি পপির এই প্রেম ধরতে পারে না। সে সরলভাবে পপির সাথে মিষ্টি সম্পর্ক চালিয়ে যায়। এরমধ্যে রাজাদের কোনো খোঁজখবর না পেয়ে রাজার মামাও চলে আসে গ্রাম থেকে। রাজার মামা নিরাপত্তা প্রহরীদের কোনোই পাত্তা দেয় না। পুলিশ তাকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিলে পুলিশের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সে পুলিশের সাথে মল্লযুদ্ধ করে জিতে যায়।
মামাকে দেখে রাজা-পপি সবাই খুব খুশি হয়। মামাও এ বাড়িতে থাকতে শুরু করে। রাজিয়া ফিরে এসে পপির সাথে অন্য সকলকে দেখে ক্ষেপে যায়। রাজিয়া সকলকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইলে পপি জানায়, তারা সকলে তার বাবার গ্রামের লোক সেই অধিকারেই এই বাড়িতে থাকবে। বাবা নিজেই যাদের একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে পপির এ ধরনের বক্তব্য প্রদানের কোনো যুক্তি মেলে না। নিজ গ্রামের লোক হলেই কি যে-কোনো লোকের একজন সচিবের বাড়িতে থাকবার অধিকার জন্মে যায়? রাজিয়া নিরাপত্তা প্রহরীদের দিয়ে সকলকে বের করে দিতে চায়। পপি রাজাদের পক্ষ নিয়ে নিজের মাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলে, নিরাপত্তা প্রহরীদের ডেকে কোনো লাভ হবে না।
রাজিয়া তাতে শুধু নিজের মান সম্মান নষ্ট করবে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, সচিবের স্ত্রীকে অসম্মান দেখাবার দুঃসাহস কি নিরাপত্তা রক্ষীরা কখনও করতে পারে? নিরাপত্তা রক্ষীরা মেয়ের কথা মতো গ্রামের লোকগুলোকে সচিবের বাড়িতে থাকতে দেয়ার জন্য সচিবের স্ত্রীর হুকুম অমান্য করবে এটা কি সম্ভব? নাট্যকারের ভাষ্য অনুযায়ী রাজিয়া কিন্তু মেয়ের এই কথা শুনে দমে যায়। নাট্যকারের চিন্তা এখানে বাস্তব প্রক্রিয়াকে, বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরকে ছাড়িয়ে যায়। নাট্যকার তাঁর কল্পনাকেই মনে করেন বাস্তব। নিজের খেয়ালী চিন্তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই তিনি সুবিধামতো বাস্তবতাকে ভাঙচুর করেন। ঐতিহাসিক বাস্তববাদের সত্য থেকে সরে দাঁড়ান। মামুনুর রশীদের এ নাটকে বারবার তা ঘটতে দেখা যাবে।
নাটকের গল্প অনুযায়ী তারপর রাজিয়া নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে মাস্তান ভাইকে পাঠায় এদের শায়েস্তা করার জন্য। বাংলাদেশের একজন সচিবের স্ত্রীর জন্য যেন আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। পপির মামা ছুরি হাতে এসে রাজাদের ভয় দেখাতে চাইলে গ্রাম থেকে আসা রাজার মামা মোটেই ভয় পায় না। পপির মামার হাত থেকে সে ছুরিটা কেড়ে নেয়। পপির মামা এরপর রিভলবার বের করলে রিভলভার দেখে রাজা কিংবা রাজার মামা কেউ ডরায় না। পপির মামার হাতে এক মোচড় দিয়ে রাজার মামা রিভালবারটাও কেড়ে নেয়। পপির মামা গ্রামের দুই বীরের সাথে লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। যারা দেশের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে গিনিপিগ নাটকে এভাবেই গ্রামের সাধারণ দুজন মানুষের কাছে তাদের হার হয়।
প্রশাসনকে তারা নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে না। বাংলাদেশের কোন্ বাস্তবতার চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেন তা বোঝা কঠিন। পপি গ্রামের তিনজন মানুষ নিয়ে পুরো বাড়ি দখল করে বসে। রাজার মা ও মামা নির্লজ্জের মতো গুণ্ডামি করে আহমেদ আলীর বাড়িতে থেকে যায়। যে-স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে তার বাড়িতে আশ্রয় নিতে জুলেখা লজ্জা বোধ করে না। আহমেদ আলীর বাড়িতে পূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় রাজাদের।
যখন আহমেদ আলী ফিরে এসে রাজিয়ার কাছ থেকে সবকিছু শোনে, সে পপির কাছে জানতে চায় ওরা কারা। পপি ভালো মানুষের মতো উত্তর দেয়, ‘তোমার সাথে কথা বলতে ওরা এসেছে এবার তুমি কথা বলো-আমার দায়িত্ব ছিলো ওদের তুমি না আসা পর্যন্ত এখানে থাকার ব্যবস্থা করা’। আহমেদ আলী তাদের আসল পরিচয় জানতে পেরে প্রথম স্ত্রী জুলেখাকে বলে, ‘কি জন্যে এসেছো? ছেলের চাকরী না আর কিছু?
বলো বলো-কিছু টাকা দিয়ে দেই-দেশে চলে যাও-এখানে এসেছো কেনো?’ পপি বাবার কাছে ওদের পরিচয় জানতে চাইলে বাবা পরিচয় বলে না। বোঝা যায়, পপি এতোদিন যাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে এসেছে তাদের পরিচয়টা জানাও প্রয়োজন বোধ করেনি। পপি তখন রাজাদের সামাজিক-পারিবারিক কোনো পরিচয় না জেনেই ঘোষণা দেয়, সে রাজাকে বিয়ে করবে। এই ঘটনায় আহমেদ আলীকে বলতে হয় যে, রাজা ও পপি ভাইবোন। রাজিয়া এই ঘটনা জেনে কেঁদে ফেললে আহমেদ আলী তাকে বোঝায় এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। জুলেখা, আহমেদ আলীর প্রথম স্ত্রী তখন জানায় সে আহমেদ আলীকে তালাক দিতেই এসেছিলো।
যেন তালাক দেবার জন্য প্রত্যেক স্ত্রীকেই স্বামী পর্যন্ত আসতে হয়, যেন গ্রাম থেকে তাকে তালাকনামা পাঠানো যেতো না। যে তালাক দেয়ার জন্য জুলেখা ছেলেকে নিয়ে ঢাকা এলো, স্বামীর অবর্তমানে তার বাড়িতে থাকলো, সেই তালাক নিয়ে নাটকের ঘটনা এখানেই থেমে গেল। জুলেখা তালাক না দিয়ে কিংবা এ ব্যাপারে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। ছেলের হাত ধরে জুলেখার ঢাকায় আসা এবং ঢাকায় অবস্থান করার কারণ তাতে একটি প্রহসনে পরিণতি পেল।
রাজারা চলে যাবার জন্য তৈরি হয়। শুধু ঘুরে দাঁড়ায় রাজার মামা। সে আহমেদ আলীকে বলে, ‘গাঙ্গের হোতের মত দিনও ঘোরবে একদিন। হেইদিন মোরা কিন্তু আবার আমু। কাচা বাইন্দাই আমু।’ রাজার মামার হঠাৎ এ কথা বলার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের ঢাকায় আসার মূল লক্ষ্যটাই হারিয়ে যায়।
পপি তাদের সাথে চলে যেতে চাইলে বাবা জোর করে পপিকে আটকে রাখে। নিজের টাই খুলে পপির মুখ বেঁধে ফেলে এবং চিৎকার করে বলে, ‘সিকিউরিটি, সিকিউরিটি, আরো ফোর্স ডাকো, এদেরকে পিটিয়ে বের করে দাও।’ যখন রাজারা নিজের ইচ্ছাতেই চলে যাচ্ছিলো তখন এই তিনজন লোকের বিরুদ্ধে ফোর্স ডাকা, পিটিয়ে বের করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশের কারণ বোধগম্য হয় না। রাজা চলে যায় পপিকে এই বলে, ‘চিন্তা কইরো না বোইন, মোরা কলাম আবার আমু’। আবার কেন সে আসবে তার কোনো কার্যকারণ নাটকে নেই। জোর করে যেন নাট্যকার একটা বিদ্রোহ ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন নাটকের শেষে।
সবকিছু জানার পর দ্বিতীয় স্ত্রী আহমেদ আলীকে ছেড়ে চলে যায়। এদিকে সুখবর আসে আহমেদ আলী মন্ত্রী হয়েছে। পপিকে হাত মুখ বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে, এ অবস্থায় সে বহু কষ্টে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লেখে রাজাকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একজন মানুষ কী করে চিঠি লেখে, ঘরে বন্দী অবস্থায় কোথা থেকে কাগজ- কলম পায় নাট্যকার তা দর্শকদের জানানো প্রয়োজন বোধ করেন না।
পপিকে দিয়ে বৈপ্লবিক একটি চিঠি লেখানোই নাট্যকারের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তার বাস্তবতা থাক না থাক। সচিবের মেয়ে কী করে বিপ্লবী হবার শিক্ষা পেল দর্শক জানতে পারে না, তবে তার চিঠির বক্তব্য হলো, ‘আমি বন্দী সেই দিন থেকে-কবে মুক্তি পাবো জানি না-তবে যদি মনে মনেও খবর পাই তোমরা এসে গ্যাছো কাছাকাছি তাহলে এ দূর্গ ভেঙ্গে আমরা বেরিয়ে আসবোই-আমি এখনো সব সময়ই চিঠি লিখি-তোমরা পাও কি না জানি না-যেদিন তোমাদের ডাক শুনতে পাবো সেদিন আর চিঠি লিখবোনা।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 10 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-২.jpg)
নাট্যকারের এই কাল্পনিক বিপ্লবীর সাথে সমাজবিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কসবাদীরা সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন এ ধরনের কোনো বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টির বিরোধী। মামুনুর রশীদ তাঁর গিনিপিগ নাটকের ভূমিকায় লিখছেন, সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে ভাবে গিনিপিগ। তৃতীয় বিশ্বের সামারিক জান্তা ও আমলারা শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার কারণে দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, কিন্তু এই বাস্তবতার একটা উল্টো পিঠও রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ যতই সক্রিয় হোক, যতই কিনে নিক বিশেষজ্ঞ, আমলা, সামরিক জান্তা বা রাজনীতিবিদদের, তবুও বিদ্রোহ অনিবার্য। সেই অনিবার্যতাই তার এ নাটক লেখার প্রেরণা। তবে নাটকে কার বিরুদ্ধে কোন অনিবার্য বিদ্রোহ মামুনুর রশীদ তুলে ধরতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় না।
নাটকে রাজার মামা বলেছে সে আবার ফিরে আসবে-সেটাই যদি তার বিদ্রোহ হয়, তাহলে সে বিদ্রোহ কি আমলার বিরুদ্ধে গ্রামের সাধারণ মানুষের? যদি তাই হয় তাহলে সে বিদ্রোহের কারণ কী? গ্রামের মানুষদের সাথে আমলার কোনো বিরোধের ঘটনা এ নাটকের কোথাও নেই। আহমেদ আলীর সাথে রাজার মামার যে বিরোধ সেটা হচ্ছে একটা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিরোধ। সেই বিরোধে গ্রামের লোকদের অংশগ্রহণের সত্যি কোনো কারণ আছে কি?
মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাট্যকারদের লড়াই খণ্ডিতভাবে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। মার্কসবাদীদের লড়াই বুর্জোয়াশ্রেণী উচ্ছেদের লড়াই। সেই লড়াই শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে হবে না। শ্রমিকশ্রেণী খণ্ডিতভাবে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়ে না। বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ধ্বংসের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রও সেখানে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। মার্কসবাদের কথা হলো বিপ্লবী চেতনা ছাড়া, রাজনীতির চেতনা ছাড়া, সমাজ বিজ্ঞানের চেতনা ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। মামুনুর রশীদের বিপ্লবীরা সেখানে সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ছাড়াই বিপ্লবী হয়ে ওঠে। গিনিপিগ নাটকে সেই বিপ্লবটাও শ্রমিক-কৃষকের নয়। রাজার মামা বা রাজারা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সেটাও নাটকে স্পষ্ট নয়। গ্রামেও শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকে।
রাজাদের পরিবারটাকে গ্রাম্য শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিই মনে হয়, অন্তত সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা। রাজার মা বোরখা পরে শহরে আসে, সে পদানসীন। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র নারী, যারা অন্যত্র শ্রম বিক্রি করে, তাদের পক্ষে পদানসীন থাকা সম্ভব নয়। পর্দা করবার বিলাসিতা তাদের পোষায় না।
মামুনুর রশীদের এ নাটকে মূলত গ্রাম্য সুবিধাভোগী মানুষের সাথে রাষ্ট্রের এক আমলার শঠতার চিত্রই ফুটে ওঠে, কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধরা পড়ে না। মামুনুর রশীদের মতো নাট্যকারদের নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন তোলা যায়, মার্কসবাদী সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করা কিংবা মার্কসবাদী দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই কি তাঁদের নাটকের নানা বিভ্রান্তি ও দুর্বলতা? রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্ত এ ব্যাপারে বলছেন, হ্যাঁ, এটা প্রধান কারণ। তিনি বলছেন, বহুজন আছেন যাঁরা নিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তারপর এসে নাটক লেখেন। তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বহুক্ষেত্রেই পাল্টায় না, দেখা যায় পাতিবুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা নাটক লিখছেন।
শ্রেণীসংগ্রামের নাটক লিখতে গেলে যেটা হওয়া দরকার তাহলো তাঁদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তাঁরা সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ মার্কসবাদ নিজের করে নেবেন। অনেক সময় তা হয় না। তাঁরা অনেক শ্রেণীসংগ্রাম, অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া সত্ত্বেও পাতিবুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণটাকেই আশ্রয় করে বসে থাকেন এবং তাঁদের লেখায়, তাঁদের কাজকর্মে সেটাই প্রকাশ পায়।
উৎপল দত্ত দেখাচ্ছেন যে, সমাজে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার প্রত্যেকটার যুক্তি, প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা তো মার্কসবাদ-লেলিনবাদেই পাওয়া যাবে। নাট্যকাররা সেসব পড়ছেন না। না পড়েই বিপ্লবী নাটক লিখতে বসে যাচ্ছেন।তিনি বলছেন, কী রাজনীতি দিচ্ছি তার ওপরেই নির্ভর করে কোন্ কথাটা কীভাবে বলবো। অথচ যাঁরা রাজনৈতিক নাটক লিখছেন বা নাটক করছেন তাঁদের রাজনৈতিক মান অত্যন্ত নিম্নে রয়েছে। যাঁরা নাটক লিখছেন, পরিচালনা করছেন, প্রযোজনা করছেন, অথবা যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের নিজেদের রাজনীতিই ঠিক পরিষ্কার নয়। তাঁদের নিজেদেরই মার্কসবাদ-লেলিনবাদের ওপর দখল অত্যন্ত নগণ্য। সেইজন্যই সর্বত্র সূত্রবদ্ধ নাটক দেখতে পাওয়া যায়। নাট্যকার অথবা পরিচালকদের রাজনৈতিক চেতনাই তৈরি হয়নি, শোষণের নানাদিকও তাঁরা বোঝেন না। ফলে রাজনৈতিক চিন্তা এবং থিয়েটার সম্পর্কে না বুঝে, থিয়েটারের আঙ্গিক-অভিনয় দখলে না এনে যা তৈরি করেন তার দ্বারা শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হয়।
রাজনৈতিক নাট্যকার সবদেশে সমকালের রাজনৈতিক সংকট অনুধাবনে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের ব্যাখ্যা আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। তাঁদের অনিষ্ট থিয়েটারের উদ্দেশ্য ছিলো সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা-কি সমাজ বীক্ষণে, কি থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে। বাংলাদেশের নাট্য-কর্মীদের বেলায় তা লক্ষ্য করা যায় না। যে থিয়েটার রাজনৈতিক সামাজিক প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করে তার মধ্যে থাকে মধ্যবিত্তসুলভ ঝোঁক। বাংলাদেশের শুরুর নাটকে আমরা মারাত্মকভাবেই সে প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, আশির দশকে আমরা সেই একই প্রবণতা দেখতে পাই।
সেখানে রাজনৈতিক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ সরাসরি তো নয়ই, রূপকের মাধ্যমেও দু-একটি নাটক ছাড়া দেখা যায় না। রাজনীতি বাদ দিয়ে প্রতিবাদটাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে কিংবা শ্রেণীবিদ্বেষহীন ক্ষোভই তাতে প্রকাশ পায়; যার প্রধান কারণ নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব। সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণার অভাব থেকেই এটা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যে-কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে সমাজবিজ্ঞান চেতনা তথা মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষার যে কী গুরুত্ব সে ব্যপারে বহু মনীষীরাই তাদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে এই সমাজবিজ্ঞানের চেতনা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মার্কসবাদী চেতনায় শিক্ষিত না হয়ে সেজন্য শ্রেণীসংগ্রামের নাটক করা যায় না।
শ্রেণীসংগ্রামের নাটক করার জন্য মার্কসবাদের জ্ঞান কতোটা জরুরি সে ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তাদের মতামত দিয়ে গেছেন। মাও সেতুঙ তার ইয়েনানের ভাষণে শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্য মার্কসবাদের শিক্ষা যে কতোটা দরকারি সে ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখেন। মাও সেতুঙ বলেন, জ্ঞানের অভাব বলতে বোঝায় জনগণকে ভালোভাবে না বোঝা।
লেখক ও শিল্পীদের সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক কাজ হচ্ছে জনগণকে, যাদের জন্য শিল্প-সাহিত্য রচনা করবেন তাদেরকে ভালোভাবে জানা এবং বোঝা। জনগণকে বোঝা ও জানার জন্য মার্কসবাদের শিক্ষা অপরিহার্য। শিল্পী-সাহিত্যিক বা নাট্যকার যাঁরা বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে এসেছেন, যাঁরা মধ্যবিত্তের ভিতর থেকে এসে শিল্প বা নাটকের চর্চা করতে চাচ্ছেন, তাঁরা যদি চান তাঁদের নাটক বা শিল্প জনগণের দ্বারা গৃহীত হোক তাহলে তাঁদেরকে অবশ্যই মধ্যবিত্ত মানসিকতা, ভাববাদী চিন্তাধারা ও অনুভূতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। নিজেদের পুনর্গঠন করতে হবে। চিন্তাধারা ও মানসিকতার এই পরিবর্তন ও পুনর্গঠন ছাড়া তারা জনগণের জন্য ভালো কিছুই সৃষ্টি করতে পারবেন না। চিন্তার সেই পরিবর্তন ও মানসিকতার পুনর্গঠনের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অপরিহার্য।
মার্কসবাদ লেলিনবাদের শিক্ষার অভাব থেকেই যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টির মধ্যে নানারকম সমস্যা দেখা দেয় মাও সেতুঙ সেটা নির্দিষ্ট করেই বলেছেন। তিনি লিখছেন, ‘সর্বশেষ সমস্যা হলো পড়াশুনার সমস্যা। এর দ্বারা আমি মার্কসবাদ- লেনিনবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা ও সমাজ সম্পর্কিত শিক্ষার কথা বলছি।
মাও সেতুঙয়ের চিন্তার পক্ষে আরো অনেকেই তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করেছেন। রাজনৈতিক নাট্যচিন্তায় মার্কসবাদের গুরুত্ব যে কতো বেশি সেটা বোঝা যায় ব্রেশটের বক্তব্য থেকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ব্রেস্ট কীভাবে মার্কসের দাস ক্যাপিটাল পাঠে ডুব দিয়েছিলেন। ব্রেস্ট তো বিশ্বাসই করতেন, মার্কসবাদ না বুঝে আধুনিককালে নাটক লিখতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি আরো বলেছিলেন, শ্রেণীসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ না নিলে আজকের দিনে আর অভিনেতা হওয়া যায় না। তিনি বলে গেছেন, যাঁরা নিরপেক্ষ, যাদের শ্রেণীসংগ্রামে কোনো আগ্রহ নেই, তারা যেন তাঁর নাটক মঞ্চায়নে হাত না দেন। ১৭ মার্কসবাদের জ্ঞান ছাড়া শ্রেণী বিশ্লেষণ করা যায় না।
আর শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে না পারলে ব্রেশটের নাটকের অন্তর্নিহিত সত্যকে যেমন বোঝা যায় না তেমনি তা দর্শকের কাছে তুলে ধরাও যায় না।রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্ত ব্রেশটের মতোই মনে করেন মার্কসবাদের জ্ঞান ছাড়া নাটককে জনগণের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের চরম বিকাশের কালে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান বাদ দিয়ে, সমাজ বিকাশের নিয়ম না জেনে নাটক বা শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে শিল্পীর নিজের খেয়ালকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়া হবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের নাটক পিছিয়ে পড়ার জন্য, ঠিক মতো সেটা বিকশিত না হওয়ার জন্য দায়ী করেন নাট্যকর্মীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন না করাকেই। তিনি মনে করেন, নাট্যকর্মীরা যদি ঠিকভাবে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের নাটক বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো।।
সকলেই কেন এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের ওপর এতো গুরুত্ব দিয়েছেন? কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক অনুশীলনেরই একটি প্রক্রিয়া। বিপ্লবীই হোক বা প্রতিবিপ্লবীই হোক, রাজনীতি হচ্ছে দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর সংগ্রাম, কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের কাণ্ডকারখানা নয়। ১২০ তার জন্য অনুশীলন অপরিহার্য। সামাজিক অঙ্গীকারাবদ্ধ নাট্যকর্মী মানে শুধু নাটকের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মীকে বোঝায় না। ইনি এমন একজন কর্মী যিনি সামাজিক দায়িত্ববোধ অনুভব করবেন প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং নাটককে যিনি অনেক গভীরভাবে দেখতে চান, বুঝতে চান ও বোঝাতে চান।
নাটককে যিনি সমাজ বিকাশের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য নাট্যকর্মীর দায়িত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের চাইতে অনেক বেশি। তাঁদের একই সঙ্গে নাটক বুঝতে হয়, বুঝতে হয় সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস ও মানুষকে।১২১ সেই জন্য নাট্যকর্মীর দরকার হয় দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক পড়াশুনার। রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি ভালো করে আত্মস্থ করতে হয় তাঁকে।
সেই প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কোনোভাবেই তিনি রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের কর্মী হয়ে উঠতে পারেন না; রাজনৈতিক নাটককে সেবা করতে পারেন না। সেই জ্ঞানের অভাব থেকেই নাট্য রচনা ও মঞ্চায়নের নানা ভুল-ভ্রান্তির জন্ম দেন, যা আশির দশকের শোষক শোষিতদের নিয়ে রচিত নাটকগুলোতে দেখতে পাই।ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতে এসময় বহু নাটক মঞ্চস্থ হয় যদিও সেগুলোর প্রদর্শনীর সংখ্যা বেশি নয়। বিভিন্ন ধরনের নাটকই এ সময় মঞ্চস্থ হচ্ছিলো। প্রচুর পুরানো নাটকও আমরা এ সময় মঞ্চস্থ হতে দেখি।
সে সময় প্রধানত যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়-আবদল্লাহ আল-মামুনের সুবচন নির্বসনে, এখন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, চারদিকে যুদ্ধ, ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার, আয়নায় বন্ধুর মুখ, মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, মমতাজউদ্দীন আহমদের বর্ণচোর, ক্ষতবিক্ষত, জিয়া আনসারির চোর চোর, আকরাম আলীর লাশ’, প্রবীর দত্তের স্ফিংস, কাজী জাকির হাসানের শরবিদ্ধ যন্ত্রণা, রাজায় রাজায়, আহসান হাবিবের পলাতক পালিয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি, জুতা আবিষ্কার, বিসর্জন, ফরিদ আহমেদ দুলালের ফুলজান সমাচার, শৈলেশ নিয়োগীর ফাঁস, রবিউল আলমের জননীর মৃত্যু চাই, এক যে ছিলো দুই হুজুর, সেলিম আল দীনের বাসন, আততায়ী, এস এম সোলায়মানের এলেকশন ক্যারিকেচার,
ঘোড়া এলো শহরে, সালাম সাকলাইনের জাহেন আলীরে ধর, মিলন চৌধুরীর একজন পিরামিড, আভ্যন্তরীণ খেলাধুলা, শামসুল হক হায়দরীর দলিল, সুবর্ণগাঁথা, অলোক ঘোষের শেওলা, অরূপ মৈত্রের সিংহাসন, ওসমান অভিকের গন্ধরাজ, মুনীর চৌধুরীর দণ্ডকারণ্য, বাদল সরকারে মিছিল, ভোমা, রাম-শ্যাম যদু, সুখপাঠ্য, মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান, চাক ভাঙা মধু, রতন কুমার ঘোষের সকালের জন্য, রাধারমণ ঘোষের হইতে সাবধান, হারাধনের দশটি ছেলে, ইতিহাস কাঁদে।
ঢাকায় মঞ্চস্থ বেশ কিছু নাটকও এ সময় ঢাকার বাইরে মঞ্চস্থ হতে দেখি। যেমন অরক্ষিত মতিঝিল, নূরুলদীনের সারাজীবন, দুইবোন, এখনো ক্রীতদাস, ইংগিত ইত্যাদি। ঢাকার বাইরে এসময় কিছু কিছু হাসির নাটক এবং খুব সামান্য হলেও বেখাপ্পা বা বিমূর্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়। সবচেয়ে বেশি মঞ্চস্থ হচ্ছিলো শোষক- শোষিতের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে রচিত নাটকগুলো, বিশেষ করে যে-সব নাটকগুলোতে একজন খলনায়ক আছে।
শোষক-শোষিতের মধ্যকার লড়াই এ সময়ের মঞ্চস্থ নাটকগুলির একটি প্রধান দিক; অনেক নাট্যদলই এগুলিকে শ্রেণীসংগ্রামের নাটক হিসাবে মনে করে। শোষক-শোষিতদের নিয়ে মঞ্চস্থ নাটকগুলির বেশিরভাগই ছিলো চড়া সুরে বাঁধা। দেশের বাইরের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু নাটক বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতে মঞ্চস্থ হয়।
মফস্বল শহরের যে সকল নাট্যদলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলো এবং যারা সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেয়নি নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে এই দুই দলের মধ্যে খুব একটা পাথর্ক্য লক্ষ্য করা যায় না। মশিউর রহমান আদনান লিখছেন, সাধারণ নাট্যদলগুলোর অধিকাংশ কর্মীদেরই রাজনৈতিকভাবে বাম চিন্তার প্রতি অঙ্গীকার থাকলেও, সেই অঙ্গীকারের প্রতি আন্তরিকতা থাকলেও দলগুলো সর্বহারাশ্রেণীর রাজনীতি ও মতাদর্শের অধীনে না থাকার কারণে এদের সকল অঙ্গীকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাগুজে হয়ে পড়ে। এদের অনেকরই ধারণা নাটক করতে গেলে বাম অঙ্গীকারই যথেষ্ট।
সেজন্য নাট্যকর্মীরা মুখে যতোই শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান দিক, নাটকে বা নাট্যচিন্তায় তাঁরা এর কোনো প্রতিফলন রাখতে পারেন না। নাটকের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীর-চিন্তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিপ্লবী নাট্য মঞ্চায়ন বা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে নাটক নিয়ে যাওয়া দু ব্যাপারেই তাঁরা তাঁদের সততার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এঁদের প্রধান একটি সংকট রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব এবং ভিন্ন সংকটটি হচ্ছে বৃহৎ দলগুলোর নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়া। সংকট আসলে এঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক এবং এঁরা যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে থাকে তা আসলে বুর্জোয়া নাট্যচিন্তার এক বিশেষ রূপ।
বিভিন্ন দলগুলো তাদের নাটকে শ্রেণীসংগ্রাম প্রচারের কথা বললেও, তাদের নাটক দেখার পর এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে, শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে তাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। চরিত্রদের মুখে সংগ্রামী সংলাপ দিয়ে নাটক শেষ করার ঝোঁক যতো প্রবল, নাটকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সেই হারে অনুপস্থিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তো ছিলো না বললেই চলে। তাদের ঘোষণা ছিলো ঘোষণাই মাত্র, কার্যক্ষেত্রে যার কোনো গুরুত্ব তারা প্রদান করেনি। বক্তব্যের চেয়ে রূপরীতি, নাটকের চেয়ে নাট্যদলের প্রচার সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকের বক্তব্য প্রমাণ করেছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর নাট্যকর্মীদের বৃহত্তম অংশের শ্রেণীসচেতনতা বিপজ্জনকভাবেই দুর্বল।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 11 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৫.jpg)
নাট্য সমালোচক অরুণ মুখোপাধ্যায় তাই আক্ষেপ করে বলছেন, যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন, যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী নন, যাঁরা ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী নন বা ব্যাপারাটা বোঝেন না, তারাও রাজনৈতিক নাটক লিখতে যান এবং নিজেদের নাটককে রাজনৈতিক নাটক বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক থিয়েটার কী, বা তা কী হওয়া উচিৎ এই বোধ এই শিক্ষাটাই এইসব নাট্যকর্মীদের মধ্যে ভীষণ কম।
ফলে তাঁদের নাটকে না পাওয়া যায় কোনো মানবিক চিত্র, না হয়ে ওঠে সেগুলো শ্রেণীসংগ্রামের দলিল। রাজনৈতিক নাটক যে কখনই মানবতার বিপক্ষে যায় না, এই ব্যাপারটাও এখন পর্যন্ত তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে তো মানবতাবাদী দৃষ্টিকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সেজন্য শোষককে আক্রমণ করাটাকেই তাঁরা নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সমাজ বিশ্লেষণকে নয়। উদাহরণ হিসাবে ঢাকার বাইরে মঞ্চায়িত দু-একটি নাটক নিয়ে এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করবো।
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এ সময় সেলিম আল দীনের বাসন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। বাসন নাটকের বিষয়বস্তু প্রধানত গড়ে উঠেছে গ্রামীণ একটি বর্গাচাষী পরিবারের সাথে বর্গাদার মালিকের সম্পর্কের টানাপোড়েনকে ঘিরে। বর্গাদার আজাজীল সাংসদ এবং শহরে থাকে। বহু বছর পর গ্রামে এসেছে জমিজমা নতুনভাবে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য। বর্গাচাষী আশেক সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে মালিক সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করলেও তার ছেলেরা তা করে না। আশেকের মেয়ে কৈতরির বিয়ে হলেও শ্বশুর তাকে বাপের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। শ্বশুর যৌতুক হিসাবে মেয়ের বাপের কাছে দাবি করে দু হাজার টাকা।
টাকা না পেলে সে ছেলের বৌকে আর ফিরিয়ে নেবে না। আশেক গরীব হলেও তার পরদাদা হাজি কমরুদ্দিন ছিলো ফরাজী আন্দোলনে দুদু মিঞার শিষ্য। দুদু মিঞার শিষ্য হিসাবে সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। এখনও তার ব্যবহৃত একটি দামী সুন্দর, বাসন রয়ে গেছে আশেকের পরিবারে। এই পবিত্র বাসনটিকে আশেকরা যেমন পবিত্র হিসাবে জ্ঞান করে, তেমনি গ্রামবাসীরাও। বর্গাদার আজাজীল গ্রামে আসার পর নিজে থেকেই নিমন্ত্রণ নেয় আশেকের বাড়িতে। গরীব আশেকের বাড়িতে কোনো ভালো থালা-বাসন না থাকায় পরদাদার সেই ঐতিহ্যবাহী বাসনেই বর্গাদারকে খেতে দেয়া হয়। বর্গাদারের এই সুন্দর বাসনটির ওপর নজর পড়ে এবং সে সেটা দখল করতে চায়। বাসনটির জন্য সে আশেককে দু হাজার টাকাও দিতে রাজি হয়।
দু হাজার টাকা পেলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো যাবে এই ভাবনায় আশেক একবার বাসনটি বর্গাদারকে দিতেও রাজি হয়। কিন্তু কন্যা কৈতরির চাপের মুখে সে বাসনটি আর জমিদারকে দিতে পারে না। বাসন না পাবার পর ভালো চেহারার বর্গাদারের দখলদারি রূপটি এবার বের হয়ে পড়ে। বাসন না পেয়ে সে আশেককে বর্গাচাষ থেকে উচ্ছেদ করে। একই সাথে সে গ্রামের সকল বর্গাচাষীর কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়ে নেয় এবং করম নামে তার এক চেলাকে সে-সকল জমি চাষ করার অধিকার দেয়। জমি হারিয়ে আশেক পাগল হয়ে যায়। চাষীরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজেকে সকল কিছুর জন্য দায়ী ভেবে কৈতরি আত্মহত্যা করে। কৈতরির ভাইসহ গ্রামবাসী এবার প্রতিশোধের নেশায় জ্বলে ওঠে। বর্গদার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। গ্রামবাসী বর্গাদারের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।
নাটকটির রচনাশৈলী এবং গঠন খুবই প্রাঞ্জল। নাটকটিতে রয়েছে হৃদয়গ্রাহী নানা সংলাপ। নাট্যকারের গভীর জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায় তাতে। গ্রাম্য মানুষের চরিত্রের নানা দিক, তাদের স্বভাবসুলভ বেশিষ্ট্য সবই চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে নাটকটিতে। কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যে যেভাবে সকল বর্গাচাষীরা মিলে বর্গাদারের ওপর আক্রমণ চালায় তা কোনো সাধারণ সমাজ বাস্তবতা নয়।
বর্গচাষীদের ক্রোধটা বাস্তব, সে ক্রোধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণেই যখন তখন আক্রমণে রূপ নিতে পারে না। শাসকশ্রেণীর প্রশাসন যন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা সকল কিছু শোষিতদের ক্রোধের আক্রমণের হাত থেকে শোষককে রক্ষা করে। বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় তাই ক্রোধ প্রকাশ করা যতো সহজ, আক্রমণ করাটা ততো সহজ নয়। গ্রামগুলো রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই গ্রামে শাসকদের ওপর আক্রমণ হলে রাষ্ট্র যে চুপ করে বসে থাকবে না গ্রামবাসীরা তা জানে। জানে বলেই খুব সহজে তারা শাসকদের ওপর আক্রমণ চালায় না। নাট্যকার দর্শকদের বিভিন্ন রাস্তবতার মুখোমুখি করলেও সে দিকটিতে নজর দেননি।
বিদ্যুৎ কর রচিত সুরমা কান্দে নাটকটি আশির দশকের শুরুতে মঞ্চস্থ করে সিলেটের নাট্যলোক। নাটকটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত জেলা ভিত্তিক নাট্যাৎসবে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার পায়। নাটকটির গল্প গড়ে উঠেছে মূলত সুরমা নদীর পাড়ের জেলেদের জীবন নিয়ে। রুস্তম মহাজন ও তার বাপ-দাদারা বহু কাল ধরে জেলেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে আসছে। কষ্ট করে মাছ ধরে জেলেরা, আর সকল মুনাফা কুক্ষিগত হয় মহাজনদের।
দু বেলা ঠিকমতো না খেয়ে জীবন কাটায় জেলেরা। জেলেরা যাতে বিদ্রোহ না করে বা তাদের হাতে কোনো টাকা পয়সা না জমে তার জন্য প্রতিটি জেলে পাড়ায় গাঁজার দোকান খুলে রেখেছে রুস্তম মহাজন। জেলেরা সে গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। যখন মহাজনের অত্যাচার সুরমা পাড়ের জেলেদের সকল কিছু গ্রাস করতে এলো বিরোধ বাধলো মহাজনের সাথে জেলেদের। শুরু হয় মহাজনের ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা প্রদর্শন। রুস্তম জেলেদের জাল কেড়ে নেয়, বিলে মাছ ধরা বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত জেলেরা বিদ্রোহ করে, মহাজনদের তৈরি করা বাঁধ কেটে দেয়। মহাজন বন্দুক হাতে বাধা দিতে এলে দুপক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। রুস্তমের বন্দুক কেড়ে নেয় বিদ্রোহীরা। পিছনে লাল সূর্য্য দেখা যায়।
কিন্তু বাস্তবে এসব নাটক খণ্ডখণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘৃণাকে, ক্রোধকে একীভূত করতে পারে, কিছুক্ষণের জন্য দর্শক একাত্ম হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না।
আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৩ ]
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 12 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৩ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/আশির-দশক-শ্লোগানসর্বস্ব-রাজনৈতিক-নাট্যের-উন্মেষ-পর্ব-৩--1024x536.jpg)
বরিশালের খেয়ালী গ্রুপ আশির দশকে মঞ্চস্থ করে মিন্টু বসুর অন্য এক কালাপাহাড় নাটকটি। নাটকের পটভূমি গড়ে উঠেছে বাবলতলী গ্রামকে কেন্দ্র করে। ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে সেই গ্রামে ভেসে আসে বিরাট আকৃতির এক মানুষ। জল নেমে গেলেই ব্যাপারটি প্রথম ধরা পড়ে। লোকটি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে-গ্রামের কেউ তাকে চেনে না, কখনো দেখেনি। সবাই ভাবে জ্ঞান ফিরলে লোকটা নিজের গ্রামে চলে যাবে। কিন্তু লোকটির জ্ঞান ফিরলে দেখা যায় সে কথা বলতে পারে না। তাকে ক্ষুধার্ত মনে হয়। গ্রামের মেয়ে সৈরভী তাকে ভাত খেতে দিলে সে গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেলে। সৈরভীকে তখন আরো খাবার এনে দিতে হয়। তার খাবার পরিমাণ দেখে সকলে অবাক হয়।
লোকটি খেয়ে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। চলে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। গ্রামের জমিদার বংশের ছোট সাহেব সকলকে পরামর্শ দেয় লোকটিকে গ্রামেই রেখে দিতে। সে বলে এই বিশাল আকৃতির লোকটির গায়ে অনেক শক্তি আছে। বন্যার পর গ্রামটিকে গড়ে তুলতে লোকটির সে শক্তি কাজে লাগবে।
ছোট সাহেবের ভাষায়, জলোচ্ছ্বাসে বাবলতলী বাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ঘর-বাড়ি গরু ছাগলের অস্তিত্ব নেই, এ পরিপ্রেক্ষিতে শহরের রিলিফের ওপর নির্ভর করে’ বসে থাকলে চলবে না। শক্তি দিয়ে বাবলতলীকে গড়তে হবে। বিশাল পাহাড়ের মতো যে মানুষটা দেখতে তার মধ্যে রয়েছে ঘুমন্ত শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে ট্যাংরামারীর বাঁধ দিতে হবে, কৃষকের ক্ষেত গড়তে হবে। লোকটি যে পরিমাণ খায় তা দেখে সাধারণ কৃষকরা তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। লোকটিকে গ্রামে রাখা বিরাট খরচের ব্যাপার। ছোট সাহেব বলে সে দরকার মতো তাদেরকে সাহায্য দেবে। ছোট সাহেবের কথা মতো লোকটিকে গ্রামে সৈরভীদের বাড়িতেই থাকতে দেয়া হয়। বিশাল শরীরের জন্য তার নাম দেয়া হয় কালাপাহাড়।
কালাপাহাড়ই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। নাটকের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা নাট্যকারের পেশীশক্তির প্রতি আস্থা দেখতে পাবো। বাংলার ইতিহাস বলে, গ্রামে বারবার বন্যা আসে, গ্রাম ধ্বংস করে দিয়ে যায়, গ্রামের মানুষই আবার সে গ্রাম গড়ে তোলে। নাট্যকার সেখানে গ্রামের মানুষের ওপর আস্থা না রেখে কালাপাহাড়ের মতো পেশীশক্তির প্রতি আস্থা রাখছেন। নাটকে সেজন্য আমরা দেখতে পাই ছোট সাহেবের কথা মতো ভীষণ খাটুনি দিয়ে কালাপাহাড় গ্রামটাকে গড়ে তোলে। হাজার বছরেও বাবলতলীর যে খেতে ফসল ফলতো না কালাপাহাড় সেখানেও ফসল ফলায়। বহু মানুষের চেষ্টার চেয়ে কালাপাহাড়ের একার চেষ্টাই সেখানে বড় হয়ে ওঠে।
বাবলতলীর দীর্ঘদিনের চেহারাটা বদলে দেয় সে। নাট্যকার তারপর আমাদের শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যান। নাট্যকার আমাদের দেখান, কালাপাহাড় গ্রামটাকে গড়ে তুললেও তাকে খাওয়াতে গিয়ে ছোট সাহেবের কাছে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। ছোট সাহেব এখন তার বিনিময়ে কৃষকের সকল ফসল তার ঘরে তুলতে চায়। ছোট সাহেবের চালাকি এবার সকলের কাছে ধরা পড়ে।
ছোট সাহেবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য গ্রামবাসীরা এবার ঐক্যবদ্ধ হয়, নিজেদের শক্তিকে কালাপাহাড়ের শক্তির মতো করে তুলতে চায়। সকলে যখন ছোট সাহেবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তৈরি তখন কালাপাহাড় ছোট সাহেবকে হত্যা করে। ছোট সাহেবকে হত্যা করলে গ্রামে পুলিশ আসে। কালাপাহাড় ছুটে গিয়ে সড়কি হাতে নিয়ে বিকট শব্দে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়। গ্রামের লোকরাও বুঝে নেয় সেটা চরম প্রস্তুতির লগ্ন।১২ নাট্যকার এটা ভেবে দেখেন না, পুরানো অস্ত্র হাতে আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় কি না। শোষকদের আক্রমণ করাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।
বাসন ও সুরমা কান্দে নাটক দুটোতে শোষক-শোষিতের মধ্যকার লড়াই এবং শোষককে আক্রমণের তাৎক্ষণিক ঘটনা ফুটে উঠলেও তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের সামাজিক চিত্র। সেক্ষেত্রে খেয়ালী প্রযোজিত অন্য এক কালাপাহাড় নাটকটির মধ্যে কোনো সমাজ বাস্তবতা ছিলো না। নাটকের প্রেক্ষাপট চারদিকের চেনা-জানা কোনো পরিবেশ নয়, নিকট কিংবা দূর অতীতের কোনো ঘটনার সঙ্গেও এর সঙ্গতি নেই। নাট্যকার এ নাটকে কাল্পনিক চরিত্রকে টেনে এনে কাল্পনিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন, বাস্তবের শোষিতশ্রেণীর লড়াইয়ের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। রচনা যে ধরনের হোক সকল ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্ন আসছে। বাস্তবতার প্রশ্নটিও এসে যাচ্ছে।
সেজন্য সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে রচনার ভিতর চরিত্র সৃষ্টির কাজ কীভাবে এগোচ্ছে। মিন্টু বসু কালাপাহাড় নামে যে চরিত্রটি সৃষ্টি করেন তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। নাট্যকার গ্রামবাংলার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন রূপকথার এক দৈত্যের মর্জির ওপর এবং শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর মিলিত সংগ্রামের চেয়ে কালাপাহাড় নামক এক দানব এই নাটকের শেষে বিপ্লবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।
পূর্বে উল্লিখিত তিনটি নাটকই শেষ হয়েছে শোষিতদের আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে। আশির দশকে এই ছিলো তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের নাটকের চেহারা। বিপ্লবের পূর্ববর্তী স্তরগুলোকে পার না করেই, বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকে বিকশিত না করেই নাট্যকাররা বিপ্লবের শেষ পরিণতি দর্শকদের দেখিয়ে দেন। প্রায়শই নাটকের শেষটা অর্থাৎ উপসংহার দেখেই দর্শককে বিচার করতে হতো তা বৈপ্লবিক কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের নাটক কি না।
ঢাকার বাইরে আশির দশকে মঞ্চায়িত সুলতান মুহাম্মাদ রাজ্জাকের পলোনাথ কোম্পানী, সালাম সাকলায়নের সেনেরখীলের তালুকদার ও চোর-নাটকেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বিপ্লবের সকল ধারাবাহিক স্তরগুলোকে বাদ দিয়ে শোষক-শোষিতের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পায়। মালিক বা শেষিতদেরকে যেনতেন প্রকারে আক্রমণ করার যে প্রবণতা আমরা মামুনুর রশীদ বা আবদুল্লাহহেল মাহমুদের নাটকগুলোতে দেখেছি এই নাটকগুলোতেও সে প্রবণতাই লক্ষ্য করি।
এই ধরনের রাজনৈতিক নাট্য প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করতে গিয়ে উৎপল দত্ত কলম ধরেছিলেন। সেখানে তিনি গণনাট্য সংঘের রাজনীতির গৎবাঁধা সূত্রবদ্ধ নাটকগুলোকে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, ‘প্রথমে এক সাহেব বা এক জমিদার চাবুক নিয়ে বেধড়ক প্যাঁদায় একদল চাষীকে।… তারপর আসে কমিউনিস্ট-সকল গুণের আধার, সে সুশীল বালক, সকল পাঠ মন দিয়া পড়ে। তার না আছে কোনো দ্বিধা, না কোনো দুর্বলতা, না কোনো দ্বন্দ্ব। এহেন এক নিষ্পাপ সন্ন্যাসী এসে চাষীদের বোঝায়, আর বুঝেই তারা গিয়ে জমিদারকে পেটায়-যবনিকা-ইতি গণনাট্য সংঘস্য নবনাটকম্।’ উৎপল দত্ত আরো লিখছেন, এসব হচ্ছে পোস্টার-এ্যান্ড-শ্লোগান স্টাইল, এতে বিপ্লবের ক্ষতি হয়, উপকার নয়।
মাও সেতুঙ বলেন, বিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে এই সব রচনাকে সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে নিম্নমানের শিল্পকে ধীরে ধীরে উন্নততর মানে সমুন্নত করা সম্ভব হয় এবং রাজনৈতিক নাটকের লক্ষ্য সম্পর্কে নাট্যকার বা নাট্যদলগুলো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।
রাজনৈতিক নাটকের লক্ষ্য যে শুধুমাত্র শোষণ দেখানো বা ধনী-দরিদ্র বা শোষক- শোষিতের লড়াই দেখানো তা কিন্তু নয়। নাট্যকারের কাজ হলো দর্শকদেরকে তথ্য দেয়া, যেন তাঁরা দেশ-কাল পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ও সমাজ বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
এঙ্গেলস বহুদিন আগেই বলে গেছেন, সমাজ বিবর্তনের নিয়মগুলি একবার সম্যক বুঝতে পারলেই মানুষ আর সে নিয়মের অন্ধ বলি হতে রাজি হবে না; সে লড়াই করবে। সেজন্য সমাজ বিজ্ঞানের চেতনা মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দেয়াটাই হবে রাজনৈতিক নাটকের কাজ। বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনে সেটা কখনই ঘটেনি। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে, নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে নান্দনিক চেতনার অভাব। নাট্যকর্মীদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির অভাব যেমন রয়েছে, তেমনি ছিলো শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততার অভাব। স্তালিন দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবী মতবাদের সাথে যদি বিপ্লবী কাজকর্মের যোগাযোগ না থাকে তা হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন; তখন অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়।
বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রেখে যদি মতবাদকে গড়ে তোলা হয়, তবে তা শ্রেণীসংগ্রামকে প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করতে পারে। সেক্ষেত্রে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখবার শক্তি যেমন আয়ত্ত করা যায়, তেমনি তা আশপাশের ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ বুঝতেও সাহায্য করে।
রাজনৈতিক নাট্যচিন্তায় নাটকের কাজ সরাসরি সমাজ পাল্টানো নয়। সে দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। রাজনৈতিক নাটকের কাজ সমাজ পাল্টাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে বোঝানো, সেজন্য মানুষকে প্রস্তুত করে তোলা। সমাজ পাল্টাবার মানুষগুলোকে তৈরি করা। সেজন্য নাটকে সরাসরি শ্রমিক কৃষকের কথা না বলা হলে নাটক বিপ্লবী হবে না, এমনও ভাববার কারণ নেই। সমাজ পরিবর্তনের নাটকের কাজ হলো বিপ্লবী তত্ত্ব প্রচার করা। সেই বিপ্লবী তত্ত্ব মানে এ নয় যে কেবলমাত্র মালিককে আক্রমণ করতে উদ্দীপ্ত করা। মার্কসবাদীরা মনে করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের সব রকম সুস্থ চিন্তা করবার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, তাকে করে রেখেছে ব্যক্তিত্বহীন উৎপাদনী এক যন্ত্রমাত্র। মার্কস দেখান যে, পুঁজিবাদী সমাজে বাঁচার জন্য মজুর নিজেকে সস্তায় বিক্রয় করেই শুধু প্রতিযোগিতা চালায় না, প্রতিযোগিতা করে একা পাঁচ-দশ-কুড়ি জনের কাজ করে।

কাজের নিগড়ে সে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী নাটকেও আমরা দেখতে পাই, শ্রমিকরা কাজ করে করে তার মানবিক সত্তা হারিয়ে ফেলে কতগুলো সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, ‘যন্ত্রের মত নিত্য কর্ম করতে করতে মানুষ প্রাণহীন যন্ত্র হয়ে যায়’।মার্কস তাই দেখিয়েছেন, যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক উপরে ওঠে না। নিঃস্ব অবস্থা আরো বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে।
মজুরি শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনোক্রমে নিজের অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া ও পুনরুৎপাদন করা চলে। যার ফলে শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়াবার জন্য। তাকে বাঁচতে হয় শাসকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতোটা প্রয়োজন ঠিক ততোখানি। মানুষ হয়ে যায় যন্ত্রের, উৎপাদনী প্রক্রিয়ার লেজুড়। তার কাছে শুধু দাবি করা হয় অতি সরল, একান্ত একঘেয়ে দক্ষতাটুকু। এভাবেই দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস।
পুঁজিবাদী সমাজের মানুষ সম্পর্কে গোর্কির উচ্চারণ ছিলো যে, ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষমতা এবং তাকে যে কাজ দেয়া হয় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত শ্রমে মানুষের স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। একপেশে ব্যবহারে বুদ্ধি ভারসাম্য হারিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের বোধ ও বিবেক ধ্বংস হয়ে গেছে। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্য। পুজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র। সেখানে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পিষ্ট ও চূর্ণ করা হয় প্রতিদিন। মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়া হয়। মানুষ আর পূর্ণাঙ্গ মানুষ থাকে না।
উৎপাদনের নাটবল্টু হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার মানসিকতায় সে হয়ে দাঁড়ায় অর্ধমানুষ। মার্কস দেখান, যন্ত্রপাতি ঠিক যে-হারে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। উল্টোদিকে মানুষ যতো বাড়তি কাজ করে তার থেকে বেশি অনুপাতে সে ক্ষয় পায়। মার্কসের মতে, সময়ের পরিসরেই মানুষের বিকাশ ঘটে। যে মানুষের হাতে খুশিমতো কাটাবার নিরঙ্কুশ সময় নেই, ঘুম, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি নিতান্ত দৈহিক ধরনের ছেদগুলো ছাড়া যার সমস্ত জীবনই পুঁজিপতির জন্য খাটতে হয়, সে ভারবাহী পশুরও অধম। দেহের দিক থেকে জীর্ণ ও মনের দিক থেকে পশুর স্তরে অধঃপতিত হয়ে সে হয় অপরের সমৃদ্ধি সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র।১* সেখানে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিকশিত হবার সুযোগ নেই।
সেইজন্য রাজনৈতিক নাটকে বিপ্লবী তত্ত্ব প্রচারের সাথে সাথে এই মানুষগুলোকে যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাদের কাছে বেশি বেশি মানবতার কথা বলতে হবে। বিধ্বস্ত মানুষরা যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষ না হয়ে ওঠে তাহলে তারা বিপ্লবী তত্ত্বকে ধারণই করতে পারবে না। রাজনৈতিক নাটকের প্রথম ধাপ হবে তাই, ভাঙা মন জোড়া দেয়া। বিধ্বস্ত মানব গোষ্ঠীকে সুস্থ, উন্নত, সৃষ্টিশীল ও সংগ্রামী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার প্রথম অভিযান, আধখানা মানুষকে পুরো করার লড়াই। তারপর সেই পূর্ণ মানুষকে দিতে হবে শ্রেণীচেতনা। তাহলেই সে সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হিসাবে দেখা দেবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্যচিন্তায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে মানবিকতা প্রচারের কোনো প্রচেষ্টা ছিলো না। যুদ্ধংদেহী মনোভাব গড়ে তোলার দিকেই ছিলো মূল লক্ষ্য।
মার্কস দেখান যে, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি মানুষ দেখতে চায়, শুনতে চায়, ঘ্রাণ নিতে চায়, কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, অনুভব করতে চায়, ভালোবাসতে চায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে এই সব ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে। সম্পত্তি, মূলধন, পুজি-মানুষের এসব বৃত্তিকে ভোঁতা করে দেয় এবং একটি মাত্র বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, তাহলো দখলের মনোবৃত্তি, সম্পদের ওপর অধিকার বিস্তারের বৃত্তি। দেউলিয়া এইসব মানুষকে একত্রিত করলে, সমষ্টিবদ্ধ করলে দেখা যায় কোনো একটি লক্ষ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেয়ে তারা নিজেদের মধ্যেই পাশবিক হানাহানি, দ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত হয়।
যার কারণ হলো মানসিক জগতে সে হয়ে পড়েছে রিক্ত, হতসর্বস্ব। মানুষ হিসাবে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় সে লিপ্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকেই সে পেয়েছে এই শিক্ষা। সে কারণে সমাজ পরিবর্তনের নাটকের দায়িত্ব হলো মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রচারের সাথে সাথে মানুষের মৃত স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগিয়ে তোলা। তার মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।
ব্যক্তি প্রতিভার নানা দিক সম্পর্কে তাকে জানতে দেয়া। মানুষের মনের গভীরতা, মানুষের আবেগ-অনুভূতির জটিলতা, মানুষ কতো বড়, কতো বিচিত্র নাটকের ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে তা বুঝতে সাহায্য করা। সেজন্য নব্য লেখকদের কাছে মার্কসের আবেদন ছিলো, শেক্সপিয়ার পড়ুন, আপনাদের রচনাকে শেক্সপিয়ারের মতো ধারালো করুন, মানবতাবাদী সাহিত্যকে এনে দিন মেহনতী মানুষের নাগালের মধ্যে। সেই জন্য স্তালিন কী করেছিলেন? শেক্সপিয়ার, বায়রন, শেলী, গ্যাটে, শিলার, পুশকিন, গোগোল, তলস্তয়, চেখভ ও হুগোর লক্ষলক্ষ বই ছাপিয়ে এবং তা প্রচার করে মার্কস-লেনিনের নির্দেশ পালন করেছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের ওপর পার্টির লাইন প্রয়োগ করার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।
স্তালিন মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যকে অবশ্যই সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করতে হবে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করা বলতে তাঁরা কেউ ঝাণ্ডাবাজি বোঝাতেন না। বিপ্লবীচেতনা বলতে তাঁরা বুঝতেন, মানুষকে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করা। কিছু মুখরোচক বিপ্লবী বুলি কপচানো নয়। যেমন রম্যা রলাঁ বলেছিলেন, যা দরকার তা হলো বুদ্ধিচর্চার মধ্য দিয়ে অথবা বুদ্ধিগত দিক থেকে জনগণের মানসিক উন্নতি, এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশিক্ষণ। ইতিহাস তাদের শেখাবে কীভাবে নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। শত্রু বা মিত্র-কীভাবে প্রত্যেককে বুঝে নিতে হয়।
তিনি আরো বলেছেন, থিয়েটারকে অবশ্যই শক্তির উৎস হতে হবে এবং জনগণকে অবশ্যই বিনোদন দিতে হবে। বিনোদন পরিবেশন করার সময় থিয়েটারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জনগণ যেন পরের দিন আরো ভালোভাবে কাজ করার মতো মানসিক শক্তি পায়। জনগণকে হতাশাগ্রস্ত করা চলবে না। রম্যা রলাঁ বলছেন, থিয়েটারকে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আলোক বর্তিকা হয়ে উঠতে হবে। মানুষের বুদ্ধি আছে ক্ষুরধার, কিন্তু তা ছায়াচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ভোঁতা হয়ে রয়েছে।
সেই জমে থাকা ছায়াচ্ছন্নতাকে আলো দিয়ে ভাসিয়ে দেবে থিয়েটার। মার্কসবাদীদের মতো রম্যা রলাঁও মনে করছেন মানুষের মন এই সমাজে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। নাটকের মাধ্যমে মানুষের সেই বিক্ষিপ্ত মানসিকতায় আনতে হবে শান্তি। জনগণকে যদি শুধু চিন্তাভাবনা করবার অবস্থায় আনা যায়, নাটকের মধ্য দিয়ে যদি জনগণকে শুধু চিন্তা করাতে পারা যায় তাহলে সেটাই হবে অনেক। নিজেরাই তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
নাটককে অবশ্যই নীতিশিক্ষা আওড়াবার প্রবণতা এড়িয়ে চলতে হবে। তিনি বলছেন, জনগণের যাঁরা সত্যিকার বন্ধু তাঁরা অধিকাংশ সময়ই নীতিশিক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করে শিল্পকে জনগণের কাছে বিরক্তিকর করে তুলেছে। নীতি শিক্ষার প্রবণতা যেমন নাটক থেকে বাদ দিতে হবে, তেমনি যেন-তেন প্রকারে প্রমোদ বিতরণ করার ব্যাপারটাকে এড়াতে হবে। সুতরাং নীতিবাক্য ছড়ানো এবং সস্তা বিনোদন কোনোটাই চলবে না।
মানুষকে তাদের দৈনন্দিন ঘটনা থেকে সরিয়ে এনে চাঞ্চল্যকর অনুভূতিতে ভরপুর করে দিতে হবে। উদ্দেশ্য থেকে আবার সরে গেলে হবে না। সবকিছুর মেলবন্ধন ঘটাতে পারার জন্যই একজন রাজনৈতিক নাট্যকারের ভূমিকা একজন রাজনৈতিক নেতার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য সমাজবিজ্ঞান সচেতন একজন রাজনৈতিক নাট্যকর্মীই শুধু পারে এই কাজটি সফল করে তুলতে। রাজনৈতিক নাটকের কাজ তাহলে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর কথা বলাই নয়, মানবিক প্রশ্নেরও অবতারণা করা। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররাই তা করেছেন। সেই প্রেক্ষিত থেকেও আমরা বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকারদের নাটকগুলো বিবেচনা করবো।
শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দেয়নি আশির দশকে এ ধরনেরও বহু নাট্যদল ছিলো; যারা সামাজিক দায়িত্ব থেকে নাটক করার কথা বলেছিলো কিংবা নাটক করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুই বলেনি। সেই দলগুলোর মধ্যে প্রধান সারিতে রয়েছে নাগরিক, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার ও নাট্যচক্র। ১৪২ অশির দশকে এসব দলগুলোর প্রযোজিত এবং বিশেষ বিশেষ নাট্যকারদের রচিত নাটকগুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।
প্রধান দলগুলোর প্রযোজনা ও প্রধান নাট্যকারদের রচনার আলোকে সারাদেশের নাট্যচর্চার চরিত্রটি আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হবে। বিশেষ করে সবচেয়ে আলোচিত নাটকগুলোকেই গুরুত্ব দেবো এই পর্যালোচনায়। রামেন্দু মজুমদারের ‘বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক’ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী, আবদুল্লাহ আল-মামুনের এখনও ক্রীতদাস, মমতাজউদদীন আহমদের রাজা অনুস্বারের পালা ও সেলিম আল দীনের কেরামতমঙ্গল। প্রথম দুটি নাটকের ওপর আগের অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। অন্যান্য নাটকের সাথে বাকি তিনটি নাটকের ওপর আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করবো।
সাথে তাঁদের আরো কিছু নাটক যা আশির দশকে মঞ্চায়িত হয়েছে তা আলোচিত হবে। যদিও উল্লিখিত নাট্যকাররা কেউ নিজেদের শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যকার হিসাবে ঘোষণা দেননি, তবে স্বৈরাচার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরা জড়িত ছিলেন। সেজন্য তাঁদের নাটকগুলোকেও আমরা মার্কসবাদী বিশ্বাসের দিক থেকে না হলেও সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চেষ্টা করবো।
ঢাকা থিয়েটার আশির দশকে মঞ্চস্থ করে সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা। শোষক শোষিতের প্রসঙ্গ নিয়ে কিত্তনখোলা একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। ফরিদপুরের মনাই বয়াতির মাজারকে কেন্দ্র করে যে বিশাল গ্রাম্য মেলা, সেই মেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকের আখ্যান। মেলায় আছে কবি গানের আসর, যাত্রানুষ্ঠান, কথকঠাকুর, জুয়ার আখড়া, মদের আড্ডা, বিভিন্ন ধরনের দোকান-পাট, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি। মেলা দেখতে এসেছে নানারকম মানুষ। এসেছে দিনমজুর সোনাই, বছির। নাটকে অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে।
নাটকের কয়েকটি দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি হচ্ছে ইদু কন্ট্রাক্টরের সাথে মিরকি রোগী সোনাইর জমি নিয়ে সংগ্রাম। ইদু সোনাইর বন্ধকী জমিগুলো আত্মসাৎ করতে চায় বিভিন্ন উছিলায়। সোনাই যাতে ইদুকে জমিটা কবলা করে দেয় সেজন্য ইদু সোনাইকে আরো কিছু টাকা দিতে চায় যদিও সোনাই জমিটা ইদুকে কবলা করে দিতে রাজি নয়। সে মেলায় এসে ইদুকে এড়িয়ে চলে।
মেলায় যাত্রা করতে আসে ছায়ারঞ্জন, বনশ্রী বালা, রবিদাশ এবং দলের ম্যানেজার সুবল ঘোষ। মদের দোকানে ছায়ারঞ্জনের সাথে সোনাইর বন্ধুত্ব হয়। ছায়ারঞ্জন বনশ্রীর সাথে সোনাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেয়। বনশ্রী যাত্রাদলের নায়িকা। বনশ্রীর প্রতি ইদু কন্ট্রাকটরেরও নজর আছে। মেলাতে আরো আসে লাউয়া সম্প্রদায়, এরা বেদে সম্প্রদায়ের মতোই। লাউয়া সম্প্রদায়ের রোস্তমের সাথে মদের দোকানে সোনাইর পরিচয় ঘটে।
সোনাইর মিরকি রোগের ঔষধের জন্য রোস্তম সোনাইকে নিয়ে যায় ডালিমনের কাছে। রোস্তম ডালিমনের প্রতি দুর্বল। সর্দার ডালিমনের স্বামীকে হত্যা করে তাকে নিজের রক্ষিতা করে রেখেছে। সেজন্য সর্দারের সাথে রোস্তমের ঠাণ্ডা লড়াই চলে। সোনাইর সাথে দেখা হওয়ার পর ডালিমন যখন জানতে পারে সোনাইর স্ত্রী মারা গেছে, ডালিমনও ভিতরে ভিতরে সোনাইর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে তবে মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারে না।
ইদু কন্ট্রাক্টর এদিকে যাত্রার আগে বনশ্রীকে তার সামনে নাচতে বাধ্য করে। দলের ম্যানেজার সুবল ঘোষ ইদুর বিরুদ্ধে যাবে না জেনেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বনশ্রীকে নাচতে হয়। সুবল বনশ্রীকে যাত্রাদল থেকে তাড়িয়ে দিলে তারও আর যাবার কোনো জায়গা নেই। বেশ্যার জীবন ছেড়ে যাত্রার দলে এসেছে, আবার সে বেশ্যার জীবনে ফিরে যেতে চায় না। সুবল ঘোষ যে ইদুর নির্দেশ মেনে যা খুশি করছে তাতে ক্ষেপে যায় রবিদাশ ও ছায়ারঞ্জন। ছায়ারঞ্জন বনশ্রীর প্রতি দুর্বল এবং তাকে ভালোবাসে। বনশ্রীও ছায়াকে পছন্দ করে, সহজ-সরল এই যুবকের প্রতি টান অনুভব করে কিন্তু তার আসল দুর্বলতা বিপত্নীক রবিদাশের প্রতি। রবিদাশ ভাল না বাসলেও এক ধরনের দুর্বলতা অনুভব করে বনশ্রীর জন্য।
বনশ্রীর দিকে ইদু কন্ট্রাক্টর তার হাত আরো বেশি প্রসারিত করলে রবিদাশ সুবল ঘোষের সাথে বিরোধে নামে। সুবল ঘোষ যে খুব খারাপ লোক তা নয়। তবে বাস্তবতা তাকে মেনে নিতে হয়। সুবল ঘোষ রবিদাশকে বোঝায়, ইদুর কথা মতো কাজ না করলে পাওনা টাকাটা তো পাওয়াই যাবে না, বরং যাত্রাদলের পেছনে সে গুণ্ডা লাগিয়ে দেবে।
ইদু কিন্তু জানতে পারে সোনাই এসেছে কিত্তনখোলার মেলায় এবং সে যে তাকে • এড়িয়ে চলছে সেটাও টের পায়। তারপরও হঠাৎ দুজনে একবার মেলার মধ্যে মুখোমুখি হয়। সোনাই তখন সরাসরি ইদুকে বলে দেয়, সে তার বন্ধকী জমি ইদুকে কবলা করে দেবে না। ইদু তখন তার চেলা মালেক ও ওদ্দাকে কাজে লাগায়। ইদুর পরামর্শ মতো দুজনে সোনাইকে মদ খাইয়ে জুয়ার আসরে নিয়ে যায়। সোনাইকে বলে ওদের হয়ে জুয়া খেলে দিতে। সোনাই সরল বিশ্বাসে ওদের ফাঁদে পা দেয় এবং জুয়া খেলে দু হাজার টাকা হেরে যায়। মালেক ও ওদ্দা তখন ইদুর পরিকল্পনা মতো সোনাইর কাছে টাকাটা ফেরত চায়।
সোনাই তখন আশ্চর্য হয় ওকে এভাবে ঠকানো হয়েছে দেখে। সোনাই স্বভাবতই টাকা ফেরত দিতে না পারলে দুজনে মিলে সোনাইকে ভীষণ মারধর করে। সোনাই বুঝতে পারে ইদুর ষড়যন্ত্র এটা এবং তার বিরুদ্ধে একটা ক্রোধ জাগ্রত হয়। সে তখন কামারের দোকানে গিয়ে একটা দা বানায়। বনশ্রীকে নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ এবং ইদুর কাছে যাওয়া-না যাওয়া নিয়ে বনশ্রী আকস্মিকভাবে আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে ইদুকে হত্যা করে সোনাই পালিয়ে যায় রোস্তমের সাথে।
বাংলার দিন মজুরদের মদ খাওয়ার ব্যাপারটা সাধারণ গ্রাম বাংলার চিত্র কি না সেটা একটা প্রশ্ন। সেটা বাদ দিলে সেলিম আল দীন শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না গিয়েও শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের একটি বাস্তব ছবি এঁকেছেন এ নাটকে। গ্রাম বাংলার মূল চিত্রটিই ফুটে ওঠে সেখানে। সমস্ত শোষণ-পীড়নের মূল উৎসের প্রতি আলোকসম্পাত করে নাট্যকার যেমন ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি নয়া-জীবনবাদ প্রচারে অকুন্ঠ তিনি।
যদিও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তিনি এক সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেননি। শোষকের বিরুদ্ধে সোনাইর মূর্তিমান বিদ্রোহ নাটককে উজ্জ্বলতা দিলেও সোনাইর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সমাজ বাস্তবতা ফুটে ওঠে। যদিও রাজনৈতিক নাটকের লক্ষ্য সাধন তাতে হয় না। কারণ মিলিত মানুষের শক্তি যে শোষকশ্রেণীর পতন ঘটাতে পারে নাটকটিতে তার কোনো ইঙ্গিত ছিলো না। নাটকের সবচেয়ে বড় গুণ শোষক শোষিতের চরিত্রগুলো অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট নয়। দ্বন্দ্বগুলোর একটি চমৎকার পরিণতি আছে।
নাটকের বিশাল অংশ জুড়ে থাকা কবিগানের আসর, কাকুনুস পঙ্খীর ডিম থেকে মানুষের কাল্পনিক জন্ম বৃত্তান্ত এবং কথকতায় মানুষ ও পরীর অবাস্তব প্রেম বিষয়ক ‘সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান’-এর কাহিনী পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। নাটকে শোষক-শোষিতের দ্বন্দটি যদিও আসে খুবই বাস্তবসম্মতভাবে যা বাংলাদেশের অন্য কারো নাটকে সাধারণত দেখা যায় না, তবে নাটকটি দর্শকদের সমাজবিজ্ঞানের চেতনা দান করে না। সোনাইর হাতে ইদু কন্ট্রাক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকে প্রতিবাদ ঘোষিত হয় মাত্র, তা থেকে কোনো পথ নির্দেশ পাওয়া যায় না। বোঝাই যায় নাট্যকার দলীয় রাজনীতি বা বিশেষ কোনো মত দ্বারা প্রভাবিত নন।
তবুও বলতে হবে, শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় গণজীবনে যে শোষণ ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ জমেছে নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে তার নানা অভিব্যক্তি। সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা নাটকে গ্রামীণ বিভিন্ন পটভূমির সাথে লাউয়াদের সমাজ জীবনের দিকে নাট্যকার তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন। পুরাতন বিশ্বাস, সংস্কার তারা আগলে আছে জীবনে। লাউয়াদের জীবনের পূর্ণরূপ এ নাটকে ধরা না পড়লেও নাট্যকার মুখ্যত তাদের ঐতিহ্যচালিত জীবন দেখাতে চেয়েছেন। অনেকেই সে জীবন ছেড়ে চাষবাসের জীবন বেছে নিতে চায়। নতুন এই জীবন বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক দুঃখ ও দুর্গতির যে চিত্র থাকার কথা ছিলো নাটকে তা ফুটে ওঠেনি।
নাটকের চরিত্রগুলি অত্যন্ত সাধারণ। সহজ সরল অনাড়ম্বর মানুষ। তাদের অন্তরে শোষণ, বঞ্চনার জন্য ক্ষোভ-দুঃখ এবং উত্তেজনা আছে, কিন্তু বিপ্লব ঘটনোর মতো কোনো চরিত্র ধর্ম তাদের নেই। জীবন ধর্মে তারা অতি সাধারণ। সমাজের কাছে বা নিজের কাছে চাইবার মতোও কিছু নেই তাদের। তাই নাটকে শ্রেণীসংগ্রামের কোনো ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়নি। জোর করে তা চাপিয়ে দিতে চাইলে নাটকের স্বাভাবিক গতি ক্ষুণ্ণ হতো, নাট্যকার তা করেননি। যদিও ইদুর সাথে সোনাইর, সর্দারের সাথে রোস্তমের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত। বিচ্ছিন্নভাবে সোনাইর ইদুকে খুন করাটা বাস্তবসম্মত এবং ইদুকে খুন করার পর সোনাইর যে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না সেটাও ইতিহাসেরই সত্য।
সোনাইরা যখন ব্যক্তিগত ক্রোধে শোষককে হত্যা করে তার পরিণাম পলায়ন, যেদিন শোষিতরা ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন সমাজের জন্য সচেতনভাবে শোষকদের ধ্বংস সাধন করবে সেদিন তাদের আর পালাতে হবে না। মানব জীবনের অনেক গভীর প্রশ্ন এ নাটকে ফুটে উঠেছে। নাটকের ঘটনাগুলো আগায় বিশ্বাসযোগ্যভাবেই, তবে ঘটনার যে পরিণতি সেখান থেকে দর্শক নতুন কোনো চিন্তার খোরাক পায় না। ইদুকে হত্যা করার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পরিণাম শুধু পালানো-এধরনের হতাশার মধ্যেই তিনি নাটককে শেষ করছেন। ইদুকে হত্যা করে সোনাইর পালানো এটা একটি সত্য, তবে ভিন্ন সত্যও তো আছে। সেলিম আল দীন যেটা দেখিয়েছেন সেটা বাস্তব সত্য কিন্তু রাজনৈতিক নাটক বাস্তব পর্যন্ত গিয়েই থেমে থাকতে চায় না, চায় বাস্তবের সম্প্রসারণ। আর মার্কসবাদীদের বিশ্বাস সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায়।
• বাস্তবতার সম্প্রসারণ হলো সমাজ বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো, তথ্যবহুলতার দ্বারা কল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ইতিহাসের গতির দিকে চোখ রেখে সেখানে নাট্যকার কল্পনাকে সাজাবেন। ঘটনা ও চরিত্রকে পরিবর্তনশীল ও দ্বন্দ্বসহ উপস্থিত করতে হবে, যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে মানুষই মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক। মানুষকে হতাশার মধ্যে ঠেলে না দেয়ার জন্যই বাস্তবের সম্প্রসারণ ঘটা দরকার। উৎপল দত্তের জপেনদার ভাষায়, ‘যাহা বাস্তবে ঘটে কেবল তাহাই নাটকের বিষয় নহে, যাহা ঘটিবে, ঘটা উচিৎ তাহাও বাস্তব, সুতরাং তাহাও নাটকের বিষয়। ‘
এই সম্প্রসারিত বাস্তবতাই বিপ্লবী নাটকের ভিত্তি কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জোর করে নাটকের মধ্যে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া। মার্কসবাদীরা বাস্তবের এই সম্প্রসারণকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় নিয়ে যেতে চান যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক নিয়মকে তুলে ধরতে হবে। মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যে সামাজিক সম্পর্কগুলো সম্পর্কিত সেই বাস্তবতার প্রেক্ষিত থেকেই ঘটনাকে বুঝতে হবে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে দেখতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানে সমাজের কার্যকারণ সম্বন্ধীয় তথ্যকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা।
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ঘটনার মধ্যে থেকে সেইসব সত্য বের করে আনতে চায় যা শোষিতদের চোখ খুলে দেবে, সুন্দর একটি সমাজের জন্য তাকে সচেতন সংগ্রামী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। দু- একটি বা ততোধিক পরাজয়ে হতাশায় মুহ্যমান হবে না। বরং বিশ্ব একদিন শোষিত মানুষের দখলে আসবে সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হবে।
সেলিম আল দীনের কেরামতমঙ্গল নাটকটি গভীর জীবনবোধে ভরা। ঢাকা থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করে আশির দশকের মাঝামাঝি। এই নাটকে সেলিম আল দীন নিম্নবর্গের মানুষের জীবন ও তাদের শোষিত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন কেরামত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ১৪৭ পাকিস্তান জন্মের সামান্য পূর্বে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নাটকের শুরু, তারপর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে এই নাটক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। পাকিস্তানের জন্ম, জমিদার প্রথা উচ্ছেদ, তেভাগা আন্দোলনকে ঘিরে হাজং বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় সবই এ নাটকে উঠে এসেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার নানারকম চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে।
হিন্দু, মুসলিম, হাজং, গারো, ক্যাথলিক, খ্রীস্টান, জমিদার, রাজনৈতিক নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, ডাকাত, কৃষক, মাঝি, সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দল, এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে কেরামতমঙ্গলের পটভূমি বিস্তৃত। ঘটনার সময়কাল প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ব্যাপ্ত। নাটকের মূল বক্তব্য, ব্রিটিশ আমলের শেষে ও পাকিস্তান জন্মের পর রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতন কিংবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এসব কেরামতদের মতো সাধারণ মানুষদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারেনি। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারেনি। সেই সাথে ফুটে উঠেছে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনের ভিতরকার নানা দ্বন্দ্ব।
বিশেষ করে এ নাটকের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর বিভিন্ন সামাজিক প্রথার ও উচ্চবর্গের শোষণের চিত্র বস্তুনিষ্ঠতা লাভ করেছে। নাট্যকার খুবই দরদ দিয়ে দ্বান্দ্বিকভাবেই এইসব শোষণের, মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন। নাট্যকার এই দেশের আধা-সামন্তবাদী এবং আধা-পুঁজিবাদী আবহমানকালের শোষিত মানুষকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করেন।
মানুষের জীবনে যে হঠাৎ হঠাৎ রাজনৈতিক বৃহৎ সংগ্রামের বাইরেও প্রতিদিনের সংগ্রাম আছে, দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, সমাজের নানা সংস্কারের দ্বারা মানুষের জীবন যে বাঁধা পড়ে আছে তারই এক চমৎকার উপাখ্যান এ নাটক। শোষক ও শোষিতের জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মঞ্চের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক এটা। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা চারপাশের জনজীবন এবং তার সমস্যা আশ্চর্যভাবে এ নাটকে উঠে আসে। সে চেনাজীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে কেরামত। রূঢ় বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে নাট্যকার জীবন সম্পর্কে কোনো অযাচিত ভাবালুতার প্রশ্রয় দেননি। স্বভাববাদী নাট্যকারের মতো তিনি বাস্তবের নগ্ন চিত্র ও অনিবার্যতাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের নাটকের জন্য তা বিরল উদাহরণ।
নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত বৃত্তবিচ্যুত, শিকড়হীন-পৃথিবীতে তার কোনো আশ্রয় নেই। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে তাকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাড়ি দিতে হয়। সে দুনিয়ার জাগতিক পরিবেশ সম্পর্কে, শ্রেণীশোষণ সম্পর্কে, মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কমই জানে। মনটা কোমল এবং সে কিছুটা বোকা ধরনের। তাই চারপার্শ্বস্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিতে পারে। মানুষের লোভ-লালসা, হিংস্রতা, মূর্খতা এবং নির্দয়তা বারবার তাকে পরিচিত গণ্ডি থেকে ছিটকে বের করে দেয় এবং বারবার কেরামত অজানার পথে পা বাড়ায়। প্রত্যেকবার সে যে ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাতে তার হৃদয় আহত হয়, রক্তাক্ত হয়। কেরামতের বয়স বেড়ে চলে। জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলিও সমান তালে বৃদ্ধি পায়।
তা সত্ত্বেও কেরামত বিপ্লবের পথে আগায় না। মাঝে মধ্যে কেরামত প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মাত্র। সেটা অত্যাচারিত না হবার জন্য, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য। অনেকটা অসচেতনভাবেই। মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কয়েকটি বিদ্রোহী আবর্তে আমরা কেরামতকে দেখি তবে সে কোনোটিতেই সক্রিয় অংশ নেয় না। শোষিতদের প্রতি কেরামতের সহানুভূতি আছে কিন্তু কেরামতের মনে কোনো সচেতন জিজ্ঞাসা জন্মাতে দেখি না। স্বাভাবিকভাবেই কেরামত তার শ্রেণীকে রক্ষার দায়িত্ব অনুভব করে না। বিপ্লবী নয়, একজন মহৎ গুণাবলীর মানুষ হিসাবেই আমরা দেখতে পাই কেরামতকে। নাট্যকার দর্শকদের শিক্ষিত বোধসম্পন্ন তীক্ষ্ম সমালোচক করার চেয়ে তাদেরকে ঘটনার প্রতি সমব্যথী এবং সহানুভূতিশীল করে তোলার বেশি পক্ষপাতি।
তিনি মঞ্চে বিশাল সমাজ জীবন তুলে ধরেন, সে সমাজ সম্পর্কে, সেই বিগত দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন ভাবে আলোকপাত করতে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করেন না। যেন তাদের মাঝে সচেতনতা বোধ, বিশ্লেষণী শক্তি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নেই তার।যদিও তিনি নাটকের সমাপ্তিতে এসে উপসংহার টানছেন এভাবে, ‘যে এই নাটক দেখে-সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায় অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রণের জন্য যেন সে হাত বাড়ায়। ‘১৫২ এখানেও নাট্যকার ব্যক্তিগত আবেদনের মধ্যেই তার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। দর্শকের সামনে সমাজবিজ্ঞানের ধারণা তুলে ধরেও তাদের লড়াই করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন না।
নাট্যকারের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও নাটকটি শ্রেণীসচেতনতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে উঠতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, নাট্যকারের কাছে শ্রেণীসত্যের চেয়ে প্রতিদিনের বাস্তব সত্য অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে কেরামত নামে একটি দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তিগত বিয়োগান্ত পরিণতি ছাড়া এ নাটক রাজনৈতিক দিক থেকে খুব বেশি কিছু দিতে পারে না। সন্দেহ নেই নাটকটি একটি মহৎ রচনা, বিশাল দিগন্ত তার-কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে তা সরব নয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক প্রশ্নে নাট্যকার কি নীরব থাকতে পারেন? নাট্যকার ব্রেশটের মতে নাটক কেবলমাত্র সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিতই করবে না বরং তা হলো সেই বাস্তবের সক্রিয় অংশ; ফলে সেই বাস্তবকে পরিবর্তন করার ব্যাপারেও নাট্যকারের অবদান থাকতে হবে। নীরবেও নাট্যকার সে দায় পালন করতে পারেন, তবে তাকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেই হবে।
ঢাকার নাগরিক সম্প্রদায় আশির দশকে মঞ্চস্থ করে সৈয়দ শামসুল হকের নুরুলদীনের সারাজীবন। ইতিহাসের ঘটনার প্রেক্ষিতে শোষক-শোষিতের চরিত্র অঙ্কনে, শোষিতদের বিদ্রোহকে মঞ্চে তুলে আনার ক্ষেত্রে আশির দশকে সবচেয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক তার নূরুলদীনের সারাজীবন নাটকে। শোষিতদের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটেই মানব মনের নানা দ্বন্দ্ব, ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির নানা বাঁক তিনি তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের চরিত্র রংপুরের নূরুলদীন কৃষকদের নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলো ইংরেজ কুঠি ও দেশীয় গোমস্তা দেবী সিংয়ের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহে নূরুলদীন মারা পড়ে এবং বিদ্রোহীরা কোম্পানীর কাছে হেরে যায়। বিদ্রোহীদের হেরে যাবার নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই নাটকে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে।
জাতীয় উন্মাদনা এখানে রোমান্টিক ভাবাবেগ দ্বারা দুর্বল নয়, সংগ্রামী মানুষের আত্মবোধের দ্বারা আলোড়িত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানবপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটকে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটায় নাট্যকারের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকারের আধুনিক চিন্তনের একদিকে আছে চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিকাশ ও পরিণতি, অন্যদিকে দেশকালের ধারায় পরিবর্তিত জীবন ও মূল্যবোধ।
কোনো ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো ব্যক্তির প্রতি আক্রোশ বা অতিরিক্ত মহত্ত্ব দান না করে তিনি ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিক দিকগুলোকেই তুলে ধরেছেন।নূরুলদীন নাটকের সংলাপে বলছে, ভারতীয় জমিদার-মহাজন কিংবা ইংরেজ, যারাই ঘরের নারীকে কেড়ে নেয়, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, যারা গরীবের রক্ত শোষণ করে তারা একজাতি। হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান হোক ইংরেজ হোক কিংবা ভারতীয় হোক, যে শোষণ করে সেই শোষক। তারা সকলেই উপর তলায় বাস করে। বাকী যারা গরীব, তারা গরীব বলেই আর এক জাতি।
নাটকের আর এক জায়গায় ইংরেজ কালেক্টর গুডল্যান্ড বলছে, কলকাতার শিক্ষিত বাবুরা যেমন চায় ইংরেজদের কৃপা, তেমনি রংপুরের লোকরা পারলে যখন তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মরিস বলে, যারা ইংরেজদের সাথে আছে তারাও আছে নিজেদের স্বার্থেই, নাহলে তারাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। গুডল্যাড বলে, ‘স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে পরমশত্রুও মিত্র হয়ে দাঁড়ায়’।
বহু চমৎকার চমৎকার এ ধরনের সংলাপে নাটকের ঘটনার বাইরেও ইতিহাসের নানা সত্য বের হয়ে হয়ে আসে। নাটকটিতে চিন্তাভাবনার গভীরতা রয়েছে, কখনও তা একপেশে নয়; দ্বান্দ্বিক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। কিন্তু শামসুল হক নাটকটি কাব্যে রচনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে নাটকের বক্তব্য পৌছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কাব্য সাধারণ মানুষের ভাষা নয়। বিশেষ করে বর্তমান কালে যখন গদ্য গ্রাস করেছে সবকিছু, সৃষ্টি করেছে মহৎ নাটক ও সাহিত্য; সাধারণ মানুষের কাছে স্বভাবতই কাব্যের আবেদন কমে এসেছে। নাট্যকারকেও তখন সাধারণ মানুষের দিকটি বিবেচনা করতে হবে। নাটকের প্রধান দর্শক সাধারণ মানুষ; বর্তমান কালের নাট্যকারকে তাই সাধারণ মানুষের ভাষায়, সাধারণ মানুষের বোধগম্য নাটক লিখতে হবে।
সৈয়দ শামসুল হকের আর একটি নাটক এখানে এখন। নাটকের মধ্যে বহু কিছুর সমাবেশ ঘটেছে। নাটকটির প্রধান তিনটি চরিত্র রফিক, মিনতি, সুলতানা। গাফ্ফার নামের একটি চরিত্র আছে যাকে আমরা মঞ্চে দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের তিন বন্ধু রফিক, গাফ্ফার ও সুলতানা। রফিক সুলতানাকে ভালোবাসলেও ছাত্র জীবনে কখনও মুখ ফুটে সে কথা বলেনি। গাফ্ফারের সাথে সুলতানার বিয়ে হয়। রফিক পরবর্তীতে আর বিয়ে করে না।
নাসিরের সাথে সে অংশীদারিত্বে ব্যবসা করে এবং গাফ্ফার-সুলতানাদের পরিবারের সাথেই থাকে। গাফ্ফার ও সুলতানা আজমীর গেলে খালি বাসা পেয়ে নাসির সেখানে মিনতিকে নিয়ে আসে সারা রাত ভোগের জন্য। রফিকেরও সে রাতে মিনতিকে ভোগ করার সুবিধা থাকলেও সে তা করে না। নাসির ভোগ সেরে ঘুমিয়ে পড়লে মিনতির সাথে গল্প হয় রফিকের।
মিনতি জানায় নাসিরের মতো আরো বহুজনের কাছে তাকে যেতে হয় বেঁচে থাকার আর্থিক সঙ্গতি লাভের জন্য। যাদের কাছে সে যায় তারা আবার তাকে অন্যদের কাছে পাঠায় নিজেদের ব্যবসা উদ্ধারের কাজে। মিনতিকে এইসব কিছু গোপন রাখতে হয় তার খদ্দেরদের স্বার্থে। কোনোরকম গোপনীয়তা ফাঁস হলে তার মুখ এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হতে পারে সেই ভয়ে মিনতি তটস্থ। এমনকি নাসিরও তার মুখ এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে। রফিক মিনতির এধরনের ভয়ের কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না।
নাসিরের সাথে এর মধ্যে রফিকের সম্পর্ক নষ্ট হয় ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। ব্যবসার স্বার্থে দেখা যায় দুই বন্ধু পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেট্রো-ডলারকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদেরকে বিকিয়েও দিচ্ছে। সুলতানার সাথে রফিকের সুন্দর সম্পর্ক, অপরদিকে গাফ্ফারের সাথে দাম্পত্য জীবনে সুখী নয় সুলতানা। গাফ্ফার ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সুলতানাকে সেভাবে সময় দেয় না। নাটকে সুলতানার অতৃপ্ত জীবনকামনা রূপান্তরিত হয়েছে মনস্তাত্বিক সংগ্রামে। বঞ্চিত দাম্পত্যজীবনের ক্ষুব্ধতা তাকে করেছে বিদ্রোহী। সুলতানা রফিককে জানায়, গাফ্ফারকে সে তালাক দেবে-সেক্ষেত্রে রফিক সুলতানাকে বিয়ে করতে রাজি কি না। রফিক সুলতানাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। দুজনে সংসার করার কথা বলে।
সে আলোচনার পর রফিক সুলতানাকে দৈহিকভাবে পেতে চাইলে সুলতানা বাধা দেয়। সে বলে বিয়ের আগে এসব নয়। রফিক জোর করতে গেলে সুলতানা তাকে চড় লাগায়। ঘটনা তাতে পাল্টে যায়। রফিক প্রথমে সুলতানার হাত মোচড়ায়, পরে তার দিকে এসিড নিক্ষেপ করে। শেষ দৃশ্যে রফিক এসেছে মিনতির কাছে। মিনতিকে আজ সে কাছে পেতে চায়। মিনতি তখনো তার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে। রফিক মিনতির মুখ দেখতে পায় না। রফিক মিনতিকে তার দিকে মুখ ফিরাতে বলে। মিনতি মুখ না ফিরালে রফিক জোর করে মিনতির মুখ তার দিকে ফেরায় এবং রফিক দেখতে পায় মিনতির মুখ এসিড দগ্ধ। এসিড দিয়ে নারীর মুখ পুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় নাটকে।
নিঃসন্দেহে এসিড দিয়ে মেয়েদের মুখ পুড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটা তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তবতার চিত্র। তবে নাট্যকার ঘটনাকে যেভাবে নাটকে আনেন, যেভাবে তার ব্যাখ্যা দেন সেটাকে মনে হয় চাপিয়ে দেয়া। ঘটনার স্বাভাবিক গতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রফিক দীর্ঘদিন ধরে সুলতানাদের সাথে এক বাড়িতে থাকছে এবং অনেক রাতে শুধু সুলতানা ও রফিকই বাড়িতে ছিলো।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 14 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৩ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৫.jpg)
সে সময় রফিক সুলতানার প্রতি কোনো অস্বাভাবিক আকর্ষণ দেখায়নি বা সুলতানার প্রতি কোনোরকম দৈহিক সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ নেয়নি। যা প্রমাণ করে সুলতানার প্রতি রফিকের কোনোকালেই তীব্র দৈহিক আকর্ষণ ছিলো না। এরপর নাটকে হঠাৎ দেখা যায়, রফিক সুলতানার সাথে যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরিকল্পনা করে এবং দৈহিকভাবে পাবার বৈধ পথও সুগম হয়, সে সময় বিবাহের আগেই দৈহিকভাবে সুলতানাকে পাবার জন্য জোর করে-সেটা খুব অসংলগ্ন মনে হয়। নাটকে এমনি আরো অসংলগ্ন বহুকিছুর সংযোজন ঘটেছে। পাশাপাশি বিবাহের আগে নর-নারীর দৈহিক মিলনের প্রশ্নে নাট্যকারের রক্ষণশীল চিন্তারও প্রকাশ ঘটেছে।
সন্দেহ নেই, অবহেলিত নারীর অবদমিত ব্যক্তিত্ববোধ নতুন মূল্যবোধ নিয়ে এ নাটকে উদ্ভাসিত। ব্যক্তিত্ব সচেতন নারীত্বের নিগৃহীত, নিভৃত হাহাকারের আর্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন নাট্যকার। নাটকের অন্যদিকে আছে দেশকাল, যা নাট্যকারকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় অস্থির করেছে। তা সত্ত্বেও চারটি চরিত্রের মনঃসমীক্ষণের বিস্তার নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রেম, যৌনতা ও নারীর ব্যক্তিগত সমস্যাই সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে। দেশকাল ও মনুষ্যত্ববোধের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক নারীত্ব সম্পর্কিত ভাবনা। সেটাই নাটকটির মূল দিক। নাটকটির যে একটি রাজনৈতিক দিক নেই তা নয়। সে রাজনীতিটি বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। এরিক রাসেল বেন্টলির মতে মঞ্চে রাজনীতিকে খুব জটিলভাবে তুলে ধরার কোনো অর্থ হয় না।
তিনি লিখেছিলেন, ‘বস্তুত জটিল রাজনীতির প্রচেষ্টা চালাতে গেলে রাজনৈতিক থিয়েটারকে ব্যর্থই হতে হবে। কারণ অস্পষ্টতা মানেই অসম্পূর্ণতা এবং এই অসম্পূর্ণতাই যে-কোনও প্রযোজনাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজনা ভালো হয়েছে তখনই যখন রাজনীতি হয়েছে অত্যন্ত সহজ সরল। ১৫৫ শামসুল হকের এই নাটকে বিপরীতটাই লক্ষ্য করা গেছে।
নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটারের একজন সক্রিয় কর্মী এবং প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি দলের প্রধান নাট্যকার ও নির্দেশক। আশির দশকের প্রথম দিকে থিয়েটার কর্তৃক আবদুল্লাহ আল-মামুনের দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এখনও ক্রীতদাস। নাটকটি বস্তির জীবন নিয়ে লেখা। পঙ্গু বাক্কা মিয়া, তার স্ত্রী কান্দুনি ও কন্যা মর্জিনা নাটকের মূল চরিত্র। বাক্কা মিয়া স্বাধীনতার আগে ট্রাক চালাতো। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে সে পঙ্গু হয়। তারপর থেকে সে সম্পূর্ণ লুলা ও অকেজো। সেজন্য অষ্টপ্রহর সে ক্ষেপে থাকে। লুলা বলে তাকে স্ত্রীর কামাই খেতে হয় আর এজন্য দিনরাত স্ত্রীর অপমান হজম করতে হয়। স্ত্রী কান্দুনি মানুষের বাড়িতে কাজ করে। রিক্সাওয়ালা হারেছ দুর্বল কান্দুনির প্রতি।
বাক্কা মিয়ার পঙ্গুত্বের সুযোগে সে কান্দুনির দিকে হাত বাড়ায়। কান্দুনিরও যে হারেছের প্রতি দুর্বলতা নেই তা নয়। কাজী আবদুল মালেক নামে একজন ধূর্ত লোকও বস্তিতে আসা যাওয়া করে। লোকটা আসলে গুণ্ডা প্রকৃতির এবং নারী-দেহের ব্যবসা চালায়। কাজী নারী সংগ্রহের কাজে বস্তিতে এলে বাক্কা মিয়ার সাথে এসেও গল্প করে যায়। কাজীর আসল পরিচয় বাক্কা মিয়া জানে না। বাক্কা মিয়ার মেয়ে মর্জিনা সিনেমার একস্ট্রা। সিনেমার একজন ফাইটার যে মর্জিনাকে পছন্দ করে, তার সাথে মর্জিনা সুটিংয়ে যায়। বহুরাত হলে সে বাড়িতে ফেরে না। ফাইটার কাজী আবদুল মালেকের কর্মচারী।
যে-রাতে মর্জিনা বাড়ি ফেরে না সে-রাতে আসলে সে কাজী ও তার লোকজনদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। ফাইটারের অজান্তে ঘটে ব্যাপারটা। ধর্ষিত হবার পর মর্জিনা বেশ্যার জীবন বেছে নেয়। এদিকে কান্দুনিও বাসার কাজে চুরি করতে গিয়া ধরা পড়ে এবং কাজ হারায়। রিক্সাওয়ালা হারেছ তাকে নতুন কাজ জুটিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত নাটক মোটামুটি স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। এরপর নাটকের ঘটনা আগাতে থাকে দ্রুত ও খুব নাটকীয়ভাবে।
বাক্কা মিয়া রাগের মাথায় মর্জিনাকে তালাক দেয়ার কথা ঘোষণা করলে সেটা তালাক হয়ে যায়। এর পর কান্দুনির সাথে হারেছের বিয়ে হয়। সিনেমার ফাইটার চরিত্রটি জারজ হলেও মা বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সে পছন্দ করে না। মর্জিনার ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা জানার পর ফাইটারের সাথে কাজীর বিরোধ বাধে। এদিকে মর্জিনা তার বাবার ওখানে কাজীকে দেখে তাকে চিনে ফেলে। কাজী তখন সিদ্ধান্ত নেয় মর্জিনাকে গুণ্ডা দিয়ে তুলে নিয়ে গুম করে দেবে। ফাইটার এ কথা জানার পর পুলিশকে খবর দেয়। এ নাটকে মনে হয় পুলিশরা যথেষ্ট দায়িত্ব পরায়ণ। পুলিশ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বস্তিতে চলে আসে। পুলিশ আসার আগেই মর্জিনা গুণ্ডাদের দ্বারা অপহৃত হয়।
পুলিশ এসে কোনো কারণ ছাড়াই ফাইটারকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর পুলিশ কাজী ও অন্যান্য অপরাধীদের খুঁজে বেড়ায়। পুলিশের ভয়ে কাজী নিজের পিস্তলটা বাক্কা মিয়ার কাছে রেখে যায়। বাক্কা মিয়া এর মধ্যে জানতে পারে কাজীই আসল অপরাধী। পুলিশের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে কাজী ফিরে আসে বাক্কা মিয়ার কাছে তার পিস্তলটার জন্য। বাক্কা মিয়া পিস্তলটা ফেরত না দিয়ে সেটা তাক করে ধরে কাজীর দিকেই। কাজীকে সে হত্যা করতে চায়। হঠাৎ সেখানে কাজীর লোকরা উপস্থিত হয় এবং বাক্কা মিয়ার কাছ থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেয়। তারপর কাজী নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে বাক্কা মিয়াকে।
নাট্যকারের নাট্যভাবনা ব্যক্তির একক বিদ্রোহের মধ্যে এক অসহায় আশাহত মানুষের আর্তনাদের মধ্যে শেষ হয়। এরকম সামাজিক ক্ষোভ বা বিদ্রোহের দ্বারা সমাজ এবং ব্যক্তি মানুষের উপকার সাধিত হয় না। শক্তিক্ষয়ের অবসাদে জীর্ণ ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে শুধু। জাগে হতাশা ও বিভ্রান্তি। প্রত্যাশিত মুক্তির সম্ভাবনা হয় অবলুপ্ত। ব্যর্থ জীবনের নৈরাশ্য, খেদ, হাহাকার, অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে বিদ্রোহ চলে, বিপ্লব বা সমাজপরিবর্তন চলে না। প্রকৃতপক্ষে সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো গঠনের কোনো ধারণাই বাক্কা মিয়ার মধ্যে ছিলো না। তার বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অধিকার চেতনা এক ক্ষয়িষ্ণু মানুষের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
বস্তুত যে সামাজিক দুরবস্থার মধ্যে সে বাস করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব থাকা তার মধ্যে খুবই স্বাভাবিক। নাটকে এ থেকে তার একটি মনস্তাত্বিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু দর্শকের জন্য কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাতে তৈরি হয় না। কোন ধরনের রাজনীতিতে নাট্যকারের বিশ্বাস তাও বোঝা যায় না।
নাট্যকার এ নাটকে বেশ জীবন্ত ও খুব গতিশীল ভাষার ব্যবহারে করেছেন। যদিও বস্তির জীবন নিয়ে নাটক রচনার পেছনে তার উদ্দেশ্যটি বোঝা যায় না। বস্তি জীবনের সমস্যাগুলোকে তিনি এ নাটকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। নাটকটিতে যুক্তির চেয়ে হৃদয় বৃত্তিকে অতিরিক্ত প্রাধ্যান্য দিয়ে ফেলার প্রবণতাও এড়ানো যায়নি। নাটকটি শেষ হয় খুবই নাটকীয়ভাবে।
বাক্কা মিয়া নামে একজন দরিদ্র ও পঙ্গু মানুষের ব্যক্তিগত বিয়োগান্ত পরিণতিই এ নাটকের প্রধান দিক। বস্তি জীবনের সামাজিক প্রেক্ষিতের চেয়ে ব্যক্তি বাক্কা মিয়ার দুঃখ কষ্টগুলোই এ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে, বস্তি জীবনের সামগ্রিক দলিল হয়ে উঠতে পারেনি। ঘটনার বাস্তবতার মধ্যেই নাট্যকার আটকে ছিলেন, ঘটনাকে বাস্তবোত্তরে নিয়ে যেতে পারেননি। মহৎ নাটকের কাজ বাস্তবকে সামনে নিয়ে যাওয়া, বাস্তবোত্তরে পৌছানো। কিন্তু আবদুল্লাহ আল-মামুন কিছু খণ্ডিত ফটোগ্রাফিক সত্যের মধ্যে নাটকের ব্যাপ্তিকে, বস্তির জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন।
বাস্তবকে, জীবনকে যথাযথ তুলে ধরা সহজ নয়। জীবন তো যুগে যুগে পাল্টায়। নতুন জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশকালে জীবন নতুন চেহারা নেয়। জীবন তাই শুধু ঘটনা স্রাত নয়। জীবন বলতে একটা যুগের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, স্বপ্ন- সাধনা সবকিছুই বোঝায়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তার একটা সম্পর্ক থাকে। সেই সামগ্রিক সময়টাকে, সেই সম্পূর্ণ যুগটাকে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনকে তুলে ধরা যায় না। জীবন মানে সেই সময়ের সমগ্র ব্যবস্থাটার সাথেই তার দ্বন্দ্ব। ১৫” দ্বন্দ্বটাই সেখানে প্রধান। সে দ্বন্দ্ব শুধু বাইরের দ্বন্দ্ব নয়, সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রের সাথে সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব।
এখনও ক্রীতদাস নাটকটিতে নিঃসন্দেহে বস্তির মানুষের প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বস্তি-জীবনের অনেক দ্বন্দ্বও এ নাটকে চমৎকারভাবে উপস্থিত তবে রাষ্ট্রের সাথে তার দ্বন্দ্বটি আমরা দেখতে পাই না। নাটকে বস্তি জীবনের নানা দুঃখ কষ্টের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হলেও বস্তিবাসীদের এই জীবনের জন্য কারা দায়ী বা কীভাবে বস্তির এই জীবন থেকে মানুষের মুক্তি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কিছুই এ নাটকে বলা হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কাজী এ নাটকে খারাপ চরিত্র হয়ে আসে।
কাজীর দ্বারা বাক্কা মিয়ার মতো একজন পঙ্গুকে হত্যা করার ব্যপারটা শেষ দৃশ্যে কতটুকু যৌক্তিক সে প্রশ্নও এখানে থেকে যায়। আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রায় সব নাটকেই শেষ দৃশ্যে অসংলগ্ন ও যুক্তিহীনভাবে অনেক অতিনাটকীয় ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যেজন্য রামেন্দু মজুমদার লিখছেন, ‘আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংলাপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুগঠিত। সোশাল স্যাটায়ার রচনায় তাঁর পারদর্শিতা স্বীকৃত। কিন্তু তার অনেক নাটকেরই সমাপ্তি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।
কাজী আবদুল মালেকের চরিত্র অংকনের ক্ষেত্রে নাট্যকার ছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট। বস্তিবাসীদের অন্যান্য চরিত্র অংকনের ক্ষেত্রে নাট্যকার একটি দ্বান্দ্বিক ধারা অনুসরণ করেছেন, তাহলো চরিত্রগুলোকে তিনি পূতপবিত্র করে তৈরি করেননি, সৃষ্টি করেছেন তাদের দোষগুণ সমেত। তাদের সবরকম নীচতা এ নাটকে ধরা পড়েছে-কান্দুনি চোর, বাক্কা মিয়া ধূর্ত, মর্জিনা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দোষগুণসহ চরিত্রগুলো উঠে আসে বলেই সেগুলো এতো জীবন্ত এ নাটকে। তবে চরিত্রগুলোর মধ্যে খুব বেশি আবেগের বাড়াবাড়ি রয়ে গেছে।
নাটকটিতে খুব গালাগাল ও খিস্তি ব্যবহার করা হয়েছে। গালাগাল বা খিস্তি ব্যবহার সম্পর্কে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নিজস্ব বক্তব্যটি আগে আমরা এখানে তুলে ধরবো। এখনও ক্রীতদাস মঞ্চে আসার বহু পরে, পচাশি সালে তিনি এক নিবন্ধে লিখছেন, ‘সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু নাটকে অহেতুক গালাগাল প্রয়োগ করার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তব, নিষ্ঠুর বাস্তব, কঠোর বাস্তব ইত্যকার যুক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রাত্যহিক জীবন থেকে এমনসব কথাবার্তা তুলে আনা হচ্ছে, যা দিয়ে আর যাই হোক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। ভাবা হচ্ছে যে, একটা বিরাট কিছু হ’লো-আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে যে, জীবন থেকে সংলাপ তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম চারদিকে।
তিনি আরো লিখছেন, ‘কিন্তু আমার ধারণায়, এতে করে নাটকের শরীরে ঘামাচি উঠছে, ফোস্কা পড়ছে, আজকের নাট্যকারকে এই দিকটা ভাবতে হবে।’এই সব বক্তব্য যিনি দিচ্ছেন তিনিই আবার তাঁর নাটকে গালাগাল ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। এখনও ক্রীতদাস নাটকের প্রথম সংলাপটি হচ্ছে কান্দুনির। কান্দুনি নেপথ্য থেকে বলছে, ‘কন হারামীর বাচ্চা, কুন্ ভাতারখাকী আমার গাতার পানি লইছে? আমি জিগাই, অই বান্দীর বাচ্চারা, অই হালার পো-রা, এই মাগীরা, যুদি সাহস থাকে ত আয়, আমার সুমখে আয়, স্বীকার যা কে আমরা গাতার পানিতে আত দিছে।’মর্জিনা তার বাপ বাক্কা মিয়াকে বলছে, ‘আমার হাত ছার শালা-ছার ছার্…’।
সারা নাটকই এ ধরনের গালাগাল বা অশ্লীল শব্দে ভরা। হারেছের সংলাপ, ‘অহন কেমুন লাগতাছে? ধইরা খারা কইরা রাখছিলাম পাছার মইদ্যে পিপড়ায় কামড় দিছিলো। বাক্কা মিয়া হারেছকে বলছে, ‘তোর চক্ষে মুখে আমি পেচ্ছাপ করুম। ‘১৬৪ আবদুল্লাহ আল-মামুনের এই সব সংলাপের ভিতর দিয়ে তাঁর দেয়া বক্তব্যের সাথে তাঁর স্ববিরোধিতা ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতাদের বক্তব্যে আমরা এ ধরনের স্ববিরোধিতা বারবার লক্ষ্য করবো যা নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সততার ব্যাপারটিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।
যদি আমরা রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার দিক থেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের এ নাটকটিকে বিচার করি তাহলে কী দাঁড়ায়? নাটক মাত্রেই নাটকীয়, জীবন থেকে অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নাটকীয়তার কারণে যেন মূল বিষয়বস্তু হারিয়ে না যায় সেটাও নাট্যকারের লক্ষ্য রাখবার ব্যাপার। নাটকে যতোই নাটকীয়তা থাক, যদি তা দর্শককে উন্নততর চিন্তার সাথে পরিচয় না করিয়ে দিতে পারে তাহলে নাটকীয়তা তৈরির ফল হয়ে দাঁড়ায় শূন্য।
পৃথিবীর যে-সকল নাট্যকাররা একই সাথে জনপ্রিয় ও মহৎ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁরা নাটকের মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন, মুহুর্মুহু চমকপ্রদ সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, দর্শককে নাটক ভালো লাগাবার যতো পেশাদারী বাণ আছে সব ছুঁড়েছেন, একইসঙ্গে দর্শককে নতুন চিন্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। জনপ্রিয় নাটক রচনার পাশাপাশি জনতার চিন্তাশক্তিকেও নাড়া দিয়ে গেছেন।
শুধু ঘটনার বর্ণনা করেই তারা ক্ষান্ত হননি, পাশাপাশি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। জগত সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে নতুন সব ধারণার সাথে মানুষকে পরিচিত করে তুলেছেন। নাটককে জনপ্রিয় করার তাঁদের কায়দা কানুন কখনও ঘটনার বাস্তবতা ও নাটকের শিল্পমানকে ক্ষুন্ন করেনি। সেখানে আবদুল্লাহ আল-মামুনের উক্ত নাটকে আমরা নাটকীয়তা পেলেও বিষয়বস্তুর নতুনত্বের চেয়ে গোটা প্রযোজনার চমক দর্শককে বিভ্রান্ত করে। বস্তি-জীবনের গালাগাল নাটকে এত মুহুর্মুহু ব্যবহৃত হয়েছে যে, গালাগালের হুল্লোড়ে নাটকের আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। যে বাস্তবকে তিনি নাটকে ধরতে চান তা বাস্তবেই থেকে যায়; বাস্তবোত্তর হয়ে উঠতে পারে না। বাস্তবের সম্প্রসারণ সেখানে দেখতে পাই না।
আবদুল্লাহ আল-মামুনের আর একটি নাটক অরক্ষিত মতিঝিল। নাটকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ঢাকার বাণিজ্য কেন্দ্র মতিঝিলের বদের দুর্নীতি। সেটা দেখাতে গিয়ে কেরানি শিহাবের জীবন সংগ্রামটাকেই বড় করে তোলা হয়েছে। শিহাবের বস্ ঘুষখোর। প্রচুর ঘুষ খায় সে। দুর্নীতি দমন বিভাগের ভয়ে সে বাজারের ব্যাগের মধ্যে করে ঘুষ খাওয়া শুরু করেছে। নাট্যকার বোঝাতে চান দুর্নীতি দমন বিভাগ খুবই দায়িত্বশীল ও সৎ।
বস্ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ফুলে উঠছে, আর শিহাব টাকার অভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারছে না। শিহাব প্রেম করে ধনীর দুলালীকে বিয়ে করে তাকে সুখ দিতে পারেনি। স্ত্রীর ক্যানসার ধরা পড়লেও সে তার চিকিৎসা করাতে পারে না। মধ্যবিত্ত এক কেরানির জীবন এভাবেই নাটকে প্রধান হয়ে ওঠে। স্ত্রী মারা গেলে শিহাব তার জন্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চায়। বকে ব্ল্যাকমেইল করে সে তার ঘুষ থেকে দুলাখ টাকার দুটো বাজারের ব্যাগ নিয়ে আসে। বস্ টাকাটা দিতে না চাইলেও বসের একান্ত সচিব বস্কে রাজি করিয়ে ব্যাগ দুটো দিয়ে দেয় শিহাবকে।
শিহাব ঘরে ফিরে দেখে তার খালি ঘরে চোর ঢুকে বসে আছে। লাকসামের এককালের ফুটবলার বাধ্য হয়ে এখন চুরি করছে। শিহাব চোরটির সাথে নাটকীয় আচরণ করে। তার হাতের ব্যাগের মধ্যে কী আছে তাও চোরকে বলে দেয় এবং ব্যাগ দুটো চোরের কাছে রেখে পাশের ঘরে চলে যায়। চোর সে সুযোগে একটি ব্যাগ নিয়ে কেটে পড়ে, বাকি ব্যাগটা রেখে যায় যাতে শিহাব তার স্ত্রীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে পারে। শিহাব আসলে চোরকে দুটো ব্যাগ নিয়েই পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলো, চোর একটি ব্যাগ রেখে যাওয়াতে সে নিম্নমধ্যবিত্তের ভীরুতা দেখে হাসে। শিহাব স্ত্রীর নামে স্মৃতিসৌধ করার জন্য টাকা এনে তা কেন চোরকে দিয়ে দিতে চায় তার কোনো ব্যাখ্যা নাটকে নেই। নাট্যকার শিহাবের খেয়াল হিসাবেই ঘটনাটা আমাদেরকে দেখান।
বসের একান্ত সচিব মনে মনে দুরভিসন্ধি নিয়ে ব্যাগ দুটো শিহাবকে দিয়েছিলো। শিহাব ব্যাগ দুটো নিয়ে চলে আসার পর বস্ ও বসের একান্ত সচিব পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশকে সাথে নিয়ে বস্ ও বসের সচিব শিহাবের বাসায় আসতে গিয়ে পথিমধ্যে চোরটাকে তারা ধরে ফেলে এবং চোরটাকে সাথে নিয়েই তারা শিহাবের বাসায় এসে উপস্থিত হয়। ব্যাগ খুলে পুলিশ দেখতে পায় তার মধ্যে আসল টাকা নেই, যা আছে তাহলো টাকার ফটোকপি। পুলিশ শিহাবকে গ্রেফতার করতে চায়। শিহাব তখন তার বস্কে গ্রেফতার করতে বলে। পুলিশ সব কিছু বুঝেও টাকা জাল করার জন্য শিহাবকেই ধরে নিয়ে যেতে চায়। শিহাব তখন চোরকে ইঙ্গিত করলে চোর তার বাঁধা দুহাত দিয়েই দারোগার মাথায় আঘাত করে। দারোগার হাত থেকে রিভলবার পড়ে যায়। সেটা তুলে নেয় শিহাব।
তারপর সকলকে দুহাত উপরে তুলে দাঁড় করিয়ে রাখে, বস্ ও একান্ত সচিবকে কিছুটা অপমান করে। ১৬৬ তারপর নাটক ঘোষণা দেয়, ‘সুদূর কালীগঞ্জের হেঁপো রোগী কলিমুদ্দি যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। দৃপ্ত পায়ে। মতিঝিল এখন ওর ভয়ে টলছে, কাঁপছে। কলিমুদ্দি এবার মতিঝিলের কাছ থেকে ওর পাওনা বুঝে নেবে কড়ায় গণ্ডায়। ‘আবদুল্লাহ আল-মামুনের এ নাটকে একজন কলিমুদ্দিই যথেষ্ট মতিঝিলের কাছ থেকে পাওনা বুঝে নিতে। কলিমুদ্দির ভয়ে কাঁপছে মতিঝিল।
ব্যক্তিকে দিয়েই মামুন এভাবে বিপ্লব ঘটান। একজন ব্যক্তি যেমন কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারে না তেমনি বিপ্লবটা নাটকীয়ভাবে রাতারাতি ঘটবে না। সেজন্য দরকার দীর্ঘ প্রস্তুতি। যাঁরা ব্যক্তিবাদের পূজারী তাঁরা ব্যক্তিকে দিয়েই রাতারাতি বিপ্লব ঘটাবার স্বপ্ন দেখেন। পিসকাটর বলেছিলেন, রাজনীতিতেই মানুষ সবচেয়ে পরিস্ফুট, রাজনীতির মধ্যেই মানুষ যথার্থ মানুষ। কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের কালে কোন্ দৃষ্টিতে মানুষকে দেখা সমীচীন সেটাই প্রশ্ন। বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের যা অবশিষ্ট ছিলো, প্রতিযোগিতার মাঠে নেমে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মানুষ এখন পরিচয়হীন। পুঁজিবাদ সত্যিই মানুষকে নামগোত্রহীন সৈনিক করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকে দেখা যায়, মানুষের পরিচয় সংখ্যায় রূপ পেয়েছে।
নাটকে এই বৃহৎ ঐতিহাসিক চিত্রের পটভূমিকায় মানুষকে দেখাতে হবে। বিজ্ঞানের যুগে নাটক লিখতে হলে তাই মানুষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন; পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে হবে মানুষকে। নাট্যকারের সঙ্গে তাঁর রচিত চরিত্রগুলির সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক এবং যুক্তি নির্ভর হতে হবে। তাহলেই নাট্যকার চরিত্রগুলির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কিন্তু নাট্যকার মামুন তা পারেননি, সব নাটকে ব্যক্তিত্ববাদের জয়গান করেছেন। ব্যক্তির হাতে তিনি পুরো সমাজের মুক্তি দেখেছেন।মমতাজউদ্দীন আহমদের রাজা অনুস্বারের পালা নাটক নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো। রাজা অনুস্বারের পালা একটি রূপকধর্মী রচনা। রূপক নাটক সর্বদা গড়ে ওঠে বাস্তবভিত্তির ওপরে।
কিন্তু মমতাজউদ্দীন আহমদের এই রূপকের নাটকের সাথে বাস্তবের, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাজা অনুস্বার তার একদল তোষামোদকারী মন্ত্রীদের নিয়ে দেশ চালাচ্ছে। অনুস্বার নিজের পিতাকে হত্যা করে রাজা হয়, পরে সিংহাসন কণ্টকমুক্ত রাখতে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করে। রাজার স্ত্রী চন্দ্রবিন্দু বন্ধ্যা। সেজন্য রাজা অনুস্বার তার ঔরসে ও তার প্রণয়ী বহুব্রিহীর গর্ভজাত সন্তানকে স্ত্রী চন্দ্রবিন্দুর কোলে তুলে দেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজার মনে হয়, সে যেমন পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতায় এসেছে তার সন্তানও ঠিক সেইভাবে ক্ষমতার লোভে তাকে হত্যা করতে পারে। সেজন্য সে গোয়েন্দা প্রধানকে দায়িত্ব দেয় তার পুত্রকে হত্যা করার।
রাজা নিজের ঔরসজাত পুত্রকে হত্যা করতে চায়, অথচ পরবর্তী উত্তরাধিকার ভ্রাতুস্পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে তার আপত্তি নেই। গোয়েন্দা প্রধান রাজার পুত্রকে হত্যা না করে গোপনে বাঁচিয়ে রাখে। গোয়েন্দা প্রধানের এতে স্বার্থ কী নাটকে সেটা বোঝা যায় না। রাজার ছেলে বড় হয়ে রাখাল বালক হয়, ভালো বাঁশীও বাজায়। রাজা কিন্তু নিজের পুত্রের বেঁচে থাকার খবর জানে না। এদিকে রাজার প্রাক্তন প্রণয়ী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার খাওয়া, তার ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। মাঝে মধ্যে জাগরণেও রাজা তাকে দেখতে পায়।
রাজা হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই সারাদেশে আইন করে দেয় কোনো রকম দুঃখ- কষ্টে কেউ কাঁদতে পারবে না। কেউ কাঁদলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। রাজা তার বা রাজ্যের কোন্ স্বার্থে আইনটি করে বোঝা যায় না। এদিকে রাজার প্রাক্তন প্রণয়ী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে। রাজার স্ত্রী চন্দ্রবিন্দুও রাজাকে ছেড়ে চলে যায়। রাজা নিজের স্ত্রীকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে বাধা দেয় না। চন্দ্রবিন্দুও রাজার বিরুদ্ধে বহুব্রিহীর দলে যোগ দেয়। এদিকে একদিন একজন কাঠুরে প্রজা গাছ থেকে পড়ে মারা গেলে তার পিতা এ ঘটনায় কাঁদতে শুরু করে। রাজার ভাতিজা আইন অমান্য করার জন্য কাঠুরেদের ওপর আক্রমণ চালায়।
কাঠুরেরাও প্রতিবাদ করে। রাজার সৈনিকরা তখন কাঠুরেদের ধরে এনে বন্দী করে রাখে, কাউকে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলায়। রাজার ছেলেও গ্রেফতার হয় করুণ সুরে বাঁশী বাজাবার অপরাধে। রাজা গেয়েন্দা প্রধানের কাছে জানতে পারে বংশীবাদক রাখাল তার নিজেরই ছেলে। গোয়েন্দা প্রধান এর আগেই রাজার ছেলের আংগুলগুলো কেটে নিয়েছে যাতে সে আর বাঁশী বাজাতে না পারে। যে গোয়েন্দা প্রধান রাজার ছেলেকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখে, সে আবার কেন তার আংগুল কেটে নেয় নাটকে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।
রাজার ছেলের একটু পরই ফাঁসি হয়ে যাবে। রাজা কয়েদখানার দিকে ছুটে যায় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য। যে ছেলেকে সে হত্যা করতে চেয়েছিলো, সেই ছেলে বেঁচে আছে জানার পর কেন সে তাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে চায় তারও কোনো কার্যকারণ বা ব্যাখ্যা নেই। এদিকে বিদ্রোহীরা প্রাসাদ দখল করে এবং তারা রাজার পরাজয় ঘোষণা করে। বিদ্রোহ শেষ হবার পর সর্দার বলে রাজ সিংহাসনে আর তাদের দরকার নেই।
রাজা এর মধ্যে ফিরে আসে এবং জানায়, তার মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী চন্দ্রবিন্দুও মৃত পড়ে আছে কয়েদখানায়। দুজনের মৃত্যুর কারণ জানা যায় না। রাজার মুদ্রাদোষ ছিলো ‘ওহ পাগল হয়ে যাব’ কথাটা বলা, সেই কথা বলে কোনো কারণ ছাড়া রাজাও হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কীভাবে এবং কেন এই মৃত্যু ঘটে বোঝা যায় না। রাজার মৃত্যুতে সবাই খুশি হয়।
রাজা অনুস্বারের পালা নাটকের পুরো কাঠামোটাই অসংলগ্ন। এই ধরনের নাটক সম্পর্কে দর্শন চৌধুরী লিখেছিলেন, নাটকের ক্ষেত্রে যারা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন সেসব নাট্যকারের কাছ থেকে বিষয়বস্তুর নতুন পরিকল্পনা ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আশা করাই যায় না। তারা যে-কোনো ঘটনাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধরেবেঁধে দেখাতে পারলেই খুশি। বিপ্লব, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, পরিচিত কিছু চরিত্র নিয়ে তামাসা-এগুলিকে মিশ্রিত করে তাঁরা একটা ককটেল তৈরি করেন। ১৬৯ মমতাজউদ্দীন আহমদের এ নাটকের সাথে দর্শন চৌধুরীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর নাটকে হাসি-তামাশা থাকলেও কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিলো না। অথচ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই হচ্ছে বাস্তববাদী শিল্পের প্রধান লক্ষণ।
সারভেনটিস ডনকুইকজোট-এ ব্যঙ্গ বা হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়েই তাঁর সময়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। ব্রেশটের নাটকেও হাস্য কৌতুকের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে ইতিহাসের নানা চেতনা। মমতাজউদ্দীন আহমদের নাটকে তা আমরা দেখি না। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, সামাজিক দায়িত্ববোধোর কোনে! চেতনাও তাঁর এ নাটকের ধরা পড়ে না। এই নাটকের অনেকগুলো চরিত্রই হচ্ছে ভাঁড়। যাদের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে, নানারকম তামাসা করে তিনি দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাতে চেয়েছেন। তাতে নাটকীয় সংহতি হয়েছে বিপন্ন। অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয় হয়েছে খণ্ডবিখণ্ড।
চিন্তায় মননে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাকে টুকরো টুকরো করে সাজাতে গেছেন নাট্যকার, কীভাবে সাজাবেন তা নিয়ে অস্থির হয়েছেন; সেজন্য নাটকটি কখনই সুগ্রন্থিত হয়ে ওঠেনি। রাজাকে মনে হয় পাগল বা উন্মাদ। রাজার বেশির ভাগ কাজের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে মমতাজউদ্দীন আহমদ এ নাটকে যে রাজনীতি প্রচার করতে চেয়েছেন তা হয়ে হয়ে দাঁড়ায় পাগলামি। নাট্য-নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জটা রাজনৈতিকভাবেই গ্রহণ করা উচিৎ। আজকাল পথনাটিকায় কাকে সাজায় আমি দেখি নি, আমাদের কালে অতুল্য ঘোষকে সাজাতো। একটা গান্ধী টুপি পরে, পেটের মধ্যে খানিকটা কাপড় দিয়ে, কালো রংয়ের চশমা পরে সে এক হাস্যকর ব্যাপার। তাতে না হয় থিয়েটার, না হয় রাজনীতি। ওটা কোনো থিয়েটারই নয়, নয় কোনো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।’মমতাজউদ্দীনের এই নাটকেও তাই ঘটে।
রাজতন্ত্র মানেই রাজার পর তার পুত্ররাই ক্ষমতা লাভ করবে। যেখানে পুত্র বা উত্তরাধিকারের সংখ্যা বেশি সেখানেই শুধু পিতা পুত্রদের দ্বারা নিহত হতে পারে। রাজা অনুস্বারের দ্বারা নিজ পুত্রকে হত্যা করতে চাওয়ার কারণটি তাই যুক্তিসঙ্গত নয়। রাজার একমাত্র পুত্র হিসাবে সঙ্গতভাবে সেই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী, রাজা তার পুত্রকেই ক্ষমতা দিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবে। অপর পক্ষে পুত্র জানে যে পিতার মৃত্যুর পর সেই ক্ষমতা লাভ করবে, সেক্ষেত্রে সেই বা কেন রাজাকে হত্যা করতে চাইবে। দ্বিতীয়ত রাজা নিজ পুত্রকে হত্যা করতে চাইলেও নিজের ভ্রাতুস্পুত্রকে ঠিকই বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই ভ্রাতুস্পুত্রই রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। পুত্র যদি ক্ষমতার লোভে রাজাকে হত্যা করতে পারে, সেক্ষেত্রে ভ্রাতুস্পুত্রও তো সেই কাজটি করতে পারে। সেক্ষেত্রে পুত্রকে হত্যা করতে পাঠিয়ে ভ্রাতুস্পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারটা নাটকে অসঙ্গতি তৈরি করে।
রাজ্য শাসন কোনো খামখেয়ালির ব্যাপার নয়। কোনো শাসকই সখ করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় না। তবে শাসকরা নিজ শ্রেণীস্বার্থে এমন সব কাজ করে, যা জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। রাজার দিক থেকে প্রজাদের কাঁদতে নিষেধ করার পেছনে তার স্বার্থটা কী? এই ঘটনায় রাজার বা তার শ্রেণীর লাভটা কোথায়? রাজার এই কাজগুলো কার্যকারণ দ্বারা সম্পর্কিত নয়। রাজাকে এখানে একজন খামখেয়ালি শাসকরূপে দেখনো হয়। রাজার ইচ্ছামতোই রাষ্ট্রে সকল কিছু ঘটছে। ইতিহাসে কোনো শাসকের পক্ষেই সবসময় নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মতো চলা সম্ভব নয়। একজন শাসকও নানারকম শৃঙ্খলা দ্বারা বাঁধা থাকে। চারদিকের ঘটনাবলী দ্বারাই রাজার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়।
ক্যালিগুলার মতো স্বৈরশাসকও তাই রোমের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে নিজের বোনকে বিয়ে করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। নাট্যকারের চোখ যখন ইতিহাসের ওপর থাকে না, তখন তিনি ব্যক্তির খামখেয়ালির ছবিই আঁকেন। অথচ চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত লালসার মধ্যে নয়, বরং ইতিহাসের যে স্রোত তাদেরকে সম্মুখে নিয়ে যায় তার মধ্যে চরিত্ররা তাদের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করবে।
রাজা অনুস্বারের পালা নাটকে রাজার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে এবং ক্ষমতা দখল করে তারা কেন বিদ্রোহ করে সেটা যেমন অস্পষ্ট, তেমনি রাজাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর তারা কী ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে ব্যাপারে কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তা নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্রোহের পর দেখানো হয়েছে তারা রাজ- সিংহাসন সরিয়ে ফেলতে চাইছে এবং বলা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হবে। পাশাপাশি বলা হচ্ছে রাষ্ট্রে নাগরিকের শাসন চালু হবে।
এই সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে দুজন মানুষ, একজন সর্দার আর একজন খোয়াবী। দুজন মানুষ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নিজেদের মতো করে তারা গণতন্ত্র চালু করবে। রাষ্ট্রপতির শাসন আর নাগরিকদের শাসন দুটো কথা একই সাথে বলা হচ্ছে যা স্ববিরোধী। রাষ্ট্রে নাগরিকদের শাসন চালু হবে, না স্বৈরশাসন চলবে সেটা কয়েকজন ব্যক্তির চিন্তার ওপর নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। পৃথিবীতে বহু বিদ্রোহ হয়েছে, বহুবার শাসক পাল্টেছে, তার অর্থ এই নয় যে সেখানে নাগরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে পৃথিবীর সমাজ এগিয়ে গেল তখনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এলো। তাই উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে না এসে, উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে রাজার শাসনকে বাদ দেয়া যায় না। ফরাসী বিপ্লবের পরেও বহুদিন পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজার শাসন টিকে ছিলো, কারণ তখনও পুঁজিবাদ সেখানে তার পরিপূর্ণ বিকাশে পৌঁছুতে পারেনি।
ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ইতিহাস চলে না, ইতিহাস আগায় সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে। মানুষই ইতিহাসকে পাল্টায় কিন্তু নিজের ইচ্ছামাফিক নয়, পূর্ব নির্ধারিত কিছু বাস্তবতার মধ্যে। ব্যক্তির ভূমিকা, জনগণের ভূমিকা সেখানে কখনই ইতিহাসের গতি- প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়াতে পারে না। প্রতিটি বিপ্লবেই দেখা গেছে, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন কোনো বিপ্লবেই ঘটেনি। ইতিহাসের বাস্তবতার মধ্যে বিপ্লবের বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমরা যা দেখতে পাই, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতা এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ এটাই, ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিলো অনেক এগিয়ে। সে কারণেই মার্কসবাদীরা বিপ্লবের নানা স্তরে বিশ্বাস করে। মার্কসবাদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্যবাদ।
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য নয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এই ধরনের দুটি ধাপ অতিক্রমের কথা বলে। মমতাজউদ্দীন আহমদ রাজা অনুস্বারের পালা নাটকে কোনো সামাজিক বিপ্লব ছাড়াই, উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করেই জনগণতন্ত্রের প্রশ্নে চূড়ান্ত রায় দিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আসে তা হলো, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পার্থক্য। বিদ্রোহী তারাই যারা সমাজের দু-একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে চায় না। সমাজের গুণগত পরিবর্তন ঘটে বিপ্লবের দ্বারা। মমতাজউদ্দীন আহমদ বিদ্রোহীদের দ্বারা সমাজের গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে চান। নাট্যকারের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণার অভাবই এক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়।
রাজনৈতিক নাট্য বলতে যা বোঝানো হয়, সত্যিকার অর্থে আশির দশকে সেই ধাঁচের কোনো নাটক রচিত হতে দেখি না। আশির দশকের শ্রেণীসংগ্রামের যে নাটক সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেমন একদিকে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি, তেমনি দেখতে পেয়েছি সেগুলো শ্রমিক বা সর্বহারাদের মাঝে অভিনীত হয়নি। সেখানে সমসাময়িক রাজনীতি বা অন্যান্য রাজনৈতিক বিরোধগুলোও স্থান পায়নি। শ্রেণীসংগ্রামের বাইরে যাঁরা নাটক নিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছেন, সেখানেও আমরা দেখতে পাই নাট্যকর্মীদের দ্বারা সে লড়াইটা রাস্তায়, সভা-সমিতিতে হলেও মঞ্চের নাটকে ঘটেনি। মঞ্চে স্বৈরাচারী শাসনকালকে ঘিরে সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো নাটকই মঞ্চস্থ হয়নি।
বিভিন্ন দলের যে নাটকগুলো সে সময়কালে মঞ্চস্থ হয়েছে তার মধ্যে সরাসরি সামরিক শাসনকে বা এরশাদ সরকারকে আক্রমণ করা হয়েছে এমন নাটক নেই বললেই চলে। শাসকদের বিরুদ্ধে যেমন সরাসরি কোনো শব্দ উচ্চারণ করা হয়নি, তেমনি সে সময়ের রাজনীতির কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আসেনি। বরং আশির দশকের মাঝামাঝি হঠাৎ নাটক সামরিক শাসন বা শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের দিকে চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ সময় হঠাৎ নাট্যচর্চার নতুন বিষয় হয়ে ওঠে। আশির দশকের শেষার্ধে বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পায়। ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ বলতে আসলে কী বোঝায় বা কী বোঝাবে সে ব্যাপারে কোনোরকম কিছু না বলেই আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সবগুলো দলই এই চেতনার জন্য লড়াই আরম্ভ করে। যদিও ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ কথাটি ব্যাপকভাবে চালু হয় অনেক পরে।
মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথাটি এসেছে, সেখানে যেটা খেয়াল করার ব্যাপার তা হলো, স্বাধীনতার দশ-পনের বছর পর্যন্ত নাট্যদল বা নাট্যকর্মীরা কখনও ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ এ ধরনের কোনো বক্তব্য নাটকে আনেননি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় তাঁরা কয়েক বছর স্বাধীনতা সম্পর্কে শুধু হতাশাই ব্যক্ত করেছেন, স্বাধীনতাকে মোটেই তখন তাঁরা কেউ গৌরবের বিষয় করে দেখেননি।
স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা তার মাহাত্ম্য নিয়ে মূলধারার নাট্যদলগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নাটক মঞ্চায়ন করেছে মাত্র একটি। সেটি পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। আর কোনো নাটকই নেই। স্বাধীনতার পরপর মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য নিয়ে যেসব নাটক লেখা হয়েছে সেগুলোর কোনোটিই মূলধারায় মঞ্চায়নের মুখ দেখতে পায়নি নাটকগুলির নিম্নমানের জন্য। পাশাপাশি এটাও একটা প্রধান প্রশ্ন, সে সময় মূলধারার যেসব নাট্যকাররা ছিলেন তাঁরাই বা কেন মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য বা গৌরব নিয়ে কোনো নাটক রচনা করলেন না? মুক্তিযুদ্ধের পরপর মুক্তিযুদ্ধের গৌরব নিয়ে নাটক মঞ্চায়িত হওয়াটাই তো ছিলো স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যই তখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গৌরব করা যেমন সম্ভব ছিলো না, তেমনি গৌরব করার মতো নাটক লেখাও সম্ভব হয়নি-যা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি।
বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত দেশের যে করুণ ও মর্মান্তিক চিত্র ফুটে ওঠে তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব চলে এসেছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পর মানুষ এমন কোনো সুসময় দেখেনি যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গৌরব করবে বা গৌরবের নাটক লিখবে। নাট্যকারদের পক্ষে স্বাধীনতাকে বড় করে দেখা সম্ভব ছিলো . না বলেই পঁচাত্তর সালের পূর্বে লেখা মমতাজউদ্দীন আহমদের কি চাহ শঙ্খচিল নাটকের সংলাপ ছিলো, ‘স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা মায়ের কোলে বাচ্চা নেই মানুষের চোখে নিদ নাই নদীর বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা।’স্বাধীনতা সম্পর্কে যদি ক্ষোভই প্রকাশিত হয় তাহলে মাহাত্ম্য প্রচার করার আর তো কোনো যুক্তি থাকে না।
স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছিলো সেজন্যই মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য নিয়ে নাটক লেখার কথা কেউ ভাবেননি। তেমনি মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য নিয়ে নাটক লেখার কোনো দাবিও কোনো দিক থেকে ছিলো না। অথচ আশির দশকের শেষার্ধে আমরা দেখতে পাই সে মুক্তিযুদ্ধকেই তাঁরা তাঁদের নাটকের প্রধান বিষয় এবং সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় করে তুললেন। ঘটনাটা যে আকস্মিকভাবে ঘটেছে তাও নয়, তার একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতাও আছে।
সে বাস্তবতা যতোটা আবেগ তাড়িত, যুক্তি বা মনন ততোটা নেই। মুক্তিযুদ্ধকে গৌরবের বিষয় করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো শ্রেণীসংগ্রামের যে বিষয়টা নাট্যকার বা নাট্যকর্মীদের চিন্তায় আশির দশকের শুরুতে দানা বেঁধেছিলো তা কীভাবে হারিয়ে যায়। দেখতে পাবো কীভাবে মুক্তিযুদ্ধই হয়ে ওঠে প্রধান বিষয়, শ্রেণীসংগ্রাম নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে এসেই আমরা দেখতে পাবো নাটকে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বটা আর প্রধান নয়, দ্বন্দ্বটা প্রধান হয়ে দেখা দিলো স্বাধীনতা বিরোধী ও স্বাধীনতার সমর্থক এই দু দলের মধ্যে। সেখানে নাট্যকাররা বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বাস্তবতা তুলে ধরলেন তা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে নয়; নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের ব্যক্তিগত ক্ষোভের জায়গা থেকে।
আশির দশকের মধ্য ভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাতামাতির কারণটি ছিলো ভিন্ন। ইতিবাচকভাবে মুক্তিযুদ্ধ কখনই গর্বের বিষয় হয়নি। আশির দশকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ব করার রেওয়াজ চালু হয়েছিলো ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট থেকে। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থানই ছিলো এর পেছনের মূল কারণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের একটি গোষ্ঠী, বিশেষ করে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং পাকবাহিনীকে সহায়তা করে। স্বভাবতই জনগণ এদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলো। শেখ মুজিব ক্ষমতা আরোহণ করার পর তিয়াত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে এদের ক্ষমা করেন।
দেশের সাধারণ জনগণ তখন দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও সার্বিক অরাজকতার কারণে স্বাধীনতার ব্যাপারে এতোই বীতশ্রদ্ধ ছিলো যে এই ক্ষমার বিরোধিতা বা তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোও নয়। নাট্যদলগুলো কিংবা তাদের কোনো নাটকেও এ নিয়ে কোনো বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা হয়নি। বরং ইত্তেফাক পত্রিকার এক সংবাদে দেখা যায় সাধারণ এই ক্ষমা সর্বশ্রেণীর জনগণ দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলো।
শেখ মুজিব যে শুধু স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমা করেছিলেন তাই নয়, তিনি স্বাধীনতা বিরোধী ঊর্ধ্বতন একদল আমলাকে দেশের সর্বোচ্চ পদগুলোতেও বসিয়েছিলেন। শেষ মুজিব যেমন এসব আমলাদের দাপট এড়াতে পারেননি তেমনি পারেননি জিয়াউর রহমানও।
জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে যেমন রাজনীতি করবার অধিকার দিয়েছিলেন তেমনি সরকারের বড় বড় পদ ও মন্ত্রীত্বও দিয়েছিলেন। সামরিক শাসক এরশাদও এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। মূলত স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত এরশাদ প্রথমে চাকরিতেই পুনর্বহাল হতে পারছিলেন না, শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব তাকে নিয়োগ দেন।
জেনারেল এরশাদের শাসনামলে স্বাধীনতা বিরোধীরা আরো শক্তি অর্জন করে এবং দেশের সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের নিধনে মাঠে নামে। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের একটি বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে যাঁরা স্পর্শকাতর, স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের উত্থান এবং তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিলেন না। শিক্ষিতদের অনেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের এই উত্থানকে কেন্দ্র করেই সৈয়দ শামসুল হক ‘স্মৃতিমেধ’ নামের এক উপন্যাস লেখেন তারই নাট্যরূপ যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। থিয়েটার নাটকটি ছিয়াশি সালে মঞ্চস্থ করে। সেখান থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটি আরও গুরুত্ব পায়। নাটকটি দর্শকদের চেতনাকে এমনভাবে আলোড়িত করে, যা অন্য দশটি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটকও হয়তো অতোটা সফলভাবে করতে পারতো না।
যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য স্বাধীনতা বিরেধী দালাল রাজাকারদের উত্থান। নাট্যকার সেটা নাটকে এনেছেন খুব চমৎকারভাবে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জিনাত, সে কলেজে অধ্যাপনা করে। তার স্বামী অধ্যাপক কলিমুল্লাহকে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। স্বামীর প্রতি রয়েছে জিনাতের গভীর ভালবাসা, নিজেও সে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক এবং মুক্তিযুদ্ধে স্বামীর সাহসী ভূমিকার জন্য গর্বিত। সেই জিনাত এগারো বছর বৈধব্য কাটাবার পর সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার, যা তার ভাসুর ও অন্যান্যদের বিচলিত করে। জিনাতের ভাসুর রহমতুল্লা জিনাতের স্বামীর নাম ভাঙ্গিয়ে বহু টাকা পয়সা বানিয়েছে, ভালো ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।
জিনাত বিয়ে করলে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসাবে তার মর্যাদা কমে যাবে সেইজন্য জিনাতের ভাসুর জিনাতকে এ কাজে বাধা দিতে চায়। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার দাঁড়ায় যখন জিনাত ঘোষণা দেয় সে বিয়ে করতে যাচ্ছে একজন স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারকে, যে তার মামাতো ভাই। সে ঘোষণায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে। জিনাতের বিয়ে করা নিয়ে তার মুক্তিযোদ্ধা দেবর সেলিমের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি একজন স্বাধীনতা বিরোধীকে বিয়ে করার ব্যাপারে।
সে এ বিয়ের ব্যাপারে জিনাতকে না করে। জিনাত তখন উত্তরে বলে, ‘রাজাকারকে তোরা ক্ষমা করতে পারিস আমি পারি না? রাজাকারকে তোরা মন্ত্রী করতে পারিস, আমি স্বামী করতে পারি না? একাত্তরের দালালকে স্বাধীনতার পদক দিতে পারিস, একাত্তরের দালালের গলায় আমি মালা দিতে পারি না? আমি করলেই অপরাধ? আর তোদের বেলা সেটা উদারতা?’এখানে স্মরণ রাখা দরকার, শেখ মুজিব দালার রাজাকারদের ক্ষমা করে বলেছিলেন তিনি উদারতা প্রদর্শন করেছেন।
যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকের মধ্য দিয়ে সেদিন ধরা পড়েছিলো সমাজ রাজনীতির অনেক চিত্র। স্বাধীনতার পর এটাই ছিলো সবচেয়ে সার্থক নাটকগুলোর অন্যতম যা দর্শকদের চেতনাকে চমৎকার ঘা দিতে পেরেছিলো। দর্শকদের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিলো জিনাতের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। নাটক যদি যুক্তিবাদী হয়, সময়কে সঠিকভাবে ধরতে পারে তাহলে সে নাটক যে কখনও কখনও কী বিরাট শক্তি ধারণ করে এ নাটকটিই তার প্রমাণ।
এ নাটক মঞ্চায়নের পরই শুরু হলো বিষয়টিকে নাট্য আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু করে তোলা। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ মঞ্চস্থ হবার পর রামেন্দু মজুমদার থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, ‘আজ আমাদের বেশি প্রয়োজন যে মূল্যবোধগুলোর জন্য আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম সেগুলো ফিরিয়ে আনা বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশে সেসব মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে।
আমরা ভুলে গেছি একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তার বাঙ্গালী দোসরদের অমানুষিক বর্বরতার কথা। সাধারণ ক্ষমার সুযোগে রাজাকার আলবদররা সময় মত নতুন রূপে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তারা পুনর্বাসিত।’১৭৮ তিনি আরো লিখছেন, ‘যে রাজাকার নেতাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ছবি সহ সংবাদ ছাপা হয়েছিলো ১৯৭২-এ আজ তারই ছবি সহ সংবাদ আমরা পাঠ করি একই সংবাদ পত্রে ভিন্ন প্রেক্ষিতে। কি পরিহাস! এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, আজ মোনেম খান বেঁচে থাকলে তিনিও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কিছু হতে পারতেন। ‘

যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটক মঞ্চস্থ হবার পূর্বে মমতাজউদ্দীন আহমদ তার ক্ষত বিক্ষত নাটকে রাজাকারদের উত্থানের প্রসঙ্গটি বা তাদের মন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটির ওপর সামান্য আলোকপাত করেছিলেন। শেখ আকরাম আলীর লাশ’ নাটকেও রাজাকারদের উত্থানকে দেখানো হয়েছিলো। তবে সে নাটকগুলো জনমনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটক মঞ্চায়নের পর থেকেই নাট্য রচনার একটি প্রধান দিক হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রচার। স্বাধীনতার বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কী ধরনের নৃশংস ভূমিকা পালন করেছিলো কীভাবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রেখেছে-এসব বিষয় নাটকে আশির দশকের শেষদিক থেকে গুরুত্ব পেতে থাকে।
যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকের বছরখানেক আগেই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে মঞ্চস্থ হয় শান্তনু বিশ্বাসের ইনফরমার নাটকটি। নাটকটিতে স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানের প্রসঙ্গটি ছিলো না, যুদ্ধকালীন সময় পাকবাহিনীর অত্যাচার ও দেশের মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষাই এ নাটকে স্থান পায়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকের পরের বছরই থিয়েটার মঞ্চস্থ করে স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থানকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ আল-মামুনের তোমরাই নাটকটি। পরের বছর ঢাকা পদাতিক মঞ্চস্থ করে এস এম সোলায়মানের এই দেশে এই বেশে। দুটো নাটকেই স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। মামুনুর রশীদ লিখলেন সমতট। সমতট নাটকে মুক্তিযুদ্ধ মূল প্রসঙ্গ না হলেও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে।
এই ধরনের নাটক যে আশির দশকে খুব বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে তা নয়। এই ধরনের নাটক রচনার উদ্বোধন হলো আশির দশকে কিন্তু রাজাকার দালালদের উত্থানকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ হয়ে ওঠে নব্বইয়ের দশকের নাটকের প্রধান সুর। নব্বইয়ের দশকে এ ধরনের নাটকের একটি মড়ক লেগেছিলো যেন।
সে আলোচনায় আমরা পরে যাবো। মূলত আশির দশকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, তোমরাই, এই দেশে এই বেশে, সমতট এসব নাটক মঞ্চস্থ হলেও সামগ্রিকভাবে ছিয়াশির পর নাটকের মঞ্চায়ন কমে গিয়েছেলো। রামেন্দু মজুমদার সাতাশির জুন মাসে থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখছেন, ‘বর্তমানে রাজধানীতে নাট্যচর্চার একটা মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করছেন। কথাটা বোধ হয় অমূলক নয়।… সম্ভবত; একটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো নতুন নাটকও নেই। যেখানে নাটকের মঞ্চায়নই কমে গিয়েছেলো সেখানে দালাল রাজাকারদের প্রশ্নে খুব বেশি নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা নয়। যে নাটকগুলো তখন মঞ্চস্থ হয়েছিলো সে নাটকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকের পর আশির দশকে রাজাকারদের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণার প্রকাশ ঘটে আবদুল্লাহ আল-মামুনের তোমরাই ও এস এম সোলায়মানের এই দেশে এই বেশে নাটকে।
নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের তোমরাই নাটকের প্রধান খলচরিত্র একজন স্বাধীনতা বিরোধী, এবং সারা নাটক জুড়ে তার বিরুদ্ধে নাট্যকারের ঘৃণার প্রকাশই এ নাটকের মূল উপজীব্য। ১৮২ তোমরাই নাটকের শুরুতেই দেখা যায় রঞ্জু একজন ছিনতাইকারী। সে যখন দলবল নিয়ে ছিনতাই চালাচ্ছিলো তার বোন ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত। রঞ্জুরা যার ব্রিফকেস ছিনতাই করার কথা ভাবে রঞ্জুর বোন সেই লোকটিকেই ছিনতাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। পরের দৃশ্যেই দর্শক জানতে পারে রঞ্জুর বাবা পাগল, রঞ্জুর মা আর বোন সায়রা সংসারটা চালাচ্ছে। রঞ্জুর আর একটি ছোট বোন আছে রাহেলা যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।
রঞ্জুদের পরিবারে আর আছে বিধবা আশ্রিতা খালা, সে সংসারের দেখভাল করে। আর রঞ্জুদের পরিবারে মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসে বেকার এক মামা, জীবিকার তাগিদে যে মানুষের হাত দেখা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে ব্যবসা চালাতে চেষ্টা করছে। তৃতীয় দৃশ্যে এসে দর্শক পরিচিত হয় রঞ্জুর বস্ হায়দার আলীর সাথে। হায়দার আলী স্বাধীনতা বিরোধী একজন রাজাকার। এই হায়দার আলীর বশংবদ রঞ্জু ও তার দলবল। রঞ্জু ও তার দলের সবাই জানে হায়দার আলী স্বাধীনতা বিরোধী একজন রাজাকার। সেটা জেনেই তারা তার হয়ে কাজ করছে। হায়দার আলীই রঞ্জুদের দিয়ে ছিনতাই সন্ত্রাস এসব করাচ্ছে।
নাট্যকার পুরো নাটকের মধ্য দিয়েই যেটা বোঝাতে চান তাহলো দেশের সন্ত্রাস ছিনতাই রাহাজানির জন্য হায়দার আলীর মতো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরাই দায়ী। স্বাধীনতা বিরোধীদের মদতেই দেশের তরুণ সমাজ অবক্ষয়ের পথে পা দিয়েছে। নাট্যকারের এ বক্তব্য অনৈতিহাসিক। নাট্যকার দেখাতে চান, স্বাধীনতার শত্রুরাই তরুণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরিয়ে রাখার জন্য পরিকল্পিতভাবে এসব করছে। নাট্যকারের এ বক্তব্য প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। বাংলাদেশে সন্ত্রাস গুপ্তহত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি এমনকি ধর্ষণ এসবের শুরু বাহাত্তর সাল থেকেই, যা আমরা পূর্বের বহু অধ্যায়ে দেখেছি।
স্বাধীনতা বিরোধী শত্রুদের বড় একটা অংশ তখন কারাগারে কিংবা পলাতক অবস্থায় ছিলো। রাজনীতিতে তখন স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান ঘটেনি। বাহাত্তর সাল থেকে পচাত্তর সাল পর্যন্ত কিংবা তারপরও ছিনতাই রাহাজানির সাথে সরকারি দলের লোকরা জড়িত ছিলো সে প্রমাণ তো খবরের কাগজগুলোতেই আছে। সরকারি দলও তা অনেক সময় স্বীকার করেছে।
সেজন্য দেশের সন্ত্রাস ছিনতাই বা তরুণ সমাজকে ক্ষতি করার দায়-দায়িত্ব শুধু মাত্র স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘাড়ে চাপানোর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি নাট্যকারের তীব্র ঘৃণা থেকেই তিনি এ ধরনের চিত্র এঁকেছেন। সেটার মধ্যে নাট্যকারের ক্ষোভ যতোটা প্রকাশ পেয়েছে ইতিহাস ততোটা নয়। নাটকটির মধ্যে নাট্যকারের এ ধরনের আরো বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ধীরে ধীরে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হবে।

চতুর্থ দৃশ্যে দর্শকরা পরিচিত হন ননীবাবুর সাথে। ননীবাবু একজন মুক্তিযোদ্ধা, সৎ রাজনীতিবিদ ও সাহসী মানুষ। শহরে সে একটি তৈরি পোষাকের দোকান চালায়। ননীবাবু রঞ্জুর বাবার বন্ধু, রঞ্জুদের পরিবারের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ। চতুর্থ দৃশ্যে এসেই আমরা জানতে পারি রঞ্জুর বাবা-মা প্রেম করে বিয়ে করে। রঞ্জুর বাবা সৎ রাজনীতি করতো ও ভালো একজন বক্তা ছিলো। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনে সে পাগল হয়ে যায়। রঞ্জুর মা কান্তা যে-কোনো পরামর্শের জন্য ননীবাবুর কাছেই আসে।
রঞ্জুর মা জামা কাপড় সেলাই করে ননীবাবুর দোকানেই দিয়ে যান। সেখান থেকে কান্তার কিছু অর্থ উপার্জন হয়। ননীবাবুর দোকানে এসে বসে থাকে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর। ননীবাবু তাকে খুবই স্নেহ করে। পঞ্চম দৃশ্যে দেখতে পাই রঞ্জুর বোন সায়রার সাথে রায়হানের প্রেম চলছে এবং তারা নিজেদের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছে।
ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যাবে কান্তার ওপর ননীবাবুর রয়েছে অসম্ভব প্রভাব। কান্তারও ননীবাবুর ওপর রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা’ও আস্থা। এই দৃশ্যে ননীবাবু আর কান্তার সংলাপের মধ্য দিয়েই দর্শক জানতে পারবে রঞ্জুর বাবা কবীর এককালে ছিলো ডাকসাইটে উকিল, সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল বলে তাকে সে পেশা ছেড়ে দিতে হলো। দুজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে কান্তা রঞ্জু সম্পর্কে সব জানে, তারপরেও রঞ্জুকে এ পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করে না। মা মনে করছে ছেলে একদিন নিজে থেকে বুঝবে এবং ফিরে আসবে, তাঁর যেন ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরানোর দায় নেই। যার অর্থ দাঁড়ায় মানুষকে বাইরে থেকে বোঝানোর শেখানোর কোনো ব্যাপার নেই। নিজেই সে বুঝে উঠবে সব।
ছেলে যে পথে গেছে তাতে করে তার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে, যে সন্ত্রাসের পথে সে আগাচ্ছে তাতে করে যে-কোনো সময় সে নিজেও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়তে পারে, তা সত্ত্বেও মা অপেক্ষা করছে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে তার ছেলে একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুপথে ফিরে আসবে।
নাট্যকার নিজেও মায়ের এই বিশ্বাসকেই সমর্থন দিচ্ছেন নাটকের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। যদি এটাই হয় নাট্যকারের বিশ্বাস যে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একদিন সন্ত্রাসীরা সুপথে ফিরে আসবে, তাহলে সন্ত্রাসীদের নিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের দুশ্চিন্তার কিছু থাকে না। ভিন্ন একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়, মা কি তাহলে অনৈতিক চরিত্রের?
না হলে তাঁর যে ছেলে অন্যের টাকা ছিনতাই করছে, অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, পথচারীদের হয়রানি করছে-ছেলে কবে সুপথে ফিরবে ভেবে সেসব মেনে নিচ্ছে কি করে? কোনো নীতিবান, দায়িত্ববান মানুষ একদিনের জন্যও ছেলের এহেন কাজকর্ম মেনে নিতে পারে কি? ব্যাপারটা এমন নয় যে ছেলের ওপর মায়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই দৃশ্যের শেষ দিকে এসে দেখতে পাই, রঞ্জু ঘরে ফিরলে বাবার সাথে রঞ্জুর তর্কাতর্কি বেধে যায়। রঞ্জু বাবাকে মোটেই পাত্তা দেয় না।
বাবা রঞ্জুকে শাসন করতে চাইলে রঞ্জুও সরাসরি বাবার শরীরে হাত তোলার কথা বলে মার সামনেই। অথচ মা যখন রঞ্জুর বাড়াবাড়ি দেখে রঞ্জুর গালে চড় লাগায় রঞ্জু তাতে মোটেই উত্তেজিত হয় না। রঞ্জু তখন মাকে বলে, ‘তোমার সঙ্গে আমার আলাদা হিসাব। আরও মারতে চাও মা? মারো। মায়ের অধিকার এখানে আমি বাধা দেব না।
আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৪ ]
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 17 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৪ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/আশির-দশক-শ্লোগানসর্বস্ব-রাজনৈতিক-নাট্যের-উন্মেষ-পর্ব-৪--1024x536.jpg)
মার কাছে যে-ছেলে এতোটাই বাধ্যগত, মা তাকে চাইলেই তো সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারে। মার যে রঞ্জু কতোটা বাধ্যগত তা আমরা পরের একটি দৃশ্যে আরো প্রমাণ পাবো। তা সত্ত্বেও মা রঞ্জুকে কেন ফেরাতে চায় না, নাট্যকারের রচনার এই দিকটা যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ষষ্ঠ দৃশ্যের পরের ঘটনাগুলো হচ্ছে নাটকের জন্য ক্রমাগত উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। হায়দার আলীর যে সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলো সেটিরই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ননীবাবু দোকান চালাচ্ছিলো। হায়দার আলী ক্ষমতার জোরে এবার ননীবাবুকে সেখানে থেকে উঠিয়ে দিতে চায়। সে এ কাজে রঞ্জুকে ব্যবহার করতে চাইলে রঞ্জু এবার ননী কাকার মুখোমুখি হয়। রঞ্জু ননী কাকাকে দোকান ছাড়ার জন্য ভয় দেখায়।
ননী কাকা তখন রঞ্জুকে তার বাবা-মার ইতিহাস শোনায়। কবীর আর কান্তা দেশের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য কতো ত্যাগ করেছে সে কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরিবার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে কথা বলে। ননীবাবুর এসব কথায় রঞ্জুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। যেন নিজের পরিবারের সাথে এতোগুলো বছর থেকেও নিজের পরিবারের এসব কিছুই সে জানতো না। যে কান্তা সর্বহারা মানুষের রাজনীতি করেছে, খুব ছেলেবেলা থেকেই তার নিজের ছেলেকে গড়ে তোলবার কথা। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলোও তার ছেলেকে বলার কথা। যুবক বয়সে ননীবাবুর কাছ থেকেই নিজের পরিবারের কথা জানতে হয় রঞ্জুকে। ননীবাবুর সামান্য দু-একটি সংলাপেই রঞ্জুর মধ্যে ছোট্ট একটা পরিবর্তন আসে।
রঞ্জু তবুও দোকান ছাড়ার জন্য ননীবাবুকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে ভোলে না। পরের দৃশ্যে মা রঞ্জুর কাছে কৈফিয়ত চায় কেন সে হায়দার আলীর কথায় ননীবাবুকে দোকান থেকে তুলতে গিয়েছিলো। রঞ্জু হায়দার আলীর পক্ষ নেয়। মা তখন হায়দার আলীর আসল চরিত্র ছেলের কাছে প্রকাশ করে, স্বাধীনতা যুদ্ধে তার বিরোধী ভূমিকার কথা বলে।
মা আরো জানায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হায়দার আলীই তার বাবাকে পাকবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলো। মা রঞ্জুকে আরো শোনায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন তারা পালিয়ে বেড়িয়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ননীবাবুই তখন শিশু রঞ্জুর জন্য দুধ জোগাড় করে এনেছে। মায়ের এইসব কথার পরেই আমরা দেখতে পাই মায়ের নির্দেশে রঞ্জু তার পিস্তল ও বোমা ভরা ব্যাগটা মাকে দিয়ে দেয় সুবোধ বালকের মতো, কোনোরকম উচ্চবাচ্য না করে।
নাট্যকার আমাদের বোঝাতে চান রঞ্জুদের পরিবারের জন্য ননীবাবুর অবদানের কথা রঞ্জু জানতো না এবং হায়দার আলীর দুশ্চরিত্রের কথাও জানতো না বলে সে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। প্রশ্ন দাঁড়ায়, রঞ্জু নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে বাস করেও ননীবাবুর অবদানের কথা জানবে না সেটা কী করে হয়?
দ্বিতীয় প্রশ্ন, মা হায়দার আলী সম্পর্কে যে তথ্যগুলো এই দৃশ্যে দিচ্ছে সে তথ্যগুলো ছেলেকে আগে দেয়নি কেন-যখন মা জানতে পারে রঞ্জু হায়দার আলীর দলে ভিড়েছে। তাহলে তো সমস্যার সমাধান আগেই হয়ে যায়। তৃতীয় যে প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বাধীনতা বিরোধীরা যে ভালো কাজ করেনি রঞ্জুর বয়সী সব ছেলেরাই সেটা জানে, রঞ্জুর সেটা না জানবার কোনো কারণ নেই।
হায়দার আলী যে খারাপ লোক সেটা বোঝার জন্য তো রঞ্জুর মার তথ্যের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় না। সে তো নিজেই জানে হায়দার আলী তাদের দিয়ে যে- সব কাজ করাচ্ছে সেগুলো ভালো কাজ নয়। মার বক্তব্যের পরেও, মাকে পিস্তল ও বোমার ব্যাগটা দিয়ে দেয়ার পরেও রঞ্জু হায়দার আলীর দল ছাড়ে না কিংবা হায়দার আলীর বিরুদ্ধে চলে যায় না। সে তার মার বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হায়দার আলীর কাছে আসে।
হায়দার আলীর কাছ থেকেই জানতে চায় তার মা যা বলেছে তা সত্যি কি না। হায়দার আলী এ ঘটনায় ক্ষেপে যায়। সে বলে, ‘বুঝেছি, মগজ ধোলাই হয়েছে। করেছে ঐ শালা ননী ব্যানার্জী।’ হায়দারের চেলা শমশের বলে, ‘ননী ব্যানার্জীর এক হাতে স্বাধীনতার ইতিহাস, আরেক হাতে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা।’
হায়দার আলী তখন ঘোষণা দেয়, ‘পুড়িয়ে দেব ঐ স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের পতাকা। নেক্সট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি দেখতে চাই ননী ব্যানার্জীর লাশ রাস্তায় পড়ে আছে।’ হায়দার আলীর নির্দেশে রঞ্জু জানায় সে তার প্রশ্নের জবাব না পেলে হায়দার আলীর আর কোনো কাজ করবে না। রঞ্জু বলে, ‘উত্তর। আগে প্রশ্নের উত্তর।’
হায়দার আলীর জবাবের জন্য এই অপেক্ষার অর্থ দাঁড়ায় রঞ্জু মায়ের চেয়ে হায়দার আলীকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, মায়ের কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। হায়দার আলীর দল সে তখনও ছাড়েনি, জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে। নাটকীয়তা ছাড়া এর মধ্যে আমরা আর কিছুই পাই না। হায়দার আলীর সাথে একাদশ বা এই দৃশ্যে রঞ্জুর যেসব কথা হয় তাতেই বোঝা যায়, হায়দার আলী স্বাধীনতার কতো বড় শত্রু।
যে বলছে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুড়িয়ে দেবো, তার কাছে রঞ্জুর আর নতুন করে জানবার কী বাকি থাকে? হয় সে তখন বিশ্বাসের জন্য, আদর্শের জন্য হায়দার আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিংবা সব জেনেশুনে নিজের স্বার্থে হায়দার আলীর সাথে রয়ে যাবে। এতোসব কিছুর পরেও আর কি উত্তর শোনার জন্য সে অপেক্ষা করতে পারে যেখানে ননী ব্যানার্জীকেও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হায়দার আলী মেরে ফেলতে চায়।
নাটকের এরপরের ঘটনা হলো, রঞ্জুদের সাথে না পেয়ে হায়দার আলী নিজেই পুরানো একজন আলবদরকে নিয়ে ননী ব্যানার্জীকে খুন করতে যায়। তাড়াহুড়োয় খুন হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা আকবর। এই ভুল হয়ে যাওয়ায় হায়দার আলী ভয় পেয়ে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিতে চায়। যে ননী ব্যানার্জীর মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ্যে হত্যা করতে ভয় পায় না, সে ক্ষমতাহীন মুক্তিযোদ্ধা আকবরকে খুন করে এতো ভয় পেয়ে যাবে সেটা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীন মনে হয়।
হায়দার আলী যখন কিছুদিন গা ঢাকা দেয়ার জন্য পালাচ্ছিলো সে সময় নাটকীয় ভাবে রঞ্জু তার পথ রোধ করে। সে তাকে প্রশ্ন করে, ‘আমার বাবাকে পাকিস্তানী আর্মীর হাতে ধরিয়ে দাও। আমার মাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়াও। ননী কাকার দোকানে আগুন লাগাও।
পঙ্গু এক মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে গুলি চালাও। কেন? কি অপরাধ করেছে এরা?’ যে রঞ্জু নীতিহীনভাবে ছিনতাই করে, বোমাবাজি করে, মানুষ হত্যা করে, সে রঞ্জুই হঠাৎ এসব নীতির প্রশ্ন তোলে। হায়দার আলী জবাবে বলে, ‘আমার পোষা কুকুরের কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেই না।’ রঞ্জু ঝট করে পিস্তল বার করে। আঁতকে ওঠে হায়দার আলী। রঞ্জু বলে, ‘পোষা কুকুর আর পোষা মানুষ এক নয়।
এ কথাটাই আজ বুঝিয়ে দিতে চাই।’ রঞ্জু ট্রিগার টানতে যাবে, এমন সময় কান্তা ওর ঘাড়ে হাত রাখে। রঞ্জু পেছনে ফিরে তাকায়। মাকে দেখতে পেয়ে সে বলে, ‘মা, হায়দার আলীর সঙ্গে তোমার হিসেবটা কি আগে চুকিয়ে নেবে?’ কান্তা দৃপ্তপায়ে হায়দার আলীর দিকে এগিয়ে যায়।
হায়দার আলীকে ভর্ৎসনা করতে করতে সে এক সময় হায়দার আলীর কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, ‘হায়দার আলী ভেবেছো সব ভুলে গেছি? হিসেব চুকিয়ে দাও। আমার সব হিসেব আজ তোমাকে চোকাতেই হবে। পাই পাই হিসেব।’ হায়দার আলী আকস্মিকভাবে কান্তার গালে চড় লাগায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোঁড়ে রঞ্জ-পরপর কয়েকটা। লুটিয়ে পরে হায়দার আলী। কান্তা রঞ্জুকে বলে, কি করলি? কি করলি তুই রঞ্জু? এতো আমি চাইনি।
মা যে কী চেয়েছিলো সেটা ধারণা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মা একটু আগের সংলাপেই হায়দার আলীকে বলেছিলো, হিসেব মিটিয়ে দিতে। হায়দার আলীর মৃত্যু ছাড়া সেটা আর কী হতে পারতো? রঞ্জুর পরের সংলাপ, ‘আমি তো বলেছি মা, তোমার সঙ্গে আমার আলাদা হিসাব। হায়দার আলী তোমার গায় হাত তুলেছে। ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।
![আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ 18 আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৪ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-৫.jpg)
রঞ্জুর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, রঞ্জু হায়দার আলীকে হত্যা করেছে কারণ হায়দার আলী রঞ্জুর মার গায়ে হাত তুলেছিলো, অন্য কোনো কারণে নয়। হায়দার আলীর পূর্বকৃত অপরাধের জন্য রঞ্জু তাকে হত্যা করেনি। রঞ্জুর মাতৃভক্তি এতোই প্রবল যে, মার গায়ে হাত তোলার জন্যই সে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। নাট্যকারের রচনার মধ্য দিয়ে এই সত্যটাই বের হয়ে এসেছে। অথচ সামান্য পূর্বেই নাট্যকার একবার দেখিয়েছেন, হায়দার আলী রঞ্জুকে পোষা কুকুর বলার কারণেও সে পিস্তলের ট্রিগার টিপে তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো। মা এসে পড়ায় সে প্রথমে মাকে মার হিসেব চুকিয়ে নিতে বলে। রঞ্জুর শেষ সংলাপে তাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, হত্যার আসল উদ্দেশ্য কোনটি।
রঞ্জু হায়দার আলীকে হত্যা করে তার একাত্তরের ভূমিকার জন্যও নয়, বর্তমানের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্যও নয়। হত্যার পেছনের দুটো কারণের একটি রঞ্জুকে পোষা কুকুর বলা, অপরটি তার মায়ের গায়ে হাত তোলা। হত্যার ব্যাপারটির মধ্যে সেখানে তাই রাষ্ট্রীয় রাজনীতির চেয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধটাই প্রাধান্য পায়। কোনো আদর্শগত বিরোধের কারণে হায়দার আলীর মৃত্যু ঘটে না। মৃত্যু ঘটে আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। দুজন মানুষের ব্যক্তিগত মান অপমান বোধ এর সাথে জড়িত।
নাট্যকার যে বক্তব্য দিয়ে নাটক শুরু করেন, যে বিষয়বস্তুকে সামনে নিয়ে আসেন ‘স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান’, তার পতনটা কিন্তু রাজনৈতিক নয়। রাজনৈতিক নয় দুটো কারণে, প্রথমত কোনো রাজনৈতিক দল বা আদর্শের মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। দ্বিতীয়ত হত্যা করা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে একজন ব্যক্তিকে, যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলো।
রাজনৈতিক আন্দোলন বা আদর্শটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সেখানে একটি পক্ষ অপর একটি পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। লড়াইটা হয় সেখানে মূলত আর্দশত কারণে, সেখানে দু’পক্ষেরই পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ কাজ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। কোনো একটি আদর্শের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সেখানে আগে নিজেদের সংগঠিত করতে হয়। নিজেদের শক্তিটাকে বাড়াতে হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য থাকে চূড়ান্ত বিজয়। একজন ব্যক্তি যখন সংগঠিত রূপ ছাড়াই নিজের ক্ষোভ থেকে অন্যজনকে হত্যা করে সেখানে রাজনীতি থাকে না, সেটা হয় নৈরাজ্যেরই নামান্তর। সংগঠিত রূপ ছাড়া রাজনীতি হয় না। তোমরাই নাটকে রঞ্জুর মতো একজন সন্ত্রাসী, যার মধ্যে কোনো নীতিবোধ নেই, কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই, সে যখন কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটায় সেটি একটি হত্যাই মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।
সোলায়মানের এই দেশে এই বেশে নাটকটিতেও স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে, খুবই স্থূলভাবে এগিয়েছে নাটকের পুরো কাঠামোটি। নাটকটিতে দেখা যায়, নানা আর নাতি এসেছে বাঙালী চেতনার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব- এর অনুষ্ঠানে। আর সেখানেই ঘটে নানারকম ঘটনা। রাষ্ট্রীয়ভাবে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রয়াত সব ব্যাক্তিদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জহির রায়হান সহ প্রয়াত আরো কিছু চরিত্ররাও সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসে। রাষ্ট্রের ধর্মমন্ত্রী হুরমত আলী সেখানে প্রধান খলচরিত্র। সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রতি দুই মিনিটে একজন করে মানুষ খুন করেছে।
হুরমত আলী নিজেই নাটকে একটি রামদা দেখিয়ে বলে, ৭১ সালে গণ্ডগোলের টাইমে নাফরমান, নালায়েক কমিনগো পোস্টমর্টেম তো এই রামদাও দিয়াই করছি। হাজারে হাজারে। কাতারে কাতার। হালারা নাকি আবার বুদ্ধিজীবী।’ সে এখনো প্রয়োজনে শত্রুর হাত পায়ের রগ কেটে দিচ্ছে। নাটকের শুরুতেই বলা হয়, স্বাধীনতার দশ বছরের মাথায় স্বাধীনতার পাত্তা নাই, রাজাকারে হলো দেশ বোঝাই, মুক্তিযুদ্ধের নামগন্ধ নিশানা নাই।
রাজাকারে দেশ বোঝাই হলো কী করে সেটা নাটকে বলা হয় না। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে থাকে তাহলে রাজাকারদের সংখ্যা হওয়ার কথা খুব নগণ্য। রাজাকারে দেশ ভরে গেলে দেশে শ্রমিক-কৃষক বা শোষিতদেরকেও রাজাকার ধরে নিতে হয়। নাট্যকার পূর্বের তোমরাই নাটকটির মতোই দেখাচ্ছেন, দেশের সকিছুর জন্য দায়ী এই রাজাকাররা, তারাই দেশ চালাচ্ছে। দেশটাকে তারাই উচ্ছন্নে নিয়ে গেছে। ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে। নাট্যকার কখনও এটা দেখাচ্ছেন না যে, দেশের সবকিছুই রাজাকাররা নিয়ন্ত্রণ করছে না। রাজাকারদের বিরুদ্ধে নাট্যকারের বক্তব্য অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। সে কারণেই নাটকের চরিত্রগুলো সব একপেশে।
নাটকে বহু প্রসঙ্গ আসে-শেখ মুজিব হত্যা, সিরাজ সিকদার হত্যা, কর্নেল তাহেরের ফাঁসি, জিয়া হত্যা। সকল বিষয়গুলো নাটকের হৈ-হুল্লোড়ে হারিয়ে যায়। নাটকে দেশের সাধারণ শ্রমিক কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। নাট্যকার মনে করছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে বলেই রাজাকারদের এতো বাড় বেড়েছে। নাট্যকারের ভাষায়, ‘ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়া যেই দেশ স্বাধীন কইরাছে, সেই দেশে স্বাধীনতার শত্রুরা থাকে কেমন কইরা? এই শালারা সারা বছর নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবে কিন্তু যখন হাত আর পায়ের রগ কাটা পড়বে তখন নাকের পানি আর চোখের পানি ফেইলে ফ্যাঁত-ফ্যাত করে কাইন্দে কইবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত কর।’
নাট্যকার নির্দিষ্টভাবে কাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলছেন সেটা সুনির্দিষ্ট করেন না। নাট্যকার যখন নাটকে এ অভিযোগ তোলেন তখন এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম চলছে। দেশের ছাত্র-সমাজ, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্তরা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। শ্রমিকরাও নানান দাবি- দাওয়ার প্রশ্নে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। সেই সংগ্রামটাকেই যেন তিনি এ নাটকে অস্বীকার করছেন। তিনি সংগ্রাম বলতে মনে করছেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা ঘৃণার প্রকাশ। মৃত ব্যক্তিদের নাটকের চরিত্র হিসাবে নিয়ে এসে নাট্যকার সোলায়মান যে প্রহসনটি তৈরি করতে চান, শেষ পর্যন্ত সেটা রুচিহীন কিছু চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে পরিণত হয়।
নাটক রচনায় নাট্যকারের নানা বিভ্রান্তি এবং অপ্রকৃতিস্থ চিন্তার পরিচয় মেলে। নাট্যকারের রাজনৈতিক বোধের অভাব যেমন ধরা পড়ে, তেমনি নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম দৃষ্টিভঙ্গির দেখাও মেলে না। ব্রেস্ট এইসব নাট্যকারদের স্মরণ করেই লিখেছিলেন, যা কিছু একটা লিখে মঞ্চস্থ করলেই তা নাটক হয় না; নাটক রচনার জন্য নান্দনিক বোধটাও জরুরি। মৃত ব্যক্তিদের চরিত্র হিসাবে নাটক রচনার আরো উদাহরণ রয়েছে ইতিহাসে। প্রথম উদাহরণ প্রাচীন গ্রীসের ভেক নাটকটি। কমেডি রচনার জন্য আরিস্তোফানিস ভেক নাটকে প্রাচীন গ্রীসের কিছু মৃত নাট্যকারদের চরিত্র হিসাবে এনেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, এই নাটকটিতে কীভাবে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে এবং রয়েছে নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনা। সে নাটকটি এখনও পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী হিসাবে স্বীকৃত।
ইতিপূর্বে দেখা গেছে তোমরাই নাটকে কোনোরকম যুক্তিকে গ্রাহ্য না করে আবদুল্লাহ আল-মামুন খামখেয়ালিপূর্ণভাবে নাটকের গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এস এম সোলায়মানের আলোচ্য নাটকটিও তাই। দুজনেই স্বাধীনতা বিরোধীদের খলনায়ক বানাতে গিয়ে এমন সব ঘটনার আমদানি করেছেন যার বাস্তব ভিত্তি নেই।
কিন্তু একই প্রসঙ্গ নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের যুদ্ধ এবং যুদ্ধ নাটকে কোনো চড়া সুরের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি; অথচ দর্শকদের ওপর নাটকটির প্রভাব ছিলো সর্বাধিক। এ নাটকে ক্রোধ প্রকাশের চেয়ে দর্শকদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরবর্তী নাটক দুটিতে দেখা যায়, এক ধরনের উন্মত্ততা নিয়ে নাট্যকারদ্বয় নাটক রচনায় হাত দেন এবং তা সত্ত্বেও দর্শককে কোনো ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন না। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি ক্রোধে অন্ধ সোলায়মান তাঁর নাটকটিকে অশ্লীল করে তোলেন, মামুন আবার তোমরাই নাটকে তা করেন না। এই পঞ্চম অধ্যায়ে আরো দুটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা হবে। তার একটি মামুনুর রশীদের সমতট এবং অন্যটি মমতাজ উদ্দীন আহমদের সাত ঘাটের কানাকড়ি।
মামুনুর রশীদের সমতট নাটকের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের সময়টাকে নাটকের সূচনা হিসাবে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের অনুভূতি, পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতা, নানা ধরনের অত্যাচার, দেশের মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি সেখানে ফুটে উঠেছে-যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সামান্য ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র। স্বাধীনতার পরের প্রশ্নে দালাল রাজাকারদের উত্থান নিয়ে এ নাটকে কোনো বক্তব্য রাখা হয়নি।
মামুনুর রশীদের সমতট নাটকটি উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভের পর মুজিব, জিয়া ও এরশাদের শাসনকাল পর্যন্ত এর সময়কাল ব্যাপ্ত। নাটকটি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি পরিবারের গল্প। সেই গল্পের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্তের রাজনীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পলায়নপর মনোবৃত্তি ধরা পড়েছে, যদিও তা কোনো সমাজ বাস্তবতার ওপর নির্মিত নয়। পরিবারটির প্রধান একজন রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক। স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে ও এক পুত্রবধু নিয়ে তার সংসার।
উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে চিকিৎসকের বড় ছেলে আশিক, যে সদ্য বিবাহিত, স্ত্রীকে পিতামাতার কাছে রেখে খুলনায় চাকরিস্থলে চলে যায়। মেজ ছেলে শাহেদ ক্রিকেট খেলে, ছোট ছেলে আরজু বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান রাজনীতির সাথে যুক্ত। মেয়েটি প্রতিবন্ধী।
চিকিৎসকের ভায়রা সামরিক কর্মকর্তা এবং পাকিস্তান শাসক চক্রের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। আশিক চাকরিতে চলে যাবার পর আরম্ভ হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় অথচ আশিক আর ফিরে আসে না। স্বাধীনতার পর নতুন দেশে নিপীড়ন বা সংকটের অবসান হয়নি। অস্ত্র রাখার অভিযোগে শাহেদকে অকারণে গ্রেফতার করা হয়। চিকিৎসকের ভায়রার হস্তক্ষেপে সে মুক্তিও পায়। নাটক এগিয়ে যায়। আরজু সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। শাহেদ জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলার সুযোগ পায়। শাহেদের প্রেমিকা তার চাচাতো বোনের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। আশিকের স্ত্রীর একটি ছেলেও জন্ম নেয়। আশিক ফিরে না আসার কারণে পারিবারিক চাপে শাহেদের সাথে আশিকের স্ত্রীর বিয়ে হয়।
আশিকের ছেলে বড় হয়ে শাহেদকেই তার পিতা হিসাবে জানে। হঠাৎ আশিক একদিন ফিরে আসে এতদিন যাকে মৃত মনে করা হয়েছিলো। এতে করে পরিবারের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আশিক জানায়, সে বিপ্লবী দলের হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। যুদ্ধের পর সে ঘরে ফিরতে পারতো, ফেরেনি তার কারণ সে ভেবেছিলো দলের কিছু কাজ সেরে তবে ঘরে ফিরবে। ঘরে একবার ফিরলে আর যদি বের হতে না পারে সেইকথা ভেবেই সে যুদ্ধের পর ঘরে ফেরে না। কোনো খবরও পাঠায় না বাড়িতে। তারপর কেন তাকে কারা নাফ নদীতে আহত অবস্থায় ফেলে দেয় তার কোনো কারণ নাটকে জানা যায় না। তারপর বার্মার আকিয়াব জেলে কেন সে পনের বছর জেল খাটে তারও কারণ নাটকে উল্লিখিত নয়।
জেলে থাকা অবস্থায় কেন সে বাড়িতে চিঠিপত্র লেখেনি বা খবর পাঠায়নি তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই নাটকে। বাড়িতে ফিরে যখন সে দেখে তার স্ত্রী শাহেদের ঘর করছে তখন সেটা সে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না। দীর্ঘদিন সে নিখোঁজ থাকার পরও তার স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করাটাকে সে মনে করে অন্যায়। সে তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। আশিক যখন ফিরে আসে, সে সময় রাজনৈতিক কারণে আরজু জেলে।

আশিক ফিরে আসার পরই আরজু ছাড়া পায়। শাহেদ আশিককে বলে যুক্তি দ্বারা চলতে, শাহেদের সাথে তার স্ত্রীর বিয়েটা মেনে নিতে। আশিক বলে শুধু যুক্তি দিয়ে জীবন চলে না। শাহেদ আশিককে তখন স্মরণ করিয়ে দেয় ‘তুমি যে রাজনীতি করতে সেখানে আবেগের কোন স্থান নেই।’ আশিক বলে, প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব যুক্তি আছে। সেই যুক্তি বিজ্ঞান নয়, অংক নয়। নাটকের এই বিশ্বাসটা কী নাট্যকারের নিজের, না শুধু নাটকের চরিত্র আশিকের বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।
দেশের সরকার এদিকে চিকিৎসকের মফস্বলে কেনা জমিটা দখল নেয়ার জন্য চিঠি দেয়, সামরিক কর্মকর্তার জন্য সেখানে বাংলো করা হবে। আরজু বলে তাদের দল এর বিরোধিতা করবে। সারা দেশ এভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে এটা হতে দেয়া যায় না।মধ্যবিত্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য এভাবেই নাটকে লড়াই করার প্রশ্ন চলে আসে। আরজু আশিককে বলে, এসব সমস্যার সমাধানের জন্য আর একটা যুদ্ধ দরকার।
আশিক জানায়, সে এ যুদ্ধে অংশ নেবে না। কারণ আজ আর তার কোনো স্বপ্ন নেই-সে একা। এতো একা মানুয় লড়তে পারে না। এর মধ্যে সামরিক লোকরা আসে তাদের বাড়িটা দখল করতে। সে সময় প্রতিবন্ধী শিলু এয়ারগান এনে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। অদৃশ্য থেকে তখন একটি গুলি এসে শিলুর গায়ে লাগলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মা তখন পরম স্নেহে গান গাইতে থাকে, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো-নাটক এভাবেই শেষ হয় একটি গানের মধ্য দিয়ে।
নাট্যকার এ নাটকে কী দেখাচ্ছেন? স্বাধীনতা যুদ্ধের পরও সমস্যার সমাধান হয়নি, সামরিক স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ওপর চেপে বসেছে। এ বক্তব্যে সঠিকতা আছে। এ ঘটনায় মূল সংকট কার, কোন্ শ্রেণীর-এই মূল্যায়নে নাট্যকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের, সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার চাইতে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের সম্পত্তি দখল হয়ে যাওয়া নিয়ে নাট্যকারের আর্তনাদ, হাহাকার। মধ্যবিত্তের ওপর শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে যে আঘাতে আসে, নাটকে বারবার তারই বিরুদ্ধে সমালোচনা ফুটে উঠেছে। এই আঘাতের বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়াতে হবে, কাদের নেতৃত্বে সে প্রশ্নের জবাব নেই।
মধ্যবিত্তের সংকট নিয়ে হাহাকার শেষ পর্যন্ত গতিহীনতা, স্থবিরতা আর হতাশায় পরিণত হয়।মামুনুর রশীদ এ নাটকে যে রাজনীতি টেনেছেন সে রাজনীতির কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই। রাজনীতিকে তিনি মাঝে মধ্যে ছুঁয়ে গেছেন। শ্রেণীসংগ্রামের প্রচারক বলে যিনি নিজের পরিচয় দেন, সেই মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকটি শেষ করেছেন হতাশার মধ্য দিয়ে। যখন তাঁর নাটকের বিপ্লবী চরিত্রটি বলে মানুষের একটা নিজস্ব যুক্তি আছে কিংবা নিজেকে সে একা মনে করছে, তখন সে আর কোনো বিপ্লবীর চরিত্র থাকে না।
বিপ্লবীরা নিজস্ব একটা যুক্তিকে গ্রাহ্য করে না। শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শে গড়ে ওঠে তার যুক্তি। সেজন্যই সে বিপ্লবী, কারণ সবকিছুর ওপর সে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে চায়। সমতট নাটকে আশিক সংসার হারিয়ে বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় একজন বিপ্লবীও কখনও কখনও ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনায় মুহ্যমান হতে পারে, ব্যক্তিগত সেই দুঃখকে ধারণ করেও যখন সে সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে তখনি তো সে ইতিহাসের নায়কদের একজন হয়ে ওঠে। আর একজন বিপ্লবী শত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও নিজেকে একা মনে করে না, কারণ তার চারদিকে আছে লক্ষলক্ষ শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতা।
নাট্যকার এই নাটকে মধ্যবিত্তশ্রেণী চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। মধ্যবিত্ত বলয়ে নিমজ্জিত নাট্যকার চরিত্রসৃষ্টিতে অন্য কোনো আশিকের কথা ভাবতেও পারছেন না। নাটকে নাট্যকারের আদর্শ হচ্ছে শাহেদ, যে শাহেদের আদর্শ ব্যবসা করা, চিংড়ি চাষের ইন্ডাস্ট্রি করা, পিতা-মাতা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখের আত্মসর্বস্ব ঘর বাঁধা।
নাটকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি নাট্যকারের হাহাকার, অথচ মার্কসবাদীরা এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করে থাকে। নাট্যকার নিজেকে শ্রেণীসংগ্রামের লোক বলেও শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তদের ব্যক্তিগত যুদ্ধটাকে বড় করে দেখেন। সেইজন্য শ্রেণীযুদ্ধের চেয়ে চিকিৎসকের ঘরের যুদ্ধটা তাঁর বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে কারণেই আরজু যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা বলে চিকিৎক তখন বলে, ‘যুদ্ধের কথা বলছিস না?
এই তো যুদ্ধ লেগেই আছে-ঘরের ভেতরে যুদ্ধ, তোর সাথে আমার, ওর সাথে তোর, এত রাজনীতি করিস-যুদ্ধ দেখতে পাস না? আমার সমতট বিশাল কুরুক্ষেত্রে পরিণত। নাট্যকার সমতট নাটকের গল্প যেভাবে সাজিয়েছেন-যুদ্ধের পর আশিকের ফিরে না আসা, তার স্ত্রীর শাহেদের সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়া, পরবর্তীতে আশিকের ফিরে আসা এবং হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া-এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে নাট্যকার কোন্ সমাজ সত্য তুলে ধরতে চান বুঝে ওঠা কঠিন। এই যে আশিকের বাড়ি না ফেরা এর সাথে তো শাসকশ্রেণীর কোনো দ্বন্দ্ব নেই; এটা সম্পূর্ণই আশিকের কর্মফল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে বহু মানুষ পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখেছে, সরাসরি সম্ভব না হলে চিঠি লিখেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে আশিক বাড়িতে একটি চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন তার কোনো উত্তর নেই; নাট্যকার যেন এক অর্থহীন গল্প ফেঁদে বসেছেন।
মূলত আশির দশকে শ্রেণীসংগ্রামের নানা শ্লোগান সত্ত্বেও মার্কসীয় রাজনৈতিক নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের যেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারা তৈরি হয়নি, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তেমনি শিল্পমানসম্মত যুক্তিবাদী মানবিক নাটকের সন্ধানও মেলে না। কিছু কিছু নাট্যকারের নাটক তো শিল্পমানের বাইরে গিয়ে কদাকার ও কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মমতাজউদ্দীন আহমদ সেসব নাট্যকারদের একজন। আশির দশকের শেষে উননব্বই সালে থিয়েটার প্রযোজিত মমতাজউদ্দীন আহমদের সাত ঘাটের কানাকড়ি নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক, কারণ এই নাটকের প্রদর্শনী সংখ্যা সর্বাধিক।
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত কিছু ব্যক্তি এ নাটক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও নাট্যাঙ্গনের বহু লোক নাটকটিকে উচ্চ মূল্য দেননি। যেমন আতাউর রহমান লিখছেন, ‘নিছক দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটকটির ভাল দিক খুঁজতে লাগলাম কিন্তু খুঁজে প্রায় কিছুই পেলাম না। নাটকের কাহিনী বক্তব্যের উপস্থাপনা, অভিনয় কোনোটির সাথেই মন সায় দিল না, তবুও নিবিষ্ট হয়ে মনের গভীরে সন্ধান চালালাম, প্রাপ্তি অকিঞ্চিতকরতায় নিরাশ হলাম, এতে আরও বিপদগ্রস্ত বোধ করলাম, কারণ ‘প্রযোজনাটি ভীষণ জনপ্রিয়। এই সূত্র ধরে নাটকটির জনপ্রিয়তার প্রশ্নে মনে ধন্ধও লাগল।’
* নাটকটির প্রশংসাও করা হয়েছিলো; বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিই নাটকটিকে পছন্দ করেছিলেন। নাটকটি সম্পর্কে তাই আর একজন সমালোচক লিখছেন, ‘নাটকটি দেখার পর আমি বেশ কয়েকজন নাট্যরসিক কবি এবং সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করেছি এবং এখানেও আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এরাও নাটকটির স্থূল চমৎকারিত্ব দ্বারা বিমুগ্ধ।’১৯৪ নাটকটির পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকম মন্তব্য করা হয়েছে। নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় লিখছেন, ‘কিছু দর্শক আমি পেয়েছি যাঁরা এ নাটক দেখে অ-খুশী হয়েছেন। তাদের মতে সাতঘাটের কানাকড়ি শিল্পসম্মত সাহিত্য হয়নি।…না, আমি শিল্পকর্মের সূক্ষ্ম ও সচেতন অভিলাষ নিয়ে সাতঘাটের কানাকড়ি রচনা বা নির্দেশনা করিনি। সাতঘাটের কানাকড়ি নাটকটি রচনার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আমার কালের দগ্ধীভূত উত্তপ্ত কথাগুলো বলা এবং কালের মানুষের ক্রোধ ও দহনকে প্রকাশ করা।
মমতাজউদ্দীন আহমদ নিজেই স্বীকার করছেন তিনি ক্রোধ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে বহু সত্য তিনি দেখতে পাননি এবং বহু সত্যকে বিকৃত করেছেন। মমতাজউদ্দীনের এ নাটকটি ভাববাদী চিন্তার নাটক। নাটকটির মূল গল্প মা আর তার সাত ছেলেকে নিয়ে। ছেলেদের পিতা বেঁচে নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পিতা মারা যায়, মা ধর্ষিতা হয়। তার শেষ সন্তানটি সেই ধর্ষণের ফল। মার সাতটি ছেলে, খুবই ভালো তারা।
স্বাধীন দেশে তাদের চলার কথা বুক ফুলিয়ে, তারা তা পারে না। সাত ছেলের একজন শাসকদের ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে মারা গেছে। দুজন খুনের আসামী হয়েছে একজন রাজাকারকে খুন করে। অন্য ছেলেরা হতাশ। মায়ের কাছে প্রস্তাব আসে, খুনী ছেলেদের ক্ষমা করা হবে যদি মা সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবেদন করে। মা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।
এরশাদ সরকারের সময়কার স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ এ নাটকের প্রধান দিক। নাটকের যেসব চরিত্রদের খুব খারাপভাবে দেখানো হয়েছে তারা সকলেই পাকিস্তানপন্থী। এ নাটক সামরিক সরকারের সমালোচনা করেছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ব্যক্তিগত আক্রোশের জায়গা থেকে। নাট্যকার কাকে ঘৃণিত দেখাবেন আর কাকে ভালো মানুষ বলবেন সেটা ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করা হয়নি, সম্পূর্ণ – নাট্যকারের ব্যক্তিগত খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল ছিলো।
নাট্যকারের ভাববাদী চিন্তা এ নাটকে খুবই প্রকট। যেমন মা মানেই ভালো মানুষ। ‘মা কখনো দোষ করতে পারে না’ এ ধরনের সংলাপও নাটকে পাওয়া যায়। মার মৃত সন্তানরা ফিরে আসে, মা তাদের আত্মার গন্ধ পায়। নাটকের সংলাপ, ঘটনা সবই অসংলগ্ন। বেখাপ্পা নাটক ও অভিব্যক্তিবাদী নাটকের সংমিশ্রণ ঘটেছে নাট্যরচনায়। মা আর তার সাত সন্তান, কে যে কার প্রতিনিধিত্ব করে তার কিছুই বোঝা যায় না। নাটকে আছে কিছু স্থূল সংলাপ। যেমন নায়ক বলছে নায়িকাকে, ‘যদি তোমাকে ছায়াছবির খচ্চর মার্কা নায়িকার মতো অর্ধ উলঙ্গ করে দেই’। ‘তুমি ন্যাংটা হয়ে নাচবে আমি ষাড়ের মতো ফাল দেব।
অন্য কিছু সংলাপ, ‘শালার বউটা মোটা হয়েই যাচ্ছে। চর্বির গোডাউন। পাঁচশো লোককে ঐ চর্বি দিয়ে পরোটা ভেজে খাওয়ানো যাবে।১৯৯ ‘প্রস্রাব করতে গেলাম, প্রস্রাব হল না।’ ‘যেখানেই যাই ফুল গাছ। কুত্তার বাচ্চা বাঙালী প্রস্রাব করার জায়গা রাখেনি।’২০০ মাকে মেয়ে বলছে, ‘তুমি বুকের আঁচল খুলে আজনবী চিড়িয়ার মতো মেলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, তোমাকে মাস্তানরা সিটি মারছিলো।’
মা মেয়েকে বলছে, ‘সাবাস, তুই আমার এ্যাসেট, আমার ডলার, আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক’। ‘তোকে নিয়ে যেখানে যাব, সেখানেই মেলা বসে যাবে’। নাট্যকারের স্ববিরোধিতা এই যে, এক জায়গায় তিনি বলছেন মা কখনই খারাপ হতে পারে না, আর এক জায়গায় তিনি এক নোংরা মাকে দেখাচ্ছেন যে টাকার জন্য মেয়েকে পর্যন্ত বিক্রি করছে। সেই মাকে তিনি দেখাচ্ছেন পাকিস্তানপন্থী। যেন যে- কোনো মা পাকিস্তানপন্থী হলেই টাকার জন্য মেয়েকে বিক্রি করে দেবে। বক্তব্যটা ভীষণভাবে অবৈজ্ঞানিক। নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় এ নাটক ভরপুর, তেমনি নানা স্ববিরোধী চিন্তায়। সপ্তম দৃশ্যে প্রহরী কেন হঠাৎ এ্যান্টিনাকে গুলি করে মারে তার কোনোই কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।
নাট্যকার নিজেও এ নাটকে মনে করেন, নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ইজ্জত অর্থাৎ তার সতীত্ব। এটা তো ধর্মীয় চিন্তা, সামন্তবাদী চিন্তা। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা নয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা নয়। পুরুষের মতোই নারীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার সতীত্ব রক্ষায় নয়, তার সামাগ্রিক কর্মকাণ্ডে, মানুষের মুক্তির জন্য তার ত্যাগের মধ্যে। পৃথিবীকে এগিয়ে নেয়ার সংগ্রামে মানুষের কর্তব্যপরায়ণতাই তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করে। মার্কসবাদীদের চোখে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটাও আপেক্ষিক। মহৎ এক মায়ের দেখা পাই আমরা এ নাটকে যার চরিত্রে কোনো পঙ্কিলতা নেই। এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেন স্বপ্নচারীরা। নাট্যকার এখানে মাকে বাংলাদেশের সাথে তুলনা করেছেন।
মানুষকে এভাবে দেশের সাথে তুলনা করা শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা বিরোধী। দেশ সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা আবেগ সৃষ্টি করে বুর্জোয়ারা। যুদ্ধের প্রয়োজনে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তারা দেশকে ‘মা’ হিসাবে দেখাতে চায়, মানুষ তখন আবেগ আপ্লুত হয়ে জ্ঞানবুদ্ধি বাদ দিয়ে দেশমাতাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উগ্র জাতীয়তাবাদীরাই এসব করে থাকে, যারা অন্য রাষ্ট্রকে সম্মান দেখাতে চায় না। কারণ জনগণ তাদের কাছে বড় নয়, বড় হচ্ছে ভূখণ্ড। দেশকে মাতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা তাদের ব্যবসার সাম্রাজ্য বাড়িয়ে তোলে, জনগণের ওপর শোষণ চালায়। বুর্জোয়াদের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ কালেই আমরা এসব বেশি লক্ষ্য করেছি।
নাট্যকার এ নাটক প্রসঙ্গে লিখছেন, দেশের সম্ভাবনা ও শক্তির জন্য আমি নিরপরাধ সরল এবং খেটে খাওয়া মানুষকে বেশি গণ্য করি। প্রথম হলো নিরপরাধ মানুষ বলতে নাট্যকার কী বোঝেন সেটা এ বক্তব্যে প্রাঞ্জল নয়। কারণ এ সমাজে খেটে খাওয়া মানুষদেরও নানা অপরাধে জড়িত হতে হয়। এটাই সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম। সরল মানুষই বা কারা? তিনি যতো বড় মুখ করেই খেটে খাওয়া মানুষদের কথা বলেন না কেন, এ নাটকে খেটে খাওয়া মানুষরা একেবারেই আলোচিত হয়নি। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মানুষদের দুঃখ-কষ্ট, লোভ-লালসাই এ নাটকের কেন্দ্র বিন্দু। মধ্যবিত্ত এক মা ও তার সন্তানদের ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে এ নাটক।
মধ্যবিত্ত সন্তানদের চাকরি না পাওয়া নিয়ে এ নাটক আহাজারি করেছে, কিন্তু যারা শ্রমিকশ্রেণী, যারা গরীব চাষী, তাদের ক্ষুধা দারিদ্র্য নিয়ে এ নাটকে কোনো বক্তব্য নেই। এক মধ্যবিত্তের দ্বারা আর এক মধ্যবিত্ত কীভাবে নিগৃহীত হচ্ছে, কীভাবে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের বিলাসী জীবন যাপন করছে তার কিছু স্ববিরোধী ও অসংলগ্ন চিত্র আছে এ নাটকে। ঢাকার মধ্যবিত্তরাই ছিলো প্রধানত এ নাটকের দর্শক এবং সমাজের খণ্ডবিচ্ছিন্ন কয়েকটি ছবি, সমাজের কিছু বিকৃতির তীব্র ব্যঙ্গ ও অতিরঞ্জিত শ্লেষ এই দর্শকরা খুব উপভোগ করেছে। সমাজের এই বিকৃতির মূল কোথায়, কোন অর্থনৈতিক শোষণে এই দুরবস্থা-সেদিকে নাট্যকারের নজর ছিলো না। দেশপ্রেমের চেতনা জাগাতে গিয়ে তিনি যে কাজটি করেছেন তা আরো বিভ্রান্তিকর।
চরিত্রগুলি মাঝে মধ্যে গুণ্ডাবাজি করে, খিস্তি খাস্তা করে, প্রেম করে পরে আচমকা দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠে। দর্শন চৌধুরী এই ধরনের নাটকগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই মনে করেন। ২০০ সাতঘাটের কানাকড়ি নাটকের রচয়িতা যে-ধরনের কুরুচিপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করেছেন কিংবা প্রযোজনায় যে-ধরনের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির আমদানি করেছেন তাতে রাজনৈতিক চেতনা তো দূরের কথা, দর্শকের ভিতরে নানা ধরনের অসুস্থ চিন্তাকে সংক্রামিত করা হয়। বাংলাদেশের নাটকে অশ্লীলতাকে প্রাধান্য দেয়া প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, ঢাকার উল্লেখযোগ্য দলগুলোর মধ্যে কুরুচির লক্ষণ প্রথম দেখা যায় ঢাকা পদাতিকের বিভিন্ন প্রযোজনায়।
ঢাকা পদাতিকের আশির দশকের প্রযোজনা ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইংগিত, এই দেশে এই বেশে, আহ কমরেড-এসব প্রযোজনায় যথেষ্ট কুরুচির ইঙ্গিত ছিলো। নাটককে বহুক্ষেত্রে তাঁরা সার্কাস বানিয়ে ফেলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই ধরনের নাটকের কিছু প্রযোজনা দেখার পর শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন, ‘আমরা সবাই দিশেহারা অধঃপতনের পথে হু হু করে নেমে এসেছি। আমাদের চিন্তার বিন্যাস নেই, আবেগের ভদ্রতা নেই।’২০৬ তিনি আরো লিখছেন, ‘যতো অভদ্র ভাষায় কপচানো হয়, ততোই জোর হাততালি পড়ে। কিন্তু সে শিল্প সংস্পর্শে দর্শকের মন উন্নত হয় না। লড়াই করবার জন্য নৈতিক জোর আসে না বুকে, ক্রোধ আসে না, আসে কেঁউচেমি।’
যার ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের নাটকের জন্য যেমন ভালো হয়নি, তেমনি বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনকেও তা ক্ষতি করেছে। ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ আল-মামুনের এখনো ক্রীতদাস নাটকেও অশ্লীল সংলাপ ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বহুজন মনে করেন গালাগাল ব্যবহার করে তাঁরা নাটককে বাস্তব করে তুলছেন। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই তাঁরা এসব কথা বলেন। মানুষের হৃদয়-মন ছুঁয়ে যাবার মতো সংলাপ তাঁরা রচনা করতে পারেন না বলেই, কুরুচিপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করে দর্শকদের আকৃষ্ট করেন এবং তাদের রুচিকে নষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার এসব করা দরকার হয় না। রক্তকরবীর মতো নাটক লিখবার যোগ্যতা থাকলে কাউকেই বাস্তবতার দোহাই দিতে হয় না।

শ্রমিকরা বাস্তব জীবনে গালাগাল করলেও রক্তবরবী নাটকে বাস্তবতার নামে রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকদের দিয়ে গালাগাল করাননি। তিনি শ্রমিকদের জীবনের গভীর বিষয়গুলোকেই সামনে এনেছেন। যাদের নাটকে গভীরতা থাকে না, তাদেরকে বাস্তবতার নামে খিস্তি করতে হয়। বলতেই পারেন যে কেউ, খিস্তি খেউর এসব তো বাস্তব জীবনে আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রশ্ন নাটকে তা তুলে আনলে লাভটা কী? তার দ্বারা তো আমাদের চিন্তা বুদ্ধিভিত্তিক হয় না, আমাদের দৃষ্টিও বিজ্ঞানসম্মত হয় না। বড়জোর তাতে কিছু হাততালি পড়তে পারে। দর্শককে কিছুটা বিকৃত প্রমোদ বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্প তো নিছক প্রমোদের আপ্তবাক্যের আফিম হিসাবে ব্যবহৃত হবার নয়। শিল্প মানুষের বোধের একটা হাতিয়ার।
বিজ্ঞান যেমন পৃথিবীকে বুঝবার অস্ত্র, শিল্পও তেমনি মানুষকে বুঝবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বুঝবার একটা অস্ত্র। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক যুক্তিভিত্তিক অনুসন্ধিৎসা ছিলো। তিনি বাস্তব পৃথিবীকে সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন। সমাজ সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে তাঁর কিছু নিজস্ব বক্তব্য ছিলো এবং সেই বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন এমন এক নাট্যরূপে, যা ধ্রুপদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য তাঁকে খিস্তি করতে হয়নি।
কী দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা? আশির দশকের নাট্যচিন্তায় সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমাজচেতনার অভাব মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়। নাট্যকার হিসাবে যাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি তাঁদের বাদ দিলেও, যাঁরা নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত তাঁদের নাটকেই সমাজ সচেতনতার অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীসংগ্রামের নাটক যাঁরা লিখছেন কিংবা যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের বাইরে সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লিখতে চেষ্টা করেছেন, দুপক্ষের রচনাতেই ঘটনা পরম্পরা ও যুক্তির অভাব ধরা পড়েছে। সেলিম আল দীন ও সৈয়দ শামসুল হক এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। বিশেষ করে সেলিম আল দীনের নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় মেলে, যদিও সেগুলো সর্বগুণসম্পন্ন নাটক হয়ে উঠতে পারেনি।
অশির দশকে বহু নাট্যকার ও নির্দেশক নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় লম্ফঝম্ফ বা কুরুচিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বড় বড় নাট্যদলের জনপ্রিয় নাট্যকাররাই তা করেছেন। এইসব দিকপালদের মতিভ্রম দেখে উত্তরসুরীরাও দিকভ্রষ্ট হয়েছেন। দিকপালদের তথাকথিত জনপ্রিয়তা দেখে নবাগতরাও তাদের পন্থা অনুসরণ করে চলেন। পরবর্তীকালে তার ফল হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ‘বহু শিল্পীর অধঃপতন হয় এভাবে।
একদা যাঁরা ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পকলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর শিল্প সৃষ্টিতে নবচেতনা আনবার প্রতিজ্ঞা নেন, উত্তরকালে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভনে পড়ে নিজেদের ঘোষিত আদর্শ থেকে অনেকখানি দূরে সরে যান এবং ব্যবসায়িক জগতের নিকৃষ্ট শিল্পকলার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।’মহৎ নাটকে এ ধরনের নিকৃষ্ট উদাহরণ কখনও দেখা যাবে না।
মার্লো, শেক্সপিয়ার, ইবসেন, শিলার, চেকভ, গলসওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকাররা যাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম মাথায় রেখে নাটক লেখেননি, তাঁদের নাটকে সমাজের যে দ্বন্দ্ব, নাটকের চরিত্রের সাথে সমাজব্যবস্থার যে বিরোধ ধরা পড়ে, তার মধ্যে রয়েছে এক গভীর সমাজবোধ ও যুক্তিবাদিতা-বাংলাদেশের-নাট্যকারদের নাটকে আমরা তা লক্ষ্য করি না। প্রাচীন গ্রীক নাটকে বা বিশ শতকের আর্থার মিলার, উগো বেটির নাটকে যে গভীর জীবন বোধ দেখতে পাই বাংলাদেশের নাট্যকাররা দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সে ধরনের নাটক লিখতেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের রচনা রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনকে পথ চলতে সাহায্য করেনি বললেই চলে। এসকল নাটক যেমন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণাকে হাজির করতে পারেনি, তেমনি যুক্তিবাদী চিন্তারও প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। নাটকের বিষয়বস্তু সে কারণে মানুষের সত্যিকার সংগ্রাম থেকে বহু দূরে সরে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে আশির দশকে মঞ্চে শ্লোগান সর্বস্ব নাটক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়, কোথাও প্রধান হয়ে ওঠে স্থূল রুচি সম্পন্ন বিষয়বস্তু। মানবিক গুণ সম্পন্ন নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারটি ছিলো খুবই স্নান। নাট্য নির্দেশক আতাউর রহমান সে সময়ের নাটক সম্পর্কে লিখছেন, দশ কি পনের বছর আগে নাটকের যেসব সত্যিকার অর্থপূর্ণ ও ভালো সংলাপে দর্শক-আনন্দ পেতো কিংবা প্রতিক্রিয়া দেখাতো সেই সংলাপ এখন আর দর্শকদের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।
কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দর্শক অমার্জিত ও অশ্লীল সংলাপ ও মঞ্চ-ক্রিয়ায় বেশি মজা পায়। রুচিশীল, শাণিত ও সুন্দর সংলাপ দর্শকের মনোরঞ্জন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে। এই দোষ শুধু দর্শকদের নয়, এর দায়ভাগ নাট্যকর্মীদের ওপরও বর্তায়। দায়ভাগ বর্তায় নাট্যকারদের ওপরেও। মমতাজউদ্দীন আহমদ, এস এম সোলায়মান ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকেও আমরা নানা অশ্লীল সংলাপ দেখতে পাই। এস এম সোলায়মান ছিলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী।
সে সময় কোনো গভীর নাট্যবোধ নাট্যকারদের লেখনিতে ধরা পড়ছিলো খুবই কম। বিষয়বস্তু রেখে আঙ্গিক-যেমন মঞ্চসজ্জা, আলো, পোষাক এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। বিষয়কে বাদ দিয়ে কেবল খোলস নিয়েই চলছিলো মাতামাতি। বিশেষ করে আশির দশকে বাণিজ্যিক ঝোঁক, আঙ্গিকসর্বস্বতা, ব্যক্তিবিশেষের আত্মজাহির করার প্রবণতা প্রকট হয়ে পড়ে।
যদি আশির দশকের নাট্যচর্চার মূল্যায়ন করা হয় দেখা যাবে, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশগ্রহণ শেষ পর্যন্ত তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। নাটককে তাঁরা তাই সত্যিকার অর্থে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিতে পারেননি যদিও সেই শ্লোগান তাঁরা তুলেছিলেন। যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান তুলেছিলেন এবং যাঁরা সে শ্লোগান তোলেননি দুপক্ষেরই প্রধান ও বড় অংশটিই নাটককে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতার পরপর নিয়মিতভাবে নাট্যমঞ্চায়ন যে সারা দেশের মধ্যবিত্তদের একাংশের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। নাটকের এই আপাতঃ সফলতার সাথে সাথে কিছু কিছু শিল্পীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো। সেই সাথে তাদের প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকলো।

আর এই প্রভাবে নাট্যকর্মীদের মাঝে এলো সুনামের সাথে অর্থের মোহ এবং বিভিন্ন সুবিধাদি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। খুব শীঘ্রই নাট্য আন্দোলনে তার ফলাফলও দেখা গেল। জনপ্রিয় নাট্যকর্মীরা আরো জনপ্রিয়তা লাভের জন্য ছুটে গেল টেলিভিশনে, কেউ কেউ সিনেমায়। এই জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে বহু নাট্যকর্মীই বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলে কিংবা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি নিয়ে এ ব্যবসায় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো। যাঁদেরকে মনে করা হয়েছিলো নিবেদিত নাট্যকর্মী দেখা গেল তাঁরা পরিণত হলো অর্থলোভী আপোষকামী এবং লুটেরা ধনিক গোষ্ঠীর চাটুকার রূপে। দলীয় কর্মীদের তারকা খ্যাতির গুণে ঐ সব দলের নাটকে প্রচণ্ড দর্শক সমাগম হতে লাগলো।
নাট্য প্রদর্শনীতে তারকা দেখার জন্য ভীড় বাড়লো। কোনো কোনো দলের প্রদর্শনী সংখ্যা পৌঁছুলো শতকের ঘরে। কোনো কোনো নাটকের দর্শক বাড়লো ঠিকই কিন্তু কোন্ ধরনের দর্শক তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না। নাটক, নাট্যকর্মী ও দর্শক সকল দিক থেকেই নাটক একটি বিশেষ বিনোদনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। সেই বিনোদনের প্রধান কারণ নাটকের বিষয়বস্তু নয়, টেলিভিশনের তারকারা।
ঢাকার বিভিন্ন দলের মঞ্চায়ন যেমন এ সময় কমতে থাকে, দর্শক আনুকূল্যও তারা লাভ করে না। ঢাকার মঞ্চে এসময় প্রধানত যে দলগুলোর দাপট ছিলো সেগুলো হচ্ছে ঢাকা থিয়েটার, থিয়েটার, নাগরিক। তারপরই আরণ্যক। যদিও পূর্বের দলগুলোর চেয়ে আরণ্যকের অবস্থান ছিলো অনেক পেছনে। প্রথম তিনটি দলের নাটকে মিলনায়তন পূর্ণ হলেও বাকিদের বেশির ভাগেরই প্রযোজনা খরচই উঠতো না। প্রথম তিনটি দলের নাটকে মিলনায়তন পূর্ণ হওয়ার পেছনে যেমন ছিলো তাদের প্রযোজনার মান, তেমনি ছিলো সেই দলের টেলিভিশন তারকাদের প্রতি দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ। ফল যা দাঁড়ালো, পিছিয়ে পড়া দলগুলোও নিজ দলের জন্য কিছু টেলিভিশন তারকা সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন উঠেপড়ে লাগলো, তেমনি নাট্যকর্মীদের বড় একটা অংশই টেলিভিশনে যাবার জন্য পাঁয়তারা শুরু করলো।
মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্র থেকে উদ্ভূত সুবিধাবাদী চরিত্রটি ছিলো. সমগ্র গ্রুপ থিয়েটার পরিমণ্ডলে বিরাজমান। প্রচুর দল গঠিত হলো বটে। তবে নাটক কিংবা নাট্যদলের পরিচিতির চেয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তা ওঠানামার ওপর দলের ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।
ব্যক্তিগত সাফল্য থেকে শুরু হলো ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। ভাঙন হতে লাগলো নানা দলে। পাশাপাশি যদিও নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলো তথাপি নাট্যচর্চার গতি আগের মতো জোর পাচ্ছিলো না কিছুতেই। টিভির দৌরাত্ম্যে মঞ্চ নাটককে ক্রমান্বয়ে এক অপ্রিয় অযাচিত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হলো। নাটকের দর্শক কেন কমে যাচ্ছে সে ব্যপারে শিশির দত্ত লিখছেন, টিভির দৌরাত্ম্যে ঢাকার বাইরে নাট্যচর্চা ক্রমশ দর্শক আনুকূল্য হারাতে থাকে। তিনি আরো লিখছেন, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীগুলো দায়- দায়িত্বের তোয়াক্কা না করে ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রয়োজনে তারকা নির্ভর নাট্যচর্চাকে অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করে।
মঞ্চের চেয়ে বেশিরভাগের কাছে তাই টেলিভিশনটাই হয়ে উঠলো মোক্ষ। মঞ্চ-নাটকের দর্শকদের মধ্যে টিভি তারকাদের দেখার প্রবণতা বাড়তে থাকলো। নাটকের বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের চাইতে মুখ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়ালো এক ধরনের গ্লামার যার সাথে নাট্যগুণের কোনো সম্পর্ক নেই।
রাজনীতি আর সমাজ মনস্কতার কথা বলে আশির দশকে ক্রমাগত রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বিপরীত আবস্থা গ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছিলো নাট্যকর্মীদের মধ্যে।
শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে নাটককে নিয়ে যাওয়ার কোনো উদ্যোগ কখনও তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। নাট্যচর্চাকে সত্যিকারের আন্দোলনের পথে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে কীভাবে টেলিভিশনে উত্তরোত্তর ইমেজ বাড়ানো যায় এঁরা সে চেষ্টাই করেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি। মূল চরিত্রের দিক থেকে এঁরা ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেই এঁদের সম্পর্ক বেশি আবার সংস্কৃতি অঙ্গনের দখলদারি ছাড়তেও এঁরা রাজি নন। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়েই এঁরা অধিক চিন্তিত। ফলে কথার সাথে এঁদের কাজের কোনো সঙ্গতি ছিলো না। আশির দশকে এরশাদের শাসনামলে দেখা গেছে, বিকালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করে রাতের টেলিভিশন সংবাদে এঁরা স্বৈরাচারের স্তুতিবাচক সংবাদ পাঠ করছেন।
বাংলাদেশে আশির দশকে সামরিক শাসনকালে স্বৈরাচারের ব্যাপক আক্রমণের মুখে প্রান্তিক নাট্যকর্মীরা পিছিয়ে যাননি, রাজপথ ছাড়েননি এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু নেতৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থে তাঁদের সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারেননি। গ্রুপ থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা ঐ সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শাসক এরশাদের সাথে কোনোরকম আলোচনায় তাঁরা যাবেন না। গ্রুপ থিয়েটারের স্বার্থেও নয়। গ্রুপ থিয়েটারের কিছু কিছু কর্মী থিয়েটারের স্বার্থে ভালো একটি মঞ্চ লাভের আশায় এরশাদের সাথে বৈঠকে বসতে চাইলে নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করেন। গ্রুপ থিয়েটারের ঐ সকল ব্যক্তিরাই সাধারণ নাট্যকর্মীদের রাজপথে আন্দোলন করতে পাঠিয়ে নিজেরা গিয়েছিলেন অথবা তাঁদের দলের তারকাদের পাঠিয়েছিলেন বঙ্গভবনে এরশাদের কাছে, যাতে টেলিভিশন থেকে তাঁরা আরো বেশি সুযোগ সুবিধা আরো বেশি সম্মানী লাভ করতে পারেন। ২১৫ খুব দ্রুতই নেতৃত্বের এই সুবিধাবাদী চরিত্র সংক্রামিত হয়ে পড়লো প্রায় সকলের মধ্যে।
প্রতিভা, বুদ্ধি, সাহস ও ক্ষ্যাপামি নিয়ে যে-দু-চারজন কাজ করতে এসেছিলেন, জনগণের জন্য বিপ্লবী নাটক করতে চেয়েছিলেন তাঁরাও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাঠে নেমে পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং খুব শীঘ্রই বিপ্লবী নাট্য আন্দোলনের মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন নতুন ভাগ্য গড়ার সন্ধানে। সর্বহারার জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তাঁদের বিপ্লবের ঘোষণা প্রহসন হয়ে রইলো মাত্র। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এভাবেই বারবার নাট্যকর্মীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ও শ্রেণীস্বার্থ ধরা পড়েছে। বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীদের শ্রেণীচেতনার মান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্রের গণ্ডি যেমন তাই আশির দশকে অতিক্রম করতে পারেনি, নব্বইয়ের দশকে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিলো।
আরও দেখুন: