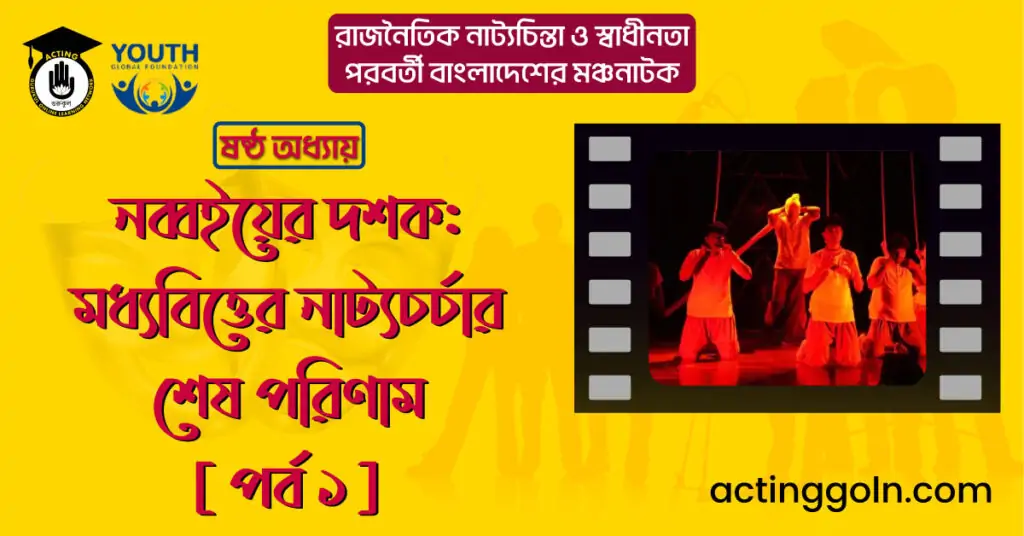নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম নিয়ে জানার জন্য আজকের আয়োজন। বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকের প্রধান ঘটনাবলীর একটি হলো দীর্ঘ নয় বছর পর স্বৈরাচারী সরকারের শাসনের অবসান। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সেনাপ্রধান এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় এক দশক তিনি ক্ষমতায় থাকেন। উনিশশো নব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি ক্ষমতা ছাড়েন একটি নিরপেক্ষ অস্থায়ী সরকারের হাতে। সেই অস্থায়ী সরকারের প্রধান হন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ। স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে মূল আন্দোলন পরিচালনা করে তিন ঐক্যদল এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। পরবর্তীতে তিন ঐক্যদল তিনদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। সেই তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী শাহাবুদ্দিন আহমদ দশজনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা দেশ শাসনের অধিকার লাভ করেন।
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 2 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/নব্বইয়ের-দশক-মধ্যবিত্তের-নাট্যচর্চার-শেষ-পরিণাম-পর্ব-১--1024x536.jpg)
মূলত এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিলো একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণের জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। শাহাবুদ্দিনের আমলে দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য মোট আসন সংখ্যা প্রয়োজন ছিলো একশো একান্নটি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল লাভ করে একশো আটত্রিশটি আসন। জামায়াতে ইসলামী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সরকার গঠনে সমর্থন জানালে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করে। ক্ষমতা থেকে এভাবেই এরশাদ শাসনের অবসান হয়।
শেখ মুজিব সরকার উনিশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ঐ পদ্ধতির শাসনই চলে আসছিলো। জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসার পর তিনজোটের রূপরেখা অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের বিল উত্থাপন করে। উনিশশো একানব্বই সালের ছয়ই আগস্ট সেই বিল পাশ হলে ঐ বছর থেকেই পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু হয়। বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।’ দীর্ঘ নয় বছর পর দেশে একটি গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু হলে মানুষ আশা করেছিলো দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।
কিন্তু খুব শীঘ্রই দেশের মধ্যে নানা ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। খালেদা সরকার বিভিন্ন কারণে খুব দ্রুত জনসমর্থন হারাতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী দলের পাঁচ বছরের শাসনে সন্ত্রাস, জাতীয় সম্পত্তি লুটপাট, বিরোধী দলগুলোর ওপর ব্যাপক আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস, হত্যা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, হত্যা, ডাকাতিরও অসংখ্য খবর পাওয়া যায়। চাঁদাবাজি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, চাঁদা না দিয়ে তখন কোনোরকম ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাচ্ছিলো না। বিশেষ করে খালেদা সরকারের শাসনের শেষ দিকে পঁচানব্বই সালে ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়।
মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় পঁচানব্বই সালে দেশে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে দু হাজার দশ ব্যক্তি। পুলিশের হেফাজতে নিহত হয়েছে চোদ্দ জন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ত্রিশ জনের বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হয়। দিনাজপুরে পুলিশ তেরো বছরের বালিকা ইয়াসমিনকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে তুলে দলগতভাবে ধর্ষণের পর হত্যা করে। সরকারি প্রশাসন এ ঘটনায় অপরাধীদের সমর্থন দেয় এবং জনগণ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়। খালেদা সরকারের পাঁচ বছরের শাসনে চার লক্ষাধিক অপরাধ, তেরো হাজার খুন ও সহস্রাধিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে।
খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ বছরে তীব্র সার সংকট দেখা দেয়। কৃষকদের চাহিদা মতো সরকার সার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। সার সংকটের কারণে চাষবাস ব্যাহত হতে শুরু করে। সার সংকটের কালে সরকার নির্ধারিত যে সারের মূল্য ছিলো একশো পঁচাত্তর টাকা, তার দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিনশো টাকা। সরকারি ছত্রছায়ায় এভাবেই একদল লোক সারের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ফায়দা লুটতে শুরু করে। সরকারি দলের লোকদের দুর্নীতিতে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসন অফিস ঘেরাও করে। টাঙ্গাইলে এ সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়। সারাদেশে এ কৃষক আন্দোলন স্বল্পসময়ের জন্য হলেও ছিলো একটি বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলন।
খালেদা জিয়ার শাসন আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আনসার বিদ্রোহ। ব্যাটালিয়ন আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সরকারের কোনো স্থায়ী বাহিনী ছিলো না। সুনির্দিষ্ট ছিলো না এ বাহিনীর সদস্যদের চাকুরি-শর্ত ও বেতন-ভাতা। উনিশশো বিরাশি সালে প্রথম ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ী করার দাবি ওঠে। উনিশশো আটাশি সালে এরশাদ সরকারের আমলে আনসারদের চাকরি স্থায়ী করার প্রাথমিক সিদ্ধান্তও হয়। নব্বইয়ের ফেব্রুয়ারি মাসে আনসার ভিডিপির জাতীয় মহাসমাবেশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ আনসারদের স্থায়ী করাসহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ পূরণের আশ্বাস দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমলাচক্র এসব প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন ফাইল চাপা দিয়ে রাখে।
আনসাররা সে কারণে প্রশাসনের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলো। সব সময়ই আনসারদের বড় বড় পদগুলো- সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা হতো। সেনাবাহিনী থেকে যাঁরা আনসার বাহিনীতে কর্মকর্তা হয়ে আসতেন, তাঁদের খবরদারি ও জুলুমের কারণে আনসারদের মধ্যে বহুদিন ধরেই চরম অসন্তোষ চলছিলো। উনিশশো চুরানব্বই সালের একটি ঘটনা সে অসন্তোষকে বিদ্রোহে পরিণত করে। সে বছরের ডিসেম্বর মাসে গাজীপুরস্থ আনসার একাডেমীতে আনসার মানিক মিয়াকে প্রহার করেন আনসার অ্যাডজুটেন্ট আজাহার আলী। প্রহারের ঘটনায় দীর্ঘদিনের ধুমায়িত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে আনসাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 3 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ১ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-১.jpg)
বিদ্রোহের পর কর্মকর্তাদের একাংশ এই আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে এবং একটি সংগ্রাম কমিটিও গড়ে ওঠে। বিদ্রোহ চলাকালীন সময় কয়েকজন কর্মকর্তা সাধারণ আনসারদের দ্বারা শারীরিকভাবে নাজেহাল হয়, বহুজনকে জিম্মি করে রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন থেকেই বিদ্রোহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আনসার ক্যাম্পগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনায় বসা হয়। সরকার পক্ষ আনসারদের দাবি-দাওয়া না মেনে নিলে সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কিছু কিছু বাম সংগঠন এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। ডিসেম্বরের চার তারিখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে সেনাবাহিনী প্রধান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আনসার বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত নেয়।
ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ মধ্যরাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী বিদ্রোহ দমনের জন্য যৌথ অভিযান চালায়, বিদ্রোহীদের ক্যাম্পগুলো ঘিরে ফেলে তারা বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। আনসাররা এতে আরো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিদ্রোহের এক নেতা বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা দেন, এক বিন্দু রক্ত শরীরে থাকতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন না।
অনেক আনসার এ সময় দল বেঁধে নিজেদের রচিত একটি বিপ্লবাত্মক গান গাইতে থাকে। তাদের ভিতর থেকে জঙ্গী শ্লোগানও শোনা যায়। সরকার পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের ভবনগুলো লক্ষ্য করে এরপর শুরু হয় বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ। টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। বিদ্রোহী আনসাররা তবুও আত্মসমর্পণ করবে না বলে জানাতে থাকলে ভোরের দিকে সরকারি বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে মর্টার হামলা চালায়। এ সময় আশেপাশের কয়েক হাজার জনতা হামলা বন্ধের দাবিতে মিছিল বের করে। অভিযানকারীদের সাথে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। রক্তাক্ত যুদ্ধের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আনসার বিদ্রোহ দমন করা হয়।”
জাতীয়তাবাদী দলের শাসনামলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশের কিছু ঘটনা তার শাসনকালকে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেও অস্থির করে তোলে। ভারতে বিরানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে একদল উগ্র হিন্দু বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে। বিজেপি রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থন লাভের আশায় বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণের চেষ্টা নেয়। ঘটনাটি ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি করে।
বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার তৎপরতা ও পরিশেষে সেটা ধ্বংস করার সময় থেকে বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরই বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক মন্দিরও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলে মুসলমান জনগণই এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তবুও অনেক অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ ও হিন্দুদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার ফলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটে সেটা পূর্বে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ ধরনের ঘটনা ছিলো এটাই প্রথম।
খালেদা জিয়া সরকারের সময়ের আর একটি আলোচিত ঘটনা গোলাম আযমকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলের প্রধান বা আমীর ঘোষণা করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন নিধনযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। স্বাধীনতার পর সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে পাকিস্তানে পরে লন্ডনে বসবাস করতে থাকে। স্বাধীনতার পরপর মুজিব সরকার গোলাম আযমসহ বেশ কিছু স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে। গোলাম আযম বিদেশের মাটিতে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নানা ধরনের চক্রান্ত চালায়।
গোলাম আযমের উদ্যোগেই উনিশশো বাহাত্তর সালে পাকিস্তানে ‘পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার সপ্তাহ’ পালন করা হয়। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে সে লওনে ‘পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি’ গঠন করে। উনিশশো ছিয়াত্তর সালের শুরুতে জিয়া সরকার কর্তৃক অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা সম্পর্কে বিবেচনার আশ্বাস পেয়ে সকলেই নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য আবেদন করে।
প্রায় সকলেই তখন নাগরিকত্ব ও বিষয় সম্পত্তি ফিরে পেলেও গোলাম আযমের বিষয়টি ঝুলে থাকে। উনিশশো আটাত্তর সালে গোলাম আযম মায়ের অসুস্থতার অজুহাতে তিন মাসের ভিসা নিয়ে সাময়িকভাবে দেশে আসে এবং আর ফিরে না গিয়ে অবৈধভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। উনিশশো আশি সালে নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আন্দোলন করে। উনিশশো একাশি সালের এপ্রিল মাসে গোলাম আযম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তার নাগরিকত্ব বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সরকারকে পুনরায় অনুরোধ জানায়। তখনো তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি।
বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও গোলাম আযম নানাভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। একানব্বই সালে যে দুজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁরা দুজনেই গোলাম আযমের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন চেয়েছিলেন। গোলাম আযম নব্বইয়ের দশকে সবচেয়ে আলোচিত হয়ে ওঠে যখন জামায়াতে ইসলামী দল তাকে দলের আমীর ঘোষণা করে।”
গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়া সত্ত্বে তাকে জামায়াতের আমীর ঘোষণা দেয়া ছিলো দেশের আইন বিরোধী। বিএনপি সরকার জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করায় এ ঘটনায় নীরব ভূমিকা পালন করেছিলো। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যান্য সংঠন, বাংলাদেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও বাম রাজনৈতিক দলগুলো এর প্রতিবাদ করে।
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি গোলাম আযম প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দাবি করে সরকারের কাছে। গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর করায় সংসদে উত্তপ্ত বিতর্ক হয় সরকার ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে। সরকারি দলের বহু সাংসদও গোলাম আযম ও জামায়াতের ভূমিকার নিন্দা করে এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেন।মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও বিভিন্ন সংগঠন গোলাম আযম ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যাপারে সোচ্চার আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদান করে। গোলাম আযম বিদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে দেশে থাকা ও আমীর হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত হয় সমন্বয় কমিটি, পরে যা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে রূপ নেয়।
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি উনিশশো বিরানব্বই সালের ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় গোলাম আযমের এক প্রতীকী বিচারের আয়োজন করে। ইতিমধ্যেই সরকার জনরোষের কারণে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সরকার একই সাথে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির দ্বারা ডাকা গণআদালতকে অবৈধ মনে করে এবং তা বাস্তবায়ন না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দেয়। নির্মূল কমিটি সরকারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গণআদালতের বিচারে গোলাম আযমের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এদিকে গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নে উচ্চতর আদালতে বিচার চলতে থাকে। বিরানব্বই সালের আগস্ট মাসে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে দুই বিচারপতি দুই মত প্রকাশ করেন। আবার নতুন বিচারকদের নিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়। উচ্চতর আদালতের সেই বিচারে বাইশে জুনের এক রায়ে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়।
বিএনপি সরকারের আমলের আর একটি বড় ঘটনা সারাদেশ জুড়ে ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। জাতীয় নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পক্ষে সারা দেশব্যাপী বিরাট গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। বিএনপি সরকার জনগণের সে দাবি মেনে না নিয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করলে প্রধান দলগুলো সে নির্বাচনে অংশ নেয় না। বিএনপি বলতে গেলে এককভাবে এ নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। জনগণ এ নির্বাচন বাতিলের দাবি তোলে। গণরোষের মুখে নতুন সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে হয় এবং গণঅভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বারা সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গঠন করে।
আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতা লাভ করার পরপরই বিরাটভাবে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে বিপর্যয় ঘটে। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের প্রথম দিকটায় বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলাদেশ ছিলো অস্থির-অস্থিতিশীল, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। শেয়ার বাজারের সূচক নিচে নেমে যায়। বিএনপি ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর শেয়ার বাজার সূচক আবার উপরে উঠতে থাকে।
শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে শেয়ার মূল্য সূচকের উল্লম্ফন আরম্ভ হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। জুলাই থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মূল্য দ্রুত উঠে যায় এবং শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের মোহগ্রস্ত করে তোলে। শেয়ার বাজারের মূল্যবৃদ্ধি এমন এক সময় ঘটেছে, যখন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো বাজার অবকাঠামো ছিলো না। এই ধরনের বাজারের এই অস্বাভাবিক সূচক উপরে ওঠার পেছনে ছিলো কালোহাতের কারসাজি। এর সুবিধা লুটেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। তারা দেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে যৌথভাবে শেয়ারের বিকৃত মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, নাহলে শেয়ার বাজারের তেজীভাবের পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ ছিলো না। অথচ সরকার এটাকে তাদের সরকারের দ্রুত উন্নতি হিসাবে প্রচার করে।
শেয়ার বাজারে এই ধরনের সূচক বৃদ্ধি দেখে বহু সাধারণ মানুষ তাদের জমি- জমা, এমনকি শেষ সম্বল বিক্রি করে শেয়ার বাজারে তা বিনিয়োগ করে। বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের এই নতুন বিনিয়োগকারীরা ছিলো সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশের জনগণের বিরাট এক অংশ তাদের টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পর হঠাৎ শেয়ারের দাম কমতে শুরু করে। সে দাম কমার সূচক এতো নিম্নগামী হয় যে, শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে। হাজার হাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এ ঘটনায় পথে বসে। বহুজন শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অথচ বিদেশিরা সাধারণ জনগণকে নিঃস্ব করে শেয়ার বাজার থেকে ছয়-সাত হাজার কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়।
দেশি বহু কোম্পানিও টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলে। শেয়ার বাজার পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে পূর্বে কোনো সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেনি। জনগণকে শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে নিঃস্ব হতে তারা সাহায্যই করেছে; এভাবেই জনগণের টাকা মহল বিশেষের লুটেপুটে খাওয়ার এক নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি হলো বাংলাদেশে। বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এটা ছিলো ভয়াবহ বিপর্যয়।
হাসিনা সরকারের আমলে নানাভাবে বিদেশিদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশি তেল কোম্পানিগুলোকে তেল উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয়। হাসিনা সরকারের আমলের একটি বড় ঘটনা ছিলো বিদেশিদের দ্বারা মাগুরছড়া গ্যাস- ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ। উনিশশো সাতানব্বই সালের চোদ্দই জুন মাগুরছড়ায় মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল লিমিটেড-এর নিয়োগকৃত ঠিকাদার জার্মান কোম্পানি ডয়েটেগের কূপ খননের সময় এক ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে, সম্পূর্ণ গ্যাস ক্ষেত্রটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বহু ঘর-বাড়ি পুড়ে যায়। বারোশো একর বন পুড়ে ছারখার হয়।
বহু বন্য প্রাণী মারা পড়ে। বাংলাদেশের সম্পদ ও জনগণের বিশাল এই ক্ষতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সরকারের সহযোগিতায় অক্সিডেন্টাল কোম্পানি উনিশশো আটানব্বই সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনোকলকে সকল দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গোটায়। মাগুরছড়ায় গ্যাস বিস্ফোরণের যে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিলো তাতে দেখা গেছে, বিদেশি কোম্পানির দায়-দায়িত্বহীনতার কারণেই সেই বিস্ফোরণ ঘটে। সরকারি তদন্ত কমিটির হিসাব মতো শুধুমাত্র দেশের গ্যাস পুড়ে যাওয়া বাবদ অক্সিডেন্টাল লিমিটেডের কাছে বাংলাদেশ সরকারের পাওনা দাঁড়ায় তিন হাজার নয়শো কোটি টাকা। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে সে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো।” দেশের জনগণের স্বার্থ না দেখে তারা বিদেশি কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করছিলো কেন-সেটা ছিলো একটি বিরাট প্রশ্ন।
হাসিনা সরকারের আমলে দুর্নীতি বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছিলো এবং অতীতের সকল অবস্থাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। বিশ্বব্যাংক, দাতা সংস্থা সকলেই তখন বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর একানব্বইটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে শীর্ষস্থানে নিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই জাতীয় সংসদে এই দুর্নীতির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি সংসদে দেয়া ভাষণে বলেন, দেশে এক চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার রাজনীতি চলছে। পরীক্ষায় দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষকরা সম্পৃক্ত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতির সঙ্গে চিকিৎসকরা সম্পৃক্ত। আর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ঘুষ না হলে প্রধানমন্ত্রীর চাকরির সুপারিশও কার্যকর হয় না।
তিনি আরো বলেন, ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না।” হাসিনা সরকারের শাসন আমলে ব্যাংক থেকে হঠাৎ নগদ অর্থ শেষ হয়ে যায়। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পেতে থাকে। এই সরকারের শাসনামলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে যেমন সমতা রক্ষিত হয়নি তেমনি শ্রমশক্তি রপ্তানিও ক্রমান্বয়ে কমে যেতে থাকে। সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণের খবরও অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জুলাই থেকে সাতানব্বই সালের মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে দেশে দুই হাজার নয়শো চুয়াত্তরটি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।
উনিশশো আটানব্বই সালে নারী নির্যাতনের সংখ্যা ছিলো সাত হাজার তিনশো সাতাশি। নিরানব্বই সালে আট হাজার সাতশো দশ জন নারী ও শিশু নির্যাতিত হয়। এর মাঝে ধর্ষিত হয় তিন হাজার পাঁচশো নারী ও শিশু। গড়ে প্রতিদিন দশ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে বিশ জন ছাত্রী ধর্ষিত ও তিনশো জন যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। নিরানব্বই সালে প্রতিদিন গড়ে সাত জন খুন হয়েছে।
নিরানব্বই সালের মার্চ মাসে শুধু ঢাকায় খুন হয়েছে আটাশ জন এবং এপ্রিল মাসে এগারো জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। সরকারি দল কর্তৃক বিরোধীদলের ওপর চলে নানা ধরনের নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা প্রদান। সরকার পুলিশ ও দলীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা বিরোধী দলের প্রতিবাদ সভা, মিছিল, ঘেরাও কর্মসূচীতে ব্যাপকভাবে বাধা প্রদান করে।” সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা বহুবার আক্রমণ করে বিরোধী দলের সমর্থকদের ওপর।
বিরোধী দলকে নির্যাতন করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশ সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। প্রকাশ্য রাজপথে বিরোধী দলের একজন মহিলা কর্মীর শাড়ি পুলিশ টেনে খুলে ফেলে। সেই দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের পেটাতে দ্বিধা করে না পুলিশ। ঘটনাটা ঘটে উনিশশো নিরানব্বই সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি হরতাল চলাকালে। সরকারের মন্ত্রী ও মন্ত্রী-পুত্ররাও নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেয়। ঘর-বাড়ি জমি-জমা দখলের কাজে জড়িয়ে পড়ে।
হাসিনা ও খালেদা সরকারের আমলে যেমন বিদেশিদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছিলো, তেমনি দুটো সরকারের আমলেই বিচার ব্যবস্থা, ছোট-বড় আমলা, প্রশাসন-পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিলো সারা দেশ। সরকারি- বেসরকারি দুর্নীতি কোটিকোটি জনগণকে নিঃস্ব করে ফেলেছিলো। বেড়ে গিয়েছিলো সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন। নাট্যকারদের নাট্য রচনায় সে সকল ঘটনা কখনও স্থান পায়নি।
নব্বইয়ের দশকের দুটো সরকারের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো কখনও নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন আনসার বিদ্রোহ, সার সংকটে কৃষক বিদ্রোহ, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, মাগুরছড়ার বিস্ফোরণ-রাষ্ট্রের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নাটকে সামান্যতম স্থান পায়নি। স্থান পায়নি শেষিত জনগণের, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিদিনের সংগ্রামগুলো।
বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ইতিহাস হচ্ছে চরম নিপীড়ন ও বঞ্চনার ইতিহাস। নব্বই ভাগ শ্রমিকই এখানে মহিলা। ন্যূনতম বেতনে মহিলাদের এখানে কাজ করতে হয়। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চোদ্দ ঘন্টা এদের খাটানো হয়। অসুস্থতার জন্যও কোনো নির্ধারিত ছুটির ব্যবস্থা নেই। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শ্রমিকদের দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের সত্তরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে।
বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে সেই সব গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে বহু শ্রমিক পুড়ে মারা পড়ে, বহু নারী-শ্রমিক ধর্ষণের শিকার হয়, বহু শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে মারা যায়। বাম রাজনৈতিক দলগুলো সেসব শ্রমিকদের পক্ষে নানা ধরনের আন্দোলন গড়ে তুললেও বাংলাদেশের কোনো মঞ্চনাটকেই এসব ঘটনার কোনো চিহ্নমাত্র নেই। ব্যবসায়ী, কারখানা মালিক, মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ এবং প্রসাশনের বিরুদ্ধে নাটকে কোনো বক্তব্য নেই। ফলে এ কথা বলা যায়, নাট্যকর্মীরা তাদেরকে জনগণের শত্রু মনে করেননি। সাম্রাজ্যবাদকেও নাট্যকর্মীরা দেশের শত্রু মনে করেননি।
নব্বইয়ের দশকে যে সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে নাটক হয়নি তা নয়, বরং সমকালীন ঘটনাকে নিয়ে বেশি নাটক রচিত হয়েছিলো এই দশকেই। সেগুলো ছিলো সমকালীন সময়ের কিছু খণ্ডচিত্র মাত্র। নব্বইয়ের দশকে নাট্যকর্মীদের চোখে জনগণের, দেশ ও জাতির একমাত্র শত্রু ছিলো মোল্লারা, স্বাধীনতা বিরোধীরা এবং ফতোয়াবাজরা। যারা ক্ষমতা ভোগ করছে, যারা দেশ শাসন করছে তারা নয়। নব্বইয়ের দশকে নাটকের রাজনীতি একটি খাতেই বইতে শুরু করে, আর তাহলো স্বাধীনতা বিরোধীদের আক্রমণ করা, তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা। নাট্যকর্মীরা মনে করতে থাকেন, দেশের প্রধান শত্রু একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধীরা।
স্বাধীনতা বিরোধীদের শুধুমাত্র রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁরা দেশের মূল শত্রুদের আড়াল করেছেন। শ্রেণীশত্রুদের ব্যাপারটা নাটকে না এনে বিচ্ছিন্ন সব শত্রুদের নাটকের খলনায়ক বানিয়ে তুলেছেন। শ্রেণীসংগ্রামের যাঁরা শ্লোগান তুলেছিলেন, তাঁরাও এসময় শ্রেণীশত্রুর প্রশ্ন বাদ দিয়ে নাটক লিখছিলেন এবং তাঁদেরও মূল আক্রমণের লক্ষ্য ছিলো স্বাধীনতা বিরোধী চক্র।
নব্বইয়ের দশকে নাটকের বেশ কয়েকটি ধারার সাথে আমরা পরিচিত হই। তার মধ্যে একটি প্রধান ধারা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আশির দশকের শেষার্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নাটক মঞ্চায়নের যে-ধারা তৈরি হয়, নব্বইয়ের দশকের এসে সেটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়। সেই সাথে শেকড়ের সন্ধানের প্রশ্নটিকে সামনে এনে লোকজধারার নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শেকড়ের সন্ধান দুটো ধারাই খুব গুরুত্ব পায়। সাম্প্রদায়িক চেতনা ও মৌলবাদ বিরোধিতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই অংশ হয়ে দাঁড়ায়। নব্বইয়ের দশকে দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও লোকজধারাকে ঘিরে বেশির ভাগ নাট্যদলগুলোই কোনো-না-কোনো নাটক মঞ্চস্থ করেছে।
ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মান্ধ দলগুলোর উত্থান ও বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সুযোগ-সন্ধানী ও মোল্লাদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের ওপর যে আক্রমণ হয়-এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতেই ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’র চেতনা নাটকে দানা বাঁধতে থাকে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের একটি সম্মেলনের শ্লোগানই ছিলো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শ্লোগান। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সময় একাধিক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয় যার শিরোনাম দেয়া হয় ‘স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাট্য উৎসব’। থিয়েটার আর্ট রিপারটরী শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে উনিশশো তিরানব্বই সালে এক নাট্য উৎসব করে, সে উৎসবের শ্লোগান ছিলো ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে নাটক’।এ সকল উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিলো নাটকের দ্বারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা।
মামুনুর রশীদ রচিত ও আরণ্যক প্রযোজিত পাথর, জয়জয়ন্তী, কৃষণ চন্দরের গল্প অবলম্বনে কুশীলব প্রযোজিত গাদ্দার,’ মোক্তার হুসেন মোল্লা রচিত ও হবিগঞ্জে জীবন সংকেত প্রযোজিত বটবৃক্ষ, মান্নান হীরা রচিত ও হবিগঞ্জের খোয়াই থিয়েটার প্রযোজিত ইঁদারা, সফদর হাশমি রচিত ও চট্টগ্রামের থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত অপহরণ, চট্টগ্রামের মঞ্চমুকুট নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে আদাব, মিন্টু বসু রচিত ও বরিশালের খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত গৌরব গাঁথা ইত্যাদি ছিলো সাম্প্রায়িক সম্প্রীতির নাটক।
নাটকগুলোতে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ সে কথাও বলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বহু নাটকে বিভিন্ন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার করুণ চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকের ঘটনা যে সবসময় যুক্তিসঙ্গত বা সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলেছে তা নয়, কোনো কোনো নাটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদেরকেই দায়ী করা হয়েছে। তবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের জয়গানই ছিলো নাটকগুলোর প্রধান দিক।
জয়জয়ন্তী নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। মুক্তিযুদ্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত একটি হিন্দু পরিবার ভারত চলে গেলে মুক্তিযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজন মুসলমান কীভাবে তাদের সম্পত্তিকে আগলে রাখে তারই আবেগময় বর্ণনা হচ্ছে নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। কীর্তনীয়া একটি দল ও তার পরিবারের সদস্যরাই এই নাটকের একটি দিক। নবদ্বীপ কীর্তনীয়া দলের প্রধান। সেখানে মুসলমান একজন সদস্যও আছে দুলাল। দুলাল কীর্তনীয়া দলে বেহালা বাজায়। কীর্তনীয়া নবদ্বীপ ও দুলাল দুজনেই সঙ্গীত চর্চার কারণে সংসারের প্রতি উদাসীন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের অস্থির সময়ে কীর্তনীয়া দলের আসর বসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই দুঃসময়ে মুসলমান দুলাল ছাড়া সবাই নবদ্বীপকে ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে হিন্দুদের জন্য সময়টা ছিলো খুবই দুর্যোগপূর্ণ।
এ অবস্থায় নবদ্বীপ, ইন্দ্র আরো অন্যান্যরা ভারত চলে যেতে বাধ্য হয়। নবদ্বীপ যাবার আগে তার ঘরের চাবি শিষ্য দুলালের কাছে দিয়ে যায়, নবদ্বীপের বাড়ি-ঘর দেখাশুনার ভারও পড়ে দুলালের ওপর। দুলাল গুরুর সম্পদ রক্ষার জন্য জীবনপণ করে এবং নবদ্বীপের বাড়িতে থেকে যায়। স্থানীয় মুয়াজ্জিন ও শত্রুপক্ষের দালালরা দুলালকে মারার জন্য গাছের সাথে লটকে রাখে। পরে শত্রুপক্ষের সেনাকর্মকর্তা দুলালকে দেখতে পেয়ে গাছ থেকে নামিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলে।
দুলাল তবুও যায় না। সে সেনাকর্মকর্তাকে বলে, ‘এই গৃহ আমার গুরুর-এখানে আমার পদে পদে শৃংখল, এ গৃহটিকে আমার রক্ষা করা কর্তব্য’। নিজের জীবনের চেয়ে গুরুর গৃহ রক্ষা করাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। দুলাল গুরুর গৃহ রক্ষার জন্য নিজের কন্যাকে বিসর্জন দেয়, নিজের জীবন দান করে। নবদ্বীপ ফিরে এসে দেখে তার তুলসীতলা, গৃহ সবই সুরক্ষিত। মান্নান হীরার ইঁদারা গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে নন্দপুকুর নামক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। সে গ্রামে প্রতিবছর ফকির দরবেশের ওরশ হয়, বসে বৈশাখী মেলা। পরিত্যক্ত অবস্থায় কালের সাক্ষী হয়ে আছে গ্রামের একটি ইঁদারা। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের বাস।
হিন্দু সম্প্রদায়ের ধারণা পরিত্যক্ত এই ইঁদারার গভীর পাতাল থেকে ভেসে এসেছিলো প্রভু রামের ব্যবহৃত খড়ম। অপরদিকে মুসলমান সম্প্রাদায়ের ধারণা মক্কা শরীফের পবিত্র মাটি রয়েছে এই ইঁদারার গভীরে। নন্দপুকুর গ্রামের এক জননীর শিশু নিখোঁজ হলে পরে শিশুটিকে ঐ ইদারা থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু শিশুটির পরনের পোষাকের কারণে শিশুটি কার, কোন ধর্মের সে নিয়ে হিন্দু মুসলিম দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্মান্ধতার কঠিনতর বলি হয় মুসলমানের হাতে হিন্দু, আর হিন্দুর হাতে মুসলমান। মানুষের ধর্মান্ধতা এভাবেই প্রকাশ পায় এ নাটকে। নাটকের শেষে ধ্বনিত হয় সবার ওপরে মানুষ সত্য।
বটবৃক্ষ নাটকের গল্প গড়ে উঠেছে একটি বটগাছ ও তার নীচের দশ বিঘা জমিকে কেন্দ্র করে। ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ঐ গাছটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। এক কালে ঐ গাছের নীচে সাত রাত সাত দিন ধরে মেলা হতো। কাঞ্চনপুর গ্রামের প্রতিটি মানুষ ঐ মেলায় আনন্দে মেতে উঠতো। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মৈত্রির বন্ধন কাঞ্চনপুরের ঐ বটবৃক্ষ। বট তলার ঐ জমির ওপর নজর পড়ে গ্রামের প্রভাবশালী মাতব্বর হারেজ জোয়ারদারের। সে জমি দখলের জন্য খুন, জখম ও ফতোয়াবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সে বট গাছ কাটার চেষ্টা চালায় এবং মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে।
গাদ্দার নাটকের গল্প গড়ে উঠেছে সাতচল্লিশের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। লালগাঁও পাকিস্তানের একটি হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম, যেখানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃপ্রতীম সহাবস্থান। নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম বৈজনাথ চৌধুরী। একজন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত হিন্দু যুবক। জন্ম লাহোরে। লালগাঁও বৈজনাথের মামা-বাড়ী। এ গ্রামেরই একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে শমসাদ। মামা-বাড়ী বেড়াতে এসে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এক সময় শমসাদ ও বৈজনাথ দুজনার মাঝে গড়ে ওঠে মধুর এক প্রেমের সম্পর্ক। সেই সময় আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারত উপমহাদেশের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে।
নিতান্ত বাধ্য হয়েই বৈজনাথকে লালগাঁও ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় লাহোরে অবস্থানরত এক বন্ধুর বাড়িতে। মুসলিম বন্ধু-পত্নী হিন্দু বৈজনাথকে দেখে এতোটাই বিরক্ত বোধ করে যে, রাতের আঁধারে বৈজনাথকে গুণ্ডাদের দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্র করতেও কুণ্ঠিত হয় না। সবদিক বিবেচনা করে বৈজনাথের বন্ধু তাকে তার দাদার গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকেও বৈজনাথ চলে আসে।
সীমান্তবর্তী এলাকায় কাছাকাছি ইরাবতী নদী সাঁতরে পার হয়ে বৈজনাথের সাথে তার বাবার দেখা হয়। বাবার মুখে মায়ের মৃত্যুর সংবাদ এবং কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক ছোট বোন সূর্যকে ধরে নিয়ে যাবার ঘটনা বৈজনাথকে অস্বাভাবিক করে তোলে। উন্মাদ-প্রায় বৈজনাথ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। উন্মাদনা নিয়ে বৈজনাথ আবারও পথ চলে। চলার পথে একটি অঞ্চলে মুসলিম একটি অসহায় মেয়েকে ঘিরে কতিপয় হিন্দুর নির্মম পাশবিকতার জঘন্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং নিজেও তাতে অংশ নেয়।
ধীরে ধীরে বৈজনাথ আত্মস্থ হয়, পুনরায় স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে আসে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারীরা বসে নেই। ভয়ংকর ত্রাস সৃষ্টিকারী চিহ্নিত গুণ্ডা বিষ্ণু বৈজনাথকে আবারও প্রতিশোধপরায়ণ হতে এবং তার দলের একজন হয়ে কাজ করতে প্ররোচিত করে। বৈজনাথ তবুও সকল কূপমণ্ডুকতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্দ্ধে একজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন স্বাধীন মানুষ রূপে স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মামুনুর রশীদের পাথর নাটকটি একই রকম রাজনৈতিক সংকট ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকে ঘিরে রচিত। নাট্যকার পাথরকে সাধারণ মানুষের নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছেন।
সাধারণ মানুষের নির্ভরতাকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহল কী কী প্রক্রিয়ায় তাদের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালায়, এই বিষয়টির ওপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিপন্নতা ও রাজনৈতিক সংকটের একটি রোজনামচা নাটকটিতে প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রামের মঞ্চমুকুট, প্রযোজিত আদাব নাটকটি সমরেশ বসুর গল্পের নাট্যরূপ। আদাব গল্পে মূলত সম্প্রদায়িকতার ভয়াল রাতে পরস্পর মুখোমুখি দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুজন মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন ফুটে ওঠে। মানুষের বীভৎসতা ও মানবিক দিক দুটোরই প্রকাশ ঘটেছে সেখানে। নাটকগুলোর মধ্যে মননের পরিবর্তে ছিলো তীব্র আবেগ।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের লোকরা মনে করে থাকেন স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘটেছে ধর্মীয় উন্মাদনা। দালাল রাজাকাররাই ছড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারটিও জড়িত। সেই একই কারণে বহু নাটকেই স্বাধীনতা বিরোধীদেরকেই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য দায়ী করা হয়েছে। মূলত ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বাবরি মসজিদ সম্পর্কিত তৎপরতাই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিজেপি কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংস বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নতুন ভাবে মাথা চাড়া দিতে সাহায্য করে।
এই ঘটনাগুলো অবশ্য বাংলাদেশের মঞ্চায়িত নাটকে আসেনি। বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাই জামায়াতে ইসলামী ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নতুনভাবে মাঠে নামার সুযোগ করে দেয়। জামায়াতে ইসলামী নিজে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন না হলেও সে এ ঘটনাকে নিজের সংগঠনের স্বার্থে ব্যবহার করে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিজ দলের পক্ষে আনার জন্য। বস্তুতঃপক্ষে যে সমস্ত ঘটনা জামায়াতে ইসলামী দল সহ বিভিন্ন ধর্মীয় দলগুলোকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করেছে তার মধ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা অন্যতম। ৩৪ বাবরি মসজিদের ঘটনার পরই আমরা বাংলাদেশে মোল্লাতন্ত্রের ব্যাপক উত্থান ঘটতে দেখি এবং এ সময় থেকেই মোল্লাদের ফতোয়া দেয়ার ঘটনা শুরু হতে থাকে। বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের একটি স্মরণীয় ঘটনা মোল্লাদের দ্বারা বিভিন্ন ফতোয়া জারি।
নব্বই দশকের পুরো সময়কালটাই এই ফতোয়াজারি নিয়ে সারাদেশে খুব হৈ চৈ চলে। মূলত কোনো একটি বিষয়ে শরীয়তের বা কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে ফতোয়া। কোরান, হাদিস, ইজমা, কিয়াস-ইসলামের এ চারটি দিক সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিই শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধান দিতে পারেন। যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ফতোয়া দেয়া সংবিধান বিরোধী, তবুও একশ্রেণীর মোল্লা-মৌলভী ইসলামী বিধান অক্ষুণ্ণ রাখার নামে দেশের নিরক্ষর অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর মাঝে মধ্যেই ফতোয়া জারি করে তাকে রাষ্ট্রীয় আইনের বিকল্প করে তোলে। নব্বইয়ের দশকেই এই ফতোয়া জারি ব্যাপকতা পেতে শুরু করে।
নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক, বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহপূর্ব গর্ভধারণ, পর্দাপ্রথা, মহিলাদের চাকরি করা কিংবা পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ফতোয়া জারি করা হয়। ফতোয়া যে সবসময় ধর্মীয় কারণে জারি করা হয় তা নয়, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মব্যবসায়ী, মোল্লা-মওলানা, পীর-ফকির, গ্রাম্য মাতব্বর, ইমাম, মুয়াজ্জিন ইত্যাদি সুবিধাভোগীরা ফতোয়া জারির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। বিচারের নামে সাধারণ অসহায় মানুষদের ওপর তারা নানা ধরনের নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। যেমন দোররা মারা, মাটিতে পুঁতে ঢিল ছোঁড়া, ঝাড়ু দিয়ে পেটানো, চুল কামিয়ে দেয়া, জুতার মালা পরিয়ে পথে পথে ঘোরানো, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে প্রকাশ্যে প্রহার, আাগুনে পুড়িয়ে মারা, একঘরে করা, জানাজা-দাফন-কাফন করতে না দেয়া, গ্রাম থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি ফতোয়ার রায় হিসাবে কার্যকর করা হয়।
শরীয়তের বিধানের নামে অদ্ভুত সব বিধান চালু করে ফতোয়াবাজরা। যে-কোনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে যে-কোনো সময় তারা ঘোষণা দিয়ে দিতে পারে অবৈধ। সেক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রীরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়। যদি তারা আবার এক সাথে সংসার করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর হিল্লা বিয়ে বাধ্যতামূলক। হিল্লা বিয়ে ফতোয়াবাজদের তৈরি একটি ধর্মীয় বিধান, যেখানে বলা হয়েছে তালাক হওয়া স্বামীর সাথে আবার ঘর করতে হলে স্ত্রীকে মাঝখানে আর একজন পুরুষের ঘর করে আসতে হবে। হিল্লা বিয়ে বলে যে বিষয়টি আছে তা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফতোয়াবাজরা তাকেই প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। ফতোয়ার শিকার হয় মূলত নারীরা।
ফতোয়ার নামে নব্বইয়ের দশকে গ্রামের মানুষের ওপর এতোবেশি নির্যাতন চলে যে, ফতোয়া জারি নিষেধ করতে সরকার এর বিরুদ্ধে নতুন আইন তৈরি করতে বাধ্য হয়। ফতোয়া জারির ক্ষেত্রে বেশ কিছু নৃশংস ঘটনা ঘটে। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার নূরজাহানের স্বামী দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকায় স্থানীয় মাওলানা মান্নান তাকে বিয়ে করতে চায়। নূরজাহানের পিতা কন্যাকে অন্যত্র বিয়ে দিলে ঐ মওলানা বিয়ের পঁয়তাল্লিশ দিন পর বিয়েটি অবৈধ বলে ঘোষণা করে এবং শাস্তি স্বরূপ নূরজাহানকে মাটিতে পুঁতে তার ওপর একশো একটি পাথর নিক্ষেপ করার কথা বলে। ফতোয়ার রায় অনুযায়ী একশো একটি পাথর নিক্ষেপ করা হলে নূরজাহানের মৃত্যু ঘটে। নূরজাহানের বাবা-মাকে পঞ্চাশটি করে বেত মারা হয়।
বিয়েতে যারা উপস্থিত ছিলো তাদেরকে দশবার কান ধরে ওঠবস করানো হয়। ফরিদপুরের মধুখালী থানার দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামে তোরাব মোল্লার স্ত্রী নূরজাহানকে অন্য এক তরুণের সাথে প্রেম করার অভিযোগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ধান মলনের বাঁশের খুঁটির সাথে নূরজাহানের হাত-পা ও কোমর রশি দিয়ে বাঁধা হয় এবং চিৎকার না করার জন্য মুখে একখণ্ড কাপড় গুঁজে দিয়ে সারা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। বগুড়ায় ফরিদা, জালাল উদ্দিন ও রাশেদাকে ব্র্যাকের ঋণ নেয়ার অপরাধে একশো একটি করে দোররা মারা হয়। শতাধিক গর্ভবতী মহিলাকে ব্র্যাকের চিকিৎসা কেন্দ্রে না যাওয়ার ফতোয়া জারি করে বলা হয়, যারা যাবে তারা খ্রীস্টানদের খাতায় নাম লেখাবে এবং তাদেরকে গ্রাম ছাড়া করা হবে। গ্রামের তিনজন যক্ষা রোগী ফতোয়ার জন্য বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে।
আটাশ বছর বয়সী রোকেয়া নামে এক গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হলে স্থানীয় পীর তাকে হাসপাতালে না নিয়ে তার আস্তানায় পৌছে দিতে বলে। সেখানে ঝাড়ফুঁক, পানি পড়ার চিকিৎসায় রোকেয়ার শরীরে পচন ধরে এবং সে মৃত্যুবরণ করে। রোকেয়ার মৃত্যুর পর পীর ঘোষণা করে অগ্নিদগ্ধ হয়ে রোকেয়া শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে এবং সে স্বর্গে পরম সুখে বাস করছে।
কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের ষোলটি গ্রামের দুই হাজার পরিবারকে স্থানীয় ফতোয়াবাজরা একঘরে করে রেখেছিলো। সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেয়ার অপরাধে তাদের এ শাস্তি দেয়া হয়। এসব পরিবারের লোকদের হাটবাজার করতে ও সামাজিক কোনো কাজে অংশ নিতে দেয়া হতো না। মুমূর্ষু রোগীদের ডাক্তার দেখানোর অনুমতি পর্যন্ত মিলতো না। রাজশাহী জেলার তানোর থানার পাচন্দর ইউনিয়নের মনোয়ারা বেগমকে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে স্থানীয় ফতোয়াবাজরা পঞ্চাশটি দোররা মারে ও তার কাছ থেকে একহাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।
রংপুর লালকুঠি জামে মসজিদের ইমাম রুহুল আমিন ইমামতির পাশাপাশি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। স্থানীয় এক জামাতকর্মী ইমামের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে যে, ইমাম রুহুল আমিন নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য মেয়েদের মুখ দর্শন করে, কাজেই তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ হবে না। সেজন্য ইমামের পদ থেকে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।** মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার জান্না গ্রামের কহিনূর বেগমের প্রথম বিয়ে আদালতের মাধ্যমে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার চার মাস পর অন্য জায়গায় তার বিয়ে হয়। গ্রামের মাতব্বর ও ফতোয়াবাজরা কহিনূরের দ্বিতীয় বিয়ে মেনে না নিয়ে তাদের বিচারের আয়োজন করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই একশো একটি করে দোররা মারা এবং মাথা ন্যাড়া করে দেয়ার রায় প্রদান এবং তা কার্যকর করা হয়।
ঘটনার পর রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ও অপমানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আত্মহত্যা করে। ** ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় শিউলি নামের বাইশ বছরের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করলে স্থানীয় ফতোয়াবাজরা তার লাশ শরীয়ত মতো জানাজা, কাফন ও দাফন করতে বাধা দেয়। এ ঘটনায় অসহায় শিউলির পরিবার কোনো কিছু ছাড়াই লাশ সরকারি রাস্তার পাশে মাটিচাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।”” দিনাজপুরের হরিপুর থানার আকলী খাতুনের লাশও একইভাবে দাফন করতে দেয়া হয় না স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করায়। ফতোয়াবাজরা ঘোষণা দেয় আকলী খাতুন ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছে।” মাগুরা জেলার শালিখা থানার তালখড়ি গ্রামের কুতুবুদ্দিন নামে একজন যাত্রা শিল্পীকে ফতোয়াবাজরা যাত্রায় অভিনয় করার জন্য মসজিদে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এক ইমাম স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শরীয়ত মতে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেয়।
ফতোয়া জারির এমনি বহু ঘটনা পাওয়া যাবে। ফলে ফতোয়া জারির বিরুদ্ধে বহু নাটক এ সময় মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। দু একটি নাটকের সারাংশ তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত ও থিয়েটার প্রযোজিত মেরাজ ফকিরের মা, একই সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে রচিত। পলাশপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকের ঘটনা। এই গ্রামেরই এক সম্পন্ন গৃহস্থ মোজাহের মণ্ডল। মোজাহের এক সময় যাত্রাদলে অভিনয় করতো। সেই সময় যাত্রাদলের মালিক ধীরেন্দ্র নাথের মেয়ে আলোরানীর প্রেমে পড়ে মোজাহের। আলোরানীও ছিলো যাত্রাদলের অভিনেত্রী।
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সম্পর্ক ধীরেন্দ্রনাথ মেনে নিতে চায় না বলে মোজাহের ও আলো পালিয়ে এসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহের পর আলোরানীর পরিচয় ঘটে আলোবিবি হিসাবে। পরবর্তীতে মোজাহের নিজ গ্রাম, পলাশপুরে ফিরে এসে নির্বিঘ্নে ঘর-সংসার করতে থাকে। মোজাহের যে একজন হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেছে একথা গ্রামের লোকজন বা মোজাহেরের সন্তানরাও জানে না। মোজাহের ও আলোবিবির বড় সন্তান মেরাজ মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষ করে গ্রামে পীর হয়ে বসে এবং কট্টরভাবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। মোজাহেরের মেজ ছেলে সেরাজ শহরে চাকরি করে এবং তার স্ত্রী শহরের আর দশটি মেয়ের মতোই পর্দা ছাড়া চলাফেরা করে। এসব বেপর্দা মেরাজের পছন্দ হয় না।
মেরাজের ছোট ভাই পিয়ার যাত্রাদলে অভিনয় করে, সে কারণে মেরাজ তার ওপর খুবই ক্ষিপ্ত। গ্রামে পীর হিসাবে মেরাজ খুবই ডাকসাইটে। সেই গ্রামে মেরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন পীর আছে যার নাম গেদা ফকির। গেদা ফকির মেরাজের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, তবে মেরাজ পীর হবার পর থেকে তার পসার কমে গেছে বলে সে সবসময় মেরাজকে ঘায়েল করার মতলবে থাকে। মেরাজ পাকিস্তানভক্ত, সে মনে করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াটা ভুল হয়েছে। জিন্নাহ ছিলো একজন মহামানব।

দেশের সকল হিন্দুদের সে মুসলমান বানাবার স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় ধীরেন্দ্রনাথ পলাশপুর গ্রামে আসে মেয়েকে একবার শেষ দেখা দেখতে। তখন সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় আলোবিবি হিন্দুর মেয়ে। মেরাজ ফকির ইসলাম অনুশাসন মতে ছিলো মায়ের খুবই ভক্ত। মাকে সে সবসময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতো, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতো। সেই মা একদা হিন্দু ছিলো জেনে সে মাকে ত্যাগ করে। মেরাজের মা যে একদা হিন্দু ছিলো গেদু ফকির তা জানার পর এই সুযোগ কাজে লাগাতে চায় এবং মেরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।
নিজের ধর্মব্যবসা ঠিক রাখার জন্য মেরাজও মাকে হত্যা করতে চায়।
যখন তরবারি হাতে সে মাকে হত্যা করতে যায়, তখন গায়েবীভাবে কুরানের বাণী ভেসে আসে, যে গায়েবী বাণীতে মায়েদেরকে সম্মান জানাতে বলা হয়। মেরাজ গায়েবী আওয়াজ শোনার পর নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। এদিকে গেদু ফকিরের নির্দেশে তার লোকরা মেরাজের মা বাবা ভাই সকলকে বেঁধে ফেলে গ্রামে ফতোয়া জারি করে যে, মুসলমানের ছদ্মবেশে এক হিন্দু রমণী মুসলমানের সন্তান গর্ভে ধারণ করে বেশরিয়তি কাজ করেছে, সেজন্য সে বিধর্মী রমণীকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে পাথর মারা হবে।
লোকজন গেদু ফকিরের ফতোয়া অনুয়ায়ী আলোবিবিকে মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে সেখানে আসে মেরাজ, মেরাজ মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিজে পাথরের আঘাত সহ্য করে। এই সময়ে গ্রামের সচেতন যুবকরা মেরাজদের পরিবারকে রক্ষায় এগিয়ে আসে, গেদু ফকির ও তার দলবলকে ধরে শাস্তি দেয়। মেরাজ মাকে কথা দেয়, সে আর ধর্ম নিয়ে কখনও ব্যবসা করবে না।
ঘা নাটকের বিষয়বস্তুও গড়ে উঠেছে ফতোয়াবাজদের নিয়ে। ফুলবানু নামের এক অসহায় নারী গ্রামের মাতব্বর কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে স্বামীর কাছ থেকে পরিত্যক্তা হয়। কন্যা আদুরীর হাত ধরে ফুলবানু আশ্রয় নেয় বিধবা মা জয়তুনের কাছে। সেখানে ফতোয়াবাজ পীর ও গ্রামের ধর্মান্ধ সমাজপতিদের বিচারে সে চিহ্নিত হয় চরিত্রহীনারূপে। তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ দেয় স্থানীয় পীর। অপমানের হাত থেকে বাঁচতে ফুলবানু আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার পর পার হয়ে যায় বারো বছর। ফুলবানুর কন্যা আদুরী বড় হয়ে একটি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গ্রামে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়।
কিন্তু ধর্মান্ধ সমাজপতিরা অবাধ্য আদুরীকে শায়েস্তা করতে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে ধর্ম বিরোধী বলে ঘোষণা দেয় এবং তাদের উপর হামলা চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আদুরীও ধর্ষণের স্বীকার হয়। ফুলবানুর মতো সে আত্মহত্যার পথ বেছে না নিয়ে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়, হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। মানব সুরৎ নাটকের মূল গল্প গড়ে ওঠে বাউল ফকির শমসের আলীকে নিয়ে। বাউলের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তার লাশ পড়ে থাকে। কারণ ফতোয়া জারি করা হয় তাঁর জানাজা হবে না।
বলা হয় সে কোনোদিন নামাজ পড়েনি, শুধু সারাজীবন গান-বাজনা করে বেড়িয়েছে। অথচ সে যে কোনদিন নামাজ পড়েনি সে কথাও কেউ হলফ করে বলতে পারে না। যেহেতু সে গরীব-নিঃস্ব, তাই ধর্মীয় অনুশাসন তার ওপরেই চাপিয়ে দেয়া হয়। সকলে এই অন্যায় মেনে নেয় না, যখন রাত বাড়ে এবং কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে কিছু তরুণ। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে মসজিদে নেয়া হয়। নাটকের মূল গল্প এটাই তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে মুক্তিযুদ্ধ।
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, মোল্লাদের ফতোয়া দানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর ধর্মীয় নির্যাতন চালানো ও গোলাম আযমের নাগরিকত্ব লাভের ঘটনাগুলো নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিশেষভাবে অনুভূতিশীল করে তোলে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযমকে তাদের দলের আমীর নির্বাচন করায় এবং বাংলাদেশ সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করায় জনমনে যে ক্ষোভ দেখা দেয়, তার পরিণতি হিসাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক মঞ্চায়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে।
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বুঝতে পারে, স্বাধীন দেশে তারা কতোটা অসহায় এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা কীভাবে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে ফেলেছে। ফলে দালাল রাজাকারদের তারা প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার জন্য সাংস্কৃতিক জগতের লোকরা ঐক্যবদ্ধ হয়। সেক্ষেত্রে নাট্যদলগুলোই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ এই শিরোনামে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে একটি নাট্যোৎসবেরও আয়োজন করা হয়।
যদিও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত একানব্বইয়ের নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। সে সময় মোট তেত্রিশটি দল উৎসবে অংশ নেয়। তার মধ্যে পাঁচটি দলের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নাটক প্রযোজনা করেছে তেমন অনেক দল যেমন সে-সময় উৎসবে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়নি, তেমনি যারা উৎসবে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু দলের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নাটক থাকা সত্ত্বেও সেগুলো তারা উৎসবে প্রদর্শন করেনি। উৎসবের বাইরে সে সময় বিভিন্ন নাট্যদলে মুক্তিযুদ্ধের নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। সে সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিলো না। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এর সংখ্যা বাড়তেই থাকে।
বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান উনিশশো আটানব্বই সালে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে এবং সে উৎসবে মোট সাতান্নটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উনিশটি নাটকের বিষয়বস্তু রচিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ, ফতোয়াবাজি, রাজাকারদের উত্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কেন্দ্র করে।
এই নাটকগুলো হচ্ছে থিয়েটার প্রযোজিত আবদুল্লাহ আল-মামুনের মেহেরজান আর একবার, ঢাকা নান্দনিক প্রযোজিত টুলু হাবীবের গল্প অবলম্বনে সৈয়দ মহিদুর রহমানের নাট্যরূপ ঘা, ঢাকার সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রযোজিত ও মান্নান হীরা রচিত ভাগের মানুষ, চট্টগ্রামের তির্যক নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত ও শেখর সমাদ্দার রচিত তীর্থযাত্রা, নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার প্রযোজিত ও কুতুবউদ্দিন আহমেদ রচিত ঘর থেকে ঘরে, ঢাকার থিয়েটার সেন্টার প্রযোজিত ও মাসুম রেজা রচিত শামুক বাস, ঢাকার পদাতিক নাট্য সংসদ প্রযোজিত ও গোলাম সারোয়ার রচিত ক্ষেতমজুর খইমুদ্দিন, ঢাকার থিয়েটার আর্ট প্রযোজিত ও আজিজুস সামাদ রচিত বৃত্ত, চট্টগ্রামের অরিন্দম নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত ও শান্তনু কায়সার রচিত সাজন মেঘ,
হবিগঞ্জের জীবন সংকেত নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত ও হুমায়ুন আহমেদ রচিত ১৯৭১, কুশীলব নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত সাজু আহমেদের নাট্যরূপ গাদ্দার, ঢাকা সুবচন নাট্য সংসদ প্রযোজিত ও মামুনুর রশীদ রচিত রাষ্ট্র বনাম, সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত ও রফিকুল আলম রচিত মানব সুরৎ, ঢাকা থিয়েটার মঞ্চ প্রযোজিত ও কৃষণ চন্দরের গল্প অবলম্বনে মাসুম আজিজ রচিত কাঠের গড়া, বরিশালের খেয়ালী থিয়েটার গোষ্ঠীর প্রযোজিত ও মিন্টু বসু রচিত গৌরব গাঁথা, কুষ্টিয়ার অনন্যা’ ৭৯ নাট্যদল প্রযোজিত ও সুনীল কুমার রচিত আশ্রয়, রংপুর থিয়েটার প্রযোজিত ও শেখ আকরাম আলী রচিত এখনো যুদ্ধ, চট্টগ্রামের অঙ্গন থিয়েটার প্রযোজিত ও সনজিব বড়ুয়া রচিত পাথর প্রতিমা এবং ঢাকার নাট্যচক্র প্রযোজিত জাঁ পল সাত্রের প্রতীক্ষার প্রহর।
ঐসময় এর বাইরেও আমরা মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বহু নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখি। যার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের অরিন্দম প্রযোজিত সৈয়দ শামসুল হকের তোরা সব জয়ধ্বনি কর, থিয়েটার প্রযোজিত অবদুল্লাহ আল-মামুনের দ্যাশের মানুষ, থিয়েটার আর্ট রিপারটরী প্রযোজিত আজিজুস সামাদের বিদেশি গল্প অবলম্বনে রচিত কীর্তিনাশা, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত এরিয়ে ডর্ফমানের নাটকের বাংলা রুপান্তর মুখোস, ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত নাসির উদ্দীন ইউসুফের একাত্তরের পালা, সময় সাংকৃতিক গোষ্ঠী ও পাবনা ড্রামা সার্কল প্রযোজিত মান্নান হীরার একাত্তরের ক্ষুদিরাম, চট্টগ্রাম থিয়েটার প্রযোজিত দীপক চৌধুরীর আবার যুদ্ধ, খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত মিন্টু বসু রচিত ঘাতক চারদিকে ও ঐ মহামানব আসে, মহাকাল প্রযোজিত নাসিরউদ্দীন ইউসুফের গল্পের নাট্যরূপ ঘুম নেই।
থিয়েটার নব্বইয়ের দশকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের লেখা যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে তার মধ্যে রয়েছে দ্যাশের মানুষ, মেরাজ ফকিরের মা, মেহেরজান আর একবার। তিনটি নাটকই একই সূত্রে গাঁথা। মেরাজ ফকিরের মা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বাকি দুটি নাটক সম্পর্কে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তান সরকারকে কিংবা পাকিস্তানের সামারিক বাহিনীকে সহায়তা করেছে; স্বাধীনতার পর সেই রাজাকার আলবদরদের পুনরুত্থানকে নিয়ে রচিত। দুটি নাটকেই রাজাকার শব্দটিকেই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তিকে বোঝাতে। দুটি নাটকেই একটি ব্যাপার খুবই লক্ষণীয় যে, রাজাকাররাই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান শক্তি-এই কথাটা নাট্যকার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।
পাশাপাশি তুলে ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের অসহায় চরিত্র। প্রতিটি নাটকেই তিনি আবার সেই রাজাকার চরিত্রের পতনও দেখিয়েছেন, যা আমরা তাঁর আশির দশকে মঞ্চস্থ তোমরাই নাটকেও দেখতে পেয়েছিলাম। নাটকগুলোতে রাজাকারদের যে পতন দেখানো হয় সেটা নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা তবে বাস্তব নয়। নাট্যকার নাটকগুলোতে ইতিহাসের সত্যের চেয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নাটক দুটিতে বাস্তবতা যতটুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা দখল করে আছে নাট্যকারের আবেগ। আলাদা আলাদা ভাবে দুটি নাটককেই আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করবো।
দ্যাশের মানুষ নাটকে দেখা যায়, যুবসমাজ সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। দেশে কেউ ন্যায়নীতি মানছে না, সবাই দুর্নীতির মধ্যে আটকে আছে। নাট্যকারের সংলাপ অনুযায়ী রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক কেউ কারো কাজ করছে না, বা করতে পারছে না বা করতে দেয়া হচ্ছে না। জায়গার লোক জায়গায় নেই, তাই কথার মতন কথাও নেই। নাট্যকার অবশ্য সেই সাথে বলতে চান, ব্যতিক্রম শুধু ছাত্ররা। এদের মূল চরিত্র এখনও ঠিক আছে। নাটকের খলচরিত্র রহমত, সে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী সাহানাকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। রহমত দাবি করে জায়গার মালিক সে। সাহানার স্বামী যার কাছে থেকে এই জমিটা কিনেছিলো, সে আবার জমিটা রহমতের কাছেও বিক্রি করে।
কিংবা রহমত সবকিছু জেনে শুনেই জমিটা ক্রয় করে। তার কাছে জমির দলিলপত্র আছে। এদিকে সাহানার স্বামী জমিটা কিনলেও সাহানা বারবার বাড়ি বদলের কারণে জমির দলিলপত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাই রহমতের দখলদারির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মূল দলিল উদ্বারের চেষ্টায় সাহানা রেজিস্ট্রারের অফিসে যায়। ঘুষ ছাড়া তারা তাকে জমির দলিল দেয় না। সে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাহায্য চায়, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন কোনোই ক্ষমতা নেই। সেখান থেকে তাকে পরামর্শ দেয় একজন মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করবার জন্য, যে মন্ত্রী তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো এবং মন্ত্রী নিজেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। সাহানা বহু কষ্ট করে মন্ত্রী পর্যন্ত পৌছালেও মন্ত্রী তাকে গুরুত্ব দেয় না, তার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না।
সাহানা যখন সবদিক থেকে একেবারে নিরুপায়, উদ্ধারের আর কোনো পথ খোলা নেই, তখন তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে তার মৃত স্বামীর এক দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই, যে একজন রাজাকার। সে রাজাকার হলেও মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাকে তোয়াজ করে চলে। নাটকে এই লোকটির পরিচয় আর কে নামে। সাহানাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। রহমতকে সে সাহানার কাছে ধরে আনে এবং সাহানার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। কথিত এই রাজাকারের সামনে দাঁড়িয়ে রহমত একেবারে চুপসে যায়।
রহমত জানায় সে আর কখনও সাহানাকে বিরক্ত করবে না। ৫২ নাটকটির শেষে আর কে-র ক্ষমতা দেখে সাহানা অবাক হয়। সাহানা আর কে-র কাছে জানতে চায়, ‘একজন রাজাকার হয়ে এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন। এত ক্ষমতা আসে কোথেকে? পান কোথায়?’ আর কে-র উত্তর, ‘টপ সিক্রেট। জানতে চাইলে আপনাকে আরো কাছ আসতে হবে।’ সাহানা তখন রেগে গিয়ে বলে, ‘ঘৃণা করি। সেই একাত্তর সাল থেকে ঘৃণা করে এসেছি। আজও করি। এত ক্ষমতা, এমন ক্ষমতা কি করে তোমার হয়? কোথায় তোমার ক্ষমতার উৎস?’
সাহানার ক্রুদ্ধ প্রশ্নে আর কে জবাব দেয়, ‘আমার ক্ষমতার উৎস কখনও পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কখনও জয়বাংলা, কখনও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
সব জায়গাতেই আমি আছি। আমার সঙ্গে অবশ্য জনগণও থাকে। জনগণকে রাখতেই হয়।’ নাটকের শেষ সংলাপটি বলে আর কে যখন তার সাথের তরুণ কোরাস বাহিনীকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো, সে সময় কোরাসকে আর কের সাথে চলে যেতে বারণ করে সাহানা। কোনো কারণ ছাড়াই তারপর নাটকে দেখা যায়, কোরাস দলের ছেলেরা ফিরে আসে এবং ঢোলের তালে তালে পরিধেয় আলখাল্লা খুলে ফেলে। ভিতরে পরে থাকা তাদের সাদা গেঞ্জির গায়ে ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক’ ও ‘গণতন্ত্র মুক্তি পাক’ লেখা জ্বলজ্বল করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আর কে ভয়ে পালাতে চায়। এসময় কোরাস দলের ছেলেরা ও মেয়েরা ঢোলের তালে তালে আর কে-কে ধরে ফেলে এবং এক সময় তাকে নিষ্পেষিত করে ফেলে।
দ্যাশের মানুষ নাটকেও আমরা দেখতে পাই দেশের সমস্ত ক্ষমতার উৎস রাজাকাররা। দেশের সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিযোদ্ধারা পর্যন্ত। নাট্যকারের এ চিন্তা কতোটা সঠিক সে বিচারে না গিয়েও যদি আমরা নাটকের শেষ দৃশ্যে লক্ষ্য করি, তাহলে আর কের মৃত্যুটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। নাট্যকার নাটকে কোরাসকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। যদি আমরা কোরাসকে জনগণের প্রতিনিধি ধরে নেই তাহলেও প্রশ্ন জাগে সেই জনগণ সাহানার এক কথায় আর কের মতো ক্ষমতাধরকে হত্যা করবে কেন? পূর্বের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়, সাহানা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী জানা সত্ত্বেও তার পাড়ার ছেলেরাই রহমতের সাথে সাহানাকে উচ্ছেদ করতে আসে, তাকে ভয় দেখায়। সাহানার মেয়ের প্রতি খারাপ ইঙ্গিত করে।
আর সাহানা একের পর এক বিভিন্ন জনের কাছে অসহায়ের মতো আশ্রয় খোঁজে। সাহানা যেখানে রহমত আলীর মতো একজন দখলদারির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না, সেই সাহানার নির্দেশে রহমত আলীর চেয়ে বহু গুণ ক্ষমতাধর আর কে-কে যুবকরা মারতে যাবে কেন? সাহানা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, সম্পদশালীও নয়। জনগণ বা সমাজকেও সে সংগঠিত করেনি। সেই সাহানার ইঙ্গিতে আর কের এই মৃত্যু খুবই অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক। শোষকশ্রেণীর পরাজয় ঘটবে সেটা ঐতিহাসিক সত্য, কবে এবং সেটা কোন পথে ঘটবে এ ব্যাপারে নাট্যকারের চিন্তা খুবই বিভ্রান্তিকর।
মেহেরজান আর একবার নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যেও আবদুল্লাহ আল-মামুনের স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। মেহেরজান আর একবার নাটকেরও খলচরিত্র একজন স্বাধীনতা বিরোধী। নাটকের পটভূমিকা গড়ে উঠেছে সাধারণ একটি রেস্টুরেন্টকে ঘিরে। রেস্টুরেন্টের মালিক হরমুজ খুব ভালো মানুষ। সেই রেস্টুরেন্টের রান্না ঘরের সকল দায়িত্ব পালন করে মেহেরজান, মেহেরজানের মেয়ে পরী এবং পুত্রবধূ সখিনা। সখিনা বিধবা এবং হিটলার নামে তার একজন প্রেমিক রয়েছে। হরমুজের বন্ধু সিকদার একজন মুক্তিযোদ্ধা, সে খলনায়ক রাজাকার হাজী সাহেবের ট্রাক চালায়।
যখন ট্রাক চালাবার দায়িত্ব থাকে না, শিকদার তখন হরমুজের রেস্টুরেন্টেরই ওপর তলায় হরমুজের সাথেই থাকে। খাওয়াটাও হরমুজের রেস্টুরেন্টেই খায়। শিকদার ও হরমুজের ওপর মেহেরজানের খুবই প্রভাব। হাজী হচ্ছে এলাকার ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যাকে হরমুজ খুবই মান্যগণ্য করে। হাজীর দৃষ্টি পড়ে মেয়েদের দিকে। সেই নিয়ে বিরোধ বাধে হাজির সাথে শিকদার ও মেহেরজানের। শিকদার চড় মেরে হাজীর দাঁত ফেলে গা ঢাকা দেয়। হাজী প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুঁজে বেড়ায় শিকদারকে। হাজী শিকদারকে কিমা বানাতে চায় এবং ঘোষণা দেয় সে একাত্তর সালে বহু লোককে কিমা বানিয়েছে। সে রেস্টুরেন্টের গ্রাহক ভারতীয় একজন হিন্দু কানু।
হাজীর মতো বদর বাহিনীর লিডাররা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে বেঁচে আছে দেখে কানু অবাক হয়। মেহেরজানের বিধবা পুত্রবধূ সখিনার প্রেমিক হিটলার, হাজীর দল ছেড়ে সে চলে এসেছে। হিটলার দল ছাড়ায় হাজীর লোকরা সখিনাকে ধর্ষণ করতে চায়। সেজন্য চার চার জন যুবক অস্ত্র হাতে রেস্টুরেন্টে আসে, আর এক মেহেরজান বটির কোপে সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। বাস্তবে কতটুকু তা সম্ভব সে প্রশ্নটি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি বটি দিয়ে আগ্নেয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেতো, তাহলে এই বটি সব ঘরে ঘরে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সামান্য পর হিটলার আসে। মেহেরজান সখিনাকে হিটলারের হাতে অর্পণ করে। হিটলার যাবার আগে মেহেরজানের হাতে একটি স্টেনগান দিয়ে যায়।
এদিকে হাজী শিকদারকে ধরার জন্য নতুন ফন্দি আঁটে। সকলকে ক্ষমা করার কথা বলে। সে ঈদের সময় ঢাকায় থাকবে না সে কথাও জানিয়ে দেয়। হাজী নেই জেনে শিকদার ফিরে আসে রেস্টুরেন্টে। ফিরে এসে সে আবিষ্কার করে নিচ তলায় রাখা হাজীর বাক্সর মধ্যে রয়েছে প্রচুর অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে হাজী মৌলবাদ ও দালাল-রাজাকারদের পক্ষে একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে চায়। হাজী আসলে ঢাকা ছেড়ে যায়নি, সে পরিকল্পনা মতো রেস্টুরেন্টে চলে আসে তার দলবল নিয়ে। শিকদারকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর সে তার সঙ্গীদের হুকুম দেয় মেহেরজান ও তার মেয়েকে নগ্ন করতে। মেহেরজান এবার স্টেনগান চালিয়ে হাজীর শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়। আবদুল্লাহ আল-মামুনের মেহেরজান আর একবার নাটকেও এভাবেই শেষ পর্যন্ত রাজাকারের পতন দেখানো হয়।
নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের শেষের দিকে রচিত নাটকগুলোর একটি প্রধান দিক হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আবেগ এবং রাজাকারদের প্রতি অন্ধ ঘৃণা। মামুনের দৃষ্টিতে দেশের সকল দুর্ভোগের জন্য দায়ী প্রধানত রাজাকাররা। মামুনের এই বক্তব্য খুবই বিভ্রান্তিকর। স্বাধীনতার পর চার বছর দেশের ক্ষমতায় ছিলো আওয়ামী লীগ, পরের পাঁচ বছর দেশের ক্ষমতায় ছিলো মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান। যখন এরশাদ দেশের ক্ষমতায় আসে তখনও সংসদে স্বাধীনতা বিরোধীদের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। সেক্ষেত্রে দেশের দুর্ভোগের দায়-দায়িত্ব স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘাড়ে চাপানো কতোটা যুক্তিযুক্ত। মামুনের রচনায় তাই যতোটা ক্ষোভ ধরা পড়ে ততোটা ইতিহাসের সত্য নয়।
সেখানে যে রাজনীতিটি প্রকাশিত তা দর্শকদের সত্যিকার ঘটনার সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের কখনও তিনি খলচরিত্র হিসাবে দেখাননি। অথচ স্বাধীনতার পর আওয়ামী সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকরা যেভাবে ব্যক্তিস্বার্থে দেশের সম্পদ লুটপাট করেছে তিনি তাঁর সব নাটকেই সেই সত্যটি এড়িয়ে গেছেন। স্বাধীনতার পক্ষেরই একটি অংশ স্বাধীনতার পর শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু মামুন সচেতনভাবে সেই সকল চরিত্রের দোষগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র স্বাধীনতা বিরোধীদেরকেই অপরাধী হিসাবে দেখাচ্ছেন এবং তিনি যা বোঝাতে চান তাহলো সকলকে রাজাকারদের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে শুধুমাত্র আবদুল্লাহ আল-মামুন একা নয়, প্রধান-অপ্রধান প্রায় সকল নাট্যকাররাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকে দেশের সকল দুঃশাসনের দায়ভার স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছেন। তার আরো কিছু উদাহরণ আমরা দেবো।
নাসির উদ্দীন ইউসুফের একাত্তরের পালা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হলেও মূলত সাতাশি সালের ঘটনাই সেখানে বিবৃত। নাট্যকার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও তথ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির উত্থানকে নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকের মূল চরিত্র সৈয়দ আলী। ফুলছরি থানার সৈয়দ আলী নিম্নবিত্ত মানুষ। সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের ষোল বছর পরেও সে যুদ্ধের ঘোরে বাস করে। সৈয়দ আলীর পিতা মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা যায় ঘাতকদের দ্বারা। সৈয়দ আলী যখন যুদ্ধের মাঠে, সে সময় তাদের গ্রাম পাকবাহিনী ঘিরে রেখে সেখানে আগুন লাগায়। সেই আগুনে গ্রামের বহু ঘর-বাড়ি পুড়ে যায়। হালের বলদ, ফসলের মাঠ পুড়ে যায়, পুড়ে মরে ঘরের ভিতরের মানুষ আর মানুষের ছাওয়াল।
সেই আগুনেই পুড়ে মারা পড়ে সৈয়দ আলীর মা। স্বভাবতই যুদ্ধ শেষে সৈয়দ আলী পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ তার কমাণ্ডারের সাথে ফুলছরি থানা দখল করে। সে সময় মুক্তিযোদ্ধা ফারুক ও সৈয়দ মিলে স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর সদস্য ইজ্জত আলী মোল্লা ও হাজী শফিউদ্দিনকে স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য হত্যা করে। তারা চারশো বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিলো। চায়নিজ রাইফেল দিয়ে গ্রামের মানুষের দাবিতেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। একাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইজ্জত আলী মোল্লা ও অক্টোবর মাসে শফিউদ্দিনকে খতম করা হয়। যুদ্ধের শেষদিকে গোলার আঘাতে ফারুকের একটা পা উড়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যিনি সৈয়দ আলীর থানা কমান্ডার ছিলেন তিনিও মারা যান।
তাঁর ছেলে ছালাম সৈয়দ আলীর কাছেই থাকে। সৈয়দ আলী একজন ভূমিহীন কৃষক-ঘরের সন্তান, যাদের ঠিকমতো দুবেলা খাওয়া জোটে না। ফুলছরি থানার বর্তমান পুলিশ ইন্সপেক্টরটিও ষোল বছর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ফুলছরি থানার দারোগা ছিলো। সে ছিলো তখন পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থক ও. সহযোগী। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস পাক-সরকারের নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীতে সে কাজ করে। ফুলছরি থানায় কর্তব্যরত অবস্থায় সে ঐ এলাকার শত শত মানুষকে হত্যা করতে পাকবাহিনীকে সাহায্য করে। সৈয়দরা যখন থানা আক্রমণ করে দখল নেয় সে তখন পালিয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের ভুল ও আপোষকামী সিদ্ধান্তের সুযোগে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীতে এদেরকেই আবার নিয়োগ দেয়া হয়।
পনের ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ছিলো হানাদারদের দোসর সতের ডিসেম্বর মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে সে হয়ে যায় স্বাধীন দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর লোক। পুনরায় সে ফুলছরি থানার দায়িত্বে এসে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করতে থাকে প্রতিশোধ গ্রহণের আশায়। মুক্তিযুদ্ধের পর সৈয়দকে বাঁচার সংগ্রামে টিকে থাকতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেও সে চাকরি লাভ করতে পারে না। সাতাশি সালে সৈয়দ আলী ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দেবার চিঠি পায়। চাকরির আশায় সে ঢাকায় রওয়ানা হয়।
ঢাকায় এসে সৈয়দ আলী দেখতে পায় তাদের এলাকার সংসদ সদস্য তৈফুর রহমান তৈয়ব রাস্তার অদূরে একটি জটলায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, বর্তমান সরকার গণবিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, বিদেশি প্রভুর পা-চাটা স্বৈরাচারী সরকার। মুক্তিযুদ্ধের সকল আদর্শ বাদ দিয়ে সরকার একাত্তরের সকল শত্রু সম্পত্তি হানাদার পাকিস্তানিদের হাতে পুনরায় তুলে দেয়ার জন্য সংসদে বিল পাশ করিয়েছে যার মধ্য দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি প্রত্যাখান করা হয়েছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার।
সাংসদ তৈয়ব বক্তৃতা শেষ করলে সৈয়দ তাঁর সাথে দেখা করে। মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দের কাছে ভোটের ব্যাপারে সাংসদ তৈয়বেরও স্বার্থ আছে। সহজ-সরল সৈয়দ রাতের বেলা সাংসদের বাড়িতে থাকতে চাইলে সাংসদ বিরক্তির সাথেই সৈয়দকে বাড়ির ঠিকানা ও দশটা টাকা দেয় বাইরে খেয়ে নেবার জন্য। সৈয়দ যখন বাইরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সাংসদের বাড়িতে যায়, তৈয়ব তখন সরকারি দলের এক রাজাকার সাংসদের সাথে বসে মদ খাচ্ছিলো আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলো। সে আলোচনা থেকে বোঝা যায় তৈয়বের দল সরকার-বিরোধী আন্দোলন করলেও সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে খুবই ভালো।
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যই তারা মধ্যরাতে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সম্মতি দিয়েছিলো। সরকারও শর্ত মোতাবেক বিরোধী দলকে বেশ কিছু আসন ছেড়ে দেয়। সাতাশি সালে নির্বাচিত সেই বিরোধী দল রাজপথে সরকার বিরোধী মিছিল করলেও সরকার যাতে সব বিল সংসদে নির্বিবাদে পাশ করিয়ে নিতে পারে তার জন্য সংসদ বর্জনের খেলা খেলে সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়। দুজন সাংসদের এসব আলাপ-আলোচনাকালে সৈয়দ সেখানে উপস্থিত হয়। সৈয়দ যে একজন মুক্তিযোদ্ধা, সরকারি দলের সাংসদ সে কথা জানতে পেরে সেখান থেকে ভেগে পড়ে।
পরদিন সৈয়দ চাকরির জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানায় সাক্ষাৎ দিতে গেলে দারোয়ান তার কাছে ঘুষ চায়। সৈয়দ ঘুষ না দিলে দারোয়ান তাকে ঢুকতে দিতে চায় না। সৈয়দ ঘুষখোর দারোয়ানকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সরাসরি সে বড়কর্তার ঘরে হাজির হয়। বড়কর্তাকে সে ঘুষ গ্রহণ করে একজনকে চাকরি দিতে দেখে। সৈয়দ বড়কর্তাকে তার কাগজপত্র, দেখালে বড়কর্তা সৈয়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ আরম্ভ করে। বড়কর্তা জানতে চায় দেশ স্বাধীন হয়েছে কবে? সৈয়দ বলে একাত্তর সালে। বড়কর্তা সৈয়দের এই উত্তরে বিস্মিত হয়। সে তখন সৈয়দের কাছে জানতে চায়, তাহলে সাতচল্লিশ সালে কী হয়েছিলো?
সৈয়দের তখন সন্দেহ হয় লোকটি রাজাকার কি না। লোকটাকে তার চেনা চেনা লাগে। সে সময় অন্য একজন পরীক্ষার্থী সেখানে ঢুকে বড়কর্তার কাছে অনুরোধ জানায় চাকরিটি তাকে দেয়ার জন্য। সে বড়কর্তাকে আরো জানায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় সে আলবদর বাহিনীতে ছিলো, পঁচিশ নং সেকশনে। বড়কর্তার নির্দেশেই সে আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।
বড়কর্তা এ সময় চোখের সানগ্লাস খুলে ফেললে সৈয়দ লোকটিকে পুরোপুরি চিনে ফেলে। লোকটি হচ্ছে মঈনুদ্দিন। আলবদর বাহিনীর কমাণ্ডার। মঈনুদ্দিন উনিশশো একাত্তরের সালের ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং যুদ্ধবন্দী হিসাবে ভারত হয়ে পাকিস্তান গমন করে। উনিশশো একাশি সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশে অবস্থান করে ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে ফিরে আসে। ফিরে এসে দেশের ভিতর বিশাল ব্যবসা ফেঁদে বসে এবং গোপন একটি রাজনৈতিক দলের মূল পরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মঈনুদ্দিনের নির্দেশে শত শত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।
স্বাধীনতার পরপরই তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য পত্রপত্রিকায় আহ্বান জানানো হয়েছিলো। বিদেশে থাকার জন্য তখন তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। ‘সৈয়দ আলী মঈনুদ্দিনকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বভাবতই ফল হয় উল্টো, মঈনুদ্দিনের অফিসের লোকরা’ সৈয়দকে ধরে মারধর করতে থাকে। মারধর করার পর মঈনুদ্দিন সৈয়দকে মতিঝিল থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। মঈনুদ্দিন মিথ্যা অভিযোগ তোলে সৈয়দের বিরুদ্ধে যে, সে অস্ত্র হাতে তাকে খুন করতে এসেছিলো।
মঈনুদ্দিন থানায় একটি অস্ত্রও জমা দেয়। থানায় এসে সৈয়দ পুলিশের কর্মকর্তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে সে অপরাধী নয়, সে একজন স্বাধীনতা বিরোধীকে শুধু পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলো এবং পুলিশের উচিৎ ছিলো মঈনুদ্দিনকে গ্রেফতার করা। পুলিশ জানায় সময়টা একাত্তর সাল নয়, সাতাশি সাল আর বঙ্গবন্ধু তিয়াত্তর সালেই দালাল রাজাকারদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। সৈয়দ বলে মুজিব তাদের মাফ করেছে সাধারণ মানুষের অনুমোদন না নিয়ে। মুজিবকে সম্মান না দেখানোতে পুলিশের কর্মকর্তা ধমক লাগায় সৈয়দকে। সে বরং সৈয়দের কাছে জানতে চায়, যে পিস্তল দিয়ে সে মঈনুদ্দিনকে আক্রমণ করতে গিয়েছিলো সে পিস্তল সৈয়দ কোথায় পেয়েছে। সৈয়দকে পুলিশ কর্মকর্তা সম্মান না দেখালেও মঈনুদ্দিনকে খুব সম্মান দেখিয়ে কথা বলে।
সবশেষে পুলিশ কর্মকর্তা পাঁচটি খুনের জন্য সৈয়দকে দায়ী করে। সৈয়দ আলীর বিরুদ্ধে মঈনুদ্দিনকে অস্ত্র হাতে খুনের চেষ্টা করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। সেই সাথে ধর্ষণ, হত্যা ও ডাকাতির মামলায়ও তাকে জড়িয়ে দেয়া হয়। সৈয়দ আলীর বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয় যে, উনিশশো উনআশি সালে সে ইজ্জত আলী মোল্লা ও হাজী শফিউদ্দিনকে হত্যা করে।
সে অভিযোগে বলা হয়, সৈয়দ আলী দলবলসহ ডাকাতির জন্য গভীর রাতে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ইজ্জত আলী মোল্লার বাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং সর্বস্ব লুট করে ফিরে যাওয়ার সময় চায়নিজ রাইফেল দিয়ে নিরীহ ইজ্জত আলী মোল্লাকে হত্যা করে। গণ্যমান্য ব্যক্তি হাজী শফিউদ্দিনকে একইভাবে একই অস্ত্র দিয়ে সেদিনই হত্যা করা হয়। সেই খুনের পর থেকে পুলিশ সৈয়দ আলীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। মঈনুদ্দিনকে খুন করতে গিয়ে অবশেষে সে ধরা পড়ে। সত্যিকার অর্থে ইজ্জত আলী ও শফিউদ্দিনকে হত্যা করা হয়েছিলো উনিশশো একাত্তর সালে। ফুলছড়ির পুলিশ ইন্সপেক্টর পুরানো প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ‘৭১’ কে ‘৭৯’ করে দেয় সামান্য হেরফের করে।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী নিজেও একজন স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি। সৈয়দকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগে। মঈনুদ্দিন আদালতে এসে সাক্ষী দেয় সৈয়দ তাকে হত্যা করতেই গিয়েছিলো। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী প্রমাণ করতে চায় যে, অভিযুক্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বাদী একাত্তর সালে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিলো। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই সে একাত্তরের অপরাধী কুখ্যাত খুনী মঈনুদ্দিনকে হাতের কাছে পেয়ে নিজেকে সামলাতে পারেনি এবং সেজন্যই তার ওপর আক্রমণ চালায়।
মঈনুদ্দিনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, যাদের হাতে খুন হয়েছে তিরিশ লক্ষ মানুষ, যারা পুড়িয়ে দিয়েছে শস্যক্ষেত্র, খামার আর লক্ষ কোটি মানুষের ঘর, যারা লক্ষ জননীর জরায়ুতে ঢেলেছে বিষাক্ত বিষ। বাদী পক্ষের আইনজীবী তার উত্তরে জানায়, তার মক্কেল যদি একাত্তরে কোনো অপরাধ করেও থাকে তবে উনিশশো তিয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে সে সকল অপরাধ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। সে বলে, বাহাত্তর সালের পর একজন রাজাকারকে হত্যা করার অধিকার কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্র দেয়নি। বাহাত্তর সালের পর হতে রাষ্ট্র এবং সংবিধান দেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকারকে সংরক্ষিত করে আসছে। বিবাদীর আইনজীবী জানায়, গোটা জাতিকে উপেক্ষা করে যে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো তা একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না।
রাষ্ট্রের যে সাত কোটি মানুষ একাত্তরে তাদের লক্ষ লক্ষ মা, ভাই-বোন, সন্তান, স্ত্রী ও বন্ধুকে হারিয়েছে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাদেরকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি তদানীন্তন সরকার। সে আদালতের কাছে প্রশ্ন রাখে, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যার সহযোগী তাদেরকে বিচার না করে ক্ষমা করা কোন মহানুভবতা? মানুষ হত্যা করা, লুট করা, নিজের জাতির বিরুদ্ধে লড়াই, সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা তবে অন্যায় নয় বরং এসবের জন্যই তাহলে কাউকে পুরস্কৃত করা হবে?
বিবাদী পক্ষের আইনজীবী প্রমাণ করতে চায়, ইজ্জত আলী ও সফিউদ্দিনকে উনআশি সালে হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে একাত্তর সালে। নিহতদের পুত্ররা আদালতে এসে সাক্ষী দেয় তাদের পিতা নিহত হয়েছে উনআশি সালে আর তাদের হত্যা করেছে সৈয়দ আলী। ফুলছরি থানার ইন্সপেক্টরও একই কথা বলে সাক্ষী দিতে গিয়ে। সেভাবেই সে সৈয়দ আলীর বিরুদ্ধে কাগজপত্র জমা দেয়।
সৈয়দ আলীকে জেল হাজতে আনা নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান তাকে জেলখানায় না নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যায় এক অজ্ঞাত স্থানে। সেখানে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় যাতে সে আদালতে সত্যি কথা না বলে বাদী পক্ষের দেয়া সব অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর ওপরেও আক্রমণ চালানো হয়। সৈয়দ বুঝতে পারে স্বাধীনতার ষোল বছরের মধ্যে দেশটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। দেশের সব কিছু বদল হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা হেরে গেছে। বিবাদী পক্ষের আইনজীবীও বুঝতে পারে স্বাধীনতা বিরোধীদের দখলে চলে গেছে দেশ। তবুও সৈয়দকে সে বাঁচাতে চেষ্টা করে। সৈয়দ আলীর পক্ষে আদালতে এসে সাক্ষী দেয় পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ফারুক।
সে জানায় সৈয়দ আলী আর সে মিলে একাত্তর সালে ইজ্জত আলী ও সফিউদ্দিনকে হত্যা করেছে। তাতে কোনোই ফল হয় না। বিচারক বাদী পক্ষের দেয়া সাক্ষী ও কাগজপত্রের ভিত্তিতে সৈয়দ আলীর মুত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। একাত্তরের একজন অপরাধীর বিচার চাইতে গিয়ে ফাঁসীর দড়ি গলায় পড়ে সৈয়দ আলী। স্বাধীনতা বিরোধীদের মুক্তিযোদ্ধা নিধনের ষড়যন্ত্র এভাবেই সফল হতে থাকে।
কাঠের গড়া নাটকে একইভাবে দেখানো হয় স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানকে। কৃষণ চন্দরের ট্যাক্সি ড্রাইভার অবলম্বনে রচিত কাঠের গড়া নাটকটির কাহিনী মূলত বিচার ব্যবস্থার উপর। বিচারের নামে প্রহসন, বিনা বিচারে জেলা খাটা, আইনের মারপ্যাঁচে নিরীহ জনগণ কতটুকু অসহায়, তারই একটি চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। ট্যাক্সি ড্রাইভার নবাব আলী মাসের পর মাস কোর্টে হাজিরা দিচ্ছে তবুও বিচার পাচ্ছে না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সবকিছু একই ধরনের বক্তব্যকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে আশ্রয় নাটকটি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধা তথা সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।
অপরদিকে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তারাই লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়েছে, হয়েছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত। এটাই এ নাটকের প্রধান বক্তব্য। পাশাপাশি দেখানো হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি চাঁদ গাজী এখনো স্বাধীনতা বিরোধী অপকর্মে লিপ্ত। মুক্তিযোদ্ধা বাবার ছেলে সোহাগ চাঁদ গাজীর এ ধরনের অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়। সেখানে প্রশাসন চাঁদ গাজীর হাতের পুতুল।”

রাজাকারদের উত্থানকে নিয়েই রচিত হয়েছে এখনো যুদ্ধ নাটকটি। এ নাটকেও দেখানো হয়, মুক্তিযুদ্ধকে বারবার কলুষিত করছে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু রাজাকার আলবদরের দল। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এই পরাজিত শত্রুরা। হায়েনা আর শকুনদের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সবার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে প্রজন্মের মাঝে সঠিক ইতিহাস তুলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে এখনো যুদ্ধ নাটকে।
রাষ্ট্র বনাম নাটকে বহু ঘটনার পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের উত্থানকে বড় করে দেখা হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন, আইন, ধর্ম, ইত্যাদি যাঁতাকলে পিষ্ট এই বাংলাদেশের ছোট্ট একটি গ্রামের গুটি কয়েক মানুষের বঞ্চনা আর অসহায়ত্বের চালচিত্র রাষ্ট্র বনাম। প্রভাবশালী একজন ব্যক্তির মৃত্যু কতগুলো চরিত্রকে রাষ্ট্রের প্রচলিত শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলে। এ যেন সহস্র গেরোতে বাঁধা এক গোলক ধাঁধা। একটি মৃত্যু, তার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তীতে আদালতে সত্য-মিথ্যার বোলচাল, আদালতের বাইরে ঘটে যাওয়া ষড়যন্ত্র সব কিছুর মধ্যে আরো অসহায় হয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। স্বাধীনতা বিরোধীরাই এর জন্য দায়ী। নতুনভাবে উত্থান ঘটেছে তাদের, সকল কিছু তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।
সেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও কেউ কেউ যুদ্ধ করে যায় মুক্তির জন্য পরাজয় নিশ্চিত জেনেও।মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলে বিশেষ করে আবদুল্লাহ আল- মামুনের নাটকগুলো, যে সত্যটি বের হয়ে আসে তা হলো ধর্মীয়ভাবে যারা উন্মাদ, যারা স্বাধীনতা বিরোধী তারাই মূলত এদেশের ক্ষতি করছে। তাদের চক্রান্তেই দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের লোকরা। স্বাধীনতা বিরোধীরাই সারা দেশে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে।
বিশাল বিশাল সব সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছে সারা দেশ দখল করে নেয়ার জন্য। বাংলাদেশের ইতিহাস কিন্তু এই বক্তব্যকে সত্য বলছে না। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসাবে আমরা যাদের নাম পাই, যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য সারা দেশে আলোচিত তাদের কেউ জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলো না। বরং স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি বলে পরিচিত আওয়ামী লীগেরই সদস্য ছিলো তারা। তাদের কেউ কেউ আবার সংসদ সদস্যও ছিলো। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য আর যাদের নাম পত্রপত্রিকায় দেখা যায় তারা হলো বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী। নকব্বইয়ের দশকে পুলিশ বাহিনী সন্ত্রাস সৃষ্টি ও সন্ত্রাসকারীদের লালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে।
বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলও সন্ত্রাসীদের লালন করে থাকে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জাতীয় পার্টির নাম প্রথমে আসবে। মামুনের বা অন্যান্যদের নাটকে তাদের অপরাধ তুলে না ধরে শুধু মাত্র স্বাধীনতা বিরোধীদের ওপর সন্ত্রাসের সকল দায় চাপিয়ে দেয়াটা কোনো বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়। বরং তা সত্যের অপলাপ মাত্র। রাষ্ট্রের ভিতর সন্ত্রাস সৃষ্টি সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকের বক্তব্য যে কী পরিমাণ অসত্য এবং পক্ষপাতদুষ্ট তা বোঝানোর জন্য বাংলাদেশের কিছু সন্ত্রাসী চরিত্রদের নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, যারা নব্বইয়ের দশকে খুবই আলোচিত হয়ে উঠেছিলো।
সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য নব্বইয়ের দশকে সব চেয়ে আলোচিত চরিত্র হয়ে উঠেছিলো খুলনার এরশাদ শিকদার, ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষীপুরের আবু তাহের, চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া-মেহেরপুর অঞ্চলের নুরুজ্জামান লাল্টু। জয়নাল হাজারী সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছিলো উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকেই। এরশাদ সিকদার সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে আশির দশকে। লাল্টুরও সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিতি ঘটে উনিশশো পঁচাশি সালে। সন্ত্রাসী হিসাবে আবু তাহেরের নাম শোনা যায় নব্বইয়ের দশকের আওয়ামী শাসনের শুরু থেকেই। এই চারজনের তিনজনই আওয়ামী লীগের সদস্য, নুরুজ্জামান লাল্টু নিজেই একটি রাজনৈতিক দল চালাতো।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপর উনিশশো বাহাত্তর সালের শুরু থেকেই জয়নাল হাজারী ফেনী শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বাহাত্তর সালের শেষের দিকে সে শহরের ট্র্যাংক রোডের জিরো পয়েন্টে আবু মিয়ার হোটেলে ভাত খাওয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আবু নাসেরকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় এনে শত শত মানুষের সামনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এ ঘটনায় বিব্রত হয়ে বাধ্য হয় নিজ দলের হাজারীকে গ্রেফতার করতে। উনিশশো তিয়াত্তর সালে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ভেঙে জাসদ ছাত্রলীগ জন্ম নিলে ফেনীর আওয়ামী ছাত্রলীগে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়।
সেই সময় সরকারি দল হাজারীকে কারাগার থেকে বের করে এনে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন স্থানীয় যুবলীগের সদস্য করে দেয়। হাজারী জেল থেকে বের হয়ে এসে ফেনীর প্রশাসনকে সরকারি মদতে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে থাকে। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনির প্রশ্রয়ে সে ফেনীর গডফাদার হিসাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং তার মাস্তানী, সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজির দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। পঁচাত্তরে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে হাজারী ফেনী থেকে আগরতলা পালিয়ে যায়। বহুদিন সে দেশের বাইরে পলাতক থাকে। পরে জিয়া সরকারের আমলে উনিশশো উনআশি সালের নির্বাচনের সময় সে ফেনীতে ফিরে আসে এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করে। এরপর সে বাংলাদেশেই বসবাস করতে থাকে।

উনিশশো বিরাশি সালে সামরিক শাসক এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করলে সারাদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই সুযোগে জয়নাল হাজারী এরশাদ সরকারের বিরোধিতার নামে তরুণ ও যুবকদের সমন্বয়ে স্টিয়ারিং বাহিনী নামে এক সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলে। সেই বাহিনীই পরবর্তীতে ব্যাপক আকার লাভ করে এবং যার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজার। সেই বাহিনীর সাহায্যে জয়নাল হাজারী একের পর এক খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ডাকাতি, প্রতিপক্ষের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নেতা-কর্মীদের দেশান্তরীকরণসহ বহু অন্যায় করেছে বলে পত্রপত্রিকায় দেখা যায়।
নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে হাজারী ফেনীতে এতোই ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে যে খুব কম লোকই তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে সাহস পায়। পুলিশ-প্রশাসন হাজারীর এতোই নিয়ন্ত্রিত ছিলো যে, হাজারীর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করে ফল পাওয়া যেতো না। শহরের চারটি ভবনে হাজারীর নির্যাতন সেল ছিলো যেখানে প্রতিপক্ষকে ধরে এনে নির্যাতন চালানো হতো বা প্রয়োজনবোধে হত্যা করা হতো। দুটি ভবনের একটি ছিলো সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন, অপরটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন। দুটিই হাজারী দখল করে রেখেছিলো তার নির্যাতন সেল হিসাবে। প্রশাসন এসব ব্যাপারে ছিলো সম্পূর্ণ নীরব। বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত এই সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারী নব্বইয়ের দশকে আওয়ামী লীগের একজন সাংসদও ছিলো।
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ২ ]
বাংলাদেশের আর একজন বহুল আলোচিত সন্ত্রাসী খুলনার এরশাদ শিকদারের উত্থান জাতীয় পার্টির শাসনামলে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মাহমুদুল হাসান ছিলো তার ক্ষমতার উৎস। ঘাটের কুলিগিরি দিয়ে যার কর্মজীবন শুরু, সেই এরশাদ শিকদার আশির দশকের প্রথম থেকেই বিরাট সম্পত্তি ও ক্ষমতার মালিক হয়ে উঠেছিলো।
চোরাচালানি, মাদকদ্রব্য পাচার এবং অবৈধ ব্যবসা করে সে মালিক হয় কোটি কোটি টাকার। উনিশশো তিরাশি থেকে আটানব্বই সাল পর্যন্ত সময়কালে এরশাদ পাঁচশো বিশ কোটি কালো টাকার মালিক হয়ে বসেছিলো। প্রায় একহাজার জনের ব্যক্তিগত সশস্ত্রবাহিনী ছিলো তার, আর ছিলো তিনশোর বেশি আধুনিক অস্ত্রের ভাণ্ডার। বিভিন্ন জায়গায় এরশাদের যে ঘাঁটি ছিলো সেখানে পুলিশ ঢুকতেও সাহস পেতো না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারানো, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো, ভোটকেন্দ্র দখল করা, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভীতি প্রদর্শন করে মানুষকে দিয়ে ভোট প্রদান, মানুষ খুন করা এসব কাজে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই এরশাদ শিকদারকে টাকা দিয়ে ভাড়া করতো। এরশাদ শিকদার বা তার বাহিনী কোথাও কোনো হামলা চালাতে গেলে সেখানে বিনা অনুমতিতে পুলিশ যেতে পারতো না।
এরশাদ শিকদারের অস্ত্রের একটি বড় চালান আসতো পুলিশ, বিডিআর বা বাংলাদেশ রাইফেলস-এর কাছ থেকে। পুলিশ ও বিডিআর সীমান্ত পথে আক্রমণ চালিয়ে যেসব অবৈধ অস্ত্র পেতো সেগুলো এরশাদ শিকদারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হতো। পরবর্তীতে সে নিজেও অস্ত্র ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে মাফিয়া চক্র ভারত থেকে অস্ত্রের চালান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতো। এভাবেই সে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য চক্রের মাফিয়া ডন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বার্মা থেকে মাদক দ্রব্য, গোলাবারুদ, সোনা, আফিম, চরস, হেরোইন, গাঁজা ও অস্ত্র চোরাই পথে নিয়ে আসতো খুলনায় এবং বিভিন্ন পথে ভারতে পাচার করতো সোনা, মূর্তি ও সীমানা পিলার।
বহু সংখ্যক মানুষ হত্যার অভিযোগ রয়েছে এরশাদ শিকদারের বিরুদ্ধে। হত্যার ক্ষেত্রে এরশাদ নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতো। রাইফেলের বাট দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শরীর থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করে নিজ হাতে প্রতিপক্ষকে সে হত্যা করেছে। কখনও কখনও প্রতিপক্ষকে পিটিয়ে আধমরা করে শক্ত হয়ে যাওয়া সিমেন্টের বস্তার সাথে বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হতো, যাতে লাশ খুঁজে না পাওয়া যায়। জীবন্ত লোকদেরকেও সিমেন্টের বস্তায় বেঁধে ডুবিয়ে মারা হতো। সাপ্তাহিক এক পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, একাত্তরের ঘাতক চক্রের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে এরশাদ শিকদারের হত্যাযজ্ঞ।
খুলনার ঘাট এলাকা ও রেলওয়ে এলাকার অসংখ্য বস্তিতে বাস করতো যে দেড়-দুহাজার পরিবার, যাদের সদস্য সংখ্যা ছিলো চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার, তারাই ছিলো এরশাদ শিকদারের অনুগামী। যাদের বেশিরভাগ ঘাটের কুলি, রিক্সাচালক, ছোটখাট দোকানদার, রেস্টুরেন্ট ও গাড়ি-ওয়ার্কশপের শ্রমিক। শিকদার এই লোকগুলোকেই মাদকদ্রব্য পাচার, চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চুরি ও সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহার করতো। এলাকার সবাই ছিলো এরশাদ শিকদারের প্রজার মতো। শিকদারকে তারা যেমন মান্য করতো, তেমনি শিকদারের কাছ থেকে বিপদে- আপদে নানারকম সাহায্যও পেতো।
খুলনায় এরশাদ শিকদারের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো পুলিশের। পুলিশের ডি আই জি ও কমিশনারদের সাথে ছিলো তার সুসম্পর্ক, নিয়মিত তারা আর্থিক সুবিধা পেতো। ঈদের আগে এরশাদ শিকদার পুলিশ কর্মকর্তাদের ঈদ-বোনাস দিতো। এরশাদ শিকদারের বিরুদ্ধে যতো মামলা হয়েছে পুলিশ বলেছে এরশাদ শিকদার পলাতক, অথচ পুলিশের চোখের সামনেই এরশাদ মিছিলে যোগ দিয়েছে, সংবাদ সম্মেলন করেছে, বিভিন্ন হামলা চালিয়েছে।
পুলিশ বহুবার তাকে গ্রেফতার করতে গেলেও বড় কর্তাদের নির্দেশে আবার ফিরে আসতো। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী দল ছাড়া আর তিনটি প্রধান দলের সাথেই এরশাদ শিকদারের সংশ্লিষ্টতা ছিলো। জাতীয় পার্টি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্পিকার আবদুর রাজ্জাকও তাকে সাহায্য ও সমর্থন জোগায়। জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতাচ্যুত হলে আওয়ামী সরকারের আমলে উনিশশো সাতানব্বই সালের এপ্রিল মাসে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষ এরশাদ শিকদারকে তেইশটি মামলার পলাতক ও সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। তারপরেই সাতানব্বইয়ের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে সার্কিট হাউসে পুলিশের উপস্থিতিতে সে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়।
সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক, হুইপ এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা, মন্ত্রী মনুজান সুফিয়ান, খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ। ক্ষমতার বলয়ে তার অবস্থান সব সময়ে সুসংহত ছিলো তাই সে ছিলো পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে।
কথিত এরশাদ শিকদারের দেহরক্ষী নূরে আলমের স্ত্রী হীরা বেগমের বক্তব্য থেকে জানা যায়, একদিন হীরাকে দেখে এরশাদের ভালো লেগে যায়। সে তখন নূরে আলমকে দিয়ে হীরাকে ডেকে পাঠায়। হীরা এলে নূরে আলমকে বলে তৎক্ষণাৎ হীরাকে বিয়ে করতে। নূরে আলমকে এরশাদ একপ্রকার বাধ্য করে হীরাকে বিয়ে করতে। বিয়ের পর সে নূরে আলমকে বিয়ের কেনাকাটা করতে পাঠায় তারপর হীরার ওপর বলাৎকার করে এবং হীরাকে জানিয়ে দেয় নিয়মিত এসে সে এরশাদকে দেহসঙ্গ দিয়ে যাবে। এরশাদের ভয়ে হীরা তাই করতে বাধ্য হয় এবং একদিন নূরে আলমের চোখে ধরা পড়ে যায়।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 7 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/নব্বইয়ের-দশক-মধ্যবিত্তের-নাট্যচর্চার-শেষ-পরিণাম-পর্ব-২--1024x536.jpg)
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ২ ]
তখন নূরে আলমকে এরশাদ জানিয়ে দেয়, সে নূরে আলমে সাথে হীরাকে বিয়ে দিয়েছে তাকে নিয়মিত ভোগ করা জন্য। হীরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এভাবেই এরশাদ হীরাকে তার সাথে দেহসঙ্গ দিতে বাধ্য করতো। হীরার প্রতিবাদ করার সাহস ছিলো না। নূরে আলমও এরশাদের ভয়ে এই জবরদস্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেই ধরনের একজন লোকই আওয়ামী লীগের সমর্থন পায় এবং সে দলের সদস্যপদ লাভ করে। যদিও আবদুল্লাহ আল-মামুন বা অন্যান্যদের নাটকে সন্ত্রাসী হিসাবে এই চরিত্ররা অনুপস্থিত। সকলেই তাঁরা একমাত্র স্বাধীনতা বিরোধীদেরকেই সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের অসত্যতা প্রমাণের জন্যই আমরা আরো কিছু উদাহরণ টানবো।
নব্বইয়ের দশকে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ভীষণভাবে আলোচিত ছিলো নুরুজ্জামান লাল্টু। উনিশশো তিয়াত্তর সালে মন্টু ও লাল্টু দু ভাইয়ের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা কারাগার ভেঙ্গে পালায় একশো বায়ান্নজন কয়েদী। সেই থেকে শুরু হয় দু ভাইয়ের গোপন জীবন। পরে নিজেদের আশ্রয়ের স্বার্থে দু ভাই যোগ দেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের গণবাহিনীতে। উনিশশো পঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মন্টু-লাল্টু বাহিনী চুয়াডাঙ্গা সদর থানার একটি গ্রামে গুলি করে সাতজন পুলিশের বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। মেহেরপুর ট্রেজারী লুট করতে গিয়ে মন্টু নিহত হলে লাল্টু দলের হাল ধরে। পরে লাল্টু গ্রেফতার হয় এবং উনিশশো উননব্বই সালে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু করে। নানাভাবে তখন সে হয়রানির শিকার হয়। উনিশশো বিরানব্বই সালে সে জাসদ নেতা আবদুল মজিদের সহযোগিতায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখায়।
তারপর সে হয়ে ওঠে সে অঞ্চলের বিভীষিকা। লাল্টু বাহিনীর হাতে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ সব ধরনের অপরাধ ঘটতে থাকে। হাট-বাজার, বিল-বাওড় ও অবস্থাপন্ন মানুষের কাছ থেকে সে আদায় করতে থাকে লাখ লাখ টাকা। উনিশশো পঁচানব্বই সালের জুন মাসে দামুড়হুদা থানার কুলবিলা গ্রামের আটজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করায় দলের সাথে লাল্টুর মতবিরোধ হলে সে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। উনিশশো সাতানব্বই সালে চাপড়া থানা পুলিশ বিএসএফ-এর অস্ত্র লুটের ঘটনায় লাল্টুকে গ্রেফতার করে। পরে সে জামিনে ছাড়া পায় ও নিজ এলাকায় ফিরে এসে পুরানো লোকজনদের নিয়ে নিজ বাহিনী দাঁড় করায়।
উনিশশো আটানব্বই সালের পহেলা ডিসেম্বর থেকে কথিত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু হয়। প্রভাবশালী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লাল্টু হয়ে ওঠে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের ত্রাস ও মৃত্যুদণ্ডদাতা। পুলিশকে দেখা যায় লাল্টুকে নিরাপত্তা দিতে। পুলিশ প্রশাসন লাল্টুর অনুগত বাহিনী হিসাবে কাজ করতো, লাল্টুর নির্দেশে পুলিশ অনেক সময় লাল্টুর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হয়রানি অভিযান চালাতো। লাল্টুর মুখের কথাই ঐ সকল অঞ্চলে আইন হয়ে যেতো। কেউ বিরুদ্ধতা করলে তাকে প্রাণ দিতে হতো। লাল্টুর নৃশংসতা আর বর্বরতার শিকার হয়ে বিগত তিন দশকে কমপক্ষে দু শতাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ইটের ভাটায় পুড়িয়ে মারা ছিলো তার শাস্তি দানের একটি বড় কৌশল।
শেষবার লাল্টুর উত্থানের পেছনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মদত ছিলো। সরকারি সমর্থন পাওয়ার কারণেই জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা লাল্টুর বশ্যতা মানতে বাধ্য হয়। সাংবাদিকরা সব কিছু জানলেও লিখতে ভয় পেতো। লাল্টু প্রসঙ্গে আলোচনায় এখানে উল্লেখ্য যে, লাল্টুর স্ত্রী ছিলেন চুয়াডাঙ্গার একমাত্র সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। লাল্টুর ভাই মন্টুও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের কাছে সেই লাল্টু ছিলো এক দানবের প্রতিরূপ।
লক্ষীপুর আওয়ামী লীগের আবু তাহের মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলো মুজিববাহিনীর সদস্য। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখনই সে লক্ষীপুরের সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসাবে পরিচিত হয়। চার বছরে লক্ষীপুরে তাহের বাহিনীর হাতে খুন হয়েছে আটত্রিশ জন, যার মধ্যে আওয়ামী লীগেরই লোক চব্বিশ জন।
লক্ষীপুর থেকে সকল বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের তাহের উৎখাত করেছিলো প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে। লক্ষীপুর বিএনপির নেতা নুরুল ইসলামকে তাহের বাহিনী লক্ষীপুর স্কুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর তার লাশ টুকরো টুকরো করে মেঘনা নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। প্রশাসনের জ্ঞাতার্থে এসব ঘটেছিলো এবং প্রশাসন তা রোধ করার চেষ্টা করেনি। লক্ষীপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে একলাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিলো তাহের বাহিনী। দিতে দেরি হওয়ায় তার তরুণী স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় এক বিকেলে। পরদিন সেই ব্যবসায়ী টাকা দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন রাতভর তাহের বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারে মৃতপ্রায় তাঁর স্ত্রীকে।
লক্ষীপুরের শ্যামপুরে এক বিরোধী দলীয় নেতাকে খুঁজতে যায় তাহের বাহিনী। টের পেয়ে সে নেতা পালিয়ে যায়। সেই নেতাকে না পেয়ে তার স্ত্রী ও মেয়েকে একসঙ্গে ধর্ষণ করে তাহেরের লোকজন। খোদ আওয়ামী লীগ এক নেতার কন্যাকে ধর্ষণ করেছিলো তাহেরপুত্র বিপ্লব। তার কোনো বিচার হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা যাদের ঘরে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ছিলো তারা পরিবার নিয়ে লক্ষীপুরে থাকতো না। সরকারি মদতে লক্ষীপুরে তাহেরের কথাই ছিলো আইন। পুলিশ-প্রশাসন তাহেরের সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু করবার ক্ষমতা রাখতো না। বরং ডিসি এসপিরা তাহেরের সাম্রাজ্যেই যেতো ফুর্তি করতে।
চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসাবে খ্যাত আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু ছিলো আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলের আওয়ামী লীগের সভাপতি। একটি খুনের মামলায় সে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে পলাতক ছিলো, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সে আবার দেশে ফিরে আসে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সে একজন পরিচালক ও সভাপতি ছিলো, ঋণ খেলাপী হিসাবে তার পরিচালক ও সভাপতির পদ চলে যায়।
উনিশশো নিরানব্বই সালে সে ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সভা চলাকালে সন্ত্রাসীদের নিয়ে সভায় হামলা করে এবং ব্যাংকের সভাপতিসহ পাঁচজন পরিচালককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ এ সময় পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে পায়নি। বরং আখতারুজ্জামান বাবু ব্যাংক দখল করে পুলিশের প্রহরায় নিজের গাড়িতে গিয়ে ওঠে। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আখতারুজ্জামানের পক্ষ নেন। বাবু যেমন সেদিন অস্ত্রধারী মাস্তান দিয়ে ব্যাংক দখল করে তেমনি ব্যাংকের সভায় যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁরাও ছিলেন অস্ত্রধারী।
বহু কোটিপতি এ ধরনের নেতা ও মাস্তানদের খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদের সাথে জামায়াতে ইসলামী বা কোনো ধর্মান্ধ দলের সম্পর্ক নেই। যারা মৌলবাদী নয়, স্বাধীনতা বিরোধীও নয়। যেমন আদমজী জুট মিল, সেখানে শ্রমিক নেতারা হয়ে উঠেছে এক একজন বিরাট সন্ত্রাসী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। অথচ এরা কেউই স্বাধীনতা বিরোধী নয় বা জামায়াতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে সম্পর্কিত।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 8 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ২ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-২.jpg)
সারা দেশ জুড়ে যে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণ, শিশু পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ দেখা দেয় তার সাথে দলীয়ভাবে জামায়াতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের সম্পর্ক খুব কম পাওয়া যাবে। বরং ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জাতীয়তাবাদী দলের নাম বা তাদের নেতা কর্মীদের যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের আলোচিত সন্ত্রাসী আসলাম, যে সুইডেন আসলাম নামে পরিচিত, চুরানব্বই সালের অক্টোবরে আসলাম খুন করে মামুন ও তার দুই সঙ্গী গোপাল কর ও নূরুকে। মামুনকে হত্যা করার কারণ আসলামের স্ত্রী আসলামকে ছেড়ে গিয়ে বিয়ে করে মামুনকে।
মামুন নিজেও ছিলো একজন সন্ত্রাসী। সুইডেন আসলাম সাতাশি সালে খুন করে শাকিলকে, তিরানব্বই সালে বিপুলকে ও সাতানব্বই সালে গালিবকে। প্রথম সে ছিলো জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের ক্যাডার। পরবর্তীতে সে অন্যদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। জামায়াতের যে সন্ত্রাসী বাহিনী নেই তা নয়। বিরাট সন্ত্রাসী বাহিনী তাদেরও রয়েছে। যারা নানা রকম হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত। যাদের নিষ্ঠুরতার নানা খবর রয়েছে।
নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বা অন্যান্য নাট্যকারদের যে বক্তব্য, স্বাধীনতা বিরোধীরাই সারা দেশে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে সে বক্তব্য সঠিক নয়। বিভিন্ন দলেই সন্ত্রাসীরা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত বহু ব্যক্তিও পরবর্তীকালে বড় বড় সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ঢাকার পুলিশ কমিশনার এ কে আল-মামুন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কালোটাকার মালিকরাই সন্ত্রাসীদের গডফাদার। কালো টাকাই সন্ত্রাসীদের টিকিয়ে রাখে।” নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বা তাঁর মতো আর যাঁরা দেশের সকল অপরাধের দায়-দায়িত্ব মৌলবাদী বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে ফরহাদ মজহার লিখছেন, বলা হয় সমাজে দুটো ‘পক্ষ’ আছে।
একপক্ষে আছে ‘মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি’ আর অন্য পক্ষে আছে ‘একাত্তরের ঘাতক-দালাল’। নিজ শ্রেণীর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ নামক মতাদর্শ বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, এই সত্যটা এখন আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। তিনি আরো লিখছেন, ‘আমি তাদেরকেই মুক্তিযুদ্ধওয়ালা বলছি, যারা মুক্তিযুদ্ধকে নিছকই তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে এবং সচেতনভাবে সমাজের শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামকে ধামাচাপা দেবার কাজে ব্যবহার করেছে’। ফরহাদ মজহার তার বক্তব্য দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, যারা ‘স্বাধীনতা বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিকে’ দেশের সমস্ত জাতীয় দুর্দশার জন্য দায়ী করছেন তাঁরা আসলে নিজ স্বার্থে দেশের শোষকদের প্রধান একটা অংশকে আড়াল করে রাখছেন।
স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানে নাট্যদলগুলো তাদের মঞ্চায়িত নাটকে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানের পেছনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করছে না। কখনও কখনও সযত্নে তা এড়িয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো স্বাধীনতার পর থেকে যেসব শাসকরা ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ। স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক ও প্রতিনিধিরাই এই রাষ্ট্রে সব থেকে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই ব্যবসায়ীরা বা বণিক পুঁজির মালিকরা প্রথম দিকে তো বটেই এমনকি সবসময়ই কালো বা বে-আইনী টাকার মালিক হিসাবেই তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে ও ব্যবহার করছে। চোরাকারবার, চোরাচালান, ইনডেন্টিং, ব্যাংক ঋণের টাকা আত্মসাত এদের দ্বারাই হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষেও এরা অবস্থান করছে।”
এই সকল লোকরা সকলেই স্বাধীনতা বিরোধী নয়, বরং এদের বড় অংশটিই স্বাধীনতার পক্ষের লোক, অনেকে মুক্তিযোদ্ধা। ফলে দেশের সকল অনিষ্টের দায়-দায়িত্ব স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াটা ইতিহাসের বিকৃতকরণ। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং তাদের শাসনের ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয়ে আসছে। আওয়ামী লীগ, বাকশাল, মুশতাক, জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া বা পরবর্তী শাসনের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য অথবা গুণগত পার্থক্য শ্রেণীচরিত্রের দিক থেকে তো ছিলোই না, উপরন্ত প্রতিটি সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত নীতিই কার্যকর করে এসেছে।”
এরা সকলেই যেমন জনগণের ওপর শোষণ চালিয়েছে তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারেও ভূমিকা রেখেছে। এবং এই সকল শাসকদের শ্রেণীস্বার্থই স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানকে দ্রুতগতি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সব নাটকের বিষয়বস্তু ছিলো প্রায় একই রকম, যার মূল বক্তব্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মানুষ আজ ভুলে গেছে।
স্বাধীনতা বিরোধীরা যখন ক্ষমতার বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে, যখন মন্ত্রী হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি হচ্ছে, জনগণ তখন তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে না। বিভিন্ন নাটকগুলো তাই স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি দর্শকদের ঘৃণা জাগিয়ে তুলবার জন্যই স্বাধীনতা বিরোধীদের অতীতের কার্যাবলী তুলে ধরেছে। স্বাধীনতার সময়কার নিষ্ঠুরতাকে চিত্রায়িত করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে ঘৃণা ছিলো নাট্যকর্মীরা আবার তা মানুষের মনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন নাটকের নানা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সে-সব আবেগের সাথে পরিচিত হবার জন্য এখানে আমরা আরো কিছু নাটকের ঘটনা তুলে ধরবো।
বিশেষ করে মান্নান হীরার একাত্তরের ক্ষুদিরাম নাটকে দেখবো কীভাবে তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে স্বাধীনতা বিরোধীদের সম্পর্কে। সে ঘৃণা এতোই প্রবল যে, নাট্যকার নিজের চিন্তাকে বহুসময়ই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, নাটকের ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জন করে ফেলেছেন। চরিত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে সাদা আর কালোতে রূপান্তরিত হয়েছে।
মান্নান হীরার একাত্তরের ক্ষুদিরাম নাটকে দেখা যায়, স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান আমলে কীরকম দুঃসময় পার করেছে বাঙালীরা।। সোনামুখী গ্রাম হচ্ছে এ নাটকের স্থান। সোনামুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ দপ্তরী নৃপেন, বাপ-মা বংশ পরিচয়ে ঠাঁই মিলবে না। দেশগেরামের মানুষরা তাকে পালাকার হিসাবে চেনে। সে ঐতিহাসিক চরিত্র ক্ষুদিরাম নামে একটি নাটক লিখেছে।
ভারতের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম মুজাফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা মেরে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ঘটনার সময় সঙ্গে ছিলো প্রফুল্ল চাকী। বোমাটি তারা মেরেছিলো কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য। কিংসফোর্ড সে ঘটনায় মারা যায় না, বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সোনামুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে একুশ বছর ধরে প্রতিবছর সে নাটকটা মঞ্চস্থ হয়ে আসছে।
সোনামুখী স্কুলের পণ্ডিত শিক্ষক খোকন ব্যানার্জী চৌত্রিশ বছর ধরে ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করছে। সে প্রতিবছর ঐ ক্ষুদিরামের চরিত্রে অভিনয় করে থাকে। শহরের লোকজন তাই তার মূল নাম খোকন ব্যানার্জী ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষুদিরাম হিসাবেই চেনে। রাস্তা-ঘাটে, বাজারে তাকে সর্বত্র সম্বোধন করা হয় ‘বৃদ্ধ ক্ষুদিরাম’ বলে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে একাত্তরের মার্চ মাসে ক্ষুদিরাম নাটকের মহড়া চলছিলো সোনামুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। ক্ষুদিরামের চরিত্রে অভিনয় করছিলো আলাল। ছাত্রদের পাঠ মুখস্থ হয়েছে, সাজপোষাক তৈরি সম্পন্ন-দুদিন বাদেই নাটক। এমন অবস্থায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডেকে পাঠায় খোকন ব্যানার্জীকে। সেখানে স্কুলের উর্দু শিক্ষক মৌলানা হাফিজুর রহমানও বসে আছে। প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে খোকন ব্যানার্জী জানতে পারে যে, মৌলানা হাফিজুর রহমান একটি নতুন নাটক লিখেছে। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একটি নাটক লিখেছে জেনে খোকন ব্যানার্জী খুশি হয় এবং নাটকটি পড়ে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বলে, নাটকটি শুধু পড়ে দেখলেই হবে না, সেটাই হবে ঐ বছর স্কুলের বার্ষিক নাটক। প্রধান শিক্ষকের কথায় ব্যানার্জী বিস্মিত হয়।
প্রধান শিক্ষককে সে জানায়, কাল বাদে পরশু বার্ষিক নাটক হিসাবে ক্ষুদিরাম মঞ্চস্থ হবে, ক্ষুদিরাম মঞ্চস্থ করার জন্য সব কিছু ঠিকঠাক। মৌলানা হাফিজুর রহমান তখন ভয় দেখিয়ে বলে, ক্ষুদিরাম নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না। ক্ষুদিরাম একটি হিন্দু চরিত্র। ক্ষুদিরাম মঞ্চস্থ হলে কারো ঘরের চাল থাকবে না, পা থেকে মাথা অব্দি হাড়গুলো আলাদা হয়ে যাবে। তার লেখা নাটকটিই মঞ্চস্থ করতে হবে। তার নাটকটি উপমহাদেশের একজন বীরযোদ্ধা মহামানবকে নিয়ে লেখা। ব্যানার্জী বলে, যেহেতু নাটকটি উপমহাদেশের একজন মহামানবকে নিয়ে লেখা তাই সে আগে নাটকটি পড়ে দেখবে। মৌলানা তখন খোকন ব্যানার্জীর কাছে জানতে চায়, নাটকটি উর্দুতে লেখা, সে ভাষা তার জানা আছে কি না। খোকন মৌলানার এ বক্তব্যে আরো বিস্মিত হয়।
সে বলে, নাটক হতে হবে মাতৃভাষায়। সে কথাই বলে গেছেন নটসম্রাট গিরিশ ঘোষ। প্রধান শিক্ষক এতক্ষণে জানায়, স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত মৌলানার লেখা উর্দু নাটকটিই করতে হবে এবং খোকন ব্যানার্জীকেই সে নাটক মঞ্চায়নের দায়িত্ব নিতে হবে। খোকন জানায় যে সে উর্দু জানে না। মৌলানা বলে, সে তাকে উর্দু শিখিয়ে নেবে।
মৌলানার বেয়াই, ফল ব্যবসায়ী উর্দুভাষী বোখারী সেই সময় সেখানে- প্রবেশ করে। বিনা অনুমতিতে সে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে প্রবেশ করে জানায় যে, সে এইমাত্র এসডিও সাহেবের সাথে সভা করে এসেছে। তাদের ধারণা, স্কুলে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতটি খুব অবহেলার সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবহেলা পাকিস্তানের সংহতির প্রতি অবহেলার সামিল। সেজন্য করাচি থেকে একদল লোক এসেছে কীভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে সেটা দেখিয়ে দেবার জন্য। প্রয়োজনে স্কুলের শিক্ষকরাও তা শিখে রাখবে। সে সাতদিন পর এসে পরীক্ষা নেবে।
প্রধান শিক্ষক বোখারীর কাছে জানতে চায়, স্কুলের যে-কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য স্কুল কমিটি আছে, বোখারী কেন এসবের মধ্যে নাক গলাচ্ছে? বোখারী জবাব দেয়, বাঙালীরা সব বেঈমান, গাদ্দার। বোখারীর এ ধরনের বক্তব্যে ক্ষেপে যায় প্রধান শিক্ষক। সে বোখারীকে জানিয়ে দেয়, স্কুলের ব্যাপারে নাক গলানো তার জন্য ঠিক নয়। বোখারীও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, বিহার মুলুক থেকে সে বাংলায় এসেছে, মালাউনদের সাথে কোনোরকম আপোষ সে সহ্য করবে না। দরকার হলে সবাইকে জবাই করে ফেলবে। কথাটা বলেই উত্তেজিত বোখারী চলে যায়। মৌলানা বোখারীর পক্ষ নিয়ে প্রধান শিক্ষককে বলে, বোখারীকে ক্ষেপিয়ে দেয়াটা তার ঠিক হয়নি।
মৌলানা খোকন ব্যানার্জীকে তার উর্দু নাটকটি মঞ্চায়নের আয়োজন করতে বলে এবং এতক্ষণে খোকন ব্যানার্জীকে জানায়, তার নাটকের নায়ক পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। খোকন সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটি শূন্যে ছুঁড়ে মারে এবং মৌলানাকে জানায়, জিন্নাহ যে নাটকের নায়ক সে নাটক স্পর্শ করতে তার গা ঘিন ঘিন করে। উর্দু শিক্ষক এ ঘটনায় ক্রোধান্বিত হয়।
চারদিকে তখন স্বাধিকার আন্দোলন চলছে। জয় বাংলা শ্লোগানে সবদিক মুখরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ পথে-ঘাটে মিছিল করছে। সোনামুখী গ্রামের স্কুলে তখন ক্ষুদিরাম নাটকের মহড়াও চলছে। উর্দু শিক্ষক ঘোষণা দিয়েছে, ক্ষুদিরাম মঞ্চস্থ করা হলে সোনামুখী কারবালা হয়ে যাবে। আর খোকন ব্যানার্জীর কথা, যতদিন বাঙালী থাকবে ততোদিন ক্ষুদিরাম মঞ্চস্থ হবে। ক্ষুদিরামের ভূমিকায় অভিনয় করছে যে আলাল তার মামা মন্টু ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। সে সোনামুখী গ্রামে এসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বোঝাচ্ছে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে। সে জানায়, এখন বাঙালীদের হাতে অস্ত্র নেই, অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। পুলিশ, আনসার, ইপিআর-রা স্বাধীনতার পক্ষে। সোনামুখীতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হবে, একটি মেয়েদের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে ছেলে ও মেয়েদের পাশাপাশি যুদ্ধ করতে হবে।
সোনামুখী স্কুলে সন্ধ্যায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলে আর তার আগে নাটকের মহড়া। উর্দু শিক্ষক এ ঘটনায় ক্ষেপে যায়। সে আর তার বেয়াই মিলে খোলা তলোয়ার হাতে বাঙালীদের নিধনের পরিকল্পনা করে। বোখারী জানায়, কাফেরের রক্তে গোছল করতে হবে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় সে হায়দারাবাদে তলোয়ার দিয়ে শত শত লোককে জবাই করেছে। উর্দু শিক্ষক বলে, মুসলমান বাঙালীরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাফের। সে বাঙালীদের হত্যা করার ব্যাপারে বিহারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে বলে। ঢাকাতে এদিকে পাকবাহিনী আক্রমণ শুরু করলে সারা দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সোনামুখীতে মন্টুরা থানা দখল করে নেয়, এদিকে বোখারী ও উর্দু শিক্ষক পাকিস্তানিদের পক্ষে সভা সমাবেশ করতে থাকে। দরকার মতো বাঙালীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।
এতে খোকন ব্যানার্জীর জীবনসংশয় দেখা দেয়, যে-কোনো সময় বোখারীর দল তাঁকে হত্যা করতে পারে। বিহারীরা উত্তেজিত হয়ে আছে। মন্টু আলালকে বলে, পণ্ডিত মশায়কে যেন জানিয়ে দেয়া হয় ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে ক্ষুদিরাম সেজে লক্ষঝক্ষ করার দিন শেষ হয়ে গেছে, যুদ্ধের সময় সকলকে দরকার মাঠে ময়দানে। খেলনা বোমা দিয়েও কোনো কাজ হবে না, যুদ্ধের জন্য দরকার আসল বোমা। কথাটা আালালকে খুব নাড়া দেয়। আলালদের বাসায় মন্টু মামা কিছু গ্রেনেড লুকিয়ে রেখেছিলো, যার খবর আলাল ছাড়া আর কেউ জানতো না। সে মহড়ায় যাবার আগে সকলের অজান্তে ক্ষুদিরামের টিনের বাক্সে সেই গ্রেনেডগুলো ভরে নেয়।
নাটক মঞ্চায়নের জন্য সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছিলো। নাটকের সহকারী পরিচালক শল্প ক্ষুদিরামের ফাঁসির দড়ি কিনতে বাজারে গেলে ফেরার পথে ফলের দোকানের মালিক রামদার কোপে তাকে আহত করে। এদিকে ক্ষুদিরামের দিদি অপরূপার ভূমিকায় অভিনয় করতো যে শোভা, সে জানায় তার পক্ষে নাটক করা সম্ভব নয়। কারণ উর্দু শিক্ষক ও বোখারী সারা শরীরে রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের বাড়িতে গিয়েছিলো এবং শাসিয়ে এসেছে, নাটক করলে তার পরিণাম ভালো হবে না। বোখারী তিনটি শিশুকে হত্যা করে সেখানে গিয়েছিলো, শিশু তিনটির অপরাধ ছিলো তারা ‘পানি’ না বলে ‘জল’ বলছিলো। যদি শোভা ক্ষুদিরাম নাটকে অভিনয় করে, তবে তাকেও একইভাবে হত্যা করা হবে।
তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং তার বাবা-মাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। সেজন্য ভয় পেয়ে শোভা নাটক ছেড়ে চলে যায়। নাটকের মহড়া তবুও বন্ধ হয় না। কাকলীকে অপরূপা সাজিয়ে নাটকের মহড়া চলতে থাকে। সেই সময় খবর আসে পাকবাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে। মহড়া কক্ষে মন্টু আসে অস্ত্র হাতে। মন্টু জানায় তারা মিলিটারীদের আক্রমণ করেছিলো তবে তাদের মেশিনগানের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বারো জন মারা গেছে। এখন অস্ত্র দরকার। সে আলালের কাছে জানতে চায় তাদের বাসায় যে গ্রেনেডগুলো লুকানো ছিলো সেগুলো কোথায়? প্রথমে আলাল গ্রেনেডগুলো মামাকে দিতে না চাইলেও পরে তা টিনের বাক্স থেকে বের করে মামাকে দিয়ে দেয়।
সে মামাকে জানায়, শত্রুদের মারার জন্যই সে বোমাগুলো তার কাছে রেখেছিলো। মন্টু তখন খোকন ব্যানার্জীকে বলে, নাটক করার সময় এটা নয়। মানুষকে হাসাবার কাঁদাবার সময়ও নয়, যুদ্ধে যাবার সময়। খোকন ব্যানার্জী যদি সত্যি ক্ষুদিরামকে ভালোবাসে তাহলে সে যেন তার ছাত্রদের যুদ্ধে পাঠায়। খোকন ব্যানার্জী মন্টুর কথা মতো সকলকে নাটক বাদ দিয়ে আগে দেশ বাঁচাতে বলে।
সকলে মহড়া কক্ষ ছেড়ে চলে যায়। খোকন ব্যানার্জী একা সিরাজদৌলা নাটকের সংলাপ বলতে থাকে। সে সময় বোখারী ও উর্দু শিক্ষক পেছন থেকে খোকন ব্যানার্জীকে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। খোকন ব্যানার্জী মারা পড়ে। বোখারী ও উর্দু শিক্ষক তারপর ক্ষুদিরামের দিদির ভূমিকায় অভিনয় করছিলো যে কাকলী, সে কাকলীকেও হত্যা করে। খোকন ব্যানার্জী ও কাকলীর মৃত্যুর খবর জানাজানি হয়ে যায়।
আলাল কাকলীর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরামের মতোই আবেগে নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করতে থাকে। সংলাপের মাঝে সে মৃত কাকলীকে উদ্দেশ্য করে বলে, একাত্তরের ক্ষুদিরামকে চেয়ে দেখ দিদি। সত্যিকার যুদ্ধের মাঠে আলাল তারপর একাত্তরের ক্ষুদিরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শহরে পাকবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলো মেজর আসলাম। আলাল তাকে হত্যা করার জন্য নয়নকে নিয়ে গ্রেনেড হাতে সোনামুখী শহরের লাশকাটা ঘরের সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। মেজর তার জীপ নিয়ে সেই লাশকাটা ঘর অতিক্রম করার সময় আলাল ও নয়ন তার জীপ লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। গ্রেনেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মেজর আসলাম আহত হয় মাত্র, মারা পড়ে না। ক্ষুদিরামের মতোই আলালরা ব্যর্থ হয় শত্রুকে হত্যা করতে। দুজনেই ধরা পড়ে। সামরিক আদালতের বিচারে আলাল ও নয়নের ফাঁসি হয়ে যায়।
শামুক বাস নাটকের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে। তারা ব্যানার্জী আর রিনা নামের দুটি মেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়। তারা ব্যানার্জী রাজশাহীর মেয়ে। তাকে একাত্তরের সাতাশে মার্চ স্থানীয় চেয়ারম্যানের জীপে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় মিলিটারী ক্যাম্পে। আর রীনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।
পাকিস্তানি বর্বররা রীনার সামনেই তার বাবা-মাকে হত্যা করে তাকে ধরে নিয়ে যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয় রীনা ও তারা। অত্যাচারের সময় দুজনেই দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে উচ্চরণ করেছে জয়বাংলা। তারপর এলো স্বাধীনতা। সম্ভ্রমহারা তারা ও রীনার মনে তখন একটাই আশা, নারীরসম্ভ্রম হারিয়েছে তারা যুদ্ধে, তাই যুদ্ধ শেষে তাদের শুধু পাবার পালা।
অথচ বীরাঙ্গনা খেতাব ছাড়া দুজনে আর কিছুই পেল না। তাই তারা ব্যানার্জী বাংলাদেশকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল সোফিয়ায়। আর রীনা রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে পাকিস্তানিআর্মিদের সাথে পা বাড়ালো পাকিস্তানের পথে। কিন্তু তার বড় ভাই কলকাতার একটা ক্যাম্প থেকে রীনাকে ফিরিয়ে আনে। নাটকটিতে ক্ষোভ ঘোষিত হয়েছে বীরাঙ্গনারা বিশেষ কিছু পেল না বলে। নাটকের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের বহু কিছু পাবার কথা। স্বাধীনতার পর কারা পাবে, কারা পাবে না, কোথা থেকে পাবে, কেন পাবে সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য নাটকে নেই।
ক্ষেতমজুর খইমুদ্দিন নাটকের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। খইমুদ্দিন একজন দরিদ্র ক্ষেতমজুর। স্বাধীনতা কী তা সম্পূর্ণভাবে না বুঝলেও সে অনুমান করে এতে তার এবং সকলের মুক্তি হবে। শহরে গিয়ে সে স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়টি সরাসরি প্রত্যক্ষ করে আবার গ্রামে ফিরে আসে এবং নিজেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কল্পনা করে। গ্রামের মাতব্বর ও শান্তি কমিটির লোকজন তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে পাকবাহিনীর সহায়তায় খইমুদ্দিকে হত্যা করে।” ১৯৭১ নাটকের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ। ময়মনসিংহ জেলার নীলগঞ্জ গ্রামের রফিক পাকবাহিনীকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে আসে এবং ইপিআর এর কাছে খবর পৌঁছে দেয়।
পাকিস্তানি মেজর রফিককে গুলি করে মারার আগে তাকে বলেছিলো, ‘তোমার কি ধারণা এই দেশ তোমার বীরত্বের কথা মনে রাখবে।’ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে এসে দেখা যায় মেজরের সেই কথাই সত্যি প্রতীয়মান হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা কেউ মনে রাখেনি।
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে মিন্টু বসুর লেখা নাটক ঘাতক চারদিকে।
মুক্তিযুদ্ধের সময়কালকে ঘিরে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্ত ও নানাধরনের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। নাটকে মাস্টারদা, তার বোন রেবতী, রহমান ও অমলরা যেমন যুদ্ধের জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখে, তেমনি মুসলিম লীগ নেতা আঃ রব, জামাত নেতা মাওলানা কুদ্দুস ও নেজামে ইসলামীর নেতা মাওলানা সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করার জন্য পাকবাহিনীর সাথে হাত মেলায়। তিন দলের এই তিন নেতা মনে করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা মানেই ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করা। সেজন্য মুক্তিবাহিনী নামের যে দুষ্কৃতিকারীরা সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, ভারতীয় চরদের যোগসাজশে ভূখণ্ডের মধ্যে যে নাশকতা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করা তারা কর্তব্য বলে মনে করে।
নিজেদের মধ্যে সভা করে তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রতি তারা পূর্ণ সমর্থন দেবে। উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাবে। দেশের হিন্দুদের মধ্যে কুমার, কামার, জেলে, নাপিত, ধোপা, মালি ছাড়া আর সকলকে হত্যা করার ব্যাপারে সরকারকে আবেদন করবে।
পাকবাহিনীকে সমর্থন করার জন্য তারা গড়ে তোলে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করার জন্য তারা যে-কোনোরকম পথ বেছে নিতে দ্বিধা করে না। পাকবাহিনীর সাথে আঁতাতের মাধ্যমে তারা গ্রামের ঘরবাড়ি লুট করা, আগুন লাগানোর কাজে সহযোগিতা করতে থাকে।
যারা রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশ বাণী ও বিবিসি শুনবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা ঘোষণা করে। দেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে তারা হত্যা করতে থাকে। তিন নেতা পাকবাহিনীর দ্বারা নারী ধর্ষণকেও অনুমোদন করে এবং এসব ঘটনায় বিকৃত আনন্দ লাভ করে। পাশাপাশি নাটকে দেখা যায় রাজাকারদের দ্বারা সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন ও কষ্ট দেয়ার চিত্র। সকল নির্যাতন আর অত্যাচারের মুখে মুক্তিবাহিনীরাও তাদের লড়াই চালিয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গপোসাগরে সপ্তম নৌবাহিনী পাঠিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে চায়, তার মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মনোবল অটুট রাখে। নয় মাসের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়।
তিরিশ লক্ষ মানুষ এর জন্য প্রাণ দেয় আর দেশের দু লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্ষমা পেয়ে যায় স্বাধীনতার শত্রুরা। পরবর্তীকালে আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং স্বাধীন দেশের নানা ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে।স্বাধীনতার এই শত্রুদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার তাই আবার গর্জে উঠুক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জয় হোক, নাট্যকার এইসব আশা ব্যক্ত করে নাটক শেষ করেন।
স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকের মূল লক্ষ্য। সেজন্য কখনও তারা নাটকে আনছে রাজাকার আলবদরদের দ্বারা বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা, কখনও তুলে ধরছে পাকিস্তানী বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা নারীদের চিত্র, কিংবা কখনও বর্ণনা করছে কীভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা বা তাদের সহযোগিতায় হত্যা করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারের লোকদের। কিংবা দেখানো হচ্ছে সেদিনের সেই শত্রুরা আজও কীভাবে সারাদেশে আবার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে, ফতোয়া জারি করছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। সেইসব কিছুই চিত্রায়িত হচ্ছে জনগণের মধ্যে প্রবল ঘৃণা ও অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার জন্য।
এসব নাটকে আরো দেখানো হয়ে থাকে স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থানের ভিতর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আজ কী পরিমাণ অসহায়। রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে কোথাও মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত অবস্থান নেই। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা আজ কোণঠাসা, মুক্তিযোদ্ধারা কোথাও আজ সুবিচার পাচ্ছে না। এমনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হচ্ছে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ হিসেবে পরিচিত নাটকগুলোর বিয়ষবস্তুর মধ্যে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রচার, মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ- তিতিক্ষাকে গৌরবময় করে তোলাও এ সবের অন্তর্ভুক্ত থাকছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কিত এসব নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা স্বাধীনতা বিরোধী শত্রুদের সাথে অলিখিত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছেন। বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি যদি কোথাও জোরালোভাবে এসে থাকে তা এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকগুলোতেই।
কেন এই নাটকগুলিকে রাজনৈতিক প্রবণতার নাটক বলা হচ্ছে? কারণ মুক্তিযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। নাটকগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি রাজনৈতিক ঘৃণা। শুধু ঘৃণাই নয়, এক ধরনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি নাটকগুলোকে টেনে আনা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন প্রকাশ এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা প্রচারের মধ্য দিয়ে নাট্যকর্মীরা এখানে একটি পক্ষাবলম্বন করেছেন।
সেই পক্ষাবলম্বনটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই, ফলে চেতনাটি রাজনৈতিক এ নিয়ে দ্বিমত বা বির্তকের অবকাশ নেই। প্রশ্ন আসতে পারে, সে রাজনীতি কতোটা স্বচ্ছ এবং তার সাথে রাজনৈতিক নাটকের বা শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটি কতোটা জড়িত। সেই রাজনীতিটি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থের কোনো সমাজসচেতন কর্মসূচী কি না। স্বাধীনতার শত্রুদের প্রতি যে ঘৃণার প্রকাশ, সে ঘৃণাটি আসলে কার স্বার্থে? সেটি কি মধ্যবিত্তের আবেগ, না শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোনো স্তরের সাথে এর কোনো যোগাযোগ আছে?
নাকি এই ঘৃণার মধ্যে আছে বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা? নাটকে যে রাজনীতিটি প্রচারিত সেটা জনগণের স্বার্থে, না গুটিকয়েক সুবিধাভোগীর স্বার্থে? এমনি নানা প্রশ্ন আসতে পারে। সত্য যাই হোক, মূল লক্ষ্য জনগণকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, যে দিনগুলোতে প্রবল আবেগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো জনগণ।
নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের বিশ্বাস, বাঙালীর হাজার বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ, যার কথা জনগণ আজ ভুলে বসে আছে। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আবেগটি এখন মৃত। নাট্যকার নাট্যকর্মীদের চিন্তায় যা ধরা পড়ে তাহলো, জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা আবেগটি মৃত বলেই স্বাধীনতা বিরোধীরা এতো প্রবল শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। সেইরকম একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা ব্যাপারটিকে দেখছেন। চিন্তাটি যেহেতু নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে সেজন্য আমরা এই মতামতটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করবো।
বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। নাট্যকার বা নাট্যকর্মীরা বলছেন, জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ বেঁচে নেই বলে রাজাকারদের উত্থান ঘটেছে। জনগণের মধ্যে যে মুক্তিযুদ্ধের প্রবল আবেগ বা সেই ত্যাগ-তিতিক্ষা আজ নেই সেটা সত্যি। তবে সেটা নেই কেন সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকে পাচ্ছি না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেন হারিয়ে গেল, সে প্রশ্নের কোনো বাখ্যা বিশ্লেষণ নাট্যকার নাট্যকর্মীরা নাটকে না দাঁড় করালেও একটি মন্তব্য তাঁরা করে থাকেন যে, বাঙালী সবকিছু দ্রুত ভুলে যায়। নাট্যকার বা নাট্যকর্মীরা যে কথা বলছেন, বাঙালী সবকিছু দ্রুত ভুলে যায় এখানে ব্যাপারটা একটু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হবে।
ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এই বাঙালীরাই খুব আবেগ নিয়ে পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা এনেছিলো, মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলো। সেখানেও তাদের সেই উন্মাদনা খুব শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে পড়েছিলো। দুটি ঘটনাকেই কি আমরা বাঙালীরা খুব দ্রুত সব কিছু ভুলে যায় সেভাবে দেখবো, না কি পিছনে ভিন্ন কোনো কারণ সন্ধান করবো?
স্বাধীনতার জন্য উনিশশো সাতচল্লিশ সালেও জনগণ সংগ্রাম করেছিলো। যদিও সেটা সশস্ত্র যুদ্ধ ছিলো না, তবুও সে সংগ্রামে বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন সেসব জাতীয় নেতাদের অনেকেই পাকিস্তানের দাবিতেও সংগ্রাম করেছিলেন, যাঁরা তৎকালে মুসলিম লীগেরই সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছিলো বাংলার মুসলমানরাই। মুসলিম লীগের জন্ম ঢাকা শহরেই। একদিন যে বাঙালী মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে পাকিস্তান এনেছিলো শীঘ্রই আবার তারা সেই পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই চলে গিয়েছিলো, মুসলিম লীগ বর্জন করেছিলো। শুধু নেতারা নয়, জনগণও। পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছিলো তারা কেন আবার সেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চলে গেলো সেই ঘটনাবলীকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা দেখবো তার সাথে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর কোনো মিল আছে কি না।
সেক্ষেত্রে জনগণ কেন নিজেই তার নিজের গর্বিত সংগ্রামের বিরুদ্ধে চলে যায় সেটাই এখানে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকগুলোর বক্তব্যের সঠিকতা-বেঠিকতা নির্ণয়ের জন্য।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে দুজন জাতীয় নেতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের একজন মওলানা ভাসানী, অন্যজন শেখ মুজিব। মওলানা ভাসানী চুয়ান্ন সাল থেকেই পূর্ব বাংলাকে আলাদা করার কথা বলছিলেন আর শেখ মুজিব একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তীর নেতা।
মুক্তিযুদ্ধের মাত্র তেইশ বছর আগে দুজন নেতাই ছিলেন ঘোরতর পাকিস্তানের সমর্থক। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক লিখছেন, বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মুসলমান, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম লীগের একজন অনুগত সদস্য ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার সমর্থক ছিলেন এবং এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তিনি আরো লিখছেন, জিন্নাহ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিতে দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ জননেতা, যিনি খুঁটিনাটি বিবেচনা করে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে কাজ করেছেন এবং তাকে প্রায় সফল পরিণতিতে নিয়ে গেছেন। সেই সফল পরিণতিতে নেয়ার পেছনে বাঙালী মুসলমানদের ছিলো বিশাল ভূমিকা।
কোনো সন্দেহ নেই যে, উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতীয় জাতির পরিচয়ে আত্মবিলুপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এই জনতাই একদিন পাকিস্তানী জাতি সৃষ্টির উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলো। বাঙালী মুসলমানের জাতীয়তাবোধ সেদিন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলো।”* বিভিন্ন বিশিষ্ট জন তাঁদের আলোচনায় দেখিয়েছেন, বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিলো কোনো কারণ ছাড়া নয়। যথেষ্ট যুক্তি ছিলো তাদের এর পেছনে। ইতিহাসও সে কথাই বলে।
ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জন্যের পিছনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ প্রথম দেখা দিয়েছিলো ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর উঁচু বর্ণগুলোর মাঝে। সে হিন্দুরা ভিন্ন ধর্মের লোক তো দূরের কথা স্ব-ধর্মের সকলের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যে শুচি-অশুচির, আচার-অনুষ্ঠান সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল তা বাঙালী মুসলমানকে অতি সহজেই বাঙালী হিন্দুর কাছ থেকে সামাজিকভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো।
আর তা ছিলো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রধান বাধা স্বরূপ। বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গজনিত কারণে যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব ঘটলো তা বর্ণধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালীকে মেলাতে সক্ষম হয়নি। স্বদেশী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বাঙ্গালী মুসলমান ছিলো পুরোপুরি অনুপস্থিত, কারণ হিন্দুরা মুসলমানদের বিশ্বাস করতো না এবং হিন্দুদের দেবীদের সামনে শপথ করেই শুধু সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হওয়া যেতো। তাই দেখা যায়, বাংলার মধ্যবিত্তের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হলো এই সময়, তার মধ্যে হিন্দুত্বের সুর ও রঙ মিশে গেল।
পরে সে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছিলো। মওলানা আবুল কালাম আজাদই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হিন্দুদের দিক থেকে এভাবেই মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো যা ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকেও হিন্দু বিদ্বেষী করে তোলে। সুপ্রকাশ রায়ের লেখা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষের আরো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শক্তি প্রধানত মুসলমান শাসকদের নিকট থেকে এদেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তাই ব্রিটিশ শক্তি মুসলিমদেরকে শত্রু বলেই গণ্য করতো।
অন্যদিকে মুসলমানগণও একই কারণে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরোধিতা করে আসছিলো। যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় তখন প্রধানত হিন্দুরাই ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতা করে এবং প্রায় সকল জমিদারি হিন্দুদের হস্তগত হয়। ফলে দেখা গেছে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও বিহারের প্রায় সকল জমিদাররাই ছিলো হিন্দু আর তাদের অধীনস্থ চাষীদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান। প্রথম দিকে মুসলমান জনসমষ্টির হিন্দু বিদ্বেষের মূলে ছিলো হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মহাজনদের প্রজা-খাতকের উপর অর্থনৈতিক নিপীড়ন। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই মুসলমান কৃষকদের হিন্দু জমিদারদের প্রতি যে বিদ্বেষ তাকেই সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করেছিলো নানাভাবে। সে সাথে বঙ্কিমের হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনা এবং হিন্দুদের মধ্যে তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের কারণে দেখা গেল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে বিকাশ তার হিন্দু পরিচয়টাই ছিলো মুখ্য।
ভারতের মুসলমানরা স্যার সৈয়দ আহমদের অনুপ্রেরণায় বৃটিশ বিরোধিতা ও অসহযোগিতার পথ পরিত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষায় নিজেদের আলোকিত করে তুলতে শুরু করে। এভাবেই বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্প্রসারিত হতে থাকে, দানা বেঁধে উঠতে থাকে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা। এই মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জিন্নাহ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটি মিলন ঘটাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন কিন্তু তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালনের কথা ভোলেন না। সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে মতিলাল নেহরু এবং জওহরলাল নেহরু মোটেই গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না।
সেখানে থেকেই ভারতের মূল রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম বিরোধ মারাত্মক আকার নেয়। ব্রিটিশদের কূট কৌশল ও নেহরু-প্যাটেলদের গোঁড়ামির জন্যই জিন্নাহর মতো অসাম্প্রদায়িক লোকও বাধ্য হয় মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পথে যেতে। চিত্তরঞ্জন দাস সেই সময় বাঙালী জাতির আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে বাংলা ভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং বাঙালী ও হিন্দুদের নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের হঠাৎ মৃত্যুতে সে ধারা খুব বেশি দূর আগালো না। ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের যে বিরোধ, দেশের সর্বত্র তার প্রভাব পড়ে।

দারিদ্র্যজাত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা শিক্ষিত মুসলমানেরা যখনই এবং যতোই ভেবেছে তখনই এবং ততোই বর্ণহিন্দু শোষকের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুদের তারা সত্যিকারের বন্ধু ভাবতে পারেনি। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে হিন্দুদের সাথে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে সহঅবস্থান করতে পারবে কি না অনেক মুসলমানের মনেই সে সন্দেহ থেকে গিয়েছিলো।
হিন্দু-মুসলিম এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভিতর দিয়েই যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম, ব্রিটিশ শক্তির ইন্ধনে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং যা মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। গান্ধীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতীয়তাবাদ তা মুসলমানদের বোঝাতে জিন্নাহকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার এই বীজটি ছিলো মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যেই, নিম্নবিত্তদের মধ্যে নয়। নিম্নবিত্তদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সৎভাবের অভাব ছিলো না, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বই সেদিন সেটাকে উস্কে দিয়েছিলেন। মুসলমান মধ্যবিত্তরা এটা বুঝেছিলো হিন্দুরাষ্ট্রের মধ্যে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।
মুসলমানদের সে চিন্তা মিথ্যাও ছিলো না। বিগত চল্লিশের দশকে তাই দেখা গেছে, বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় ছিলো খানিকটা দৈশিক আর অনেকটাই সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতাই তখন ছিলো জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দেশবাসীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়নি, দেশবাসীর বেশিরভাগই তা স্বেচ্ছায় উৎসাহ সহকারেই মেনে নিয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষ হয়ে গেল পাকিস্তানি, আর অল্প দিনের জন্য হলেও অধিকাংশের জন্যই পরিচয়টা ছিলো গৌরবের ব্যাপার। জঙ্গী আবেগেরও। যদিও সে আবেগটা বেশি দিন থাকলো না।
পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালীরা যেমন পাকিস্তানের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণায় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে নিজেদের জাতিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছিলো তেমনি খুব শীঘ্রই তারা টের পেল মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাদের কোনো কাজে আসছে না। পাকিস্তানি শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে সময় লাগলো না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে। ধর্মের চেয়ে ভাষত্ন ব্যাপারটা বড় হয়ে দেখা দিলো শোষিত মধ্যবিত্তের চেতনায়। সেখানেও ছিলো আবেগ। সাধারণ বাঙালী, শ্রমজীবী বাঙালীর মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা পাকিস্তান রাষ্ট্র নিয়ে গৌরব করার ব্যাপারটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো পাকিস্তানি শাসকচক্রের চরম শোষণে।
যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তারা পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন করেছিলো সেই মুসলিম লীগ ক্ষমতায় বসার পর যেভাবে দুর্নীতি ও দুঃশাসন চালিয়েছিলো তাতে জনগণের, বিশেষ করে পূর্ববাংলার জনগণের স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে গিয়েছিলো। ব্রিটিশদের শাসন, হিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করে তারা যে পাকিস্তান বানিয়েছিলো, সে পাকিস্তান তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে তো পারেইনি, উপরন্তু তাদের উপর পূর্বের চেয়ে আরো বেশি নিপীড়ন চাপিয়ে দিয়েছিলো। বহুজনই তখন মনে করতে শুরু করেছিলো এর চেয়ে ব্রিটিশ শাসনই ভালো ছিলো। স্বভাবতই পাকিস্তান নিয়ে গৌরব করার কিংবা পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের আর কোনো উৎসাহ ছিলো না।
পাকিস্তানের সরকারগুলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যতোই বড় করে দেখাক না কেন পূর্ববাংলার জনগণের এই রাষ্ট্রের প্রতি আর দেশপ্রেম ছিলো না। পাকিস্তান বানাবার সংগ্রামের জন্য তাদের কোনো গর্বও ছিলো না। পাকিস্তানের জন্ম সেদিন অনেকের কাছেই ভুলে মনে হয়েছিলো শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীর শোষণের কারণে, তাদের দুর্নীতি ও জুলুমের জন্য। স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনোরকম মোহ আর না থাকাটাই তখন ছিলো স্বাভাবিক। মোটের উপর বলা চলে, পাকিস্তানি জঙ্গী আবেগের স্থলে দ্রুততার সঙ্গেই এলো আরেকটি জঙ্গী আবেগ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অনেক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে হলো বাঙালী, বিসর্জন দিলো মুসলিম বা পাকিস্তানি জাতীয়তাকে।
সেটা এজন্য নয় যে, তারা জাতি হিসাবে সচেতন হয়ে উঠলো বরং শতকরা নিরানব্বই জনই জানতো না তাদের জাতীয়তার পরিচয় কী, যথার্থ জাতি হয়ে ওঠে কী করে। পূর্বের পরিচয়কে বিসর্জন দেয়ার ভিতর দিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদই ঘোষিত হয়েছিলো। সে যে নিজের সংগ্রাম করে আনা পাকিস্তানের ব্যাপারে আর কোনো গৌরব বহন করে না, সেই চিন্তারই প্রতিধ্বনি সেটা।
সাতচল্লিশে যাকে তারা মনে করেছে স্বাধীনতা, দু-এক বছরের মধ্যে সেটাই তাদের কাছে মনে হলো পরাধীনতা। সে কারণে পূর্ববঙ্গের জঙ্গী পাকিস্তানিরা হঠাৎ বাঙ্গালী হয়ে গেল। সত্তর-একাত্তরের নিবার্চনে তাই বিপুলভাবে আওয়ামী লীগ জয়ী হলো। কিন্তু ক্ষমতা পেল না বলে চব্বিশ বছরের মধ্যে দেশটি আবার স্বাধীন হলো, সেই প্রবল জাতীয়তার আবেগ নিয়েই-প্রথমবার যার নাম ছিলো মুসলিম জাতীয়তাবাদ সেটারই নতুন নামকরণ হলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। সেটা কোনো সত্যিকারের জাতীয়তার চেতনা ছিলো না, ছিলো শুধুই আবেগ।
মূলত আবেগ বস্তুটা কখনই চিরস্থায়ী হয় না, বাংলাদেশেও হয়নি। স্বাধীনতার পর ঠিক পূর্ব পাকিস্তানেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো বাংলাদেশে। পাকিস্তান যখন জন্ম নেয় তখন শাসকবর্গের শাসন জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি দেখে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বহুজন যেমন মনে করেছিলো ব্রিটিশরাই ভালো ছিলো, বাংলাদেশের জন্মের পর ঠিক তাই ঘটলো। শাসকবর্গের শোষণে বহুজনই মনে করতে শুরু করে পূর্বের রাষ্ট্রেই তারা ভালো ছিলো। দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অভাব-অনটন এবং দারিদ্র্য স্বাধীনতার প্রতি সাধারণ মানুষকে বিরূপ করে তুলেছিলো যৌক্তিক কারণেই। দীর্ঘ সংগ্রাম তারা কেন করেছিলো? নতুন দেশে তারা খেয়ে পরে স্বচ্ছল থাকবে সেইজন্য।
স্বাধীন দেশে তারা পেল মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি এবং দুর্নীতিপরায়ণতা। দুর্ভিক্ষ, মন্দা, খ্যাদ্যাভাবের অর্থই ছিলো সমাজের কিছু কিছু শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত মুনাফা।** স্বাধীনতা-উত্তর কালে চোরাচালান মজুতদারি ছিলো টাকা বানানোর একটি ক্ষেত্র এবং দুর্ভিক্ষ ছিলো কোটিপতিদের উত্থানের জন্য স্বর্ণসময়।
দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকা শহরের বিলাসী জাঁকজমক পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে বেশি ছিলো। যারা এমনি সময়কে প্রত্যক্ষ করেছে স্বাধীনতা নিয়ে তাদের গর্ব করার কোনো কারণ থাকে না; যা সাতচল্লিশের পর আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। যে লক্ষ্য নিয়ে মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে সেটা যখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতাও তখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। স্বাধীনতা তাকে শোষণ থেকে মুক্তি তো দেয়ইনি বরং তার ওপর নিষ্পেষণ বহু গুণ বাড়িয়েছে। সেজন্য এদেশের শোষিতরা যেমন পাকিস্তান নিয়ে গর্ব করতে পারেনি, তেমনি বাংলাদেশ নিয়ে গর্ব করাও তাদের জন্য সম্ভব ছিলো না। স্বাধীনতার পরপরই লুন্ঠিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের চেহারা দেখে কিছু কিছু লোক মনে করেছিলো এর চেয়ে পাকিস্তানই ভালো ছিলো।
এবং আরও কিছু লোক নতুন করে পুনরায় মনে মনে পাকিস্তানপন্থী বনে গিয়েছিলো। সেটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। ভ্লাদিমির লেনিন বলেছিলেন, অত্যাচারিত মানুষের প্রথম প্রতিবাদ ঘোষিত হয় এই বক্তব্যে যে, আমরা পূর্বাবস্থায় ভালো ছিলাম। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সম্ভাবনাই সৃষ্টি হয় না। আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের যদি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত না হয় তাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি মানুষের সাধারণ শ্রদ্ধা, আস্থা ও আশা ক্ষয় পেতে থাকে। সাধারণ মানুষ ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয় স্বকীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আগেকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং বিশেষ বিশেষ জাতীয় দিন তারিখগুলোও অপেক্ষাকৃত উদ্দীপনাহীন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়।
এই প্রক্রিয়াটি থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা বের হয়ে আসে যে, যে-কোনো দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে যদি অথনৈতিক মুক্তির দিকে অগ্রসর করে না নেওয়া যায় তাহলে সে দেশের খোদ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিবীদ এম. এম. আকাশ দেখান যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সংহত করার প্রকৃত পথ একটিই, মৌলিক আর্থ-সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে তলের দিকের অসংখ্য দুঃখী মানুষের দুয়ারে স্বাধীনতার স্বাদ পৌছে দেয়া। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিতাড়িত করে সেখানে যে নতুন জাতীয় শাসকদের অধিষ্ঠিত করে, তাতে অবশ্যই তাৎক্ষণিক লাভ হয় প্রচুর। কিন্তু তারা যদি সেই লাভকে ব্যাপক মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট না হয় তাহলে স্বাধীনতার সুফল সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। স্বাধীনতার তাৎপর্য সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।
ফলে স্বাধীনতা-উত্তর কালে স্বাধীনতার শত্রু দালাল-রাজাকারদের উত্থানের পেছনে জড়িয়ে আছে এই ঘটনাগুলো। জনগণের নিষ্ক্রিয়তা সেখানে প্রধান নয়, প্রধান শাসকবর্গের শোষণ। শাসকদের ক্রমাগত অত্যাচারে সে যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চলে গেছে কিংবা স্বাধীনতা নিয়ে গৌরব করার কারণ খুঁজে পায় না সেটাই তার জন্য স্বাভাবিক। সেটাই তার নিজ শ্রেণীর সংগ্রাম। কী দেখতে পাছি তাহলে আমরা?
নাট্যকার বা নাট্যকর্মীরা যে বক্তব্য দিচ্ছেন, মানুষ স্বাধীনতার জন্য গৌরব করার কথা ভুলে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে গেছে সেটা সত্যি। তবে তার কারণ এ নয় যে বাঙালী সবকিছু দ্রুত ভুলে যায়। শাসকশ্রেণী জনগণের ওপর যে যাঁতাকল চাপিয়ে দিয়েছে সে কারণেই স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ভেঙে গেছে। যারা আজ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে, যারা সুবিধাভোগী, স্বাধীনতা যাদের ভাগ্য পাল্টাতে সাহায্য করেছে, স্বাধীনতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের গৌরব থাকতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা যাদেরকে শুধু বঞ্চনাই করেছে তারা গৌরব করবে কোন্ প্রেক্ষিতে?
বাংলাদেশের একজন নাগরিক একবার বলেছিলেন, ‘সরকারি দলের লোকজনের জন্যই এ দেশ সোনার বাংলা আমাদের জন্য নয়’। সরকারি দলের এক সাংসদের পুত্র তার ভাইকে নৃশংসভাবে সকলের চোখের সামনে হত্যা করার পর তিনি একথা বলেন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্বিচারে যেভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলো তার সাথে এ ঘটনার পাথর্ক্য কতোটুকু সে প্রশ্নই তিনি তুলেছিলেন।
মূলত স্বাধীনতার পর সরকারের ব্যর্থতাই সাম্প্রদায়িক শক্তি ও দালাল রাজাকারদের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কথাটাই ছিলো শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা ছিলো শোষকদের উৎখাত, শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের জায়গায় দেশীয় শোষকদের ক্ষমতায় বসানো নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা রাজাকার আলবদর বাহিনীর হয়ে হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুন্ঠন চালিয়েছে তারা ঘৃণিত।
পাশাপাশি যারা স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের কথা বলে ক্ষমতায় বসেছে এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ বিকিয়ে দিয়ে লুটপাট করেছে জনসাধারণ বা শোষিতদের চোখে তারাও কি সমান ঘৃণ্য নয়? স্বাধীনতার পক্ষের শাসকদের লুন্ঠন, নিষ্পেষণ ও নিষ্ঠুরতা-এসবই রাজাকার দালালদের উত্থানে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের মনকে বিষিয়ে তুলেছিলো। পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একটা শক্তি ও দালাল রাজাকাররা সমান চিন্তার অংশীদার হয়ে উঠেছিলো। দালাল রাজাকারদের উত্থানের পেছনে উল্লিখিত এই কারণগুলো বাদ দিয়ে শুধু রাজাকার দালালদের দেশের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী করলে সেটা হয় ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা। সেটা পূর্ণ সত্য নয়, খণ্ডিত সত্য। স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানে ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা ও সরকারি নীতিমালা।
ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল পাকিস্তান থেকে। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও, যেখানে জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ মুসলমান সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে গেল শাসকদের শ্রেণীস্বার্থে। বিশেষ করে তিয়াত্তরের পর সরকারের ভূমিকা এই আদর্শের প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে ছিলো স্ববিরোধী।
দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি, প্রশাসনিক দুর্নীতি, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, ভারত প্রভাবিত প্রশাসন ও পররাষ্ট্র নীতি, সর্বোপরি পঁচাত্তরের শুরুতে বাকশাল গঠন ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন দেশের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সংশয়ের জন্ম দেয়। এই সুযোগে দেশে ধর্মীয় শ্লোগান জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। একদিকে সাধারণ ক্ষমা পেয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর সহযোগী দালালরা বিশেষ করে বেআইনী ঘোষিত সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপির সদস্যরা জেল থেকে বের হয়ে আসে এবং নতুন করে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকে-তাদের বিভিন্ন অংশ জাতীয় গণতান্ত্রিক দল, রিপাবলিকান পার্টি, ইসলামী তহজীব তমুদ্দুন কমিটি ইত্যাদি সংগঠন গড়ে তুলে মাঠে নামে। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ শাসনামলে জামায়াত, মুসলিম লীগ নিজেদের দলীয় পরিচয়ে মাঠে না থাকলেও তারা একেবারে মাঠের বাইরেও ছিলো না।
ওয়াজ নসিয়ত, ধর্মীয় জলসা, সিরাত মাহফিল ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং বেনামী সংগঠনের ছত্রছায়ায় তারা সংগঠিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি কঠিন আদর্শ। কোনো মানুষই রাতারাতি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। পাকিস্তানের দীর্ঘ দুই যুগ শাসনে যে মানুষ সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মধ্যে বর্ধিত হয়েছে, মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধেই সেই মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পরিশুদ্ধ হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার শেকড় থাকে সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত। মানুষকে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করা সম্ভব ছিলো। তবে এসব ব্যপারে সরকার যেমন ছিলো উদাসীন তেমনি আবার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহারও করেছে।
দালাল রাজাকারদের উত্থানের পেছনে ধর্মের একটি ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে হঠাৎ অতি ইসলামচেতনা পশ্চিমা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের দান ও চাল। সমাজতন্ত্রের ভয়ে ভীত মার্কিন শক্তি ও আরবদেশগুলো সমাজতন্ত্রের বিরোধিতার কৌশল হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে ইসলামনিষ্ঠ করার ব্যাপারে মৌলবাদী দলগুলোকে মদত যুগিয়েছে। সেটা যেমন রাজাকারদের উত্থানকে সুযোগ করে দিয়েছে, সেই সাথে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের উত্থানকেও সাহায্য করেছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উত্থানকে সাহায্য করছে প্রধানত দিল্লী সরকারের মোড়লীপনা। বিপুল সম্পদ পাচার এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের পাঁয়তারা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিলো সত্তরের দশকেই।১০০ বাংলাদেশে মঞ্চস্থ নাটকগুলোতে এই বিশ্লেষণ একেবারেই নাই। বাংলাদেশের নাট্যকাররা ইতিহাসের একটি দিক নিয়ে কথা বলেছেন, অন্য দিকটিকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে প্রশ্ন সেটা মূলত শাসকশ্রেণীরই মতবাদ। স্বাধীনতার প্রশ্নটি ধ্বনিত হয়েছিলো বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর দ্বারাই, সুবিধাভোগীশ্রেণীর দ্বারাই। সত্তরের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সেই সময়কার শাসকশ্রেণী যখন বিজয় অর্জন করেও বুঝতে পারলো শাসন ক্ষমতা লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তারাই স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিলো। অন্যরাও অনেকে এই প্রশ্নে একমত হলেও এই স্বাধীনতা লাভের পুরো যুদ্ধটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো শাসকশ্রেণীর দ্বারাই। শাসকশ্রেণীই অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং তারাই যুদ্ধটাকে পরিচালনা করে। যুদ্ধের মাঠে সরাসরি অস্ত্র হাতে-যুদ্ধ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের ব্যাপক অংশটি যদিও ছিলো নিম্নবর্গ থেকে আগত, তবে তাঁরাও ছিলেন শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে।
যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনাগুলোও ছিলো প্রধানত শাসকশ্রেণীর চিন্তাভাবনা। শাসকশ্রেণী তাঁদের চিন্তার রাজ্যে একটি স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলো যে, দেশ স্বাধীন হলেই সমস্ত রকম শোষণ বঞ্চনার অবসান হবে। শাসকশ্রেণী নিজ স্বার্থেই এধরনের একটি বক্তব্য প্রচার করেছিলো এবং মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্যকে অনেক বড় করে তুলে ধরেছিলো। শাসকশ্রেণীর মতবাদের বিরুদ্ধ মতবাদও তখন ছিলো। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের একটি সম্প্রদায় স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে সমস্ত রকম শোষণ বঞ্চনার অবসান হবে তা বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, সত্যিকারভাবে শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে দরকার মুক্তিযুদ্ধের পরে একটি ব্যাপক শ্রেণীসংগ্রাম। শাসকশ্রেণী এই শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটিকে বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত রকম মুক্তির কথা বলেছিলো। সাধারণ মানুষ, নিম্নশ্রেণীর মানুষ শাসকশ্রেণীর কথা বিশ্বাস করেছিলো।
যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই যুদ্ধের পক্ষে ছিলো এবং মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। শাসকশ্রেণী ও ভারতীয় সরকার কোনোভাবেই চাইছিলো না মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাক। ভারত সরকার এই যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিলো নিজ স্বার্থে। ভারত সরকার ছিলো ভারতীয় বুর্জোয়াদের সরকার। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের ভূমিকা ভারতের সংসদীয় বাম দলগুলোরও সমর্থন লাভ করলো। ভারত সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর বাংলাদেশের মুক্তিদাতা রূপে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পেছনে যে একটি ষড়যন্ত্র ছিলো সেটা তারা নজরে আনলো না।
বামশক্তি বুঝতেই পারলো না, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে একটি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় তার জন্য তড়িঘড়ি করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে মুক্তিযুদ্ধকে অর্ধপথে থামিয়ে দেয়া হলো। লাওস, কম্বোডিয়ার পথে যাতে বাংলাদেশের গণপ্রতিরোধ গতি না নেয় সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের হস্তক্ষেপ ভারতের বাম দলগুলো লক্ষ্য করলো না।
বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও সংগ্রামের পথ পরিহার করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই চক্রান্তের সাথে হাত মেলালো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভটা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল হয়ে দাঁড়ালো। সিরাজ সিকদারের ভাষায়, ষোলই ডিসেম্বর ইন্দিরার ঢাকা দখলের দিবস হিসাবে চিহ্নিত হলো। স্বাধীনতার পর শাসকশ্রেণীর লুটপাট, ধনলিন্সা ও তাদের অত্যাচার দেখে আতঙ্কিত হয়ে স্বাধীনতা সম্পর্কে শীঘ্রই সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটলো। সত্তর দশকের মঞ্চায়িত নাটকগুলোতেও তা আমরা দেখেছি।
পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে শাসকশ্রেণীর যে ধরনের সুসম্পর্ক তৈরি হয়, দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যেভাবে বিশ্বায়নের নামে জনগণের ওপর শোষণ চলতে থাকে, যেভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলে তাতে স্বাধীনতার ধারণাটাই শোষিতদের কাছে বিমূর্ত রূপ লাভ করে। স্বাধীনতা নিয়ে তাই শোষিত মানুষ আর মাথা ঘামাবার তাগিদও বোধ করে না। নতুন নতুন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার লুণ্ঠনের হাত থেকে মুক্তি লাভই তখন শোষিতদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ব করা নয়।
ইতিহাস প্রমাণ করেছে শাসকশ্রেণীর ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতার পর সমস্ত মানুষের মুক্তি আসেনি, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত – হয়নি সত্যিকারের গণতন্ত্র পর্যন্ত। স্বাধীনতার পরেও একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে, বারবার সামরিক শাসন জারি হয়েছে, নানা রকম কালাকানুন ঘোষিত রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে একজন ইতিহাসবিদ লিখছেন, স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা নয়, একই সঙ্গে শোষিতের ওপর শোষকের বিজয়ের স্বীকৃতিও। তিনি আরো লিখছেন, বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী দুই দফায় জয়লাভ করেছে। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে তারা বর্ণহিন্দু ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে জিতেছিলো এবং উনিশশো একাত্তর সালে তারা জিতেছে নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে।
তারপরেও মুক্তিযুদ্ধের যে মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই হচ্ছে। বিশেষ করে যে শাসকশ্রেণী মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের ক্ষমতা লাভের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। শাসকশ্রেণীর এই চিন্তা শিল্পী- সাহিত্যিক, নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের ওপর যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে তার প্রমাণ সমস্ত নাট্য আন্দোলনই হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আন্দোলন। সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদসহ অন্যান্য শোষকদের চরিত্রকে আড়াল করে কেবল দালাল-রাজাকার ও মোল্লাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল শত্রুকে ছাড় দিয়ে শুধু একপেশেভাবে দালাল রাজাকারদের বিরোধিতা করা।
উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, নাটকের গতিপ্রকৃতি শুধুমাত্র নাট্যকারের খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না; প্রায় সময়ই শাসকশ্রেণীর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। নাট্যকার যেটাকে মনে করছেন তাঁর নিজের ইচ্ছা, সেটা আসলে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থ দ্বারা, শাসকশ্রেণীর ইচ্ছা দ্বারা। যেটাকে তিনি একান্তভাবে তাঁর স্বাধীন মতামত বলে মনে করছেন, একটু দূর থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেটি আসলে শাসকশ্রেণীর দর্শন।
অনেক সময় নাট্যকার নিজেই জানতে পারেন না তিনি অন্যের মতামত প্রতিধ্বনিত করছেন মাত্র। শাসকশ্রেণীর মতাদর্শটা তাঁর মজ্জার ভেতরে ঢুকে গেছে, তাঁর চিন্তার অভ্যাসকে পর্যন্ত প্রভাবিত করছে। তিনি তাঁর চেতনে এবং অবচেতনে হয়ে উঠেছেন শাসকশ্রেণীর প্রচারক। কারণ তিনি শাসকশ্রেণীর নানা সুবিধাগুলো ভোগ করছেন। না খেয়ে থাকা সাধারণ জনতার আর্তনাদ তাই তাঁর কানে পৌছায় না।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকে আমরা সেই সত্যটাই দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা বলা হচ্ছে, এই চেতনা শাসকশ্রেণী কিংবা সুবিধাভোগীশ্রেণীর চেতনা; শোষিতশ্রেণীর কিংবা নিম্নবর্গের চেতনা নয়। শ্রমিক-কৃষক তথা নিম্নবর্গের মানুষরাই হচ্ছে জনগণের ব্যাপক অংশ। জনগণের এই ব্যাপক অংশ যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে নাট্যকর্মীদের প্রচার চালানোর প্রয়োজন পড়তো না। জনগণের ব্যাপক অংশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না বলেই নাট্যকর্মীরা সেই চেতনাকে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, যা একটি খণ্ডিত চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় দিক ছিলো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নব্বইয়ের দশকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে তা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত।
সাধারণ জনগণের, শোষিত মানুষের এই চেতনাকে ধারণ করার কোনো কারণ নেই প্রধানত এই জন্য যে, স্বাধীনতা তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দেয়নি। ব্রিটিশদের শোষণ থেকে পাকিস্তান লাভ আর পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম শোষিতদের জন্য একই ফলাফল বহন করে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও তারা নিপীড়িত, রাষ্ট্র ও সরকারের আইন দ্বারা নিগৃহীত। পক্ষান্তরে মধ্যবিত্তরা এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নানা ধরনের সুবিধা লাভ করেছে ব্যবসা- বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি সর্বাঙ্গনেই। মধ্যবিত্তদের মধ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি দল। একদল সুবিধাভোগী ও শাসকশ্রেণীর কাছাকাছি অবস্থান করে, অনেক ক্ষেত্রে তারা শাসকদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। অন্যরা পশ্চাদপদ মধ্যবিত্ত এবং শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহ প্রার্থী। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের সুবিধাভোগী অংশটি মুক্তিযুদ্ধের পর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং নানাভাবে শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে।
স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সুবিধাভোগী এই মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং নিম্নবর্গের বিভিন্ন শোষিতশ্রেণী সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অবস্থানে রয়েছে। নিম্নবর্গ যেমন শাসকশ্রেণী দ্বারা শোষিত হচ্ছে, মধ্যবিত্তশ্রেণী তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোষিত হলেও শাসকশ্রেণীর শোষণের ভাগ পাচ্ছে। মধ্যবিত্ত এই সুবিধাভোগীদের স্বার্থ আর নিম্নবর্গের শোষিতশ্রেণীর স্বার্থ এক নয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাই দু পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভিন্ন। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এক ধাপ এগিয়ে গেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকেও প্রসারিত করেছে কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির প্রশ্নে এই যুদ্ধ কোনো ভূমিকা রাখেনি। পাকিস্তানি শোষক চক্রের দ্বারা শোষণের জায়গাটা শুধু বাঙালী শাসকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের সুবিধাভোগী অংশ দখল করেছে।
মধ্যবিত্তরা যে নিজেদের চেতনে এবং অবচেতনে শাসকশ্রেণীর পক্ষ নিচ্ছে তার কারণ শাসকদের লুণ্ঠনের সেও ভাগীদার। ফলে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যারা নিজেদের ভাগ্য পাল্টে নিয়েছে, দিনে দিনে আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, সেই মানুষদের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হৈ চৈ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যেমন পাকিস্তান জন্মের মধ্য দিয়ে যারা গাড়ি- বাড়ি-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করেছিলো, তাদের একটি অংশ ধর্মীয় উন্মাদনায় ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির কারণেই পাকিস্তানের ধ্বংস চায়নি। সেই জন্য সাধারণ বাঙালী মুসলমানরা যখন শোষিত হচ্ছিলো, যখন তারা ক্ষুধা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলো, সুবিধাভোগীরা তখনও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য গৌরব করছিলো।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। বাংলাদেশে জন্ম নেয়ায় যারা সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে স্বাধীনতা তাদের অনেকের কাছেই গৌরবের ব্যাপার। পাকিস্তানের সুবিধাভোগীরা ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করেছিলো, বাংলাদেশের সুবিধাপ্রাপ্তরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা তৈরি করেছে, অন্যপক্ষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্মাদনা তৈরি করেছে জনগণের মধ্যে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার কথা তারা কেউ বলছেন না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিলো জনগণের ভাগ্য পাল্টানো, পকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূলমন্ত্র ছিলো সমাজতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ আসলেও সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ কখনও আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সমাজতন্ত্রের যে প্রশ্নটি ছিলো তা সম্পূর্ণই বাদ দিয়ে রেখেছেন নাট্যকারা ও নাট্যকর্মীরা। স্বাধীনতার মূল একটি প্রশ্ন সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে তাঁরা সেটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে দাবি করছেন।

মানুষের মূল লড়াইটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাঁচার লড়াই। মুক্তির লড়াই। সেটা কখনও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের চেহারা ধরে আসে, কখনও পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন হিসাবে, কখনও মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে। যুদ্ধটা সেখানে প্রধান নয়, মানুষের মুক্তিটাই প্রধান। মুক্তিযুদ্ধের সার্থকতা সেখানে শুধু যুদ্ধে বিজয়ের ভিতরে নয়, জনগণের সত্যিকারের মুক্তিলাভের মধ্যে। যুদ্ধটা সেখানে উপলক্ষ্য, মুক্তিটাই লক্ষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিচার হবে সেই প্রেক্ষিত থেকে। যে-মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই সেই মানুষের মুক্তি ঘটেছে কি না, জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত সুখ, সমৃদ্ধ জীবন লাভ করেছে কি না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকে সে প্রসঙ্গটাই প্রাধান্য পাবার কথা, যা আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটকের মধ্যে দেখতে পাই না।
উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন “কলকাতা শহরে স্বাধীনতা উৎসব চলছিলো। উৎসব পালনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো কংগ্রেস দল। সেদিনই নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে দুঃখীর ইমান নাটকটি দেখানো হয়। সেই নাটক মঞ্চায়নের আগে শিশির কুমার একটি রক্তব্য রেখেছিলেন। শিশির কুমার জানতেন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে তখন জনতা উল্লাস করছে। তা জেনেও তিনি বলেছিলেন, এ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনো মাউন্টব্যাটেনের হাতে। শিশির কুমারের এই বক্তৃতায় দর্শক সেদিন উল্লাস প্রকাশ না করলেও আপত্তি করেনি। ঠিক পরের বছর স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, এ স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা।
মধ্যবিত্ত দশর্কদের ততোদিন স্বাধীনতা সম্পর্কে পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। সেজন্য পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসে তিনি নাটক মঞ্চায়নের আগে বলেন, ‘আজ দুঃখের দিন স্বাধীনতা দিবস নয়। স্বাধীনতা কোথায়? দেশ বিভক্ত হয়েছে, এক বাঙালী, এক পাঞ্জাবী আজ দুই রাষ্ট্রে। ১০ তিনি আরো বলেন, ‘সাধারণ লোকের খাদ্যের কথা বিচার করুন। দেশে আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা-রেশনের চালে পাথর খেয়ে খেয়ে রেশনের এলাকার লোকেরা পেটের রোগে মরণাপন্ন। ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। মানুষ যদি মানুষের মত খেতে এবং বাস করতে না পারে কিসের স্বাধীনতা?১৬ শিশির কুমার মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা।
সেই তিনিও মানুষের দুঃখে স্বাধীনতা সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দেখেও স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের কেন উত্থান ঘটলো সেটাই ছিলো নাট্যকারদের মূল ক্ষোভ। স্বাধীন দেশে বিরাট জনগোষ্ঠী না খেয়ে আছে কেন, শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি ঘটছে না কেন সে প্রশ্ন তাঁরা তোলেননি। শ্রমিক-কৃষকদের মুক্তির প্রশ্ন বাদ দিয়ে কোনো নাটকই মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাজনৈতিক নাটক হতে পারে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নাটক সেক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তার সম্পূর্ণ বাইরে রয়েছে। বুর্জোয়া একটি রাষ্ট্রে যারা বুর্জোয়াকে মূল শত্রু হিসাবে না দেখে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমালোচনা না করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে তাঁরা মার্কসীয় চিন্তার বিরোধিতাই করে। মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাট্যচিন্তায় এ ধরনের নাটকের স্থান নেই।
মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বা দালাল রাজাকার ও মৌলবাদ বিরোধিতার নাটক মঞ্চায়নের প্রশ্নে রাজশাহীর অনুশীলন নাট্যদলের মলয় ভৌমিক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের কথা নাটকে উল্লেখ থাকলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এমন ধারণা করার কোনো কারণ নেই। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক প্রতিফলন নাটকে ঘটানো গেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি আরো বলেন, দর্শককে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী করে তোলা এবং সুস্থ জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণা দেয়া যদি নাটকের সাধারণ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে নাটকে স্বৈরাচার ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন পৃথকভাবে করার প্রয়োজন পড়ে না।
এ ধরনের পৃথকীকরণ নাটককে চটুল রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত করে যা ইদানিং বাংলাদেশের অনেক নাটকে দেখা যাচ্ছে। দর্শকের চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে এসব নাটক এড়িয়ে যায়; প্রকারান্তরে যা স্বৈরাচার ও মৌলবাদকেই শক্তিশালী করতে পারে। তিনি নব্বই সালে দেয়া ঐ সাক্ষাৎকারে আরো উল্লেখ করেন, দুই দশক ধরে এদেশে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার পরও সাধারণ গ্রামীণ জনসমাজে এর প্রভাব উল্লেখ করার মতো নয়। চট্টগ্রামের অরিন্দম নাট্য সম্প্রদায়ের কর্ণধার ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শিশির দত্ত প্রশ্ন তোলেন, নাটকে মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়ের যে সকল কথা এসেছে সামাজিকভাবে তা কতোটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে?

তিনি মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে দেখলে উৎসাহী হবার মতো তেমন কাজ খুব একটা চোখে পড়ে না। বেশি কাজ হয়নি বলেই দুই একটা যা হয়েছে তাকে অনেকেই খুব বড় করে দেখছে। তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ চেতনা যেখানে সবখানে ভুলুন্ঠিত সেখানে আমাদের নাটকেই কেবল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে এমনটি ভাবা কি সঠিক হবে?’
মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রসঙ্গে মঞ্চায়িত নাটক সম্পর্কে উন্মা প্রকাশ করেন নরসিংদীর সংকেত নাট্যগোষ্ঠীর তপন দাস। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম সুকৃতি হিসাবে গ্রুপ থিয়েটার চর্চাকে আখ্যায়িত করা যায় না। নাট্যকার, নাট্যকর্মী, নাট্যগোষ্ঠী ও নাটক অধিকাংশই ভুলপথ যাত্রী। তিনি আরো বলেন, নাটক যদি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয় তাহলে প্রথমে প্রশ্ন আসে আমাদের শত্রু-মিত্র কে? কাকে আমরা সেই হাতিয়ার বা নাটক দিয়ে আঘাত করবো। শুধু স্বৈরাচার বা মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে কি আমাদের চূড়ান্ত মুক্তি আসবে? তবুও কিছু কিছু নাট্যকার তাদের নাটকে স্বৈরাচার ও মৌলবাদ বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা নিজেকে জাহির করার স্থূল লক্ষ্যেই করে থাকেন।
মুক্তিযুদ্ধের এসব নাটক প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়টি খুবই আপেক্ষিক এবং ব্যাপক। যদি মৌল আদর্শের কথা বলি তাহলে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বারবার লংঘিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক করলেই এই চেতনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে এ কথা ভাবা যায় না। বরং বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটকগুলিতে একেবারেই উল্টো কিছু বিষয় চলে এসেছে। তিনি বলছেন, চেতনার বিষয়টি আরো গভীর এবং চেতনাকে যাঁরা ধারণ করবেন তাঁদের প্রশ্নটাও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একথাও স্বীকার করেন, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে চিৎকার করাটা অদ্যাবধি একটা ফ্যাশনের অংশ ।
সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও ঢাকা পদাতিক নাট্যদলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস এ ব্যাপারে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নাটকে প্রতিফলিত কি না এ বিষয় আলোচনার আগে বুঝতে হবে সত্যিকারভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী? এই মৌলিক বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নিজ নিজ শ্রেণী ও দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করছে।
এ ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের চেতনাকে আত্মস্থ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। তিনি বলছেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থানের অধিকার আদায় বা শোষণমুক্ত সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অধিকার ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা।
তিনি নব্বই সালে দেয়া ঐ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন, ‘বর্তমানে নাটকের দল এবং নাটকের সংখ্যা অনেক হলেও সে তুলনায় বলিষ্ঠ বক্তব্য সম্পন্ন মঞ্চ নাটক আমরা কটা পেয়েছি? আসলে আমরা যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হই বা সত্যিকারের জনকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হই তবে মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে মঞ্চে উপস্থাপন সম্ভব নয়। কারণ লক্ষ্য নির্ধারিত না থাকলে উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম কখনো সুফল বয়ে আনে না।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 12 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৩ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/নব্বইয়ের-দশক-মধ্যবিত্তের-নাট্যচর্চার-শেষ-পরিণাম-পর্ব-৩--1024x536.jpg)
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৩ ]
মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগীশ্রেণীর নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের নাটক নিয়ে হৈ চৈ করলেও তাঁরা যে সে ব্যাপারেও আন্তরিক ছিলেন না তারও প্রমাণ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কথা ঘোষণায় বলা হলেও সে সময়ের দলগুলো যে সত্যিকারভাবে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নাটক মঞ্চস্থ করছিলো পরবর্তীতে আমরা তা দেখতে পাবো। মুক্তিযুদ্ধ শব্দটিকে তারা যতো গালভারি বুলি হিসাবে ব্যবহার করেছে, দেখা যাবে তাদের নিষ্ঠা সেভাবে প্রমাণিত হয়নি। মূলত নাটক মঞ্চায়নে তারা নানাভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছে। সেজন্য সুযোগ পেলেই তারা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যবিহীন হাসির নাটক মঞ্চস্থ করেছে, যা অনেক সময় রুচির দিক থেকেও ছিলো নিম্নমানের।
একইভাবে তারা রাজনৈতিক বক্তব্যবিহীন লোকনাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারেও ছিলো সমানভাবে আগ্রহী, যে-সকল লোকনাটক কুসংস্কার ও ধর্মীয় প্রভাব দ্বারা ছিলো আচ্ছন্ন। নাট্যদলগুলোর চিন্তার স্ববিরোধিতা ধরা পড়ে তাদের লোকনাট্য মঞ্চায়নে। মুক্তিযুদ্ধের নাটকে যেখানে তারা কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসনকে আঘাত করেছে, লোকনাটকে আবার তারা সেগুলিকেই প্রচার করেছে। নাট্যদলগুলোর লোকনাট্য মঞ্চায়নের ভিতর দিয়েই তাদের চিন্তার স্বরূপটি ফুটে ওঠে। সেজন্য এ অধ্যায়ে আমরা লোকনাট্য মঞ্চায়নের নানা – দিকগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবো।
নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে লোকনাট্য করার প্রবণতা সত্যিই খুব বেড়ে যায়। তার একটি কারণও ছিলো, নাট্যদলগুলোর নাটকে দর্শকদের সংখ্যা ভীষণ কমে গিয়েছিলো। সে অবস্থায় দলগুলো বুঝতে পারছিলো না কী ধরনের নাটক করলে দশর্কদের মিলনায়তনে টেনে আনা যাবে। দর্শক কমে যাওয়ায় তখন থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, নাগরিক ছাড়া সকলকেই ভাবতে হচ্ছিলো কী করে মিলনায়তন দর্শক দিয়ে পূর্ণ করা যায়। উল্লিখিত তিনটি দল তখনো তাদের নাটকের প্রযোজনার গুণে ও পাশাপাশি টেলিভিশন তারকাদের বদৌলতে দর্শক পাচ্ছিলো। দর্শক সংকটের কারণেই বড়-ছোট সকল নাট্য দলগুলোর কাছে তখন আদর্শ কিংবা তথাকথিত গ্রুপ থিয়েটার চেতনা আর বড় ছিলো না। যে-কোনো প্রকারে দর্শককে মিলনায়তনে নিয়ে আসাই ছিলো তাদের লক্ষ্য।
লক্ষ্য পূরণের কোনো একটি পথ তখন তারা খুঁজে ফিরছিলো। সেই অবস্থায় ঢাকায় আরণ্যকের নাট্যোৎসবে কলকাতার অন্য থিয়েটার মঞ্চস্থ করতে এলো ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে তাদের নতুন নাটক মাধব মালঞ্চী কইন্যা। সেই নাটক বিপুল সাড়া ফেললো নাট্যদল ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে। কলকাতার মঞ্চেও এই নাটক বিপুল সাড়া ফেলেছিলো। কলকাতায় যখন গ্রুপ থিয়েটারগুলোর নাটকে দর্শক কমে আসছিলো মাধব মালঞ্চী কইন্যা সেখানেও দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলো। স্বভাবতই এখানকার নাট্যদল ও নাট্যকর্মীদের মনে হলো, দর্শক ধরে রাখার জন্য মাধব মালঞ্চী কইন্যার মতো নাটকেই হচ্ছে আদর্শ নাটক।
উননব্বই সালের নভেম্বর মাসে থিয়েটার ঢাকায় এক নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। সে উৎসবের নামকরণ করা হয়েছিলো ‘উৎসের সন্ধানে: থিয়েটার উৎসব’। থিয়েটার সে উৎসবে কবির লড়াই, পালাগান, গম্ভীরা ও ঝুমুর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, সে সময়ের মঞ্চ নাটকের সাথে যার কোনোরকম সম্পর্ক ছিলো না। থিয়েটার সবসময়ই মঞ্চে আধুনিক নাট্যরীতির চর্চা করেছে।
গেরাসিম লিয়েবেদেফ ভারত ভূখণ্ডে পাশ্চাত্যধারার যে থিয়েটার আমদানি করেছিলেন থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী ছিলো সেই ধারারই উত্তর-সাধক। ১২ দলটির নামকরণও করা হয়েছে বিদেশি শব্দে। থিয়েটার তার জন্মলগ্ন থেকে, এ উৎসবের মাসখানেক পূর্ব পর্যন্ত যে বিশটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলো তার কোনোটিই লোকধারার ছিলো না। অথচ উৎসবের কিছুদিন পূর্বে তারা ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে বিষলক্ষ্যার ছুরি নাটকটি মঞ্চস্থ করে। তারপরেই তারা উৎসের সন্ধানের ঘোষণা দেয়। সে উৎসের সন্ধান যে কী সে সম্পর্কে তারা কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখেনি।
নাট্য উৎসবের স্মরণিকায় শুধু বলা হয়েছিলো, ‘নাটকের মুক্তির সন্ধানে আমরা দৃষ্টি ফেরাই পেছনের দিকে, হাজার বৎসরের জীবনচর্যার ধারায় বাংলার মানুষ যে সংস্কৃতি ও শিল্পরূপ গড়ে তুলেছে, নদী-বিধৌত পলিমাটির জনগোষ্ঠী শত বিপত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৃজনশীলতার ফল্গুধারায় যেভাবে জীবনকে সিক্ত করেছে, সংস্কৃতির সেই আদিরূপের পরতে পরতে নাট্য উপাদান সমূহ কিভাবে মিশে আছে আমরা তা গভীরভাবে বুঝে নিতে চাই। লোকায়ত বাংলার সুরধ্বনির যে বহুবিচিত্র ও বহুব্যাপ্ত প্রকাশ সেখানে বারবারই বিচ্ছুরিত হয়েছে নাটকের একান্ত বিশিষ্টতা। বিশ্বমানবের সংস্কৃতিসাধনায় বাঙালী জাতিও যোগ করেছে তার নিজস্ব রূপ-রস-বর্ণ গন্ধময় সৃষ্টিশীলতা।’
সেখানে আরো বলা হয়েছিলো, ‘লোকজীবনের গভীর থেকে উৎসারিত এই সংস্কৃতিধারার সঙ্গে আমাদের বিযুক্তি ঘটে গেছে বহুকাল আগে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানী যুগের সাম্প্রদায়িক কলুষ-দৃষ্টি এবং পুঁজিশাসিত শোষণভিত্তিক সমাজের বিকৃত জীবনাদর্শ বিভাজিত ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সমাজকে। আজও শাসক ও কর্তৃত্ববান শ্রেণী কখনও ধর্মের ধ্বজা তুলে, কখনও জাতিসত্তার বিকৃত ব্যাখ্যার সাহায্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগধারার সাধনাকে বিপথগামী করতে সচেষ্ট।
সেখানে আরো বলা হলো, উৎসের সন্ধানে যে নাট্যোৎসব তা পেছন দিকে দৃষ্টি ফেরানো নয়, বর্তমানকে বিকশিত ও আগামীকে প্রতিশ্রুতিময় করে তোলার জন্যই মুখ ফেরানো অতীতের দিকে। ধমনীতে অনুভব করা যুগ-পরম্পরায় বহমান সংস্কৃতি ধারার শক্তি। যার লক্ষ্য জাতির কাছে, দেশমাতৃকার কাছে দায়মোচনের মধ্য দিয়েই নাটকের শিল্পিত সাধনায় নতুন প্রাণপ্রবাহ শুরু করা।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 13 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৩ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-১.jpg)
থিয়েটারের উপরের এই বক্তব্য কিছুই স্পষ্ট করে না বরং পরস্পর বিরোধী মনে হয়। থিয়েটার পিছনে ফিরতে চায় না, আবার পিছনের ঐতিহ্যকে অনুভব করতে চায়, যার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরা পড়ে না। জাতির কাছে, দেশমাতৃকার কাছে দায়মোচন যে কী বা বাঙালীর নাট্য সাধনা বলতে থিয়েটার কী বোঝাচ্ছে সেটাও এখানে পরিষ্কার নয়। যেটা আমরা বুঝতে পারি তাহলো, বাংলার ঐতিহ্য ও লোকায়ত ধারাকে থিয়েটার গুরুত্ব দেয়ার কথা ভাবছে। সেই স্মরণিকায় উৎসের সন্ধান সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক লিখছেন, ‘নাটকে আমাদের ঐতিহ্য কি, যাকে আমি বলি ‘মাটির নিজস্ব নাট্যবুদ্ধি’-সেইটিও আমাদের জানতে হবে, খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে-এবং, হ্যাঁ, এবং প্রয়োগ করতে হবে আমাদের নাট্যনির্মাণে।
আসলে আমি মনে করি, জানা- খোঁজা-বোঝার চেয়েও যে কাজটি আমাদের করা দরকার তা হলো বাংলা নাটক থেকে নাট্যপ্রযুক্তির যে ধারাটি একদা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো,… বাইরের যে নাট্যপ্রযুক্তি আমরা গ্রহণ করেছিলাম তা এই মুহূর্তে বর্জন করে, ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনা; এই ধারাবাহিকতা আমাদের কথকতা, যাত্রা, পালাগান, কবির লড়াই-এর সংগে, উন্মুক্ত মঞ্চের সংগে, দেহছন্দ এবং কাব্যছন্দের সংগে,… ময়মনসিংহ গীতিকায়-যে ‘গীতিকা’ আমি মনে করি, আধুনিক অর্থে আদৌ ‘গীতিকা’ নয়, ইংরেজী বর্ণনায় ‘ব্যালাড’ নয় বা নয় ‘সাগা’, আমার বিশ্বাস এই ‘গীতিকা’ আসলে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যবুদ্ধি দ্বারা রচিত ‘নাটক’। ‘
শামসুল হক উপরে প্রাঞ্জল করেই বলছেন, বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের কাছে নাটককে ফিরে যেতে এবং বিদেশি নাট্যরীতিকে বর্জন করতে হবে। শামসুল হকের বক্তব্যে বাংলার নাট্য ঐতিহ্য বলতে ময়মনসিংহ গীতিকার কথা চলে আসছে। আর সে বক্তব্য আমরা তার কাছ থেকে পাচ্ছি মাধব মালঞ্চী কইন্যা মঞ্চস্থ হবার পর। বোঝাই যাচ্ছে মাধব-মালঞ্চী কইন্যা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো নাট্যকর্মী ও নাট্যবোদ্ধাদের ওপর। শামসুল হকও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেন আমাদেরকে যখন বলেন, ‘উৎস সন্ধান করব, তার অর্থ এই নয় যে, যা ছিল, তাইই আবার ফিরিয়ে আনব এবং অবিকল ব্যবহার করব; এই ভুলটি আমাদের অনেকেই করে থাকেন এবং ‘উৎস’ বলতে বোঝেন তাঁরা ‘আকর’-ঘটনাটি আদৌ তা নয়।
শামসুল হক তারপর আর এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না। বিষয়টি যে শামসুল হক বা তাঁদের কারো কাছেই স্বচ্ছ ছিলো না তা তাঁদের বক্তব্যের দোলাচল থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি। বরং আমরা বলতে পারি তাঁরা আসলে আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন। থিয়েটার পত্রিকায় যদিও সাতাশি সালেই এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে উৎসের সন্ধানে অভিযাত্রা। একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় যদি উৎস নির্ভর না হয়, তবে সে পরিচিতি স্থায়ী হয় না। নাটক নিয়েও তাই আজ দেশে বিদেশে নানা নিরীক্ষা। নাটকে নিয়ে আসা হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের অনেক নিদর্শন।
তাতে করে একটা জাতির নাটক একটা নিজস্ব রূপ পাচ্ছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। কাজটা মোটেই সহজ নয়। তবুও বাংলাদেশেও এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে, কাজ কর্মও একটু একটু হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে নাটকে এমন কিছু আনা যায় কি না যা দেখে বলা যাবে এটা বাংলাদেশের নাটক। ভারতের হাবিব তানভির তাঁর প্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের ভাষা ও জীবন যাত্রা নিয়ে যে অসাধারণ কাজ করে চলেছেন, তাঁর নয়া থিয়েটারের প্রযোজনাগুলো তার প্রমাণ।
রামেন্দু মজুমদার যখন উপরের বক্তব্য দিচ্ছেন তখন তিনি সে বক্তব্য দিচ্ছেন নয়া থিয়েটারের চরন দাস চোর নাটকটি দেখার পর। লোকজ ধারার ওপর ভিত্তি করে হাবিব তানভিরের চরণ দাস চোর নাটকটি সারা ভারতবর্ষে তখন বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলো। পাশাপাশি ছিলো জব্বার প্যাটেলের ঘাসিরাম কোতওয়াল ও মনিপুরের রতন থিয়ামের নাটকগুলো। ঘাসিরাম কোতওয়াল ছিলো রাজনৈতিক নাটক।
চরণ দাস চোর আন্তর্জাতিক একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলো। বাংলাদেশের সাধারণ নাট্যকর্মীদের তখন পর্যন্ত সে-সব নাটক দেখার সুযোগ হয়নি বলেই লোকজধারার নাটক নিয়ে চিন্তাভাবনা করা তখনও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। উনিশশো উননব্বই সালে ঘটলো পরপর তিনটি ঘটনা। প্রথম আরণ্যকের নাট্য উৎসবে মঞ্চায়িত হলো মাধব মালঞ্চী কইন্যা, তারপর থিয়েটারের উৎসবে পদ্মশ্রী তীজন বাঈর লোকজ ধারার পাণ্ডবানী খুব সমারোহে মঞ্চস্থ হলো এবং তারপর নাগরিকের উৎসবে প্রদর্শিত হলো চরণ দাস চোর। পরপর এই তিনটি নাটকের মঞ্চায়ন এবং থিয়েটার-এর উৎসের সন্ধানে নাট্য উৎসব, ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাবার আহ্বান-সব মিলিয়ে নাট্যকর্মীরা লোকনাট্য সম্পর্কে বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়লো এবং নাট্যদলগুলোর ঘোষিত শ্রেণীসংগ্রাম প্রসঙ্গটি হারিয়ে গেল।
নব্বইয়ের দশকে আমরা দেখবো, রামেন্দু মজুমদার, সৈয়দ শামসুল হক বা শুধু থিয়েটার দলই নয়, বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা ময়মনসিংহ গীতিকাকে খুবই গুরুত্ব দিতে শুরু করে। মাধব মালঞ্চী কইন্যার সাফল্য দেখে এখানকার নাট্যকর্মীদের মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, নাটকের সাফল্য বোধ হয় লুকিয়ে আছে অতীত ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার নাট্যকর্মীরা ‘শেকড়ের সন্ধানে যাওয়া দরকার’ এ ধরনের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে উঠলো। বহু লেখনীতেই তাঁদের এ বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকলো। ঐতিহ্যই সবচেয়ে বড় কথা-সেইরকম বিশ্বাস থেকে শুরু হলো পেছন ফেরা।
প্রায় সকলেই নির্ভর করলো ময়মনসিংহ গীতিকা কিংবা বাংলার লোকজ উপাদানের ওপর, যেখানে ভূত-পেত্নী আর প্রেমের গল্প প্রধান উপজীব্য। লোকজ এই ধারা শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন, লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্মভাবের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং ব্যক্তির ও সমাজের জাগতিক কল্যাণ কামনায় রচিত হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। সাহিত্য বলতে যা বোঝায় এ তা নয়। এ হচ্ছে শাস্ত্রকথার, সংস্কারের, লোককাম্য আদর্শের ও প্রত্যাশার হৃদয়বেদ্য শিল্পায়ন।
আহমদ শরীফ তাঁর একটি প্রবন্ধে আরো দেখাচ্ছেন যে, সারা মধ্যযুগব্যাপী তাই এ সাহিত্য আঙ্গিকে, ছন্দে, বিষয়ে, বক্তব্যে ও লক্ষ্যে বৈচিত্র্যহীন। শাহ-সামন্ত শাসিত অশিক্ষার, দাসত্বের, বৈষম্যের সে-যুগে মানুষের জগতচেতনা ও জীবনভাবনা ছিলো সাধারণভাবে শাস্ত্রনির্ভর তথা বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ন্ত্রিত। ভাগ্যে সমর্পিত দৈবনির্ভর জীবনে রোগে-শোকে, দুঃখে-দৈন্যে, পীড়নে-শোষণে ভরসায় বুক বেঁধে টিকে থাকার ও প্রবোধ পাওয়ার জন্যে বিশ্বাস ছিলো একমাত্র পুঁজি। মধ্যযুগ অবধি সভ্যজগতের সব মানুষের চিন্তা-চেতনা-অনুভব এমনই ছিলো। কিন্তু সবদেশে মধ্যযুগ সমকালীন ও সমপরিসরের নয়। বাংলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো।
তার কারণ এদেশ ছিলো চিরকাল বিদেশি-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী শাসিত। পরাধীন বাঙালীরা বিকৃতভাবে হলেও নিজের ভাবনা ভেবেছে। আত্মপ্রত্যয়ী হবার উপায় ছিলো না বলেই সে হয়েছে দৈবনির্ভর-অদৃষ্টবাদী। তার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রয়োজনেই সে দেব-অনুকম্পা ও দৈবসহায়তা কামনা করেছে। এভাবেই হয়েছে নানা লৌকিক, কালিক ও স্থানিক অরি ও মিত্র দেবতা-উপদেবতার উদ্ভব। ধনে-বলে অসমর্থ বলেই সে মন্ত্রযোগে তাবিজে কবচে দারু-টোনায় বাণে-উচাটনে অলৌকিক শক্তিধর হয়ে দেবতা- দানবকে জব্দ করার ফন্দি এঁটেছে। সেজন্য তাদের দেব কল্পনায় জীবনের কোনো মহৎ ও বৃহৎ আদর্শের ও উদ্দেশ্যের সন্ধান মেলে না।
জীবনের কোনো গভীর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনাও নেই এসব দেবকাহিনীতে। স্বার্থসচেতন সংকীর্ণচিত্ত ভীরু-ধূর্ত মানুষের মাটি- সংলগ্ন জৈবজীবনের স্কুল ও তুচ্ছ ভয়-ভরসা আশা-প্রত্যাশা মূর্ত হয়ে উঠেছে এসব দেবপ্রতিমায় এঁদের গুণ-মান-মাহাত্ম্য কল্পনায়। মধ্যযুগের সমাজমানসের এই রূপ তার সাহিত্যে প্রতিফলিত। মধ্যযুগের সাহিত্যও তাই বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, গানে গল্পে রসিয়ে বলা শাস্ত্র-কথা মাত্র। সেখানে গর্ব করার মতো কুচিৎ কিছু মেলে।” ময়মনসিংহ গীতিকার ক্ষেত্রে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। সেখানে মানুষের অন্ধত্ব ও কুসংস্কারই বড় হয়ে ওঠে।
মাধব মালঞ্চী কইন্যা এই নাটকটির মধ্য দিয়েই যেহেতু লোকনাট্য চর্চার চিন্তা জন্ম হয়েছিলো এখানকার নাট্যকর্মীদের মধ্যে, নাট্যকর্মীদের শেকড়ের সন্ধানের পেছনেও যখন ছিলো মাধব মালঞ্চী কইন্যার সাফল্য-তখন উপরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই এই নাটকটি নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার। নাটকটির বিষয়বস্তু মাধব মালঞ্চীর প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমের মিলনে নাটকের পরিণতি।
নাটকটির গল্প শুরু হয় এভাবে, বৃদ্ধ রাজা দুর্লভ, মৃত্যু তার সন্নিকটে। রাজার স্ত্রী বিগত, ছয় পুত্রের জনক তিনি। শেষ পুত্র মাধব তখন খুবই ছোট। রাজা মৃত্যুর আগে পুত্রবধূ চন্দ্রবন কন্যার হাতে মাধবের দেখা শুনার ভার দেন। পিতার মৃত্যুর পর বয়স্ক পাঁচ ভাইর মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে চন্দ্রবন ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে বিরোধ এড়িয়ে গণক নজ্জমের সহাযোগিতা নিতে বলে। গণকের বিচারে দেখা গেল, জ্যেষ্ঠ পাঁচ ভাই নয়, কনিষ্ঠ মাধবই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। গণনায় বারবারই মাধবের নাম আসছে দেখে বাকি ভাইরা এ ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে মাধবকে হত্যা করার চিন্তা করে। চন্দ্রবন ভয় পায়, মাধবের জীবন রক্ষার জন্য সে মাধবকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলে।
মাধব বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হলে চন্দ্রবন তাকে একটা হার দেয়। যে হার গলায় থাকলে ছয়মাসের পথ এক দণ্ডে পার হওয়া যাবে। শেকড়ের সন্ধানে নাটক এভাবেই আবার রূপকথার জগতে ফিরতে শুরু করে। যেখানে মানুষ পরিশ্রম বাদ দিয়ে কল্পরাজ্য গড়ে তোলে। ছয়মাস পথ হাঁটার শ্রমকে সে মুহূর্তে পার হতে চায় অলৌকিকভাবে। মানুষের সংগ্রামে যাদের আস্থা নেই বা ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তারা কল্পরাজ্যর পথেই সমস্যার সমাধান খোঁজে। নাট্যকার তাই মাধবকে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি করার চেয়ে অলৌকিক হারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলেন।
মাধব ঘর ছাড়ার পর অন্যদেশের এক জঙ্গলে ঘুমিয়ে পড়লে সে দেশের উজির প্রাতঃকর্ম সারতে এসে মাধবকে দেখতে পায়। মাধবের রূপের ছটায় তখন জঙ্গলের অর্ধেক আলোকিত হয়ে আছে। মাধব নিজেকে আশ্রয়হীন বলে পরিচয় দিলে উজির তাকে নিজ গৃহে নিয়ে আসে। নিঃসন্তান উজিরের স্ত্রী মাধবকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে। রাজার কন্যা মালঞ্চী পড়াশুনা করছে যে পণ্ডিতের কাছে উজিরের পোষ্য মাধবেরও সেখানে পড়াশুনার সুযোগ ঘটে এবং যথারীতি রচয়িতার কল্পনার জোরে মাধব সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে ফেলে। তাকে শেখাবার মতো পণ্ডিতের আর কোনো জ্ঞানই বাকি থাকে না।
মালঞ্চীর পড়াশুনার উন্নতি ততোটা ঘটে না। মালঞ্চী মাধবের নাম শুনেছে, দেখেনি, যদিও ঘরের নিচতলায় মাধব আর উপরে মালঞ্চীর বাস। মেধাবী মাধবকে এক নজর দেখার জন্য সে উপর থেকে নিজের কলমটা নিচে ফেলে দেয়। মাধব সেটা মালঞ্চীকে ফিরিয়ে দিতে গেলে দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম সাক্ষাতেই মাধব মালঞ্চীর প্রেমে পড়ে যায় এবং মালঞ্চীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। মাধবকে মালঞ্চীর জিজ্ঞাস্য যে, সে রাজকন্যা, চাকর মাধব তাকে বিয়ে করতে চায় কোন সাহসে? মাধব উত্তর দেয়, মালঞ্চীর বাবার মতো রাজারাও মাধবের বাবার চাকর ছিলো। মালঞ্চী সেটা জানার পরই মাধবকে বিয়ে করতে রাজি হয়। মাধব মালঞ্চীর এই প্রেম তাহলে কী দাঁড়ালো?
প্রেমের চেয়ে সম্পদকেই মালঞ্চী সেখানে অগ্রধিকার দেয়। সারা নাটক জুড়ে। রচয়িতা সেই প্রেমেরই মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। মালঞ্চী মাধবকে জানায় একদিন আগেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে অন্য এক রাজার সাথে, সে সাত মন সোনা দিয়ে বিয়েটা পাকা করে গেছে। একদিন পরই তার সেই রাজার সাথে বিয়ে। মাধব যদি দিবস পার হয়ে যাবার পর যে-রাত আসবে সেই রাত পোহাবার আগে মনপবনের নাও নিয়ে মালঞ্চীর নিদের্শিত জায়গায় হাজির থাকতে পারে, তাহলে সে মাধবের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। মাধব সে শর্তে রাজি হয়। মাধব রাজকন্যাকে কথা দিলেও মনপবনের নাও জোগাড় করা সহজ ছিলো না। সে রাতের বেলা গলার হারছড়ার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে বড় ভাইর স্ত্রী চন্দ্রবনের কাছে হাজির হলো। ভাবীর কাছে সে রাত পোহাবার আগেই একটি মনপবনের নাও আব্দার করলো।
মাধবের ইচ্ছা পূরণের জন্য চন্দ্রবন পেয়াদা পাঠালো মনা পুতারের বাড়ি এই হুকুম দিয়ে যে, রাত পোহাবার আগে তার মন পবনের নাও চাই। না হলে মনা পুতারের পরিবারের সকলের গর্দান নেয়া হবে। মাত্র এক রাতের মধ্যে মনপবনের নাও তৈরি করা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। সবগুলো দাবিই এখানে অযৌক্তিক। মালঞ্চীর মনপবনের নাওয়ের দাবি যেমন অযৌক্তিক এবং নাও না পেলে মনা পুতারের পরিবারের জন্য চন্দ্রবন যে শাস্তির বিধান করেছিলো সেটিও ছিলো রীতিমত অন্যায়। অথচ দুটো দাবির প্রতিই রচয়িতার সমর্থন আছে। মাধবের জন্য ভ্রাতৃবধূর উদারতাই এখানে তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের প্রয়োজনে যে-কোনো ভাবে মাধব মালঞ্চীর প্রেম সার্থক • হওয়াটাই রচয়িতার প্রধান লক্ষ্য, ন্যায়-অন্যায় বিচার করা তার কাজ নয়।
মাধব মালঞ্চীর এই প্রেম কিন্তু কোনো সাধারণ লোকের প্রেম নয়। প্রেমটি রাজকন্যা আর রাজপুত্রের। সেই প্রেমের সার্থকতার জন্য যথাসময়ের মধ্যে মনা পুতারের ছেলে নাতিরা মিলে মনপবনের নাও তৈরি করে দেয়, আর সে অসাধ্য সাধিত হয় শুধুমাত্র রচয়িতার কল্পনার দ্বারা-বাস্তবে যা সম্ভব ছিলো না। নাও নিয়ে মাধব চলে যায় মালঞ্চীর শর্ত দেয়া নির্দিষ্ট জায়গায়। মালঞ্চীর আসতে দেরি দেখে অস্থির মাধব নাও রেখে ঢুকে পড়ে রাজবাড়ির মধ্যে এবং বিয়ের হৈ চৈ-এর মধ্যে জড়িয়ে যায়। এদিকে হাছইনা পাটনি, যে নৌকায় লোক পারাপার করে, সে রাজবাড়িতে বিয়ের খাওয়া খেয়ে এসে নিজের নৌকা আর খুঁজে পায় না। মনপবনের নাওটাকে নিজের নাও ভেবে তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। মালঞ্চীও বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মনপবনের নাওয়ে উঠে পড়ে এবং ঘুমন্ত পাটনিকে সে মাধব মনে করে।
মাধবের ঘুমের ব্যঘাত না ঘটিয়ে সে নিজেই নৌকা ভাসিয়ে দেয়। বহুদূর চলে আসার পর তার ভুল ধরা পড়ে। তখন আর ফিরবার পথ নেই। পাটনিকে মারধর করে সে নিজের রাগ ঝাড়ে। পরে খাওয়ার আয়োজন করার জন্য পাটনিকে বাজারে পাঠায় হাতের দুটো কঙ্কণ দিয়ে। বাজারের লোকরা সেই দামী কঙ্কণ নিতে চায় না, পাটনিকে তারা চোর মনে করে। পাটনি শেষে টাকার জন্য সেই কঙ্কণ দিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে কঙ্কণও হারায় এবং নিজে জুয়াড়ীদের দাসে পরিণত হয়। জুয়াড়ীরা তাকে বেঁধে রাখে। পাটনিকে ফিরতে না দেখে মালঞ্চী সিপাহীর বেশ ধারণ করে।
সিপাহীর পোষাক কোথা থেকে আসলো সে প্রশ্নের জবাব নেই। সিপাহী সেজে মালঞ্চী জুয়া খেলে নিজের কঙ্কণ ও পাটনিকে উদ্ধার করে। মালঞ্চী চালডাল জোগাড় করে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করতে থাকলে পাটনি পুনরায় রাজকন্যার মারধরের ভয়ে মনপবনের নাও নিয়ে পালিয়ে যায়। মালঞ্চী তখন হেঁটে হেঁটে মাধবের সন্ধান করতে থাকে। হেঁটে হেঁটে সন্ধান করা কষ্টকর বলে সে একটি ঘোড়া কিনে নেয়। মালঞ্চীকে সিপাহীর বেশে ঘোড়া চালাতে দেখে সে দেশের রাজা মুগ্ধ হয় এবং মালঞ্চীকে পুরুষ ভেবে নিজের সেনাবাহিনীতে চাকরি দিতে চায়। মালঞ্চী একহাজার টাকা রেতন দাবি করে।
রাজা শর্ত দেয় যে, তাকে একহাজার টাকা বেতন দেয়া হবে যদি সে গাঁয়ের সেই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলতে পারে, যে প্রতিরাতে একজন করে মানুষ খায়। রাজা জানায়, আগে রাক্ষসটা আরো বেশি মানুষ খেতো কিন্তু রাজার সাথে শর্ত মতো এখন তাকে প্রতিরাতে একজন করে মানুষ দিতে হয়। মালঞ্চী রাজি হয় সেই রাক্ষসটাকে মারার জন্য এবং দুটি তরবারি চায়। গ্রামের সমস্ত লোকরা মিলে হাজার সৈন্যবাহিনী মিলে যে রাক্ষসটিকে মারতে পারলো না, মালঞ্চী একাই সে রাক্ষসকে বধ করে। এটাই ‘ বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ ও সামন্তযুগের কল্পকাহিনী। ব্যক্তিই এখানে বিরাট ক্ষমতার উৎস, একজন ব্যক্তির হাতেই এখানে সকল ন্যায়-অন্যায়ের পতন ঘটে, যা অনৈতিহাসিক।
মার্কসবাদীরা মনে করেন, সমাজ বিপ্লব সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, বা যারা সমাজ বিপ্লব চায় না-তারা এভাবেই সমাজের খারাপ কিছুর পতন দেখিয়ে দশর্কদের বিভ্রান্ত করে, বাস্তবে যা সম্ভব নয়। সেই ব্যক্তিবাদেরই জয় দেখি মালঞ্চী চরিত্রে। ইতিহাসের আলোকে নয়, নিজের খেয়ালখুশি মতোই রচয়িতা মালঞ্চীকে নির্মাণ করেছেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাটকে এ ধরনের চরিত্র নির্মাণ গ্রহণযোগ্য নয়।
রাজা মালঞ্চীর কাছে নিজের কন্যাকে বিয়ে দিতে চায়। মালঞ্চীর কাছে তো সে প্রস্তাব মেনে নেয়া আর সম্ভব নয়। মালঞ্চী তাই মাধবকে খুঁজে পাবার জন্য এবং কিছু সময় লাভের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে বিয়ে করার পূর্ব শর্ত হিসাবে রাজাকে একটি দীঘি কাটার কথা বলে। রাজা সে প্রস্তাব মেনে নেয়। দীঘি কাটার বিরাট আয়োজন সম্পন্ন হয়। বহুলোক জড়ো হয় সে দীঘি কাটার জন্য। বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। মাধবও মালঞ্চীকে খুঁজতে খুঁজতে অর্থাভাবে সেই দীঘি কাটতে আসে, সেখানে মাধব মালঞ্চীর আবার সাক্ষাৎ হয়। রাজা তখন মালঞ্চীর আসল পরিচয় জানতে পারে, জানতে পারে মাধব সম্পর্কে। দুজনের বিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিণিত ঘটে।
বিভাস চক্রবর্তী মাধব মালঞ্চী কইন্যা নাটকে যেভাবে বাস্তব সমস্যা এড়িয়ে রূপকথার আশ্রয় নেন এবং বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে আঙ্গিক নিয়ে মাতামাতি করেন তার প্রেক্ষিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত নাটকটি সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে লিখছেন, ‘প্রগতিশীল থিয়েটারে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সমধিক। আঙ্গিক আসে তারই প্রয়োজনে। আঙ্গিক কখনো বিষয়ের বিকল্প হতে পারে না।’
সমালোচক আরো লিখছেন, ‘যদিও বিভাস বাবুর প্রযোজনা আঙ্গিক সর্বস্ব নয়, তবুও মাঝে মাঝেই আঙ্গিক ছাপিয়ে গেছে বিষয়কে। একথা নিশ্চয় বিশ্বাস করতে চাই যে বিভাস বাবু আঙ্গিক সর্বস্ব থিয়েটারবিন্দের পদানুসারী নন। আশা নিয়ে থাকবো যে তাঁদের পরবর্তী প্রযোজনা প্রমাণ করে দেবে যে লোক আঙ্গিকের সার্থক ব্যবহারে বর্তমান সময়ের জীবন্ত সমস্যাগুলি নাট্যায়িত করতে তাঁরা পিছপা নন।’বিভাস চক্রবর্তীর মাধব মালঞ্চী কইন্যা নাটকে সমকালীন জীবন যে প্রতিফলিত নয়, সমালোচক তা খুব ভদ্র ভাষায় বলে দিয়েছেন; এবং নাটকটি যে বাস্তব জীবন বর্জিত একটি রূপকথা সমালোচনার অন্যত্র তিনি সে-কথা বলতেও দ্বিধা করেননি।
সমালোচক বিভাস চক্রবর্তীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেননি যে, ‘শিল্প তো শিল্পের জন্যই নয়, মানুষের কাছে সহজে পৌছোবার উপর-ই তো শিল্পকে খুঁজে বের করতে হয়। লোক সংস্কৃতির প্রচারের জন্যই নাটক প্রযোজনা করতে হবে-মার্কসীয় দৃষ্টিতে এই ধরনের প্রবণতা প্রতিক্রিয়াশীল।
নাটকটির রূপকথা বা অবাস্তব সবদিক যদি এ আলোচনার বাইরে রাখা হয়, তাহলেও প্রশ্ন দাঁড়ায় নাটকটির মূল বক্তব্য বা মূল বিষয়বস্তুটি কী? নাটকটির মূল বিষয়বস্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাধব-মালঞ্চীর প্রেম। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো সমাজ পরিবর্তনের যে শ্লোগান তুলেছিলো, একজন রাজকুমার এবং একজন রাজকুমারীর এই প্রেমের গল্প সমাজের সে পরিবর্তন আনতে পারে কি? মাধবের মতো একজন যুবক যার দেশ জাতি নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, যে একটি নারীর প্রতি দুর্বলতাবশত সবকিছু করে চলেছে তার সাথে জনগণের ভাগ্যের সম্পর্ক বা সমাজ পরিবর্তনের সম্পর্ক কোথায় সে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক।
মাধব-মালঞ্চীর প্রেমের পথে বাধা কোনো সমাজ নয় যে তারা প্রেমের জন্য সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। সমাজের সাথে এখানে ব্যক্তির কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মাধবের প্রেমের পথে বাধা তার নিজের কর্মদোষ। সমাজ ব্যবস্থার কোনো দ্বন্দ্বই এখানে ফুটে ওঠেনি, কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও ঘোষিত হয়নি এ নাটকে। সমাজ পরিবর্তনের নাটকের কাজ দর্শককে সচেতন করে তোলা। মাধব মালঞ্চীর মতো নাটক দর্শককে কোনো বিষয়ে সচেতন করতে পারে না বরং নানা কুসংস্কার জন্ম দিতে পারে কিংবা দর্শকদের সংগ্রামবিমুখ করে তুলতে পারে। মাধব-মালঞ্চী কইন্যা নাটকের বক্তব্য তো এই যে, একজন নারীর একজন পুরুষের জন্য এবং একজন পুরুষের একজন নারীর জন্য জীবন যৌবন সব বিসর্জন দেয়ার মধ্যেই গৌরব।
যদি সেই পুরানো প্রেমের কাহিনীকে নাটকের বিষয়বস্তু করতে হয়, যদি প্রেমের গল্পকেই আবার ফিরিয়ে আনতে হয়-তাহলে স্বাধীনতার পর পুরানো বিষয়বস্তুকে বাদ দেয়ারই বা কী দরকার ছিলো কিংবা নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানেরই বা কী প্রয়োজন পড়েছিলো সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্নটি এসে যায়। বাংলাদেশের নাটকের বিষয়বস্তু তো স্বাধীনতার পূর্বেও ছিলো ড্রইং রুমের গল্প, আর নারী-পুরুষের প্রেম। মাধব মালঞ্চী কইন্যায় যেখানে দেখা গেছে রাজপুত্র আর রাজকন্যার প্রৈম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বের নাটকে ছিলো সেখানে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত নারী পুরুষের প্রেম। যদিও থিয়েটারের ঘোষণায় বা শামসুল হকের লেখনীতে বলা হয়েছে, শেকড়ের সন্ধান মানে পেছনে ফেরা নয়; অথচ আমরা এ গবেষণায় দেখতে পাচ্ছি আসলে সেটা পেছনে ফেরাই। প্রতিবাদ বা সংগ্রামের পথ থেকে সরে দাঁড়ানো।
বিষয়টাকে এ অধ্যায়ে আমরা আরো স্বচ্ছ করে তুলবো এবং দেখাতে চেষ্টা করবো কী ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এ চিন্তা। থিয়েটারের উৎসের সন্ধানে থিয়েটার উৎসব-এর স্মরণিকায় সৈয়দ শামসুল হক লিখছেন, থিয়েটার যেহেতু নাট্যদল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর বর্তায় নাটকের ক্ষেত্রে উৎস সন্ধানের দায়, কিন্তু এ এমন নয় যে নাটকের উৎস অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের উৎস থেকে আলাদা কিছু। তিনি লিখছেন, ‘নাট্যদল হিসাবে ‘থিয়েটার’ জানে, যখনই আমরা শিল্পে প্রাণিত, আমরা বস্তুতপক্ষে মানুষ দ্বারাই প্রাণিত; মানুষই আমাদের উৎস, জীবনই আমাদের উৎস, স্বপ্নই আমাদের উৎস-এই স্বপ্ন এমন একটি সমাজব্যবস্থার যেখানে সবার আছে সম অধিকার সম্পদের সমস্ত কিছুর ওপরে, এ জীবন এমন একটি জীবন যেখানে আমরা অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত, এবং এ মানুষ এমন মানুষ-যার আছে সেই সংগ্রামে জয়ী হবার প্রত্যয়।’
নাটক মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে শামসুল হক সম অধিকারের কথা বলছেন, মানুষের সংগ্রামের কথা বলছেন। সম অধিকার মানেই সাম্যের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি, সম অধিকার বা মানুষের সেই ধরনের কোনো সংগ্রামের সাথে ময়মনসিংহ গীতিকার সম্পর্ক নেই। ফলে তাঁর বক্তব্য হয়ে যাচ্ছে স্ববিরোধী। যাঁরা নাটককে মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করতে চাচ্ছেন, শেকড়ের সন্ধানে সেখানে মাধব মালঞ্চী কইন্যার কাছে কিংবা ময়মনসিংহ গীতিকার কাছে ফিরবার যুক্তিটা কোথায় সে ব্যাপারে তাঁরা কিছুই বলছেন না। ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলার ঐতিহ্য কোনো সন্দেহ নেই তাতে।
চরকা শিল্পও বাংলার ঐতিহ্য, পোষাক হিসাবে নেংটিও বাংলার ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য কি আজ আর কেউ ধরে রাখতে চাইছে, কিংবা কারাখানার বিরুদ্ধে কি কেউ চরকাকে দাঁড় করাতে চাইছে? মানুষের অতীত নিয়ে গর্ব করা সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখছেন, ‘যারা দেহে-মনে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, শক্তিতে-নৈপুণ্যে, সাহসে-প্রত্যয়ে যত অসম্পূর্ণ, সে বা তারা সেই পরিমাণেই অতীতমুখী, ঐতিহ্যগর্বী ও পিতৃসম্পদ- নির্ভর। অর্থাৎ অক্ষমের অতীতপ্রীতি, ঐতিহ্যগর্ব ও আর্তনাদ-লুকানো আস্ফালন অধিক।… নির্জিত মানুষের বাঁচার এও এক অবলম্বন। মাধব মালঞ্চী মঞ্চায়নের পূর্বে বাংলাদেশে ময়মনসিংহ গীতিকা বা লোকজ উপাদান নিয়ে কোনো নাটক মঞ্চায়ন হতে দেখা যায় না।
সে সময় লোকজ গল্প যেমন নাট্য মঞ্চায়নে গুরুত্ব পায়নি তেমনি লোকজ আঙ্গিকও নয়। মাধব মালঞ্চী কইন্যা মঞ্চায়নের পরপরই ঢাকা ও ঢাকার বাইরে এক নাগাড়ে বেশকিছু নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয় ময়মনসিংহ গীতিকা ও লোকজ উপাদানকে কেন্দ্র করে। ঢাকায় মাধব মালঞ্চী কইন্যার মঞ্চায়ন হয় উনিশশো উননব্বই সালের প্রথম দিকে, আর ঐ বছরের তেশরা আগস্ট ময়মনসিংহ গীতিকার ওপর ভিত্তি করে থিয়েটার চৌধুরী কামরুজ্জামান রুনুর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে বিষ লক্ষ্যার ছুরি। নব্বই সালের মার্চ মাসে কুমিল্লার যাত্রিক মঞ্চায়ন করে পূর্ববঙ্গ গীতিকা অবলম্বনে চন্দ্রাবতী। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন চৌধুরী কামরুজ্জামান রুনু। পরে পদাতিক নাট্য সংসদও ঢাকায় চৌধুরী কামরুজ্জামানের নির্দেশনায় মঞ্চায়ন করে চন্দ্রাবতী। মহাকাল প্রযোজনা করে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে সুনাইকন্যার পালা। খুলনা থিয়েটার ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে মঞ্চস্থ করে মহুয়া।
ঢাকা পদাতিক মঞ্চায়ন করে চট্টগ্রামের লোকগাথা অবলম্বনে আমিনা সুন্দরী। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন এস এম সোলায়মান এবং তিনিই এটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর ঢাকা পদাতিক থেকে সোলায়মান বের হয়ে এসে নতুন দল গঠন করেন, সেখানেও এই একই নাটক মঞ্চায়ন করা হয় ভিন্ন নাম দিয়ে। নতুন নামকরণ হয় সখিনা সুন্দরী। নব্বই দশকে দেখা গেল, একই নাটক আমিনী সুন্দরী নাম দিয়ে মঞ্চায়ন করছে ঢাকা পদাতিক এবং সখিনা সুন্দরী নাম দিয়ে মঞ্চায়ন করছে সোলায়মানের গঠিত নতুন দল।
ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বহু দলই এই সময় ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প অবলম্বনে নাচে-গানে সমৃদ্ধ নাটক মঞ্চায়ন করতে আরম্ভ করে। লোকনাট্য দল ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে মঞ্চায়ন করে সোনাই-মাধব। থিয়েটার আরামবাগ মঞ্চায়ন করে চৌধুরী কামরুজ্জামান রুনুর নির্দেশনায় রূপভান। ঢাকার বাংলাদেশ থিয়েটার মঞ্চায়ন করে গোলাম সারোয়ারের নির্দেশনায় বিদ্যাসুন্দর।
শেকড় সন্ধান এবং জাতীয় নাট্য নির্মাণ-এসব প্রশ্নকে সামনে এনে চলতে থাকে এধরনের মঞ্চায়ন, যার শুরু আশির দশকের একেবারে শেষে এসে এবং যা চলতে থাকে পুরো নব্বইয়ের দশক জুড়ে। নব্বইয়ের দশকে নাজমুল আহসান বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গাজীকালু চম্পাবতী, শোভনার বাঁধ, সুখী রমণী গুনাই বিবি, মহুয়ার পালা ও সৎমা। খুলনা থিয়েটার নাজমুল আহসানের নির্দেশনায় সে নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে। এর বাইরেও মঞ্চস্থ হতে দেখি রুমা মোদক রচিত কমলাবতীর পালা, ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত ভূত এবং আরো বহু নাটক।
বিদ্যাসুন্দর নাটকটি রাজকন্যা বিদ্যাবতী ও যুবরাজ সুন্দরের প্রেমের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত। বর্ধমান নগরীর রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যাবতীর বিবাহ সংকট নিয়ে নাটকের শুরু। বিদ্যাবতীর পণ অনুযায়ী কোনো যুবরাজ পাওয়া গেল না, যে তার উপযুক্ত। মহারাজের জন্য এটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সে তার মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ চাইলে কাঞ্চিপুরের মহারাজা গুণসিংহের পুত্র সুন্দর-এর কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী। সেই যুবরাজ জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী সুপুরুষ। রাজকবিকে নির্দেশ দেয়া হলো যুবরাজ সুন্দরকে নিয়ে আসার জন্য। যুবরাজ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে না এসে ছদ্মবেশে বর্ধমান নগরীতে আসে। সেখানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যুবরাজ বহু সমস্যার মাঝে পড়ে।
এই অবস্থায় যুবরাজ হীরা মালিনীর সাথে পরিচিত হয়ে আশ্রয় নেয় তার কুটিরে। সেখানে থেকে তার উদ্দেশ্যের পথে সে এগিয়ে যেতে থাকে। রাজকুমারীর কাছে পৌঁছে যায় প্রেমের বার্তা নিয়ে রাজকুমারের গাঁথা মালা মালিনীর হাত ধরে। রাজকুমারী মালিনীর সাহায্যে পেয়ে যায় রাজকুমার সুন্দরের সাক্ষাৎ। সিঁধ কেটে রাজমহলে প্রবেশ করে সুন্দর।
সেখানে বিদ্যাবতীর সাথে রাতের অন্ধকারে মিটিমিটি চাঁদের আলোয় দুজন দুজনের মাঝে হারিয়ে যেতে থাকে। সখীদের উপস্থিতিতে মালাবদল করে দুজনে গন্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হয়। রাজমহলে চোরাই পথে কারো প্রবেশ ঘটেছে বিষয়টি জেনে মহারাজ কড়া নির্দেশ জারি করে কোতোয়ালকে চোরকে ধরার জন্য। চোর ধরা পড়ে গেল। হীরা মালিনীকে বন্দী করা হয় সুন্দরকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে। সুন্দর এবং হীরা মালিনীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বিদ্যাবতী সংবাদ পেয়ে দিনরাত কাঁদতে থাকে, জ্ঞান হারায় বারবার। প্রেমের এই দুঃসহ পরিণতিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে বিদ্যাবতী। সকল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে রাজকবি।
সে মহারাজ বীর সিংহকে জানিয়ে দেয় যে বন্দী যুবকই মহারাজ গুণসিংহের পুত্র সুন্দর। মহারাজ সংবাদ পেয়ে মন্ত্রীকে দিয়ে রাজকুমারকে কারাগার থেকে ফেরত এনে বিদ্যাবতীর সংগে বিয়ের ব্যবস্থা করে। প্রেমের বিজয় হয়। নাটকের শেষে রাজপ্রাসাদের সকলেই প্রেমের আনন্দে নৃত্যগীত করতে থাকে। মূলত, নাটকের শেষ পরিণতিতে যা প্রমাণিত হয় তাহলে প্রেম শাশ্বত, প্রেম চিরন্তন, অমর, বিজয়ী। যুগে যুগে প্রেমেরই জয় হয়েছে।
মালঞ্চমালা একটি লোক কাহিনী। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম অধ্যায় ‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’র পাঁচটি নারীপ্রধান কাহিনীর অন্যতম কাহিনী মালঞ্চমালা। চন্দ্রপুরের নিঃসন্তান চন্দ্ররাজা সন্তান প্রাপ্তির অভীষ্টে দেবতার নির্দেশে স্বর্ণযুগল আমের সন্ধানে গেলেন। দেবতার শর্ত থাকে ডানেরটি খাবেন রাজা আর বামেরটি খাবেন রানী। আনন্দের আতিশয্যে শর্তপালনের ব্যর্থতায় বারোদিনের আয়ু নিয়ে জন্মালো রাজপুত্র।
ঘটনা প্রবাহে বারোদিন আয়ুর রাজপুত্রের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বারো বছরেব মালঞ্চ। নাটকটি সম্পর্কে দলের প্রচারপত্রে বলা হয় যেহেতু কাহিনীটি সমাজসৃষ্ট অর্থাৎ সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ এর স্রষ্টা যাঁরা জগৎ ও জীবনের সহজ অনুভূতি হতে সৃষ্টি করেছে এ কাহিনী সেহেতু এতে রয়েছে নানা রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা ইত্যাদির সমাবেশ। তবে কাহিনীটি শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনা নির্ভর নয় বরং এতে উঠে এসেছে সামাজিক নানা অসঙ্গতি, নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় মালঞ্চকে হতে হয় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ। এ মালঞ্চ অসংখ্য অবহেলিত নারীর প্রতীক, এ. মালঞ্চ বাংলার একজন।
প্রচারপত্রে যাই বলা হোক, নাটকটি শেষ হয় নানা অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে ও প্রেমের উপাখ্যান হিসাবেই। দেওয়ানা মদিনা ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত। নাটকটিতে যেমন প্রাচীন সময়কে ধরা হয়েছে, তেমনি মাঝেমধ্যে আছে তার আধুনিক রূপায়ণ। উৎসের সন্ধানে এ নাটকে প্রাচীন কবিগানের মতো পালার পূর্বে সাধু, পীর-পয়গম্বর, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও স্মরণীয় স্থান সমূহের বন্দনা করা হয়েছে।
নাটকটি সম্পর্কে দলের বক্তব্যে বলা হয়, প্রাচীন লোককাহিনী কৃষ্ণলীলার রাধার বিরহকে মদিনার বিরহের সাথে একাকার করা হয়েছে। মা ফাতেমা ও সীতার বিলাপ, ফরিয়াদী কন্ঠের উচ্চারণ যেন মদিনারই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন স্বরূপ। উৎসের সন্ধানে এ নাটকে, এ দেশের ঐতিহ্য কিস্সা কাহিনী, নৌকা বাইচের গান, জারী, বাইস্কোপ, গ্রাম্য কবিতা, যাত্রা-পালা ও পুঁথি যোগ করে বাংলাদেশের নিজস্ব লোকজ আঙ্গিককে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১২৯ সুনাই কইন্যার পালা নাটকটিও ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ান ভাবনা অবলম্বনে রচিত।
সুনাইকে ঘিরেই এই পালাটির বিন্যাস। যৌবনের রঙিন সকালে পিতৃহীনা নিরাশ্রয় সুনাই মায়ের হাত ধরে এসে নিঃসন্তান মামা মামীর সংসারে আশ্রয় লাভ করে। মামা সুনাইয়ের বিয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করে। যোগ্য পাত্রের অভাবে বিয়ে হয় না। এমতাবস্থায় রূপসী সুনাইয়ের সঙ্গে জলের ঘাটে সাক্ষাৎ ঘটে দীঘলহাটের তালুকদার পরিবারের একমাত্র পুত্র মাধবের। মাধব শিকার করতে এসে মন নিয়ে যায় সুনাইয়ের। সুনাই-মাধবের প্রেমের দূতরূপে কাহিনীতে আবির্ভাব ঘটে বাঘরা নামক এক দুষ্ট চরিত্রের।
বাঘরা সুনাইয়ের চোখ ঝলসানো রূপের খবর সামন্ত দেওয়ান ভাবনার নিকট টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। সামন্তগোষ্ঠীর এক প্রতিভু দেওয়ান ভাবনা, যার ঘৃণ্য শোষণের পরাকাষ্ঠে বন্দী সমাজের সাধারণ মানুষ-বন্দী মাধবের প্রেম। সুনাইয়ের প্রেমের পদাবলী তাই সুনাই কন্যার পালা, মাধব-সুনাইয়ের প্রেমই সেখানে প্রধান।
ঢাকার লোকনাট্য দল প্রযোজিত সোনাই মাধব নাটকটিও ময়মনসিংহ গীতিকার উপরের গল্প দেওয়ান ভাবনা অবলম্বনেই রচিত। নাটক মঞ্চায়নে তারা আরো বিপ্লব ঘটাতে চাইলেন। সেজন্য এই দলের সোনাই মাধব প্রয়োজনায় সেই আগের যুগের মতোই নারী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতা অভিনয় করে। নাট্যদলটি তাদের প্রচারপত্রে দাবি করে নাটকটি পদাবলী কীর্তন ও যাত্রার সমন্বয়ে তৈরি। মইধর বাদশা নাটকের গল্প রূপকথা ভিত্তিক।
বাদশাহ ও বাদশাহপত্নী সন্তানের কামনায় দীর্ঘদিন আরাধনার পর এক পুত্র সন্তান লাভ করে। পুত্রের নাম মইধর বাদশা। জন্মলগ্নেই মইধর বাদশাহর বিধিপ্রদত্ত বারো বছরের দুঃখ ভোগ থাকায় বাদশাহ ও তার পত্নী শত চেষ্টা করেও তার প্রতিরোধ করতে পারে না। একদিন ঘটনাক্রমে মইধর একটি যাদুর ময়ূরে চড়ে শ্যামবরণ কন্যার দেশে যায় এবং সেখানে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্যামবরণ কন্যাকে বিয়ে করে। প্রেমের সার্থকতার মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়।
নব্বইয়ের দশকের নাট্যচর্চায় তাই রাজনীতি, শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে নর-নারীর প্রেমই হয়ে উঠলো নাটকের বিষয়বস্তুর প্রধান আর একটি দিক। নর-নারীর এই প্রেম হলো একধরনের ভাববাদী চিন্তা। মহৎ কোনো নাট্যকারই নর-নারীর ক্ষুদ্র প্রেমের গণ্ডির মধ্যে তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তুকে আটকে রাখেননি। প্রাচীন গ্রীসের সফোক্লিস, ইস্কাইলাস, ইউরিপিডিস, আরিস্তোফানিস কারো নাটকের বিষয়বস্তুই নারী-পুরুষের প্রেম নয়। শিলার, ইবসেন, বার্নার্ড শ, গলসওয়ার্দি, ব্রেস্ট এদের কারো নাটকেই নারী-পুরুষের প্রেম বিষয়বস্তু হিসাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং নারী-পুরুষের প্রেম বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সবসময়ই এদের নাটকে সমালোচিত হয়েছে।
ব্যতিক্রম হিসাবে শেক্সপিয়ারের রোমিও এন্ড জুলিয়েট ও মিড সামার নাইটস ড্রিম দুটি নাটকে নারী- পুরুষের প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি, শেক্সপিয়ারের সময়কালে বিভিন্ন ধরনের দর্শকের রুচিকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তাঁকে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়েছে। প্রেমকে ঘিরে শেক্সপিয়ারের আরো নাটক আছে কিন্তু সেখানে নর-নারীর প্রেম নয়, রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলোই গুরুত্ব পেয়েছে।
কোনো প্রগতিশীল নাটকের বিষয়বস্তু নর-নারীর ক্ষুদ্র প্রেমের গল্পে আটকে থাকতে পারে না। ব্রেস্টও সে কথাই বলেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্রেস্ট নর-নারীর- চিরন্তন প্রেমে বিশ্বাস করেন না; সেজন্য তার নাটকে নারী-পুরুষের প্রেমের কোনো প্রসঙ্গই খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্কসবাদীরা মনে করেন, নারী-পুরুষের প্রেমের আবেগ দিয়ে বহুকাল মানুষকে বিপথগামী করা হয়েছে, চেতনার জগতকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নারী-পুরুষের প্রেম নিয়ে যেসব মিথ্যাচার ও আবেগধর্মী রচনা আছে, রাজনৈতিক নাট্য প্রচেষ্টার কাজ হচ্ছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়া। সেটাকে আরো মহিমান্বিত করা নয়। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে দেখা যায় শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা যারা দিয়েছিলো, সেসব নাট্যদলই নর-নারীর প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচারে জন্য ময়মনসিংহ গীতিকার নাট্যরূপ মঞ্চায়নে দ্বিধা বোধ করেনি।
পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আশির দশক পর্যন্ত বেশির ভাগ দল নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন সমাজ পরিবর্তন কিংবা সৎ নাটক করা, গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শকে সমুন্নত রাখা ইত্যাদি। নব্বইয়ের দশক থেকে অনেক দলই তাদের লক্ষ্যের মধ্যে নতুন একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তাহলো শেকড়ের সন্ধান। যেমন জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার তাদের ঘোষণার মধ্যে লিখছে, ‘নিজস্ব ঐতিহ্য লালন করে আমরা পৌছাতে চাই আমাদের প্রতিটি ঠিকানায়। আমরা উৎসের সন্ধানে আত্মখননে নিমগ্ন দূরগামী শ্রমিক বিপ্রতীপে বৈশ্বিক।
সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্যের মধ্যে লিখছে, ‘মাটি ও মানুষের ঐতিহ্যে লালিত আবহমানকালের কৃষ্টি সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধানে আমরা নিবেদিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের করোটিতে সংরক্ষিত। মূলতঃ এই অঙ্গীকারেই আমরা পথ চলছি এবং চলব। রাজশাহী থিয়েটার লিখছে, ‘দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সবার মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে…আমরা দেশজ আঙ্গিকের স্পর্শে রচিত নিগুঢ় শিল্পবোধ সম্পন্ন নাটক ও নাট্য চর্চায় বিশ্বাসী’। থিয়েটার সেন্টার লিখছে ‘বাঙ্গালী জাতির নিজের মাটি উদ্ভূত জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে থিয়েটার সেন্টার চায় আপন অধিকার। পদাতিক নাট্য সংসদ-এর বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে ‘বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য শেকড় থেকে উঠে আসা বাঙালি লোকজ সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ে পদাতিক এগিয়ে চলে তার চিন্তায় ও কর্মে’।
কুমিল্লার জনান্তিক নাট্য সম্প্রদায় লিখছে, ‘আমরা আমাদের ঐতিহ্যের মুখোমুখী হতে চাই’।গাইবান্ধার পদক্ষেপ নাট্যগোষ্ঠীর ঘোষণা, ‘আমরা দেশজ সংস্কৃতির আন্তরিক লালনের পাশাপাশি মানুষের কর্ম স্পৃহাকে তুলতে চাই বিপন্ন মানুষের দ্বারে দ্বারে’। বহু দলের নাট্য মঞ্চায়নের লক্ষ্য সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য ঘোষিত হয়েছে। পাশাপাশি আবার তাদের চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতাও দেখা গেছে।
লোকজ নাট্যরীতি নির্মাণের কথা বলে তারা মূলত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যেই আটকা পড়ে থেকেছে। লোককাহিনীগুলোকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে উপস্থাপন করেই তারা মনে করেছে লোকজ ধারার কাছে ফিরে যাওয়া হলো। সেটাও দলগুলো করেছে কোনো স্থির লক্ষ্য হিসাবে নয়। দলগুলো যতোই শেকড়ের সন্ধানের ঘোষণা দিক মূলত তারা প্রসেনিয়াম বা ইউরোপীয় ঢংয়ের নাটকই মঞ্চায়ন করেছে। কেউ কেউ মাঝখান দিয়ে দুটো একটা ময়মনসিংহ গীতিকা বা অন্য কোনো লোকগল্প অবলম্বনে নাটক মঞ্চায়ন করেই তাদের শেকড় সন্ধানের কাজ শেষ করেছে। দলগুলো দশটি প্রযোজনা করলে তার মধ্যে একটি কিংবা দুটি হয়েছে লোকগল্প ঘিরে। যেমন থিয়েটার, যারা উৎসের সন্ধানের কথা বলেছিলো তার মূলত কী করেছে?
থিয়েটার বাহাত্তর থেকে উননব্বই সাল পর্যন্ত একুশটি নাটক প্রযোজনা করে যার কোনটিই লোকজ ধারার নয়। সবগুলোই প্রসেনিয়াম ধারার নাটক এবং পাশ্চাত্য থিয়েটারের প্রচলিত আঙ্গিকই অনুসরণ করা হয়েছে তাতে। তারপরই শেকড়ের সন্ধানের কথা বলে হৈ চৈ ফেলে তারা মঞ্চায়ন করে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে বিষ লক্ষ্যার ছুরি। এই একটি নাটক মঞ্চায়ন করার পরই তারা আবার সেই পুরোনো ধারার নাটকই করতে থাকলো। বিষ লক্ষ্যার ছুরির পর তারা আরো দশটি নাটক প্রযোজনা করে উনেশশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত যার কোনটিই লোকনাট্য নয়।
বিষয়বস্তুর বেলায় তো নয়ই, এমনকি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নয়। সেক্ষেত্রে তাদের উৎসের সন্ধান এই ঘোষণার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হতে পারে তারা মাধব- মালঞ্চী দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সেই পথকেই পরম জ্ঞান করে ছিলো, বাস্তবতাব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হয়তো সেই পথ ধরে আর আগাতে পারলো না। সেজন্য আবদুল্লাহ আল- মামুন নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে স্বীকার করেন, ‘নিজস্ব ঐতিহ্য নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ভুল পথে এগিয়েছি। ফিরে এসেছি। আবারও বিভ্রান্ত হয়ে আরেকটা ভুল পথে পা রেখেছি।’বাকি সকলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়িয়েছে। যে যতো জোরেই শেকড়ের কাছে ফিরবার জন্য ঘোষণা দিক না কেন, সকলকে সমসাময়িক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কাছে বাঁধা পড়ে থাকতে হয়েছে।
ঢাকা থিয়েটার সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এ কারণে যে, ঢাকা থিয়েটার লোকনাট্য নিয়ে হৈ চৈ না করে জাতীয় নাট্যরীতি নির্মাণের কথা বলে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরে। সে চেষ্টা কতোটা সফল হয়েছে বা বিফলে গেছে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। ঢাকা থিয়েটারের জাতীয় নাট্যরীতি নির্মাণের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে, তবে আশির দশকের শুরু থেকেই ঢাকা থিয়েটার জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের কথা বলে আসছিলো।
ঢাকা থিয়েটারের ক্ষেত্রেই এটা ছিলো একমাত্র সুদীর্ঘ পরিকল্পনা। নাট্যকার সেলিম আল দীনকে ঘিরে নাট্য রচনা ও মঞ্চায়নে তারা ঢাকার মঞ্চে একটি ভিন্ন ধারা গড়ে তুলেছিলো। বাকিরা হঠাৎ যে শেকড়ের সন্ধান কিংবা ঐতিহ্যর সন্ধানে দেশীয় নাট্যরীতি নির্মাণের কথা বলেছিলো তা ছিলো এক ধরনের হঠকারিতা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করেই সেইসব দলের নাট্যকর্মীরা শুধুমাত্র আবেগের বশে এই পথে নেমেছিলেন। ময়মনসিংহ গীতিকা ছিলো এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান অবলম্বন।
অথচ আমরা জানি ময়মনসিংহ গীতিকায় অসংখ্য নাটক নেই আর নাট্যদল আছে শতাধিক। ময়মনসিংহ গীতিকার সবগুলো নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা কী করবে সে প্রশ্নটিও তাহলে সঙ্গতভাবেই এসে যায়। যে বিষয়টি কখনই তাদের চিন্তা বা প্রযোজনায় স্থান পায়নি, তাহলো তারা কি লোকজ বিষয়বস্তু নাকি লোকজ আঙ্গিক গ্রহণ করতে চাইছে। লোকজ আঙ্গিকের কথা বলে তারা যা কিছুই করেছে তা করেছে পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম কাঠামোর মধ্যে থেকেই।

ভারত তথা পশ্চিমবাংলায় লোকনাট্য নিয়ে, হঠাৎ হৈ চৈ দেখে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, ইদানিং বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা সর্বত্র শিক্ষাগবী একদল যুবক লোকনাট্য-লোকনাট্য করে ছাতারের নৃত্য শুরু করেছেন। সবাই খাঁটি ভারতীয় থিয়েটার সৃষ্টির সৃষ্টিছাড়া নেশায় কৌতুকের গান গাইছেন, কোমর দোলাচ্ছেন, দুনিয়া বহির্ভূত পোষাক পরে হঠাৎ নাটকের মাঝে ঢুকে পড়ে সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে অশ্লীল, সবচেয়ে কুৎসিত কিছু লোকগীতি গেয়ে রসিকতা করছেন। তাঁদের এই পরীক্ষা- নিরীক্ষাগুলো বস্তাপচা, পুরানো ও কীটদুষ্ট।
বাংলাদেশের লোকনাট্য চর্চার ক্ষেত্রেও উৎপল দত্তের এই বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা এখানে লোকনাট্য চর্চার কথা বলেছেন, প্রথমত তাঁরা খেয়াল করে দেখেননি লোকনাট্য নতুনভাবে তৈরি করা যায় না। একটি জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের জীবন-যাপন ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে লোকশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। লোকশিল্প বহু ব্যক্তি পরম্পরায় গড়ে ওঠে এবং তা একটি অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর শিল্প হিসাবেই প্রতিভাত হয়।
যেমন ময়মনসিংহ গীতিকা বলতে ময়মনসিংহ এলাকার গীতিকাকেই বোঝায়। সারা বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যকে বোঝায় না। সেজন্য লোকনাট্যের সাথে জাতীয় ঐতিহ্য বা জাতীয় নাট্যরীতির সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। জাতির ধারণা আর লোক ধারণা পরস্পর বিপরীত। বরিশাল, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট সকলের নিজস্ব আঞ্চলিক শিল্প-সাহিত্য, আচার অনুষ্ঠান রয়েছে।
জাতির ধারণা সেগুলোকে ভেঙেচুরে নতুন ভঙ্গির এক শিল্প-সাহিত্য, আচার- অনুষ্ঠান সৃষ্টি করে যা বিশেষ অঞ্চলের না হয়ে সকলের হয়। কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, যশোরের আলাদা আলাদা আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা সকল আঞ্চলিক ভাষার ওপর প্রভুত্ব সৃষ্টি করে জাতীয় রূপ লাভ করেছে। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার সাথে তাই লোকশিল্পের যেমন বিরাট বিরোধ রয়ে গেছে, তেমনি ব্যাপক বিরোধ রয়েছে আধুনিক চিন্তার সাথে।
বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা সেখানে লোককৃষ্টিকে ঘিরেই জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন।বহুজনই বলেছেন বাংলার পাঁচালি, গম্ভীরা, হরিকথা, মনসার গান, নাট্যগীত ঝুমুর ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমেই নাটক ফিরে পেতে পারে তার স্বকীয়তা। এসবের ব্যবহার নাটকে কীভাবে হবে সে সম্পর্কে কেউ কিছুই বলেননি। হারিয়ে যাওয়া এইসব প্রাচীন রীতি সত্যিকার অর্থে নাটকের অগ্রগতিতে কোনো সাহায্য করতে পারে কি না সে নিয়েও কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেননি।
এইখানে লোকশিল্পের কিছু লক্ষণ বুঝে নিতে হবে। লোকশিল্প শুধু বিনোদন নয়, জীবনযাত্রার অংশ। বাংলার লোকশিল্পে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত রয়েছে ধর্ম ও দেব-দেবী। যেমন মনসার গান। সেটা ধর্মের অঙ্গ; ফলে সেখানে পুরাণ বিবৃত হয়, গীত গাওয়া হয়, মাদল বাজে, লম্ফঝম্ফ হয়, বক্তব্য প্রচারে নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। যা প্রকাশ পায় না তাহলো আধুনিক চিন্তা। লোকশিল্পের নেপথ্যে থাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকাচার ও ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা।
লোকজীবনে বিশেষ ধর্মের প্রভাব আছে বলেই, লোকশিল্পে বিশেষ ধর্মের প্রভাব থেকে যায় এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণেই তা সার্বজনীন নয়। বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে সেখানে দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়, যৌথভাবে নিজেদের সমর্পণ করা হয় বিশেষ দেবতার পদতলে। থিয়েটারে বা নাট্যশালায় এই ইচ্ছাপূরণের কামনা একেবারেই থাকে না। স্বভাবতই প্রতিটি দর্শক থিয়েটারে আলাদাভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। নিজের চিন্তাশক্তিকে দর্শক দেবতার পায়ে সমর্পণ করে না। নাটক আর হরিকথা এক ব্যাপার নয়। হরিকথা ধর্মের অঙ্গ, তাই বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছেই তার মূল্য। ভিন্নধর্মের কারো কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক কিংবা যে-কোনো নাটকই কোনো বিশেষ ধর্মের সম্পদ নয়; সকল ধর্মের মানুষের কাছেই তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
নাটক সার্বজনীন, ধর্ম সার্বজনীন নয়। যখন কেউ নাটক দেখে সেটা কি কোনো বিশেষ ধর্মের হয় বা বিশেষ ধর্মের অঙ্গ হিসাবে কেউ কি কখনও নাটক দেখতে যায়? মধ্যযুগের শেষে গীর্জায় যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হতো যিশুর গুণকীর্তন করে তা শেষ পর্যন্ত নাটক হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ তা ছিলো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের, বিশেষ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সার্বজনীন কোনো চরিত্র তার ছিলো না, কিন্তু প্রকৃত থিয়েটারের চরিত্রটি সার্বজনীন।
দর্শক প্রাচীন গ্রীসের কোনো নাটক দেখতে গিয়ে ভাববে না যে, সে কোনো উপাসনালয় ঢুকেছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে নাটকের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস আর নাটক হচ্ছে একটি সচেতন প্রয়াস। নাট্যকার স্থান-কাল-ঘটনার প্রেক্ষিতে নতুন চিন্তা, নতুন মত প্রকাশ করতে পারেন। ধর্ম তা পারে না। কারণ সেটা মানুষের গভীর বিশ্বাসের জায়গা।
বিভিন্নভাবে দেখা গেছে, লোকধর্মগুলো অনেক ক্ষেত্রে নাটকের পূর্বসূরী তবে তা নাটক নয়। গ্রীক নাট্যকলার মূল উৎস নিহিত ছিলো লোক উৎসবে। নাটকের দ্রুণ দেখা গেছে মন্দিরে কিন্তু মন্দির ছেড়ে যখন সে সকলের হয়ে উঠলো, সার্বজনীন চরিত্র লাভ করলো তা হয়ে উঠলো নাটক। নাটকের উৎপত্তিতে ধর্মের বিরাট ভূমিকা আছে, তা সত্ত্বেও নাটক আর ধর্ম এক নয়। গম্ভীরা বা আলকাপ নাট্যক্রিয়া নয়, যদিও তার মধ্যে নাট্য লক্ষণ বর্তমান। শিল্পের সব শাখাকেই নাটক বলা যায় না। পাঁচালি- কথকতাও তেমনি নাটক নয়।
গ্রীক নাটক জন্মের পূর্বে মন্দিরের পুরোহিত বাক্কাসের গল্প শোনাতেন নানা অভিব্যক্তি সহকারে, তখনও তাকে নাটক বলা হয়নি। বলা হচ্ছে তা নাটকের উত্থানপর্ব। নাটক তখনই হলো, যখন কাহিনীর একটি আখ্যানভাগ রচিত হলো, সেখানে চরিত্র এলো, রাষ্ট্র সমাজ সম্পর্কিত কিছু বলা হলো।
পৃথিবীর বহু শিল্প মাধ্যমই হারিয়ে গেছে তার আর প্রয়োজন নেই বলে। ইতালির কমেডিয়া ডেল আর্তে ছিলো, আজ আর নেই। গ্রীসে বাক্কাসের কাহিনী বলার সেই পাঁচালিকার আজ ইতিহাস মাত্র। বাংলার লোকনাট যদি নতুন চিন্তার খোরাক না যোগায় তাহলে তা নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। ময়মনসিংহ গীতিকাকে একধরনের নাটক বলা যায়, কারণ নাটকীয় উপাদান তাতে আছে। চরিত্র আছে, সংলাপ আছে, নাট্যকারের নিজের কিছু বলার আছে।
সেগুলো কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসও নয়। কিন্তু সেগুলো এতোই কুসংস্কার আচ্ছন্ন যে, নাটকের প্রধান যে কাজ মানুষকে উদ্দীপ্ত করা, মানুষের চিন্তাকে এগিয়ে নেয়া, তা ময়মনসিংহ গীতিকা পারে না। পারে না বলেই তা বর্জনীয়। ময়মনসিংহ গীতিকার বিষবস্তুর প্রসঙ্গে যদি আসা হয় তাহলে সে বিষয়বস্তুটি কী হবে-শুধুই প্রেমের কাহিনী বলা?
না অন্য কিছু, সে সম্পর্কে নাট্যদলগুলো বা নাট্যবোদ্ধাদের কোনো বক্তব্য নেই। ময়মনসিংহ গীতিকা বা লোক উপাদানে যেসব ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানব, রাক্ষস ও গণক কিংবা যাদুকরী সামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে সেই সকল কুসংস্কারও কি তাহলে নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে? সেসব প্রশ্নে নাট্যবোদ্ধারা নীরব, যাঁরা ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই যে-সকল দল লোকনাট্য হিসাবে ময়মনসিংহ গীতিকার আশ্রয় নিয়েছে সেখানে নানা কুসংস্কার, নানারকম ধর্মীয় বন্দানাগীত স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। পীর-আউলিয়াদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। স্বভাবতই শেকড়ের সন্ধান-এই পর্বে নাটকে যেসব বক্তব্য দেয়া হয় তার সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটির আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাট্যদলগুলো দর্শকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে।
দীর্ঘদিন নাট্য আন্দোলনের যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিলো, শিল্পের জন্য শিল্প চর্চা নয়, সমাজ পরিবর্তনের জন্য নাটক; শেকড় সন্ধানের নাটক ঠিক তার বিপরীত পথ ধরেই চলতে থাকে। সেখানে নাটকের দলগুলোর টিকে থাকার ব্যাপারটাই প্রাধান্য পায়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটি হারিয়ে গিয়ে নানাভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের পথে নাটক পা বাড়ায়। শেকড়ের সন্ধান আসলে শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বের আওতাভুক্ত হয়ে পড়লো, কারণ তা শুধু নাটকের জন্যই নাটক, দর্শককে বিনোদন দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য।
সেজন্যই তার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম এবং যতো সব কুসংস্কার। যদিও সেক্ষেত্রে মান্নান হীরা রচিত একজন লক্ষীন্দর, তৌফিক হাসান ময়না রচিত কথা পুণ্ড্রবর্ধন কিছুটা ব্যতিক্রম। কথা পুণ্ড্রবর্ধন নাটকে শেকড় খোঁজার প্রবণতা থাকলেও লোকনাটক সে অর্থে তাকে বলা যাবে না। কোনো লোকগল্পের ভিত্তিতে নাটকটি লেখা হয়নি, বরং তার মধ্যে রয়েছে বাংলার একটি অঞ্চলের কিছু ঘটনাপঞ্জি।
যাঁরা লোকনাট্য নিয়ে হৈ চৈ করছেন, নাট্যকলা তাদের কাছে সার্বজনীন নয়, কিন্তু একটি শাশ্বত ব্যাপার। তাঁরা মনে করেন নিজ দেশ-কালের সীমানার মধ্যেই শিল্পকলার স্থান। লেনিন বলেছিলেন, শিল্পকলাকে ভোটে দেয়া যায় না এবং তার কোনো জাতীয় সীমানা থাকে না। তিনি বলছেন, কোনো শিল্পকলাকেই শাশ্বত বলা যায় না। পরিবর্তনশীল বিশ্বে কিছুই যে শাশ্বত নয়, এই সত্যটাই শেকড়ের সন্ধানের নাট্যকর্মীরা বুঝতে চাননি। বুঝতে চাননি, পাশ্চাত্যের থিয়েটার বা প্রাচীন গ্রীক নাটক, শেক্সপিয়ার, ইবসেন আজও মানুষকে নতুন চিন্তার খোরাক যোগায় বলেই তা টিকে আছে।
পাশ্চাত্যের থিয়েটারের একটি ইতিবৃত্ত আছে, লোকমাধ্যম থেকে আধুনিক থিয়েটারে পৌঁছুবার ইতিবৃত্ত। বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এমন কোনো ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে না। যার অর্থ বাংলা থিয়েটার প্রধানতই অধমর্ণ, তার সবটাই বিদেশ থেকে ধার করা এবং প্রথম থেকেই নাগরিক। প্রথম পর্বে তা ছিলো নগর সভ্যতার বিনোদন মাত্র। ফলে এ কথা সত্য যে, এই থিয়েটার কোনো মৌলিক চেতনার তাগিদে তৈরি হয়নি। নগর কলকাতার নাগর রুচির দাবি মেটাতে এই থিয়েটারের জন্ম ও বিস্তার।
কলকাতার বাবুরা যখন এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁরা নাট্যশিল্পের কথা ভাবেননি, জনরুচি চরিতার্থ করার বাইরে তাঁদের কিছু করার ইচ্ছা ছিলো না। স্বভাবতই লোকজ বা দেশজ শিল্পের সাথে এ নাটকের কোনো যোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা বা ইতিহাস কোথাও স্থির থাকে না। প্রতিনিয়ত তার মধ্যে নানা গুণের সমাহার ঘটে।
বাংলা নাট্য যে বাইরের ব্যাপার তা নিয়ে বিতর্ক নেই কিন্তু কালক্রমে এই মাধ্যমটিই বাঙালীর সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলো। ব্রিটিশদের দেয়া নাট্য মাধ্যমটিকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়েছিলো। নীলদর্পণ তার প্রথম উদাহরণ।
বাংলা নাটক যখন নীলদর্পণ থেকে নবান্ন হয়ে কল্লোল-এ প্রবেশ করেছে, নতুন বিপ্লবের হাওয়া বয়ে এনেছে, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে-সেই নাট্যধারা যা একদিন লিয়েবেদেফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে নাট্যধারা বা নাট্যরীতি ইংরেজকে ভীত করে তুলেছিলো, যে নাট্যরীতিকে ভয় পেয়ে ইংরেজ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু করেছিলো এবং যে নাট্যধারা দুশো বছর ধরে নানান উত্থান-পতন ঘটিয়েছে, সমাজ রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে-এক কলমের খোঁচায়, এক উৎসবেই তাকে বর্জন করার ঘোষণা দিলে, তাকে বর্জন করে পিছনে ফিরতে চাইলে-তার মধ্যে গভীর কোনো চিন্তা, প্রগতিশীল চিন্তার সন্ধান মেলে না। পেছনে ফেরা এটা শাসকশ্রেণীর ভাবধারা: প্রতিক্রিয়াশীলদের চিন্তা। ইতিহাস কখনো পিছনে ফিরতে পারে না।
শম্ভু মিত্র তাই লিখছেন, ‘অনেকে বলছেন যে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সকল প্রকার যান্ত্রিকতা উড়িয়ে দিয়ে সহজ সরল নাট্যপ্রয়োগের দিনে ফিরে যেতে হবে।’ ‘তাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ পিছনে ফিরে যাওয়াই তো সম্ভব নয়। তাহলে তো দেশে যতো বড়ো কারখানা হচ্ছে সব’ বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। তাহলে যাঁরা এ-কথা লিখছেন তাঁদের ফাউন্টেন পেনে না-লিখে খাগড়ার কলমে লেখা উচিত, এবং আধুনিক ছাপাখানার যান্ত্রিকতার সাহায্য একেবারেই নেওয়া উচিত না।
মাথার উপরে পাখা ঘোরানো উচিত না, এবং ঘরে রেডিও রাখা উচিত না। ১৪ শম্ভু মিত্র যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেভাবে করে কি আমরা ঐতিহ্যের নামে পশ্চাদপদ হয়ে থাকবো। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির বেলায় আমরা দেখতে পাবো তারা নিজস্ব ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেছে, কিন্তু পুরানো ঐতিহ্যের ধারায় তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্পকলা-সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই তারা আধুনিক চিন্তাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে।
থিয়েটারকে যদি দর্শকের সেবা করতে হয় তাহলে তাকে প্রতি যুগে এমন ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে যা হবে যুগ রা সময়োপযোগী। থিয়েটারকে বারবার নবজন্ম নিতে হয় নতুন নতুন কালের উপযোগী হয়ে উঠবার জন্য। সেই নবজন্ম ঘটে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে কিংবা রাজনৈতিক উত্থান পতনে যখন পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থা জন্ম নেয়, থিয়েটারকেও তখন ভঙ্গি পাল্টাতে হয়। মানুষের নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মিলিয়ে থিয়েটারকে চলতে হয়।
নতুন মানুষকে পুরানো ভঙ্গি তখন আর সম্যক আনন্দ দিতে সক্ষম হয় না। ১৬৬ সেজন্যই শুরুর ধ্রুপদী নাট্যধারার বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নানা ধারার আগমন; রোমান্টিক নাট্যধারার পর ন্যাচারালিজম ভঙ্গির আবির্ভাব, ন্যাচারালিজম-এর পর রিয়েলিস্টিক ভঙ্গি, রিয়েলিস্টিক ভঙ্গির পর এক্সপ্রেশনিজম, এবং তারপর মহাকাব্যিক বা দ্বান্দ্বিক ভঙ্গি-সে ভাবেই নাটক বা নাট্য প্রযোজনা এগিয়ে গেছে। মানুষের মন জয় করার জন্য বারবার তাকে ভঙ্গি পাল্টাতে হয়েছে।
সেই ভঙ্গি পাল্টাতে গিয়ে সে শুধু সামনেই এগিয়ে গেছে, পিছনে ফিরে তাকায়নি। যদিও পিছনের ইতিহাসটাকে সবসময়ই জানতে চেষ্টা করেছে। ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারের প্রবক্তা এমিল জোলা বলেছিলেন, থিয়েটারকে অতীতের সব বস্তাপচা জিনিস বাদ দিতে হবে, নাটককে উপকথা ও কাল্পনিক জগতের সাজানো কাহিনী ছেড়ে সতেজ জীবনে ফিরতে হবে। সেখানে থাকবে জীবন্ত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিকতা। বিগত দিনের অবক্ষয়ী চিন্তা নয়, বিগত দিনের অবক্ষয়ী চিন্তার পথ পরিষ্কার করে নতুন থিয়েটারের জন্ম দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানই একমাত্র থিয়েটারকে বাঁচাতে পারে। থিয়েটারে প্রধানত যা দরকার তা হলো মানুষের মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।
বিখ্যাত আমেরিকান শিল্প নির্দেশক লী সাইমন মনে করতেন, যদি কাঠকাটরা দিয়ে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় এলিজাবেথীয় থিয়েটারের প্রতিরূপ তৈরি করা হয়, সেখানে তাহলে নতুন চিন্তা জন্ম নেবে না, আরেকজন শেক্সপিয়ার কিংবা দ্বিতীয় মার্লো সেখানে আটকা পড়ে যাবে। ফলে ময়মনসিংহ গীতিকার মধ্যে কিংবা সেই লোকধারার মধ্যে আটকে থাকার জন্যই কি নতুন যুগের নাট্যকারদের সেই পুরনো যুগের নাটক লিখতেই বাধ্য করা হবে, নাকি নতুন যুগের নাট্যকারকে নতুন নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করা হবে সে প্রশ্নের জবাব আমরা শেকড় সন্ধানীদের কাছ থেকে পাই না।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে যখন নাটকের দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য বারবার পর্দা পড়ার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেল, নাট্যকারদের রচনার উপরেও তা প্রভাব ফেললো, নতুন ঢংয়ে তাদেরকে নাটকে লিখতে হলো। বিষয়বস্তুকে ভিন্নভাবে সাজাতে হলো। যদি সেই বাংলার প্রাচীন নাট্য বা পাঁচালির আঙ্গিকে ফিরতে হয়, বিশাল মঞ্চ জুড়ে বিশাল ব্যাপক ঘটনা বহুল নাটক লেখা সেখানে চলবে না এটাই তো স্বাভাবিক।
যুগে যুগে থিয়েটারের ইতিহাসে থিয়েটারের ভঙ্গি যেভাবে পাল্টেছে, পূর্বের চেয়ে উন্নততর হয়েছে তাকে সম্যক না বুঝলে থিয়েটারের যথার্থ ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম হবে না। নাটকের ইতিহাসে এ্যারিস্টটল নাটক সম্পর্কে যে কড়া আইন জারি করেছিলেন, যেসব তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেগুলো তার যুগের জন্য উত্তম চিন্তা হলেও পরবর্তীকালে তিন ঐক্যের ঐতিহ্যের চাপে ভবিষ্যৎ নাট্যচর্চার কন্ঠরুদ্ধ হতে চলেছিলো। শেক্সপিয়ার সেই নিয়ম ভেঙে নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় বিপ্লব ঘটালেন। নতুন থিয়েটারের জন্ম দিলেন তিনি বুর্জোয়া যুগের উন্মেষকালে। যারা পরবর্তীকালে নাট্যকার হয়েছেন, সকলকে সেই ঐতিহ্য ভেঙেই আসতে হয়েছিলো।
যুগের দাবিতেই ধ্রুপদী থিয়েটারকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হলো, সেখানে রোমান্টিসিজমের ধারা এলো এবং শহুরে সমাজ সমর্থিত শেক্সপিয়ারের জনপ্রিয় থিয়েটারকে বলা যায় ইতিহাসের প্রথম মধ্যবিত্তশ্রেণীর থিয়েটার। ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তরাও যে ঠিক সেই থিয়েটারই গ্রহণ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক ছিলো। যারা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পেয়েছে, শেক্সপিয়ার ছাড়া কে তাদের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারবে? সামন্তযুগীয় ময়মনসিংহ গীতিকার পক্ষে কি তা সম্ভব ছিলো? মধ্যবিত্তের পায়ের সামনে সামন্তযুগীয় বিশ্বাসগুলো তখন ভেঙে পড়তে শুরু করেছিলো। ব্রিটিশরা যখন যুগ যুগ ধরে ঘুণে ধরা মরিচা পড়া পুরানো ভারতীয় সমাজটাকেই ভেঙে ফেললো, নিজের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই তখন তাকে তাদের সভ্যতার বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বয়ে আনতে হলো। ভারতের জন্য সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথেই এসে গেল শেক্সপিয়ার, এসে গেল পাশ্চাত্যের নাট্যচিন্তা।
সেই সময় ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য নাট্যরীতিই যে জায়গা করে নেবে সেটাই ইতিহাসের লিখন, ব্রিটিশরা মহান এক সংস্কৃতির বীজ বপন করলো এর ভিতর দিয়ে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস লিখেছিলেন, ‘বৃটিশরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য’। অর্থাৎ ব্রিটিশদের পূর্বে যারাই ভারত দখল করেছে, ভারতের সংস্কৃতি ছিলো তাদের চেয়ে উন্নত, তাই তারা সকলেই ভারত দখল করার পর ভারতের সংস্কৃতিই গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ সভ্যতা শুধু ভারতের চেয়ে উন্নত ছিলো বলেই ভারতীয়রা ব্রিটিশ সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলো ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই। সেজন্য কোনরকম হীনমন্যতা থাকার কারণ নেই, বিভিন্ন রকম গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের সংস্কৃতি বেঁচে থাকে এবং উন্নততর স্তরে পৌছায়। পৃথিবীব্যাপী সংস্কৃতি- সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিবর্তিত হয়েছে ও এগিয়েছে দীপ থেকে দীপ জ্বালানোর পদ্ধতিতেই।
নিজস্ব নাট্যরীতি নির্মাণের নামে যাঁরা নব্বইয়ের দশকে ময়মনসিংহ গীতিকা ও অন্যান্য আঞ্চলিক লোকনাট্য মঞ্চায়নের জন্য পা বাড়ালেন খুব বেশি দূর তারা যেতে পারলেন না, মাঝপথেই থেমে পড়লেন। সত্যিকার অর্থে লোকনাট্যের ঘাড়ে পা রেখে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব ছিলো না। লোকনাট্য তো বেঁচে ছিলো না, বহু আগেই তা হারিয়ে গিয়েছিলো। বিদেশি শাসন এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে এখানকার সবধরনের ঐতিহ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো।
নিজস্ব নাট্য নির্মাণের জন্য সেখানে পেছনে ফেরার মানে হলো সেই উত্তরণের পথ থেকেই সরে দাঁড়ানো। যেখানে সমস্ত পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে-পুরানো অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, শিক্ষা কাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ, পোষাক পরিচ্ছদ-সেখানে পুরানো সংস্কৃতিও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। রম্যা রলাঁ বলেছিলেন যে, সদা পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে শিল্প একাই শুধু থাকবে স্থির হয়ে এ জিনিস কখনই হতে পারে না। কোনো বিধি নিয়মই শাশ্বত নয়।
সামাজিক পরিবর্তনগুলি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, সেগুলো বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনের মতো কতকগুলো নিয়ম অনুসারে ঘটে। শিল্প সংস্কৃতির বিবর্তনও সেই পথ ধরে আগায়। সেজন্য হঠাৎ পিছনে ফিরবার আগে বাস্তব অবস্থাটাকে ভেবে দেখা দরকার হয়। ময়মনসিংহ গীতিকা যদি এতোই মূল্যবান এবং চিরকালীন হতো তাহলে সেটা হারিয়ে যেতো না। সেটাকে আজ খুঁজেও বের করতে হতো না, নিজের শক্তিতেই সে বেঁচে থাকতো। ময়মনসিংহ গীতিকা সময়ের দাবিকে পূরণ করতে পারেনি বলেই তাকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে জোর করে এখন কেউ আর একে দাঁড় করাতে পারবে না।
পশ্চিমবঙ্গে মাধব-মালঞ্চী কইন্যা মঞ্চস্থ করার পরেও সেখানে শেকড় সন্ধানের পথ ধরে নাট্যদলগুলো চলছে না। যিনি মাধব মালঞ্চী কইন্যা প্রযোজনা করেছিলেন তিনিও পাশ্চাত্যরীতির নাট্যধারার কাছেই আবার ফিরে গেছেন। দু-একজন যারা তীজনবাঈকে অনুসরণ করে পাঁচালির পথ ধরে নতুন নাট্যরীতি তৈরির চেষ্টা করেছিলেন তারাও সেখান থেকে সরে পড়েছেন। সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গেও প্রসেনিয়াম ধারার নাটকই এখনো জায়গা দখল করে আছে।
হাবিব তানভির নিজেও নিয়মিত প্রসেনিয়ামের ভিতর নাটক করছেন। সৌখিনভাবে দু একটা পুরোনো রীতির নাটক করা যায় বটে, তাকে টিকিয়ে রাখা যায় না। মৃতকে আর জীবন দেয়া যায় না। পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এখনো দর্শকদের ক্ষুধা মিটাতে পারে বলেই তা এখনো উজ্জ্বল। সমস্যা নাট্যরীতির ততোটা নয়, যতোটা বিষয়বস্তুর। বিষয়বস্তুর হাত ধরে নতুন নাট্যরীতি আসবে, নতুন নাট্যরীতি জন্ম নেবে। এভাবেই নাটকের ইতিহাস আগায়।
গ্রীক নাটক বেঁচে থাকলেও গ্রীক সেই পুরানো নাট্যরীতি আজ আর বেঁচে নেই। থাকতেও পারে না। গ্রীক নাটকগুলো এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে, কারণ সেগুলো ধ্রুপদী। আর বেঁচে থাকার জন্য তাকেও রূপ পাল্টাতে হয়েছে। গ্রীক নাটকের, কোরাস আজ উধাও। গ্রীক নাটকে প্রথম একটি মাত্র চরিত্র ছিলো, মানুষের চিন্তার উত্তরণের সাথে সাথেই সেখানে দুটো, তারপর তিনটে এভাবে চরিত্রের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রীক নাটকে প্রথম যখন একজন অভিনেতা মাত্র অভিনয় করতেন, তিনিই ঘুরে ঘুরে সব চরিত্রের অভিনয় করতেন। যেমন বাংলার পাঁচালিকার। যিনি একাই গল্প বলেন এবং সবার চরিত্র নিজেই অভিনয় করে দেখান, গ্রীক নাটকের শুরুটা তেমনি ছিলো।
সে ধারা নাটকের গল্পকে গতি দিতে পারছিলো না বলেই সেখানে বহু অভিনেতার আবির্ভাব। সেটাই উত্তরণ। শেকড়ের সন্ধানীরা বহু অভিনেতাকে বাদ দিয়ে সেই পাঁচালির যুগে ফিরতে চান। সখ করে সেটা করা চললেও শেষ পর্যন্ত সেটাকে ধরে রাখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গেও শেকড় সন্ধানের নামে একবার দুবার সে চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই, ব্যস ঐটুকুই। পাশ্চাত্যরীতির নাটকই চলছে সেখানে বছরের পর বছর।
– যাঁরা এই যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে নিজস্ব নাট্যরীতি তৈরি হলেই তা নিজ দেশের মানুষকে বেশি আকর্ষণ করবে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যও সত্য প্রমাণিত হলো না। দেখা গেছে ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির নামে যে নাটকগুলো এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে, তার কোনোটিই তেমন হৈ চৈ ফেলাতে পারেনি। দর্শকও টানেনি। নাগরিকের নাটক বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। এই দল বেশিরভাগ বিদেশি নাটক মঞ্চস্থ করেছে এবং পাশ্চাত্যরীতিতে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব জনপ্রিয়তা পায়, সেগুলো মূলত পাশ্চাত্য ঢংয়ে লেখা। মামুনুর রশীদ বা মমতাজউদ্দীন আহমদের যে নাটকগুলো দর্শকরা বেশি দেখেছে, সেগুলোও পাশ্চাত্যরীতিতে লেখা।

বাংলাদেশে এ যাবৎকালে যে প্রযোজনাগুলো বিষয়বস্তু চরিত্র ও প্রযোজনার মান রক্ষা করে দর্শকদের কাছে সার্বজনীনভাবে আদরণীয় হয়েছে সেগুলো হচ্ছে গ্যালিলিও, শেষ সংলাপ, ম্যাকবেথ, কোপেনিকের ক্যাপ্টেন, সমাধান, তোমরাই, বিষাদ সিন্ধু, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, কিত্তনখোলা, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, দেওয়ান গাজীর কিসসা ইত্যাদি, যার কোনোটাই লোকনাট্য নয়। বিষাদ সিন্ধু ও কিত্তনখোলা পাশ্চাত্য নাট্যরীতি ভেঙে প্রযোজিত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু লোকধারা থেকে নেয়া হয়নি। বিষয়বস্তু ও প্রযোজনার মান রক্ষিত হয়নি তেমন নাটকগুলোকেও যদি জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে বিচার করি তাহলে সাতঘাটের কানাকড়ি, কঞ্জুস, বিচ্ছু যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে লোকনাটকগুলোর কোনোটাই সে জনপ্রিয়তা পায়নি। যা প্রমাণ করে শিকড়ের সন্ধানের পেছনে ছোটায় আসলে দর্শক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যদলগুলোর কোনো লাভ হয়নি। লোকজ ধারার নাটক না দর্শক সৃষ্টি করতে পেরেছে, না নাট্য প্রযোজনার মান রক্ষা করতে পেরেছে।
মূল যে প্রশ্ন, লোকজ ধারা জোর করে তৈরি করা যায় না। লোকজধারা হচ্ছে গ্রাম্য স্বাভাবিক জীবন যাত্রার স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পরূপ যা বছরের পর বছর ধরে লোকপরম্পরায় গড়ে ওঠে। সামন্ত সমাজকাঠামোর মধ্যেই সে ধারার বিকাশ লাভ এবং টিকে থাকা সম্ভব হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যবস্থা বাইরের চিন্তা ও সংস্কৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে তার লোকজ ধারার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারে। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যখন শহর ও গ্রাম মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় তখন আর সে শিল্পরূপকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পৃথিবীতে কোথাও সম্ভব হয়নি। যেসব দেশ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে তাদের সরকার সেই গোষ্ঠীগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন দ্বারা।
প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। যেমন জাপানের কাবুকি থিয়েটার। কাবুকি জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্য, লোকজ ধারা। সারা জাপানে আজ আর এই ঐতিহ্য বেঁচে নেই। সেখানেও সারাদেশ জুড়ে মঞ্চস্থ হয় পাশ্চাত্য ঢংয়ের থিয়েটার। জাপানে এখন যে কাবুকি মঞ্চস্থ হয়, সারা জাপানের নাট্য প্রচেষ্টার সেটা একটা গৌণ অংশ। সেই কাবুকিগুলো মঞ্চস্থ হয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়।
জাপানীরা দেখতে পাচ্ছিলো বুর্জোয়া ব্যবস্থার ধাক্কায় কাবুকি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই সরকারগুলো কাবুকিকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। সে আইন অনুযায়ী যাঁরা কাবুকি নাট্যরীতির সাথে বংশ পরম্পরায় জড়িত সরকার তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, বিনিময়ে তাঁরা এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখবে। কাবুকি ঐতিহ্যের সাথে জড়িত নয় এমন কেউ যদি কাবুকি নাটক করতে যায়, সে আইনত দণ্ডনীয় হবে। কারণ কাবুকি ঐতিহ্যের সাথে যারা জড়িত নয় তাদের জন্য জাপানী আইনে কাবুকি মঞ্চায়ন করা নিষিদ্ধ। কেন এটা করা হয়েছে? কারণ তারা জানে, হঠাৎ করে কেউ চাইলেই কাবুকি মঞ্চায়ন করতে পারবে না, তার জন্য দরকার সেই ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হওয়া। দরকার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ।
শহরের লোকদের কারো খেয়াল চাপলো আর কাবুকি মঞ্চায়ন করে বসলো ব্যাপারটা তা নয়। বিশ-ত্রিশ বছর প্রশিক্ষণ নেয়ার পর, কাবুকির জন্য একজন শিল্পী যোগ্য হয়ে ওঠেন। কাবুকি বেঁচে ছিলো বলেই সরকার তাকে প্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। সরকারের দৃষ্টি পড়ার আগেই যদি কাবুকি ধ্বংস হয়ে যেতো সরকার সেই মৃত ঐতিহ্যকে তাহলে আর ফিরিয়ে আনতে পারতো না। সেক্ষেত্রে যেটা ফিরে আসতো সেটা সত্যিকারের কাবুকি নয়। কাবুকি নামের কোনো ভিন্ন রীতি। বছরের পর বছর বহু প্রজন্মের হাত ধরে যে রীতি গড়ে ওঠে দু-একজন লোক হঠাৎ খেয়ালের বশে সেই রীতি ফিরিয়ে আনবে, সেই চিন্ত াটাই বৈজ্ঞানিক নয়, যে চিন্তা বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা করেছিলেন।
ইতিহাসের ঘটনাবলীর বাইরে পা রাখবার ক্ষমতা কারোরই নেই। নিজের খেয়াল মতো বাস্তবকে নির্মাণ করা যায় না, যা বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা করতে চেয়েছিলেন। চরণ দাস চোর নাটকের সার্থকতা কোথায় সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। চরণ দাস চোর নাটকে হাবিব তানভির কোনো মৃত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে যাননি, শহরের কিছু লোকরা মিলে পুরানো শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে সেখানে টানাহ্যাঁচড়া করেননি। হাবিব তানভির চরণ দাস চোর নাটকে ছত্রিশগড়ের বেঁচে থাকা একটা ঐতিহ্যকেই মঞ্চে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, সে ঐতিহ্যকে তুলে এনেছেন তাদের দ্বারাই যারা এর ধারক বাহক। শহুরে লোকরা সেখানে কোনো জায়গা পায়নি। যাদের ঐতিহ্য তারাই সেটাকে তুলে ধরেছে, সেজন্যই সেটা ছিলো কৃত্রিমতা বর্জিত, সেজন্যই তা ছিলো প্রাণবন্ত। হাবিব তানভির নিজেও ছিলেন ছত্রিশগড়ের সেই সংস্কৃতির একজন উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে নাটকের শেকড় সন্ধানের ক্ষেত্রে তেমন কিছু কি ঘটেছিলো?
যারা এই ঐতিহ্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন তাদের কি কোনোরকম যোগসাজশ ছিলো সেই ঐতিহ্যের সাথে? ছিলো না। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে তাঁরা শুধু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে ঐতিহ্যের সন্ধান শুরু হয়েছিলো সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে। কেন তারা হঠাৎ শেকড়ের সন্ধানে বের হলো? কারণ সমাজ পরিবর্তনের বিপজ্জনক চিন্তাধারাকে তারা ভয় পেয়েছিলো এবং সেখানে থেকে সকলের দৃষ্টিকে তারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলো। নাট্যকর্মীরা সেই প্রচারে ভুল পথে পা রেখেছিলেন।
পিসকাটরের যুগে ইউরোপে একবার একই ঘটনা ঘটেছিলো। সকলে হঠাৎ খ্যাতিমান সব নাট্যকারদের পরিত্যাগ করে প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধানে নেমে পড়েছিলো। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই সবকিছু নিহিত সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে তারা আধুনিক যুগের চিন্তার বিরাট জগতটাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলো।
পিসকাটর লিখছেন, যারা এতোদিন বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ে বড় বড় কথা বলেছে তারা উন্মাদনার জোয়ারে গা ভাসালো। প্রাচীন ঐতিহ্যকে কোনোদিন যারা আমলই দিতো না, যারা বলতো বন্দুকের চেয়ে কলম অনেক বেশি শক্তিশালী, সামান্য কয়েকজন বাদে ইউরোপের সেই বুদ্ধিজীবী অভিজাত সম্প্রদায় হঠাৎ জাতির ঐতিহ্য রক্ষায় এককাট্টা • হয়ে উঠলো। তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, পুশকিন, জোলা, বালজাক, আনাতোলে ফ্রাঁস, বার্নার্ড শ এবং শেক্সপিয়ার প্রমুখের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো এরা, যুদ্ধ ঘোষণা করলো গ্যাটে ও নিৎসের বিরুদ্ধে। এবং এইভাবে গোটা প্রজন্ম নিজেদের চিন্তার দেউলিয়াপনাকেই প্রকট করে তুললো।
কী প্রমাণ করে ঐ সকল নাট্যকারদের ছুঁড়ে ফেলে লোক ঐতিহ্যের সন্ধান করা? লোকসাহিত্যের পেছনে ছুটে বেড়ানো? মহৎ নাটক সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতাই ধরা পড়ে তাতে। মহৎ নাটক মানবিক সম্পর্কের দলিল হওয়ার সূত্রেই হয়ে ওঠে সময়ের দলিল এবং তার আবেদন হয় চিরকালীন। সেজন্য তা যুগ যুগ ধরে অভিনীত হয় এবং দর্শক চিত্তে আলোড়ন তোলে। ময়মনসিংহ গীতিকা বা লোকনাট্যগুলোর পক্ষে তা সম্ভব নয়।
বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের কাছেও লোক ঐতিহ্যের সন্ধান বা লোক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা বড় প্রশ্ন ছিলো না। প্রধান লক্ষ্য ছিলো নিজেদের দলের নাটককে দর্শকদের মনোরঞ্জনের বিষয় করে তোলা। সত্যিকারের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা শেকড়ের সন্ধান করেছিলেন কি না সে প্রশ্ন দেখা দেয় তাদের কার্যক্রমের দ্বারা। যদি তাঁরা লোক ঐতিহ্যের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর কথা ভাবতেন তাহলে তাঁরা বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি যাত্রা নিয়ে কাজ করতেন।
যাত্রা মাধ্যমটি বাংলার লোক-ঐতিহ্যেরই আরো বিকশিত রূপ। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৃত্যগীত সম্বলিত জনপ্রিয় নাট্যাভিনয় ঝুমুর, পাঁচালি, কথকতা, কবিগান ও কীর্তন-এই বিভিন্ন শাখাগুলি যাত্রাভিনয়ে সংযুক্ত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছে। যাত্রায় অভিনেতারা আসেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, ফেরিওয়ালা, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী। যাত্রা ছিলো বহু ধরনের মানুষের মিলনকেন্দ্র।
বংশ পরম্পরায় বিশেষশ্রেণীর মধ্যে এর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিলো না, ভারতের অন্যান্য অনেক লোকনাট্যের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, অভিনেতার পেশা সেখানে বংশানুক্রমিক। যাত্রায় কিন্তু লোক সঙ্গীত নেই, আছে ধ্রুপদী সঙ্গীত। মালকোশ, দেশ, পুরিয়া বাগেশ্রী, ভৈরোর খেলা। যাত্রায় এমন কোনো অভিনেতা ছিলেন না যিনি ধ্রুপদী সংগীত সম্বন্ধে সম্যক অভ্যস্ত নন।
ধ্রুপদী সংগীত আর লোক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটেছিলো যাত্রায়। সে যাত্রা মাধ্যমটি মৃত নয়, এখনো টিকে আছে-যাত্রা মাধ্যমটি এখনো প্রচুর লোককে একত্রিত করে আনন্দদানের গৌরব বহন করে চলেছে। শেকড়ের সন্ধান যাঁরা করলেন তাঁরা কিন্তু এ মাধ্যমে জড়ালেন না। ময়মনসিংহ গীতিকা বা অন্যান্য লোকজ বিষয়বস্তুকে পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তুলে এনে লোকজধারা বলে চালাতে চাইলেন।
রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্ত নাটকের পাশাপাশি যাত্রায় কাজ করেছেন। গণনাট্যর মতো গণযাত্রার কথা তিনি ভেবেছিলেন। সাফল্যও এনে দিয়েছিলেন। যাত্রা করতে গিয়ে তিনি পুরানো বিষয়বস্তুর কাছে ফিরে যাননি। রাজনৈতিক যাত্রা করেছিলেন, লালঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন। পালার নাম দিয়েছিলেন মাও সেতুং, লেনিন ইত্যাদি। সেখানে দর্শকের কোনো কমতি ছিলো না। দেশীয় নাট্যরীতিকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তিনি তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি, স্তালিন বলেছিলেন বিষয়বস্তু হবে সমাজতান্ত্রিক, আঙ্গিক হবে জাতীয়। স্তালিনের সে বক্তব্য মতো যাত্রার কাছে ফিরে যাওয়া মানে পুরানো বিষয়স্তুর কাছে ফিরে যাওয়া নয়। বিষয়বস্তু মূলগতভাবে সমাজস্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে, তবে সেই আঙ্গিকটিই নিতে হবে যা লোকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য। আঙ্গিকের প্রয়োজন এখানে বিষয়বস্তুকে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য। আসল কথা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু।
আঙ্গিক দেশকাল সাপেক্ষ, বিষয়বস্তু চিরন্তন। বিষয়বস্তুই যেহেতু প্রধান সেহেতু আঙ্গিকের প্রশ্নে এ কথাই বলা যায়, যে আঙ্গিক বাংলার জনগণ বুঝবে, ভালবাসবে যা দেখে সে উদ্দীপ্ত হবে, সেই আঙ্গিকের মোড়কে রাখতে হবে বিপ্লবী বিষয়বস্তু। কিন্তু বাংলাদেশে যারা লোকনাট্য রীতির সন্ধানে বের হয়েছিলেন তাঁরা বিষয়বস্তুকে কোনো আমলই দেননি। স্তালিনের চিন্তার বিপরীতটাই করেছিলেন তাঁরা। লোকনাট্য থেকে বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন আর এমন আঙ্গিক নিয়েছিলেন যা এখন মৃত। এব্যাপারে উৎপল দত্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।
তিনি বলছেন জপেনদার মুখ দিয়ে, ‘স্তালিন যখন বলেন ফর্ম হবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, সেটা হচ্ছে কৌশলগত প্রশ্ন। জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হলে সাধারণত ফর্ম বা আঙ্গিক সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও লোকগ্রাহ্য হয়। কিন্তু যে- বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে গেছে, সেটাকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনলে লোক মেনে নেবে কি? বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য মানে বর্তমানের জীবন্ত বৈশিষ্ট্য।’ বাংলার জীবন্ত বৈশিষ্ট্য মানে যাত্রা এবং দুশো বছর যাবৎ পাশ্চাত্যের যে নাট্যরীতি এদেশের মানুষের সম্পদ হয়ে গেছে সেটিও। যারা রাজনীতি কিংবা যে-কোনো চেতনা প্রচার করতে চান তা করতে হবে এ দুটো মাধ্যমেই এবং বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমগুলোকে আরো বিকশিত করতে হবে।
যারা বিষয়বস্তুকে রেখে শুধু আঙ্গিক নিয়ে ছুটোছুটি করছেন তাদেরকে বিচার করা যায় কোন্ দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন তুলেছিলেন উৎপল দত্ত। নাটক যার কাছে প্রচারের অস্ত্র তার কাছে আঙ্গিক গৌণ ব্যাপার। যেনতেন প্রকারে ছলে-বলে-কৌশলে কথাগুলো দর্শকের অন্তরে গেঁথে দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দরকার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, লোককাহিনীর মধ্যে তা পাওয়া সম্ভব নয়। লোককাহিনীকে সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন তা আজকের প্রেক্ষাপটে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। সমসাময়িকতার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে গ্রহণযোগ্য পুরাতনের তাৎপর্যকে। এ বক্তব্যের সার কথা এ নয় যে সমাজ পরিবর্তনের জন্য লোক কাহিনীর কাছেই ফিরতে হবে।
যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রচার করার কথা ভাবছেন তারা কি লোক ঐতিহ্যের মধ্যে এই চেতনার কোনো কিছুর সন্ধান পাবেন? যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রচারই নাট্যদলগুলোর মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে লোক ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাওয়া স্ববিরোধিতারই নামান্তর হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেও স্থির থেকে ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের সত্যিকার অনুরাগ প্রমাণ করতে পারলে না। সত্যিকার অর্থে তাঁদের নানা শ্লোগানের বা নাটক করার মূল উদ্দেশ্যই বোঝা গেল না।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 17 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৪ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/নব্বইয়ের-দশক-মধ্যবিত্তের-নাট্যচর্চার-শেষ-পরিণাম-পর্ব-৪--300x157.jpg)
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৪ ] :
নব্বইয়ের দশকের নাট্যচর্চায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তাহলো নাট্যদলগুলোর কাছে ‘হাসির নাটক’ খুব গুরুত্ব পেতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে বলছেন, নাটকগুলোতে বর্তমানে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, ‘নাটকগুলোকে খুব স্থূল হাস্যরসাত্মক করা হচ্ছে। দর্শক খাবে কি না এই চিন্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।’১৫৯ মামুনুর রশীদ সঠিক বলেছিলেন। বিশেষ করে আশির দশকের শেষ দিক থেকে পুরো নব্বইয়ের দশকে এটি ছিলো নাট্যচর্চার আর একটি প্রধান প্রবণতা।
সেই প্রবণতারও মূল কারণ ছিলো দর্শকের মনোরঞ্জন করা। সে সময় বাংলাদেশে হাসির নাটকের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের। মলিয়েরের নাটককে ঘিরে নব্বইয়ের দশকে শুরু হলো ভিন্ন একটি পথ যাত্রা। লোকনাট্য দলের কঞ্জুস, নাট্যকেন্দ্রের বিচ্ছু, নাট্যচক্রের ভদ্দরনোক, দৃষ্টিপাত নাট্য সম্পদায়ের বুন্ধু, কুশীলব নাট্য সম্প্রদায়ের গিঠঠু, মঞ্চ মুকুট নাট্য সম্প্রদায়ের ভালোবাসা কারে কয়, সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর তারতুফ মঞ্চস্থ হওয়ার ভিতর দিয়ে যা প্রমাণ করে। যদিও নব্বইয়ের দশকের আগে মলিয়ের দু- একবার মঞ্চস্থ হয়েছে তবে দর্শকদের কাছে তা তেমন আদরণীয় হয়নি। দর্শকদের মধ্যে তখন রুচিবোধ ছিলো এবং দর্শকরা সমাজচিন্তামূলক নাটক দেখতেই তখন আগ্রহী ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে মলিয়েরের নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে দর্শকদের মধ্যে-যার কারণ বিভিন্ন ধরনের সস্তা নাটক মঞ্চায়নের ফলে কিছু দর্শক তখন মঞ্চনাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।
মলিয়েরের হাসির, নাটকের দর্শক হয়ে উঠেছিলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু ফুর্তিবাজ লোক। মামুনুর রশীদ লিখছেন, ‘দেখা গেল চটুল হাস্যরসাত্মক হালকা নাটক দেখে দর্শক হাসছে। নাটক দেখছে এবং বাইরে এসে মন্তব্য শুনে অশিক্ষিত কিছু ডিগ্রিধারীর প্রতি করুণা হচ্ছে। ‘ দর্শক নাটক দেখবার আগে জানতে চায় বিষয়বস্তু কী, জানতে চায় নাটকটি হাসির কি না। হাসির নাটক দেখার জন্যই, শুধু বিনোদন লাভের জন্য তারা নাটক দেখতে আসতে লাগলো।
নাট্যদলগুলোও দর্শকদের সেই চাহিদা মেটানোর জন্য নাটকে হাসি বিতরণ করতে লাগলো। এই সব নাট্যদলই একদা ঘোষণা দিয়েছিলো, শিল্প শিল্পের জন্য নয়। নাটকের কাজ শুধু বিনোদন বিতরণ করা নয়। যারা শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলো তারাও এই পথের পথিক হলো। সেই অবস্থায় বহু নাট্যদলের মধ্যেই টিকে থাকার সংগ্রামটাই প্রধান হলো-গুরুত্বপূর্ণ অনেক দলও এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারলো না। মলিয়েরের নাটক এ অবস্থাতেই বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে বিরাট জায়গা করে নিলো।
উনিশশো আটান্নবই সালে আতাউর রহমান এক প্রবন্ধে লিখছেন, ‘ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের কথা আলাদাভাবে বলা দরকার। মলিয়ের বর্তমান বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেকে বলেন বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী, বিশেষ করে ঢাকা শহরে মলিয়েরকে নষ্ট বা বিকৃত করে জনপ্রিয়তার ক্যাপসুলে ভরে বিক্রি করছে। ১৬৮২ নাটকের এইসব সস্তা হাস্যরস দেখে শম্ভু মিত্রর একটি গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক।
নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৪ ]
বহুদিন আগে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে যাত্রা দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। যাত্রায় রাম এলো, সীতা এলো, দশরথ বিলাপ করলো কিন্তু সাহেব বাংলা বোঝে না, তাই নাক ডাকতে শুরু করলো। এমন সময় লম্বা ল্যাজ নিয়ে হনুমানকে প্রবেশ করতে দেখে ছোটো ছোটো বাচ্চারা কলরব করে উঠলো। সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি এতক্ষণ পর হনুমানের ল্যাজ নাড়ায় কিছুটা রস গ্রহণের স্বাদ পেলেন এবং খুশী হয়ে হনুমানকে দশ টাকা বখশিশ দিলেন।
সাহেব খুশী হয়েছে দেখে হনুমান ফের মঞ্চে এসে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় পশ্চাদদেশ আন্দোলিত করে ল্যাজ নাড়লো। সাহেব এবারও কড়া হাততালি দিলেন। যাত্রার মূল বিষয় বাদ দিয়ে তখন সাহেবকে খুশী করতে লেগে গেল সকলে। সাহেবকে খুশী করার জন্য এরপর রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি সীতাও ল্যাজ লাগিয়ে আসরে নামলো দর্শকদের মাত করতে। হয়তো এটা একটা গল্প।
কিন্তু এর ভিতর দিয়েই আমাদের শিল্পচর্চা বা নাট্যচর্চার চেহারাটা বোঝা যাবে। নব্বইয়ের দশকের নাট্যচর্চায় সকল দলই মলিয়ের নামের ল্যাজ লাগিয়ে দর্শক হাসাতে লেগে গেল। সমাজচিন্তা, দায়-দায়িত্ব কোথায় উবে গেল। মলিয়ের সম্পর্কে রম্যা রলাঁ লিখেছিলেন যে, বুর্জোয়াদের থেকে মলিয়েরের দৃষ্টি অনেক বেশি প্রসারিত ছিলো জনগণের প্রতি, তবে শ্রেণীসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সবসময় মলিয়েরের সঙ্গে মেলে না। তিনি একই প্রসঙ্গে লিখছেন, হাসি হলো একটা শক্তি, এবং লাম্পট্যের প্রতি সুচতুর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সেক্ষেত্রে কারণটাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। কিন্তু মলিয়েরের মধ্যে আমরা যেটা পাই না সেটা হলো কাজে নামার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।
তিনি দেখাচ্ছেন যে, মলিয়েরের নাটক সমাজ ও জীবনকে বিশ্লেষণ করার চেয়ে জীবনকে ভরিয়ে দেয় হৈ-হুল্লোড়ের মত্ততায়। দর্শকরা আবিষ্ট হয়ে থাকে মঞ্চে ঘটে যাওয়া ঘটনার তোড়ে। সেজন্য রম্যা রল্যার মন্তব্য, জনগণ যদি মলিয়েরের কাছ থেকে কিছুই না পায় শুধু নীচু মানের কমেডি ছাড়া, তাহলে তার প্রয়োজনটা কি? জনগণ হয়ত লাভবান হতে পারে ভাষার দিক থেকে, ভালো ভাষার ব্যবহারে; তাতে চেতনার বিকাশ কিছু ঘটবে না, মলিয়েরও ছুঁতে পারবেন না তাদের। তিনি মনে করেন, মলিয়েরের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী নাটকগুলো দর্শকদের বিচলিত বা উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা রাখে না, দর্শকদেরদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারে না।
ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটকেও হাসির ব্যাপার আছে তবে হাসিটা সেখানে প্রধান নয়, রাজনীতিটাই প্রধান। বুর্জোয়া সমাজকে হাস্যকর করে তোলার জন্যই নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ব্রেশটের নাটকে হাসির উদ্রেক করে। রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া নিছক হাসির ব্যাপার সেখানে নেই। ব্রেস্ট হাসি দিয়ে শুরু করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শককে ফিরিয়ে আনেন চিন্তার জগতে। শুধুমাত্র হাসির নাটক কখনই কোনো মহৎ নাট্যকারের অনুমোদন পায়নি। প্রাচীন গ্রীসের কমেডির মধ্যে যে কী পরিমাণ রাজনীতি ছিলো ভেক নাটকের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি। চেকড নিজের হাসির নাটকগুলোকে সস্তা প্রমোদকরণের বেশি মূল্য দেননি। স্থূল জনরুচিকে তিনি বিদ্রুপ করেছেন নিজের মঞ্চায়িত হাসির নাটকগুলোর প্রশ্নেই।
![নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম 18 নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৪ ]](https://actinggoln.com/wp-content/uploads/2024/01/স্বাধীনতা-পরবর্তী-বাংলাদেশের-মঞ্চনাটক-২.jpg)
চেকভের দি বিয়ার বিপুল সাড়া ফেলেছিলো দর্শকদের মধ্যে হাসির জন্য, প্রথম জীবনে অর্থোপার্জনের জন্য তিনি সে নাটকটি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সেগুলোকে নিজের বুদ্ধিহীনতা ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। দর্শকদের রুচির সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, মৃঢ়তায় ভরা নাটক বলেই তাঁর দি বিয়ার আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত দুটো প্রহসন বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতা। মধুসূদনের বন্ধুরা নাটক দুটির প্রশংসা করলেও তিনি নিজে নাটক দুটি লেখার পর ভাবিত হয়ে পড়েন। এমন চিন্তাও তাঁর মনে আসে যে, নাটক দুটি লেখা তাঁর আদৌ উচিৎ হয়নি। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, নাটক দুটিকে তিনি প্রকাশের অনুমতি দেবেন না।
তিনি সে চিঠিতে আরো লেখেন যে, জাতীয় নাট্যরীতি গড়ে তুলবার জন্য প্রথম ধ্রুপদী নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়েই দর্শকদের রুচি গড়ে তুলতে হবে। দর্শকদের রুচি গড়ে না ওঠার আগে কোনোভাবেই প্রহসন মঞ্চায়ন করা উচিৎ নয়। নিছক হাসির বিরুদ্ধে চার্লি চ্যাপলিনও বক্তব্য রেখেছিলেন। মশিয়ে ভের্দু ছবি করার পর তিনি বলেছিলেন, এতাদিন যা করেছি তার সব কিছুতেই ফাঁকি দিয়েছি, জীবনের তরল দিকটাই তাতে শুধু প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে জীবনের গভীর দিকগুলোকেই ফুটিয়ে তোলা দরকার।
চ্যাপলিন বিদ্রুপ, সংবেদনশীলতা ও চমৎকারিত্বের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিক তৈরি করলেন চলচ্চিত্র শিল্পে সমাজকে বিশ্লেষণ করার। হাসির আবরণে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন গর্বস্ফীত সমাজের গোটা ব্যবস্থাকে। ব্যঙ্গ করলেন সামাজিক বৈষম্যকে, ঠুনকো অভিজাত্যবোধকে, ওপর তলার ঔদ্ধত্য, শঠতা আর মিথ্যা ভড়ংকে। প্রথমদিকে সবই করলেন কৌতুকরস সৃষ্টির মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করে। হাস্যরস প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তিনি রূপায়িত করলেন তাঁর জীবন দর্শন। মানুষের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহও কখনও কখনও স্থান পেল সেই হাস্যরসের মধ্যে। চ্যাপলিনের গোড়ার প্রহসনগুলোতে সমাজকে তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে। দারিদ্র্যের প্রতি আছে সেখানে অপার মমতা, ধনীর প্রতি আছে শ্লেষ, প্রেমের প্রতি আছে সহানুভূতি-সেই ভাবালুতাকে কাটিয়ে চ্যাপলিন দৃঢ় পদক্ষেপে ভের্দুর রাজনীতিতে এসে উপনীত হলেন।
বহুদিন সবাইকে হাসিয়ে তারপর যখন তিনি গ্রেট ডিকটেটর নির্মাণ করেন, তিনি স্পষ্ট করেই সকলকে জানিয়ে দিলেন দীর্ঘকাল হাসির ছবি করে সভ্যতার দারুণ দুর্দিনে বক্তব্য প্রকাশের তাগিদই তিনি অনুভব করছেন। এই ঘোষণার পর যারা প্রগতি বিরুদ্ধ তারা খুব ক্ষেপে গিয়েছিলো চ্যাপলিনের উপর।সমাজপতিরা নানারকম ভয়ভীতি দেখালেন চ্যাপলিনকে। কিন্তু চ্যাপলিন লিখছেন, ছবিটা আমার অস্ত্র, ছবির ভিতর দিয়েই আমি আমার মনের কথা বলবো। কার কী মনে হলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই হলো চ্যাপলিন। সমাজ বিশ্লেষণ বা সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলাটাই তাঁর কাছে প্রধান, হাসিটা নয়।
সেজন্য হাসির জায়গা থেকে বের হয়ে এসে তৈরি করলেন মশিয়ে ভের্দু। মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা-বেদনা মশিয়ে ভের্দুতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলো। মশিয়ে ভের্দু হচ্ছে চ্যাপলিনের সমাজচেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশ, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের দ্বিধাহীন ঘোষণা। চ্যাপলিন তখন আর ভাসাভাসা মানবিকতা আর দরিদ্র নারায়ণের প্রীতিতে আবদ্ধ নেই, তিনি তখন সচেতন এক রাজনৈতিক যোদ্ধা। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণে তিনি নেমে পড়লেন সরাসরি। দীর্ঘকাল হাসির ছবি করে যে চ্যাপলিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন, মশিয়ে ভের্দু ছবি করার পর সেই চ্যাপলিনের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
চ্যাপলিন কি তাঁর জীবনের শুরুতে লোক হাসাবার কথা আদৌ ভেবেছিলেন? না তিনি তা ভাবেননি। তিনি ছিলেন গভীর জীবনবোধে উদ্দীপ্ত। চ্যাপলিন লিখছেন,নাটুকে বংশে জন্ম হওয়ার জন্যে স্বভাবতই রঙ্গমঞ্চের কথাই আমি ভাবতাম। কিন্তু তার লঘু দিকটা আমাকে টানত না। আমি বরং ভাবতাম রোমিও হয়েছি, জুলিয়েটের সঙ্গে পার্ট করছি।’ তিনি লিখছেন, ‘ভালো নাটকে গভীর আবেগপ্রবণ ভূমিকায় নামতে আমার ইচ্ছা হতো।’ পিছনের দিকে তাকালে আজও মনে পড়ে নিজের ঘরের নিরালা কোণে আমার সেই সসম্ভ্রম মহলা দেওয়া, আমার সযত্ন পদক্ষেপ, আমার মার্জিত ভঙ্গি।’ ‘হায় কোথায় সেদিনের চার্লি, আর কোথায় আজকের চার্লি।’ ‘সবসময় আকাঙ্ক্ষা ছিলো থিয়েটারের পয়লা নম্বরের অভিনেতা হবো বা নায়ক গোছের তারকা- টারকা। আমার সব পরিশ্রম, সব প্রচেষ্টা, সব জানা-বোঝার লক্ষ্য ছিলো ঐদিকে। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি হব হাস্যরসিক, ওটা একটা দুর্ঘটনা’।
চ্যাপলিন লিখছেন, ‘আমার ভাঁড়ের মতো উদ্ভট অঙ্গভঙ্গিগুলো খুব সফল হতো।’ ‘যে কারণে গ্যালারিতে ভিড় করা গাঁয়ের ছেলেদের জয়ধ্বনি, ‘পিট’ থেকে চটপটে হাততালির আওয়াজ আর স্টলগুলো থেকে ভাঙ্গা গলায় যে গর্জন উঠতো আমার অভিনয়ের তারিফ করে, তা কিন্তু আমার প্রাণে নাড়া দিত না। আমি তখনও স্বপ্ন দেখছি সিরিয়াস অভিনেতার, যাকে বলে ‘ঋজু’ ভূমিকা তাতে অভিনয় করার, আর ওদিকে দর্শকের মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার আমি ঘটাতাম তা দেখে আমার রাগ হতো। নিজের সাফল্যকে আমি অনাদর করতাম।’ কারণ ‘উচ্চতর শিল্পের সন্ধানে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার সুযোগ আমায় দেওয়া হলো না। রঙ্গ-তামাশার লোক হিসাবে আমায় ইতিমধ্যেই দেগে দেওয়া হলো।’
তিনি নিজের সম্পর্কে লিখছেন, ‘মনের কষ্টে এক ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে তাকে বললাম, ‘ভাঁড়ামো করে করে আমি ক্লান্ত। আমি একটা আসল নাটকে অভিনয় করতে চাই। শ্রোতাদের আমি শিহরিত করতে চাই।’ কিন্তু ম্যানেজার কাছে এসে বললেন, ‘দেখো ভায়া, তুমি হলে জাত কমেডিয়ান, বড় ট্র্যাজেডিয়ান হতে চেয়ে তোমার চিন্তার অপচয় করছ কেন? আরে ভায়া দুনিয়াটাকে হাসাও। সেটাই বেশি কাজে লাগবে।
চ্যাপলিন মানুষকে হাসাতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সমাজ সম্পর্কে গভীর কথাগুলো গভীরভাবে বলতে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, চ্যাপলিনকে হতে হলো ভাঁড়। চ্যাপলিন লিখছেন, ‘আমাকে ছুঁড়ে দিল রঙ্গ-তামাশার আবর্তের মধ্যে। আমাকে করে তুলল ফিল্ম জগতের ভাঁড়।’ হাস্যরস সৃষ্টিতে যিনি পৃথিবীতে এখনো শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়, কী গভীর বেদনা নিয়ে নিজের জীবনীতে তিনি বারবার একথা লিখেছিলেন তা আমাদের বুঝতে হবে। সত্যিকার অর্থেই শুধুমাত্র হাস্যরস ধাক্কা দিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাতে পারে না, ইবসেনের সিরিয়াস নাটক ডলস হাউস যা পেরেছিলো।
নিছক হাসির নাটকের বিরুদ্ধে যেখানে সকল বড় বড় স্রষ্টার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে সেখানে মলিয়েরকে আরো বেশি হাস্যরসাত্মক করতে গিয়ে এখানকার নাট্যদলগুলোর কেউ কেউ তাদের প্রযোজনকে খিস্তির আখড়ায় পরিণত করেছে। সেজন্যই আতাউর রহমান লিখেছিলেন, বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে রুচির অবনতি হয়েছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষা মানুষের শিল্পবোধ ও রুচিকে আক্রান্ত করেছে। নাট্যাঙ্গনও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি।১৩০ বাংলাদেশে যাঁরা হাসির নাটককে সমালোচনা করেছেন, সেই সকল ব্যক্তিবর্গও বিভিন্ন সময় নিজ দলের প্রয়োজনে হাসির নাটক মঞ্চায়ন করেছেন যেখানে দর্শকদের বিনোদন দেয়া ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য ছিলো না।
হাসির নাটক বা সস্তা নাটকগুলো গুরুত্ব পেল এ কারণেই যে, হাসির নাটক হলেই দর্শক পাওয়া যায়। কোন ধরনের দর্শক সেটা বড় কথা নয়, নাট্য দলগুলোর কাছে যেটা বিবেচ্য তা হলো অধিক সংখ্যায় টিকেট বিক্রি, প্রেক্ষাগৃহপূর্ণ করা। নাটকের বিষয়বস্তু সেখানে প্রধান নয়। সেজন্য নব্বইয়ের দশকেই আতাউর রহমান একবার লিখেছিলেন, ‘পণ্য থিয়েটারের পদধ্বনি ইতিমধ্যে আমরা অল্প বিস্তার শুনতে আরম্ভ করেছি’।
বিষয়টা যে নব্বইয়ের দশকে শুরু হয়েছে তা নয়। নাট্যান্দোলনের শুরুতেও আমরা কম-বেশি লোক হাসাতে দেখেছি বহু দলকে। বিশেষ করে ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটককে পর্যন্ত সস্তা হাসির উপাদানে পরিণত করা হয়েছিলো। সত্তরের দশকে ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটককে হাসির মোড়কে ভরে দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিলো নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় তাদের দু-দুটো প্রযোজনায়।
রাজনৈতিক নাট্যকার ব্রেশটের নাটক ঢাকায় প্রথম মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের। ব্রেশটের গুড উওম্যান অব সেৎজুয়ান ও হের পুন্টিলা এন্ড হিজ ম্যান মাটি নাটক দুটির রূপান্তর সৎ মানুষের খোঁজে ও দেওয়ান গাজীর কিসসা নাগরিক সত্তর দশকেই মঞ্চস্থ করে। মঞ্চায়িত তাদের নাটক দুটির প্রযোজনা সম্পর্কে সমালোচনা ছিলো, ব্রেশটের নাটকের রাজনীতি বাদ দিয়ে শুধু গল্পের কাঠামো ও হাসি তামাশাগুলোই দর্শকদের মনোরঞ্জনে তারা ব্যবহার করেছিলো। চিন্ময় মুৎসুদ্দী লিখছেন, ব্রেস্ট সমাজ সচেতন নাট্যকার, বক্তব্যহীন নাটক তিনি লেখেননি। কিন্তু নাগরিকের দেওয়ান গাজীর কিসসা নাটকে ব্রেশটের বক্তব্য অপ্রধান হয়ে গেছে, নাটকের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে দেওয়ান গাজীকে প্রধান করে তোলা হয়েছে।
মূল নাটকের যে দ্বন্দ্ব তা এ নাটকে পাওয়া যায় না। নাগরিককে মনে রাখতে হবে জনপ্রিয়তাই মহৎ শিল্পের একমাত্র উপাদান নয়। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মতোই বহুবচন নাট্যদল তাদের প্রযোজনায় ব্রেশটের থ্রি পেনি অপেরা নাটকের মূল বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে তাকে শুধুমাত্র হৈ চৈ আর হাসি-তামাশার ব্যাপারে পরিণত করেছিলো। সন্তা নাটক করার প্রবণতা, দর্শকদের মাতানো-এসব আসলে শুরু থেকেই নাট্য আন্দোলনে লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।
নাটকের বিষয় যদি গণজীবন থেকে গ্রহণ করা না হয়, যদি তার মধ্যে দ্বান্বিততার প্রকাশ না ঘটে, যদি তার মধ্যে ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাগুলো স্থান না পায়, তবে মাত্র কল্পিত রাজ্যে ভ্রমণ করে দর্শকের মন বেশি দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দর্শকের মনে যে প্রশ্ন আছে; তার উত্তর যদি থিয়েটারে এসে পায়, তাহলে সে থিয়েটারের ভক্ত হয়ে উঠবে এবং থিয়েটারেকে প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করবে।
কিন্তু দর্শককে যদি কেবল আনন্দ দেবার চেষ্টা করা হয়, যদি শুধু হাসির খোরক যোগানো হয়-তাহলে সে আসবে, দেখবে ও চলে যাবে। কিছুই তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। নাটকের সাথে, নাট্যদলের সাথে দর্শকের গণসংযোগ ঘটবে না। কোনো ধরনের আদর্শের পক্ষে তারা দাঁড়াবে না। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় বিশেষ কতগুলো দল কেবলমাত্র হাসি বিতরণ করে নাটককে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি। নাটকের ইতিহাসে চোখ রাখলে তাঁরা দেখতে পেতেন, প্রাচীন রোমের নাটকে এবং বুর্জোয়া সমাজের উন্মেষকালে কমেডিয়া ডেল আর্তের কর্মকাণ্ডে লোক হাসানোর সকল প্রচেষ্টা বড়ো মাপের শিল্প সৃষ্টি করতে পারেনি।
স্মরণ রাখতে হবে, রোমের অধিকাংশ অভিনেতারা ছিলেন দাসশ্রেণী থেকে উদ্ভুত যাদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিলো না। জাতে এঁরা ছিলেন নিছক পেশাদার আমোদদাতা, ভবঘুরে নিম্নশ্রেণীর মান-মর্যাদাহীন মানুষ, যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় হৈ-হুল্লোড় প্রিয় জনতাকে আনন্দদানের চেষ্টা করতো। সংলাপ বলার চেয়ে মজাদার বজ্জাতি এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাৎক্ষণিক হাস্যরসের উদ্রেক করে তাঁরা দর্শকদের মাতিয়ে রাখতেন। এই সকল দলের সঙ্গে অভিনেত্রী হিসাবে থাকতো গণিকারা যাঁরা প্রয়োজনে স্ত্রী-ভূমিকা বা নর্তকীর দায়িত্ব পালন করতো। বহু পরে ষোল শতকে আমরা এই পদ্ধতির নাট্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি কমেডিয়া ডেল আর্তে।
সেখানে কোনো নাট্যকারের রচনা ছাড়াই দশ থেকে বারোজন অভিনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক কথোপকথন সৃষ্টি করে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কি আরো বেশী সময় দর্শকদের হাসির তুফানে মাতিয়ে রাখতেন। কথোপকথন ছিলো এইক্ষেত্রে নিছক অনুষঙ্গ, পরিবর্তে আংগিক অভিনয় বা হাঁটা-চলা এবং উদ্ভট মঞ্চক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলো। নাটকের কাহিনী বা সংলাপকে গৌণ করে প্রতি অভিনেতা একাধিক মঞ্চক্রিয়া খুঁজে বের করতেন যেগুলি নিছক অবাস্তব ও হাস্য- উদ্দীপক। ডিগবাজি খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক কলাকৌশল যা সাধারণত সার্কাসের ক্লাউনের কার্যকলাপের সাথে মেলে।

নাট্যকারের ভূমিকা অগ্রাহ্য করে, নাটকের ব্যাখ্যা বাতিল করে দিয়ে, ইতালীর কমেডিয়া ডেল আর্তের অভিনেতারা বলতে চেষ্টা করেন মঞ্চেই নাটকের যথার্থ বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই ধারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না, নাট্যকারের গুরুত্ব অচিরেই প্রমাণিত হতে থাকে। যখন বড় বড় নাট্যকাররা মঞ্চ কাঁপিয়ে তুললেন, কমেডিয়া ডেল আর্তের রঙ্গ-তামাশা স্তিমিত হলো।
চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় কমেডিয়া ডেল আর্তের ধারা থেকেই এসেছিলো কিন্তু বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে নয়। চ্যাপলিন লিখছেন, কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা প্রচণ্ড হাসির উদ্রেক করে। দর্শককে হাসতে হাসতে পাগল করে তোলাটা কোনো কোনো অভিনেতার স্বপ্ন। কিন্তু আমি চাই হাসিটাকে ছড়িয়ে দিতে। পেট ঘুলিয়ে ওঠে তেমন হাস্যরোলের চেয়ে আমি পছন্দ করি ছোটো ছোটো হাস্যরোল। কিন্তু স্বভাবতই তাকে আমি ভাঁড় বানাবো না, তারমধ্যে থাকবে বুদ্ধিদীপ্ততা। কমেডিয়া ডেল আর্তের অভিনেতারা বুদ্ধিদীপ্ততাকে বাদ দিয়ে শুধু লোক হাসাতেই ব্যস্ত ছিলেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অধিক নাট্যদলের কাম্য। সস্তা নাটক করার প্রবণতা, দর্শকদের মাতানো, নাটকে অশ্লীলতাকে প্রাধান্য দেয়া, এসব ঢাকার প্রথম সারির দলগুলোর মধ্যে প্রথম দেখা যায়।
সেই প্রচেষ্টাগুলোই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, দিনে দিনে ফলে ফেঁপে মহীরুহ হয়েছে। ফলে সমাজ পরিবর্তন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এসব মুখে বলা হলেও বেশির ভাগ দলগুলোরই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো দর্শক শিকার করা। দর্শককে যে-কোনোভাবে মঞ্চে আনতে হবে এবং টিকেট বিক্রি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যে- কোনো ধরনের অপসংস্কৃতি প্রচারেও তখন আর নাট্য দলগুলোর আপত্তি দেখা গেল না। সমাজচিন্তা আর তখন তাদের কাছে গুরুত্ব পেল না, দর্শকের মনোরঞ্জন করা হয়ে উঠলো প্রধান বিষয়। সেজন্যই চটুল গল্প ও চটুল সংলাপ নিয়ে মাতামাতি আরম্ভ হয়েছিলো। বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এসব ব্যাপারে কোনোই ভূমিকা রাখতে পারেনি তার ঘোষিত আদর্শ ও নীতিমালার কারণেই।
গ্রুপ থিয়েটারের নীতিমালা অনুযায়ী যে-কোনো দল নিয়মিত নাটক করলেই গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করতে পারে। দলগুলো কী ধরনের নাটক করছে সেটা গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের বিবেচ্য নয়। সদস্য দলগুলির মঞ্চায়িত নাটকগুলি কী সমাজপরিবর্তনের পরিপূরক চিন্তায় ভরপুর, না বিপরীত চিন্তায়, সেটা ফেডারেশনের দেখার বিষয় নয়। ফেডারেশনের দেখার বিষয় প্রতি বছরে দলগুলো ন্যূনতম তিনটি প্রদর্শনী করছে কি না। সে যে-কোনো ধরনের প্রদর্শনী হোক। মঞ্চায়িত নাটকের বিষয়বস্তুর প্রশ্ন তুলে কখনো কোনো দলের সদস্য পদ বাতিল হয়নি। ফেডারেশন আয়োজিত নাট্যোৎসবগুলিতেও তাই বিভিন্ন দলের সস্তা নাটকগুলোও জায়গা পেয়েছে।
সমাজ পরিবর্তন বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতার যে অভাব রয়েছে তা রূপকথার লোকনাট্য বা সস্তা হাসির নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। সেজন্য আলী যাকের এক সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করেছেন, ‘সংস্কৃতির যে দুরবস্থা এটার জন্য আমরা সবাই দায়ী।… সামগ্রিকভাবে চিন্তাটা লঘু ব্যাপারে চলে এসেছে এবং এই লঘু ব্যাপারের জয় জয়কার চলছে। এবং সেটাতে আমরা কিন্তু মশলা দিচ্ছি। আমরা সেটাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছি।’১৭° সেই সাক্ষাৎকারে তিনি একথাও বলেছেন, নাট্যদলগুলো অনেক দূরে সরে এসেছে তাদের ঘোষিত আদর্শ থেকে।
নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা যাকের উপরে যে মন্তব্যটি করেছেন, নাটক তার আদর্শ ছেড়ে বহুদূরে সরে এসেছে। মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিণতি হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। প্রথম থেকেই আমরা দেখে এসেছি নাটকের কোনো সুদূর লক্ষ্য বা সুসংহত রূপ ছিলো না। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আরো দেখেছি মধ্যবিত্ত মানসিকতা দ্বারা আক্রান্ত এ নাটকের লক্ষ্য ছিলো প্রথম দিকে শুধুমাত্র নাটক করা।
পরে ঘটনাচক্রে সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ সচেতনতা সৃষ্টির বক্তব্য আসলেও বৈজ্ঞানিক বিপ্লববাদ দ্বারা এ নাট্যধারার উদ্বোধন কখনই হয়নি, পরিচালিতও হয়নি। কোনো নাট্যদলই নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। সুবিধামতো তারা নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছে, একটি আদর্শকে বেছে নিয়ে সে আদর্শের ধারাবাহিকতায় নাটক মঞ্চায়ন করেনি। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক ছিলো প্রতিবাদের সর্ববৃহৎ ও সর্ববলিষ্ঠ রূপ তবে সেটা বিপ্লবী রূপ নয়, সেটা রাজনৈতিক নাট্যধারা নয়। সেই প্রতিবাদের রূপটিও ছিলো বুর্জোয়া মতবাদে ঠাসা ও সীমাবদ্ধ। সেই প্রতিবাদেরও কোনো ধারাবাহিকতা ছিলো না।
মাঝে মাঝে প্রতিবাদ, মাঝে মাঝে লোক হাসানো, মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ গীতিকার নামে প্রেমের গল্প শোনানো। ফলাফল কী দাঁড়ালো? সারা নাট্যাঙ্গন ভুগতে লাগলো অপরাজনীতির ব্যামোয়। সামাজবিজ্ঞানের চেতনাহীন নাট্যকর্মীরা যখন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলেন নাট্যকর্মীদের শেকড়ে তখন ঘুণ ধরলো। সেই ঘুণে ধরা থেকে নাট্যমঞ্চ ক্রমশই বিরান ভূমিতে পরিণত হতে থাকলো। দর্শক নেই, দর্শককে টেনে আনবার মতো নতুন নাট্যচিন্তা নেই। এর থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজে বের করা গেল না। কেন এমন হলো? আসলে শিল্প যদি তার সঠিক রাজনীতি খুঁজে না নিতে পারে তাহলে বুর্জোয়া রাজনীতি তাকে কিনে নেয় এবং একসময় ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের নাটকের অবস্থাও বিশ শতকের শেষে এসে দাঁড়িয়েছিলো তাই। নব্বইয়ের দশকে ঢাকার মঞ্চে হাহাকার শোনা যাচ্ছিলো।
বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে খুব প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন উনিশশো আটানব্বই সালে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ইউসুফ। তিনি লিখছেন, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে নাটক একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে স্বীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ অর্জন। সামান্য পরেই আবার তিনি লিখছেন, ‘পঁচিশ বছরের উপান্তে দাঁড়িয়ে আজ নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মচিত হয়েছিলো আমাদের সামনে তার কতটুকু আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি। নতুন কিছুই ঘটছে না নতুন কিছু দেখছি না। আমাদের নাটক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে আছে।
চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা নয় যেন সযত্নে চ্যালেঞ্জকে পাশ কাটিয়ে নিরাপদ প্রযোজনা করা আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’তিনি আরো লিখছেন, নির্লিপ্ত নির্বিকার নাট্য প্রযোজনা আমাদের থিয়েটারকে এক স্থবির জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নাসির উদ্দীন ইউসুফের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাটকের মূল চেহারাটা বের হয়ে এসেছে। নাসির উদ্দীন ইউসুফের বক্তব্য যেন বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের উপসংহার বা শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যে নাটককে বলা হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, যে নাটক বারবার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার ঘোষণা দিয়েছে, নাসির উদ্দীন ইউসুফ পঁচিশ বছর পর দেখতে পাচ্ছেন সেই নাটক প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ বাদ দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে দেখবো নাটক আর সরকার বিরোধী ভূমিকাও পালন করছে না বরং সরকারের সাথে নানাভাবে আঁতাত করে বসে আছে। সরকারের সকল অন্যায়কে নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে। সরকারের কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তারা প্রতিবাদ মুখরিত হচ্ছে না। সরকারের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাট্যদলগুলোর ইচ্ছাকৃত মুখ বুজে থাকা নিয়ে নিরানব্বই সালে থিয়েটারওয়ালা পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে লেখা হচ্ছে, ‘আমরা, থিয়েটারওয়ালারা, প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়েছি। রাষ্ট্রে সমসাময়িককালে ঘটে যাওয়া বড় অনিয়ম, অত্যাচারেও আমরা নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছি।
অন্যান্য পেশাজীবী কিংবা শ্রমজীবীদের উপর রাষ্ট্রের এই যে অন্যায় এবং এতে আমাদের নীরবতা, সেই নীরবতা এক সময় নিজেদের উপর রাষ্ট্রকৃত অনাচারেও নীরব থাকতে বাধ্য করে।১* কামালউদ্দিন কবির লিখছেন, অনেক আনন্দ আর আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের নিয়মিত নাট্যচর্চা। সাতাশ বছর অতিক্রমের পর সার্বিক হিসেবের ফলাফলে যতোটা না আনন্দ তারচেয়ে বেশি বিষণ্ণতা এবং আশার বদলে হতাশার চালচিত্র ফুটে ওঠে।'”* নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে এই যে নাট্য আন্দোলনের স্থবিরতার কথা সবাই বলছেন এর প্রধান কারণগুলো কী? শুরু থেকেই নাট্য আন্দোলনের লক্ষ্যহীন দিক ভ্রষ্ট হয়ে পথ চলার পরিণাম হচ্ছে এই স্থবিরতা। নাট্যকর্মীদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার শেষ পরিণামই হচ্ছে এক সময় এসে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা। সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়ানো।
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সাঈদ মাহমুদ লিখছেন, ‘সত্যিকার গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার পথে আজ যে মূল বাধাটা প্রথমেই বিরাজ করছে তা হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও লাইন। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান তথা নাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব হচ্ছে সাবিকভাবেই বুর্জোয়া নেতৃত্বের অধীন, যা অন্যদিকে আবার স্বাধীন বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে কাজ না করে সাম্রাজ্যশক্তির পক্ষেই কাজ করছে। সামাগ্রিকভাবে সারা দেশের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের নেতৃত্ব থিয়েটার, নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক-এই ধরনের ঢাকা কেন্দ্রিক বড় বড় দলগুলোর নেতাদের হাতে কুক্ষিগত। এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অধিকাংশই বড় বড় ব্যবসা ও বিজ্ঞাপনী সংস্থার মালিক যা আবার বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত।
এঁরা যেমন বহুজাতিক কোম্পানির পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তেমনি বড় বড় পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের পণ্যেরও প্রচারণা চালায়, যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং দেশীয় পুঁজিপতিরা এদেশের শ্রমিকদের শোষণ করেই তাদের মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান বা বড় বড় নাট্যদলগুলো তাদের নাটক বা নাট্য উৎসব করে বাংলাদেশ টোব্যাকো, আলাফা টোব্যাকো ধরনের বড় বড় পুঁজিবাদী সংস্থার সাহায্য ও সহযোগিতায়। এভাবেই তারা নাট্য আন্দোলনকে বড় বড় বুর্জোয়া বা সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।
সেই জন্য তারা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই না করে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। যে সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের মূল শত্রু তাদের তোষণ করে, তাদের মুক্ত বাজারকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে রক্ষা করারই নামান্তর।
মসিউজ্জামান মহসিন দেখাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গুত্ব থেকে মুক্ত করতে হলে সাম্রাজ্যশক্তির প্রতিভূ বিটিসি, লিভার ব্রাদার্স এই সব বহুজাতিক কোম্পানিকে রুখে দাঁড়ানো দরকার ছিলো। নাট্যকর্মীদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের জন্য যতো সহজ, বিটিসি, লিভার ব্রার্দাস-এর মতো বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের জন্য সহজ নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদের মূল প্রতিভূ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে তাঁরা অর্থনৈতিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন।
সুতরাং এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব শ্রমিক-কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে দেবে না তা অত্যন্ত সহজবোধ্য। নাট্য আন্দোলনকে এঁরাই তারকা প্রথার নিগড়ে বেঁধে ফেলছেন। পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের অন্তর্ভুক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্যযুক্ত অন্যান্য ছোটখাট মাঝারি দলগুলো এবং তাদের নেতা ও কর্মীরা অধিকাংশই এই বুর্জোয়া নেতৃত্বের অন্ধ দাসত্ববৃত্তি করেন। নব্বই সালে সাঈদ মাহমুদ যে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং যেভাবে তিনি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বড় বড় নাট্য দলগুলোকে দায়ী করছেন, নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে সাঈদ মাহমুদের সেই বক্তব্যই সত্য হয়ে ওঠে। নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে মামুনুর রশীদ নিজেই স্বীকার করছেন, নাট্যদলগুলো উচ্চবিত্তের আগ্রাসনের কাছে থিয়েটারকে বিক্রি করে ফেলেছে।

মামুনুর রশীদ এসময় এসে মনে করছেন থিয়েটারটা হয়ে গেছে উচ্চবিত্তের বিনোদনের জায়গা এবং থিয়েটার বেনিয়া পুঁজির ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। নাটকের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এগিয়ে আসছে বহুজাতিক কোম্পানি। ১৮৩ প্রশ্ন দাঁড়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কি শ্রমিকশ্রেণীর নাটককে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? স্বভাবতই সেটা সম্ভব নয়। ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যে নাটকগুলোকে বা যে দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে তারা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষের নয়। কারণ শত্রুর কোলে বসে তার ইচ্ছার বাইরে আর কোনো ভূমিকা রাখা যায় না।
মামুনুর রশীদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সম্পূর্ণ নাট্য আন্দোলনই হয়ে উঠেছে উচ্চবিত্তদের বিনোদন দেবার মাধ্যম, যা নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে বিরাট এক প্রশ্ন তুলে বসে। মামুনুর রশীদ দেখাচ্ছেন, নাট্য আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তো নয়ই এমনকি রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের পক্ষেও নয় বরং তা হয়ে উঠেছে শোষকশ্রেণীর তথা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসংরক্ষণকারী মাধ্যম।
সাম্রাজ্যবাদ সব সময় প্রগতিশীল ধারার উন্মেষকে রোধ করার কাজে, প্রগতিশীল সকল ধারাকে দুর্বল ও পথভ্রষ্ট করার কাজে অধ্যবসায় নিয়ে নিয়োজিত। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনকে প্রতিরোধমুক্ত, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুন্ঠন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।
বাংলাদেশে তাই নাট্যক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার উন্মেষের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছে। কতিপয় সুবিধাবাদী নাট্যকর্মীকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান, পুরস্কারের নামে অর্থ দান, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া, ব্যবসায়িক আনুকূল্য প্রদান-এসবের মাধ্যমে নাট্যক্ষেত্রে প্রগতি বিরুদ্ধ বিষয়াবলীর প্রতিষ্ঠাকরণ চলছে। নাটক মঞ্চায়ন, নাট্যোৎসব, নাট্য-সেমিনারকে আর্থিক সহায়তা দানও সেই ষড়যন্ত্রের অংশ। প্রথম সারির নাট্যদলগুলোর সাথে, তাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনি তাঁদের জন্য সেখানে সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারটিও রয়েছে। ফলে নাট্যান্দোলনের শিল্পীরা আগের মতো আর আদর্শের পেছনে নেই।
নৈরাশ্য, প্রাচুর্যের লোভ, রাতারাতি টিভি-নক্ষত্র বনে যাওয়ার হীন প্রচেষ্টা, বিজ্ঞাপনে পণ্যের মডেল সাজা এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁদের সামগ্রিকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং একদা মঞ্চের প্রতি বিশ্বস্ত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ নাট্যশিল্পীরাও তাঁদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। নাটকের কোনো দর্শন বা আদর্শ কাউকে আর আকর্ষণ করছে না বরং সস্তা জনপ্রিয়তার পথে, তাঁরা ছুটে বেড়াচ্ছেন। যে কোনোভাবে ‘টাকা’ আয় তাঁদেরকে তাড়িত করছে। ফলে বাংলাদেশের নাটক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের চাহিদা পূরণে সক্ষম হলেও মূল লক্ষ্যের দিকে এগুতে পারেনি, ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে।
নব্বইয়ের দশকের শেষে এই অবস্থা আরো প্রকট হতে দেখি। এর প্রধান কারণ নাট্যান্দোলনে মধ্যশ্রণীর প্রাধান্য, যে মধ্যশ্রেণী নিজেই স্বার্থান্ধ এবং দোদুল্যমান। সেইজন্য এই মধ্যশ্রেণী দেশের নাট্যচর্চায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে নাটককে নিজেদের স্বার্থান্ধ বৃত্তের মধ্যেই আটকে রাখতে চান। বিপ্লব বিরোধী কর্ম পরিকল্পনার অংশরূপেই তাঁরা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করেন। সাম্রাজ্যবাদের দেয়া তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে নাটকে এখন শেকড়ের সন্ধান করে বেড়ান। নাটকে শেকড় সন্ধান করতে গিয়ে কিংবা হাসির হুল্লোড় বা বিনোদন বিতরণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে সরে দাঁড়ান। এভাবেই তাঁরা মানুষের ক্রোধকে বিপ্লবের বিপরীতে সংস্কারের পথে ধাবিত করতে পারছেন। নারী স্বাধীনতার পক্ষে শ্লোগান তোলা, ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোতে তাই তাঁরা তৎপর ছিলেন কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নে নয়।
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নাট্যচর্চার সাথে স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্যচর্চার বিচার করলে দেখা যাবে, পূর্ব পাকিস্তানে বহু নাটক লেখা হয়েছে যার রাজনৈতিক গভীরতা স্বাধীনতা পরবর্তী কালের চেয়ে অধিক ছিলো। স্বাধীনতার পূর্বের তেইশ বছরে নাটক লেখা হয়েছে অনেক বেশি এবং প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়, সাড়ে পাঁচশোর মতো। স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকে প্রকাশিত নাট্য গ্রন্থের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম।
স্বাধীনতা পূর্বের নাটকগুলোর সামগ্রিক মান বিচার করতে গেলে তা স্বাধীনতা- উত্তরকালের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে ছিলো। স্বাধীনতার পূর্বে নাট্যকার বা নাট্য দলগুলোর পক্ষ থেকে সমাজপরিবর্তন, শ্রেণীসংগ্রাম এসব ঘোষণা দেয়া হয়নি কিন্তু বেশ কিছু সাহসী নাটক লেখা হয়েছে। ভূমিকাতে আমরা সেসব নাটকের কিছু উদাহরণ দেখেছি। সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান তাদের প্রত্যেকের নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় মেলে।

সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজদ্দৌলা, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর বহিপীর, শওকত ওসমানের বাগদাদের কবি সর্বকালের নাটক বলেই বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকারদের বহুজনই ঐ মানের নাটক রচনা করতে পারেননি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের নাট্যচর্চায় বহুবিধ ঘোষণা আর শ্লোগান এবং স্থূলভাবে রাজনীতির প্রকাশ ঘটেছে। খুব কম নাটকেই চিন্তার গভীরতা ছিলো, জীবনবোধের প্রকাশ ছিলো। বেশিরভাগ নাটকগুলো ছিলো উচ্চকিত এবং নন্দনতত্ত্বের বিচারে সেগুলো নাটকের মধ্যেই পড়বে না।
সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন সারাদেশে নাট্যচর্চার আগ্রহ বাড়িয়েছে এবং স্বাধীনতা পূর্বের যাত্রার উচ্চকিত ঢং থেকে নাটককে মুক্ত করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্য নির্দেশনা নাট্যচর্চায় বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন দেশকে ভালো কিছু নাট্য প্রযোজনা দিতে পেরেছে। কিছু কিছু কালজয়ী প্রযোজনারও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার পরিধি কতটুকু? মূল কারণ খুঁজতে গেলে আমরা দেখবো, বাংলাদেশের যে নাট্য আন্দোলন, নাটক সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। তা হয়ে উঠেছিলো সস্তা শ্লোগান। ফলে ‘শিল্পকলা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার’, ‘শিল্পকলা সমাজকে সুন্দর করে’, ‘নান্দনিক বোধের জন্ম দেয়’ ইত্যকার ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি নাটক বা সামগ্রিক নাট্য আন্দোলন বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিলো।
স্মরণ রাখা দরকার, শিল্পকলা বা নাটক যদি কলা না হয়ে ওঠে তবে তা নানা ব্যাধিও ছড়াতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী নাটকের ইতিহাসে চোখ বুলালে দেখা যাবে, শিল্পকলার বিচারে বহু নাটকই নাটক হয়ে ওঠেনি বলেই তা শুধু কটু গন্ধ ছড়িয়েছে। প্লেটোর ভাষায় নাটক নানা কুশিক্ষাও দিয়েছে।