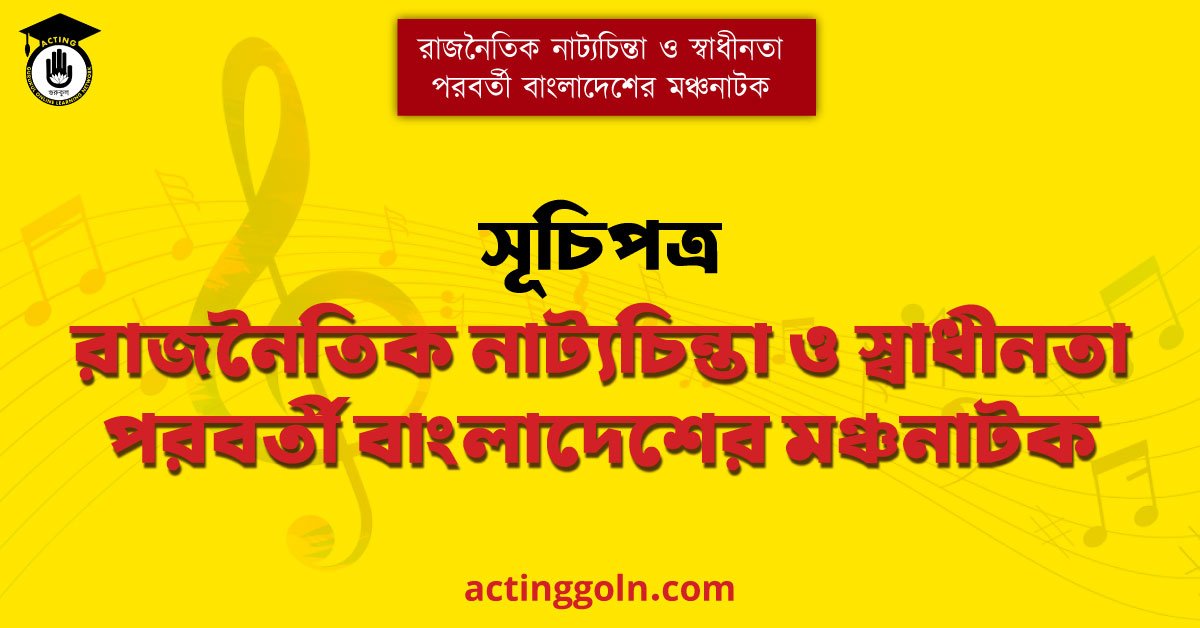রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক – হাজার বছরের বাংলা নাট্যচর্চা ঔপনিবেশিক শাসন- শোষণে আপন কক্ষপথ চ্যুত হয়ে আধুনিক থিয়েটার অভিধায় যে বাঁক পরিবর্তন করেছিল, বঙ্গীয় পূর্বাঞ্চলের নাট্যক্রিয়া সে প্রাণ বাঁচিয়ে আপন সত্তায় তা বজায় রেখেছিল দীর্ঘদিন। বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের যে চর্চা পরিলক্ষিত হয় তা স্বাধীনতা পরবর্তী। ১৯৪৭ এর দেশভাগ দুটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড সৃষ্টি করলেও পাকিস্তানি নব্য উপনিবেশ এ দেশে থিয়েটার চর্চার বড়ো অন্তরায় ছিল। আধুনিক থিয়েটার অভিধায় বাংলা নাট্যের যে প্রচলন তা পূর্ব বাংলার নিজস্ব কোনো কৃতি নয় বরং তা কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা নাট্যচর্চারই অনুকৃতি মাত্র। যতটা স্বাতন্ত্র্য তার প্রেক্ষিত হিসেবে বলা যায়- বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনই নাটককে প্রোসেনিয়ামের চার দেয়ালের বাইরে রাস্তায়-সভামঞ্চে প্রতিবাদ- বিক্ষোভের ভূমিতে জনতার সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক
প্রথম অধ্যায়
- নাটক মঞ্চায়নের উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার পশ্চাৎপট [ পর্ব ১ ]
- নাটক মঞ্চায়নের উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার পশ্চাৎপট [ পর্ব ২ ]
- নাটক মঞ্চায়নের উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার পশ্চাৎপট [ পর্ব ৩ ]
দ্বিতীয় অধ্যায়
- বিশ শতকের রাজনৈতিক নাট্যধারায় মার্কসীয় প্রভাব [ পর্ব ১ ]
- বিশ শতকের রাজনৈতিক নাট্যধারায় মার্কসীয় প্রভাব [ পর্ব ২ ]
- বিশ শতকের রাজনৈতিক নাট্যধারায় মার্কসীয় প্রভাব [ পর্ব ৩ ]
তৃতীয় অধ্যায়
- বাংলাদেশের মঞ্চনাটক : উৎস ও কর্মধারার ব্যাপকতা [ পর্ব ১ ]
- বাংলাদেশের মঞ্চনাটক : উৎস ও কর্মধারার ব্যাপকতা [ পর্ব ২ ]
- বাংলাদেশের মঞ্চনাটক : উৎস ও কর্মধারার ব্যাপকতা [ পর্ব ৩ ]
চতুর্থ অধ্যায়
- সত্তরের দশক: নাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব ও গতিধারা [ পর্ব ১ ]
- সত্তরের দশক: নাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব ও গতিধারা [ পর্ব ২ ]
- সত্তরের দশক: নাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব ও গতিধারা [ পর্ব ৩ ]
পঞ্চম অধ্যায়
- আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ১ ]
- আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ২ ]
- আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৩ ]
- আশির দশক: শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক নাট্যের উন্মেষ [ পর্ব ৪ ]
ষষ্ঠ অধ্যায়
- নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ১ ]
- নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ২ ]
- নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৩ ]
- নব্বইয়ের দশক: মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চার শেষ পরিণাম [ পর্ব ৪ ]
উপসংহার
বিভিন্ন অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা বলতে যা বোঝায় তার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকের নাট্যচর্চার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনই এখানকার নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় সচেতন রাজনৈতিক ধারার প্রবর্তন করেছে যদিও তা সকল দল বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটেনি। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তা কখনই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি হয়ে উঠতে পারেনি।
রাষ্ট্রের সাথে বিরোধের প্রশ্নে তা রাজনৈতিক এবং ক্ষোভ প্রকাশ বা প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণেই তা রাজনৈতিক। কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতি থেকে তা ছিলো বহু দূরে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলো এই প্রচেষ্টা বা আন্দোলন কখনো স্থির থাকেনি। বারবার ধারা পাল্টেছে, বক্তব্য পাল্টেছে। অস্থিরভাবে দিকবিদিক ছটাছুটি করেছে। নাটক শুরু হয়েছিলো নিয়মিত প্রদশর্নী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পুরানো নাট্যরীতির বিরুদ্ধতা করে।
পরে নাটককে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলেছে, আরো পরে তাকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছে। নাট্যচর্চা শেষ পর্যন্ত এখানেও থেমে থাকেনি। শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে তারা নাটককে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষে গড়ে তুলতে চেয়েছে, পাশাপাশি তারা শ্লোগান তুলেছে শেকড় সন্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাটককে করে তুলতে চেয়েছে পেশাদার; জীবন জীবিকার উপায়।
বহু ধরনের শ্লোগান তুললেও প্রকৃত অর্থে নাট্য আন্দোলন কোথাও এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সব প্রচেষ্টা, সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। উদ্যোগ যেমন ছিলো অনেক, ব্যর্থতাও তেমনি বিশাল। নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই যে বারবার উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হয়ে যাওয়া এর প্রধান কারণ হচ্ছে নাট্যকর্মীদের চিন্তার বিভ্রান্তি, আন্তরিকতার অভাব এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার হাতছানি।
পুঁজিবাদী সমাজে সকলেই সচ্ছলভাবে, সুন্দরভাবে বাঁচার তাগিদে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বাংলাদেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যদলের মধ্যেও তা লক্ষ্য করা গেছে। নাট্যকর্মীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও নাট্যদলগুলোর পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা বারবার তাদেরকে দিক ভ্রষ্ট করেছে। নিজেদের ঘোষিত লক্ষ্যের পক্ষে কখনো তারা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন আবার শেকড়ের সন্ধানে চলছে। শেকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে তারা প্রসেনিয়ামের বিরোধিতা করেছে প্রসিনিয়ামের মধ্যে আটকে থেকেই।
এই ধরনের নানা স্ববিরোধিতার মধ্যেই বাংলাদেশের নাটক বেড়ে উঠেছে। স্ববিরোধিতার জন্যই কোনো একটি নাট্যধারাকেও তারা চূড়ান্ত সাফল্যের জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি। নানা বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা কখনো শ্রেণীসংগ্রাম বা সমাজ বদলের রাজনীতি হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রমিকশ্রেণীর সাথে কিংবা দেশের অধিকাংশ জনগণের সাথেও এ নাট্যচর্চার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যচর্চার প্রথম ধাপ এ্যাজিটপ্রপ, যা শ্রমিকদের-শোষিতদের মধ্যে জাগরণ তৈরির জন্য রাশিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশে বিগত বিশ-ত্রিশ-চল্লিশের দশকে মঞ্চস্থ হতে দেখেছিলাম। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় তেমন কোনো এ্যাজিটপ্রপ ধারাও লক্ষ্য করা গেল না। বিভিন্ন দেশে এ্যাজিটপ্রপ ধারা সাধারণত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে মঞ্চস্থ হতো। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলদেশের কোনো নাটকই আমরা শ্রমিক-কৃষকদের জন্য মঞ্চস্থ হতে দেখি না। শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে কোনো নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো যেমন কোনো মার্কসবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না, নাট্যকর্মীদের মধ্যেও তেমনি মার্কসবাদের বিশ্বাসকে লালন করতে দেখা যায় না। বিভিন্ন দলগুলোর দেয়া সমাজ পরিবর্তন বা শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগানগুলো ছিলো শ্লোগান মাত্রই, কোনো, নাট্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে বা দলের নাটক মঞ্চায়নে সে বিশ্বাসের ধারাবাহিক প্রতিফলন ঘটে না।
বরং বহু ক্ষেত্রেই তাদের মঞ্চায়িত নাটকে মার্কসবাদ বিরোধী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। স্তালিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র তিনটি ঝোঁকে বিভক্ত; সংস্কারবাদ, নৈরাজ্যবাদ এবং মার্কসবাদ। বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় সমাজতন্ত্র কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের নামে নৈরাজ্যবাদেরই দেখা মিলেছে। নাট্যদলগুলোর দেয়া দীর্ঘদিনের শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা ছিলো যে ব্যক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত তা বিভিন্ন দশকেই ধরা পড়তে থাকে।
ঘটনাবলী প্রমাণ করে শ্রেণীসংগ্রামে মূলত তাদের বিশ্বাস ছিলো না, বিশ্বাস ছিলো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারে। নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের লক্ষ্যেই তারা শ্রেণীসংগ্রামের মতো মতবাদটিকে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে ব্যবহার করেছিলো। দরকার মতো আবার সে অবস্থান থেকে সরেও দাঁড়িয়েছিলো।
বিভিন্ন নাট্যদলগুলো শ্রমিকশ্রেণীর কথা বললেও তারা শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়ায়নি বরং দাঁড়িয়েছে বিপরীত পক্ষে। বারবার তারা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সাথে, শোষকশ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়েছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো বক্তব্য ছিলো না। সাম্রাজ্যবাদীরা সবসময় প্রগতিশীল ধারার উন্মেষকে রোধ করার জন্য, পথভ্রষ্ট করার জন্য সব দেশেই তৎপর। বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনে যে-টুকু প্রগতিশীল কার্যক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছিলো, মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা উন্মেষের যে সম্ভাবনা ছিলো, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই তাকে পথভ্রষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়।
সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দু-একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলকে নাটক মঞ্চায়ন করবার জন্য টাকা দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে, যা অন্য দলগুলোকে নাটকের খরচ জোগাড়ের জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে, বা তাদের অনুদানের প্রতি লালায়িত করে। দেশের নাট্য আন্দোলন তাই দেশের ব্যাপক জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, শ্রমিক- কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বহুজাতিক এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা বিদেশি দাতা সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা আশা করতে থাকে।
সাম্রাজ্যবাদীরা আরো নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিলো। সে ষড়যন্ত্র তারা চালিয়েছিলো শুধু দেশীয়ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিলো বিশ্ব জুড়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধে জাতীয় নাট্য ঐতিহ্য লালন বা শেকড়ের সন্ধানে নাট্য দলগুলোকে প্ররোচিত করা। সভা-সেমিনারের নামে টাকা পয়সা দিয়ে, নাট্যব্যক্তিত্বদের বিদেশে যাবার সুযোগ করে দিয়ে নানাভাবে এই বক্তব্যকে তারা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়েছিলো। নাট্যদলগুলোর কিছু কিছু সচেতনভাবে, অনেকে আবার না বুঝেও সে ষড়যন্ত্রে পা দেয়। মধ্যবিত্তদের মানসিকতার মধ্যেই বাস করে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ, সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা খুব সহজে তাদের পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে পারে। প্রগতিশীল নাট্যকর্মীরাও মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও স্বচ্ছ মার্কসবাদী ধারণার অভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের সত্যিকার পরিচয় বুঝে উঠতে পারে না। নাটক সম্পর্কে নিজেদের স্বচ্ছ ধারণার অভাবে তারা প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর সাথে সুর মেলায়।
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ছিলো নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গা থেকে, মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে। শ্রমিকশ্রেণী বা বৃহত্তর শোষিতশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করে নয়। সুবিধাজনক পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। দরকার মতো তারা সরকার বিরোধী কিংবা সরকার পক্ষ দুটি ভূমিকাই পালন করেছে। বিশেষ করে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত হাসিনা সরকারের আমলে তারা সরকার বিরোধী কোনো ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করেনি। নাটকে সরকার বিরোধী কোনো বক্তব্য রাখেনি। সরকারের সাথে নাট্যদলগুলো সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলো এবং মিলিতভাবে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো।
সরকারের সাথে এভাবে আপোষ করতে গিয়ে নাট্য আন্দোলনে যতোটুকু প্রগতিশীলতার ধারা বজায় ছিলো তা ফিকে হতে হতে অন্তঃসারশূন্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শোষণ ব্যবস্থায় মূল শত্রু কারা নাট্যকর্মীরা তা আর চিহ্নিত করতে পারে না। রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার প্রধান একটি কাজ জনগণের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করা, বাংলাদেশের নাটক মূলগতভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। নাট্যকর্মীরা সমাজের ভিতরের শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁদের নিজেদের ভূমিকা কী হবে তা যেমন কখনো সুনির্দিষ্ট করতে পারেননি, তেমনি নাটকে শোষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন অর্থনৈতিক বন্ধনগুলো তারা পরিস্ফুট করেননি। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির
অভিলাষে নাটককে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শোষকশ্রেণীর লুন্ঠন বজায় রাখবার হাতিয়ার করে তোলেন। আশির দশকে তাঁরা যে শ্লোগান তুলেছিলেন তার ঠিক বিপরীত অবস্থানই তাঁরা নেন। বিশেষ করে আশির দশকের শেষদিক থেকে লোকনাট্য চর্চার নামে নাট্য প্রযোজনায় নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিলো। ভূমিকাতে আমরা তিন প্রকারের নাট্যচর্চার উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম। সে বিচারে দ্বিতীয় দলেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে স্থান দেয়া যেতে পারে।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক নাট্যচর্চার নামে যে ধারা আরম্ভ হয়েছিলো সেখানে তাহলে আমরা কী দেখতে পাই? গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শুরু থেকেই বিমূর্ত বা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার আবির্ভাব, নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে শ্রেণীচেতনার অভাব, গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চায় শ্রমিক-কৃষক তথা প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর অনুপস্থিতি, নাট্যকর্মীদের মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী অবস্থান ও সমগ্র আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই ধরনের একটি নাট্যচর্চাকে কোনোভাবেই মার্কসীয় রাজনৈতিক চিন্তা হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। পূর্বেই আমরা বলেছি সকল শিল্প-সাহিত্য বা নাটকই রাজনৈতিক। সে রকম মূল্যায়নে যারা মার্কসীয় রাজনীতি করেন না তারাও এক ধরনের রাজনীতিতে জড়িত। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের নাট্যদলগুলোর একটি রাজনৈতিক চরিত্র অবশ্যই আছে। সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সুবিধাবাদী রাজনীতি; যারা নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন রাজনীতিতে অংশ নেয় কিন্তু কোনো রাজনৈতিক আদর্শে অনড় থাকে না। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো বিভিন্ন সময় সুবিধাবাদী রাজনীতিরই লেজুড়বৃত্তি করেছে। বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলন তাই ব্যাপকতা না পেলেও, সারা দেশের মানুষের কাছে পৌছুতে না পারলেও প্রথম সারির নাট্যকর্মীরা পৃথিবীর দরিদ্রতম এই দেশে বাস করেও দামী গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছেন। সরকারি শিল্প মাধ্যমগুলোতেও তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন।
ধনিকশ্রেণীর মতোই তাঁদের জীবন যাত্রার মান। নাট্য আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও নিজেদেরকে তাঁরা ঠিকই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারাদেশের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সদস্য দলগুলোর কাছে, অধিকাংশ নাট্যকর্মীর কাছেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্য পরিষ্কার ছিলো না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি বরং ফেডারেশানের নেতৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ মতোই ফেডারেশানকে পরিচালিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার পক্ষে তারা কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি বা তা করার আগ্রহ দেখায়নি।
সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়গানই শুধু গেয়েছিলো তারা। আর এ ধরনের গণতন্ত্রের মতবাদ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের, সুবিধাভোগীদের মতবাদ। নাট্যকর্মীদের চিন্তা ছিলো সেই সুবিধাভোগীদের মতবাদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের রাজনীতিও ছিলো তাই সমাজতন্ত্র বা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণীসংগ্রামের কথা মুখে বলা হলেও সকলেই আসলে সংসদীয় রাজনীতির চারদিকেই ঘুরপাক খেয়েছে। নানা উপায়ে তারা জনসাধারণকে শুধু নিজেদের সংসদীয় রাজনীতির স্বার্থের অনুকূলে সামিল করতে চেয়েছে।
মধ্যবিত্তরা এ ধরনের একটি নাট্য আন্দোলনে যতোখানি প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশে নাট্যকর্মীরা তাও পারেননি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তদের দ্বারাই ব্যাপক রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়, সে নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো শ্রমিক-কৃষকদের নিয়েই। পশ্চিমবঙ্গের সে নাট্য আন্দোলন শুরুতে শ্রমিক- কৃষকদের মধ্যে অভূপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলো। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সাথে এখানেই পার্থক্য আমাদের গ্রুপ থিয়েটারগুলোর। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারগুলোর অনেকেই সরাসরি মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী আবার কেউ কেউ আছেন যারা মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হলেও বিশ্লেষণাত্মক নাটক মঞ্চায়নে আগ্রহী। কিছু গ্রুপ থিয়েটার আছে যারা উগ্র রাজনীতি প্রচারে বিশ্বাসী, যাদের কাছে নাটক আর শ্লোগানে পার্থক্য নেই।
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য ধারাটি প্রধানত কাজ করেছে শ্রমিকশ্রেণীর একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় বারবার শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান দেয়া সত্ত্বেও সেই ধরাটি দেখতে পাই না। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের একটি অঙ্কুর দেখা গিয়েছিলো, স্বাধীনতার পূর্বে তাও দেখা যায়নি বাস্তব কারণেই।
কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সেই রাজনৈতিক নাট্যচর্চার অঙ্কুরটি আর বেড়ে উঠতে পারলো না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, এ আন্দোলন এরকম হতে বাধ্য ছিলো; কারণ এ আন্দোলন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত যুবসমাজের গড়ে তোলা আন্দোলন। এই মানুষগুলো যে সামাজিক ব্যবস্থা থেকে এসেছে, তাঁদের মানসিকতাও সেরকম হয়েছে। এই মানসিকতার দ্বারা তাঁরা এমন নাট্য আন্দোলনে গড়ে তুলতে পারলো না যা মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতাকে পার হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে সকলেই যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আটকে থাকতে চেয়েছেন তা নয়। বহুজনেই নাটককে মধ্যবিত্তের বৃত্ত ভেঙে গণমানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে সময় প্রমাণ করেছে কেউ বৃত্ত অতিক্রম করতে পারেননি। ব্যষ্টিক পর্যায়ে কোনো নাট্যকার বা নাট্যদল কখনও কখনও সে বৃত্ত অতিক্রম করলেও সামগ্রিক নাট্যচর্চা সেই বৃত্তকে অতিক্রম করতে পারেনি।
রাজধানী ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরে এবং বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে কিংবা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নাটক গিয়েছে কিন্তু মৌল বাস্তবতার কোনো হেরফের হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তরা যা পেরেছিলো বাংলাদেশ তা পারেনি শুধুমাত্র স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় মার্কসবাদী চিন্তার অভাবে। মূল কথা হলো, নাট্যকর্মীদের শ্রেণীচরিত্র ও সমাজবিজ্ঞান চেতনার অভাব থেকেই এসব হয়েছে। নাট্যকর্মীরা যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে বড় হয়েছেন, তার থেকে মুক্ত না হয়ে তাঁদের পক্ষে কোনো সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি করা সম্ভব ছিলো না।
মার্কসবাদী চিন্তাই মধ্যবিত্তের নানা দুর্বলতা, নানা ক্ষোভ-আক্ষেপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী চিন্তার অভাবেই বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে তা ঘটেনি। মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে তারা নাটককে মধ্যবিত্ত সীমানার ভিতরেই আটকে রাখলেন। মধ্যবিত্ত মন-মানসিকতা যদি সামনে আগাতে না পারে তাহলে সে শুধু পিছিয়েই পড়ে। বাংলাদেশের নাটক তাই সামনে আগাতে পারলো না বলেই পিছিয়ে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সাথে মিশে গেল। সত্তরের দশকে যেখানে প্রেমসর্বস্ব নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিলো, দু দশকের মাথায় নাটক আবার সেখানেই ফিরে গেল এবং অবশেষে মুখ থুবড়ে পড়লো।
বহুল আলোচিত ও উচ্চকিত বাংলাদেশের নাটক বা নাট্য আন্দোলনের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি এমন এক চেহারা নিয়েছে যে, এক বাক্যে বলা সম্ভব পুরো উদ্যোগটিই মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্বারা দিয়ে কর্তৃক। এই বৃত্তেই পুরো নাট্য কর্মকাণ্ড আবদ্ধ এবং মৃতপ্রায়। নাট্য আন্দোলনের শেষ পরিচয় যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধু রাম সর্দার।
আরও পড়ুনঃ