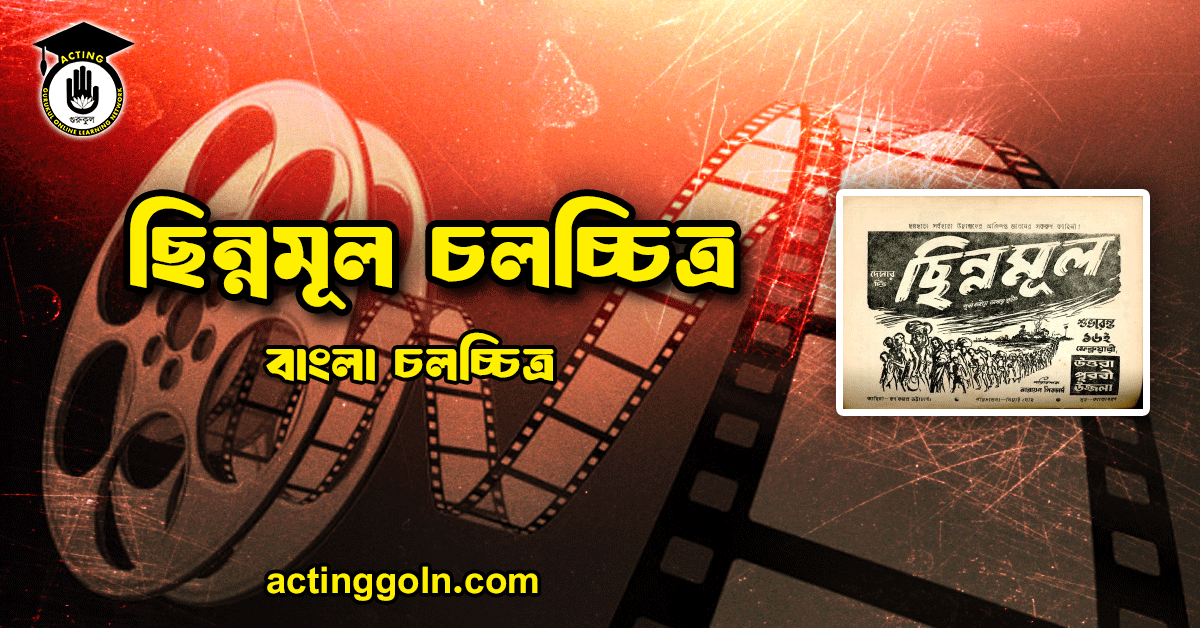ছিন্নমূল চলচ্চিত্র ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত বিমল দে প্রযোজিত ও নিমাই ঘোষ পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র। দেসা পিকচার্সের এই চলচ্চিত্র পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে জলজ্যান্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এটিই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা ভারত বিভাজনকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। ছিন্নমূল চলচ্চিত্রকে ভারতের প্রথম নব্য বাস্তববাদী চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিখ্যাত রাশিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ভেসেভলড পুডোভকিন সেই সময় কলকাতায় এই চলচ্চিত্রটি দেখেছিলেন। ছবিটি দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে ভারত সরকারের অনুমুতি নিয়ে চলচ্চিত্রটি রাশিয়ায় প্রকাশের জন্য এই ছবির প্রিন্ট কিনেছিলেন। সেইসময়ে চলচ্চিত্রটি রাশিয়ার ১৮১টি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার দর্শক-সমালোচকমন্ডলী দ্বারা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের কাছে চলচ্চিত্রটি সমাদৃত না হওয়ায় এটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি।
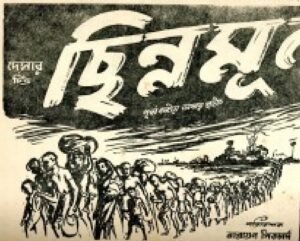
ছিন্নমূল চলচ্চিত্র
- প্রযোজনা— দেশা পিকচার্স।
- প্রযোজক – বিমল দে।
- পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও চিত্রগ্রহণ— নিমাই ঘোষ।
- কাহিনি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।
- সংগীত পরিচালনা — কালোবরণ।
- শিল্প নির্দেশনা— অনিল পাইন।
- সম্পাদনা— গোবর্ধন অধিকারী।
অভিনয়:
শোভা সেন, প্রেমতোষ রায়, গঙ্গাপদ বসু, শাস্তি মিত্র, সুশীল সেন, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, সুনীল রায়চৌধুরী, শাস্তা দেবী।
কাহিনি:
পূর্ব বাংলায় জলাঙ্গী গ্রামের খেটে খাওয়া চাষি, কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর সাম্প্রদায়িক ঐক্য ছিল। ছবির কেন্দ্রে আছে শ্রীকান্ত (প্রেমতোষ) এবং তার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী বাতাসী (শোভা)। দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, যুদ্ধ, দেশভাগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সব আন্দোলনেই শ্রীকান্ত সবার আগে তাই কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে।
দেশ ভাগের ফলে পাশের গ্রামে দাঙ্গা বাধলে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা মোড়লের (গঙ্গাপদ) নেতৃত্বে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। বাতাসীও তাদের সাথে কলকাতায় আসে। কলকাতায় তারা আশ্রয় না পেয়ে প্রথম দিকে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকতে বাধ্য হয়, শুরু হয় তাদের বেঁচে থাকার লড়াই।
উষান্তরা এক বড়লোকের পরিত্যক্ত বাড়ি জোর করে দখল নেয় এবং সেখানেই বাতাসীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অপর দিকে শ্রীকান্ত জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামে গিয়ে জানতে পারে তার প্রতিবেশীরা দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গিয়েছে। সে কলকাতায় আসে এবং অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে গ্রামের মানুষদের সাক্ষাৎ পায়, এক নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে সে স্ত্রীর দেখা পায়, বাতাসী তখন মৃত্যুশয্যায়, নবজাতকের ক্রন্দন নতুন যুগের সূচনা ঘোষণা করে।
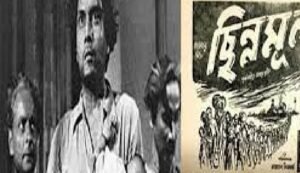
ছবিটি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নয়া বাস্তববাদী ধারার সূচনা করে। দেশভাগ বাঙালির জীবনে যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার জীবন্ত দলিল এই ছবি, ছবিতে বেশ কিছু আশে বাংলা দেশের মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা কোনোরকম মেকআপ ছাড়াই অভিনয় করেছেন।
সমগ্র ছবি জুড়েই পরিচালক সিনেমার ভাষা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। শিয়ালদা স্টেশনে সত্যিকারের উদাত্ত শিবিরের ব্যবহার ছবিটিকে একটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। বাংলা ছবিতে নতুন ধারার ছবি ‘পথের পাঁচালী’র সার্থক পূর্বসুরি এই ছবি। এই ছবি মুক্তির সময় সেন্সরশিপের ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির আপত্তি ছিল।
বীরেন্দ্রনাথ সরকার, তৎকালীন চেয়ারম্যানের, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ছবিটি সেন্সর সার্টিফিকেট পায়। রাশিয়ান কালচারাল ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে ভি. আই. পুদভকিন কলকাতায় এই ছবিটি দেখেন এবং Pravda পত্রিকায় এই ছবিটির দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন, মূলত তাঁর উদ্যোগে এই ছবিটি রাশিয়ায় দেখানো হয়। ছবিটি কার্লো ভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবিটি নিয়ে মৃণাল সেনের লেখা সমালোচনা পরিচয় (ফাল্গুন, ১৩৫৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রকাশনা:
ছিন্নমূল নিমাই ঘোষের প্রবন্ধ বক্তৃতা সাক্ষাৎকার এবং তাঁর জীবন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা। সম্পাদনা করেছেন সুনীপা বসু ও শিবাদিত্য দাশগুপ্ত। কলকাতা, সিনে সেন্ট্রাল ও মনচাষা, ২০০৩।