গত পর্বে আশিস গোস্বামীর “বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা” বইয়ের বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় এর লেখা ভূমিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলে। এবার প্রকাশ করা হল জনাব আশিস গোস্বামীর নিজের লেখা ভূমিকাটি। নাটক, অভিনয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জানতে সাহায্য করতে পারে ভেবে আমাদের ওয়েবে যুক্ত করে দিলাম। আশা করি কাজে লাগবে।

“বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা” বইয়ের ভূমিকা – আশিস গোস্বামী
সম্ভবত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চ। আমি হলে ঢোকামাত্রই শ্রীমতী শোভা সেন বললেন, ‘উৎপল (দত্ত) তোকে ডাকছে। হলে এসেই তোর খোঁজ করেছে।’ আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, কোনো দোষ করে ফেলেছি কি? শোভাদিকে বললাম, আজ তো ‘এপিক থিয়েটার’-এর ‘কল্লোল সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা। সেটা বেরিয়েছে কি? শোভাদি বললেন, ‘হ্যাঁ, তারপরই তোর খোঁজ করেছে।’
ওই সংখ্যাটির কিছু দায়িত্ব আমার ছিল। তাই নিশ্চিত গালমন্দের কথা ভেবেই হাজির হলাম উৎপলদার সামনে। কিন্তু এ কী কাণ্ড! আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চওড়া বুকের মাঝে তখন আমার নিশ্চিত পুরস্কার প্রাপ্তি—‘এ সংখ্যার সবচেয়ে ভালো লেখা হয়েছে তোমার। তাই লাল সেলাম’। আর কী চাই আমার! এমন মানুষের কাছ থেকে এমন প্রাপ্তি ক’জনের জোটে। ওঁরাই পারতেন এমন ভাবে সব উজাড় করে ভালোবাসা দিতে।
তারপর আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন কোথা থেকে সংবাদপত্রের ক্লিপিংসগুলি জোগাড় করেছি, কোন লাইব্রেরিতে গিয়েছি ইত্যাদি সব। মেকআপ রুমে ঢোকার আগে বললেন, ‘এরকম কাজ ভীষণ জরুরি, ইতিহাসের স্বার্থেই জরুরি, ওই কাজ বড়ো আকারে করো। আমার কানে এখনও অহরহ সেই কথাগুলিই মন্ত্রোচারণের মতো বেজেই চলেছে। আমার বর্তমান কাজটি সেই মন্ত্রোচারণের প্রথম ফসল বলা যেতে পারে।
আমাদের দেশে কোথাও নাট্য সমালোচনা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। অথচ এই ধারাটিকে বাদ দিয়ে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়-এর মতো মানুষেরা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং সেই কাজে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেরই সাহায্য নিয়েছিলেন কিন্তু সেই সাহায্যকারী মাধ্যমটি নিয়ে কোনো অধ্যায় রচনা করেননি। তবে তাঁরাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, নাট্য সমালোচনা ইতিহাসের স্বার্থে কতখানি প্রয়োজনীয়। আকর গ্রন্থগুলি আশ্রয় করেই আরও অনেক নাট্য ইতিহাস, অভিনয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে কিন্তু নাট্য সমালোচনার কোনো ঐতিহাসিক ধারা নিয়ে কোনো চর্চা হল না।
এই অনালোচিত দিকটির প্রতি প্রথম মনোনিবেশ ঘটিয়েছিলেন আমার প্রিয় অধ্যাপক ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর থেকে হলেও তিনি এই অভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সদ্য এম এ পাশ করা শেষ বেঞ্চের একটি ছেলের কাছে কেন তিনি এ কথা বলেছিলেন জানি না। তার ইচ্ছে আর উৎপলদার আদেশ আমাকে আজীবনের মতো এই কাজে নিযুক্ত করে দিল।
বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আরও উপলব্ধি করলাম, এ কাজ প্রায় আজীবন ধরে করে যেতে পারলেও সম্পূর্ণ হবে না। কারণ, বহু পত্র পত্রিকার তো কোনো হদিসই নেই। সম্পাদকই জানেন না তাঁর পত্রিকার কোনো কপি আছে কি নেই! গ্রন্থাগারগুলি সুনিয়ন্ত্রিত নয়, থিয়েটারওয়ালারা সঞ্চয়ী নন ফলে অসম্পূর্ণতা থাকবেই। যতগুলি পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করেছি, ততগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারিনি। প্রথম তিনটি অধ্যায়ের কয়েকটি পত্রিকা দেখতেই পাইনি, অন্যান্য কিছু বইয়ে তার উল্লেখ ও আলোচনা থেকেই আমার আলোচনার গতিপথ ঠিক করে নিতে হয়েছে। তবে যতটুকু পেয়েছি তাকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।
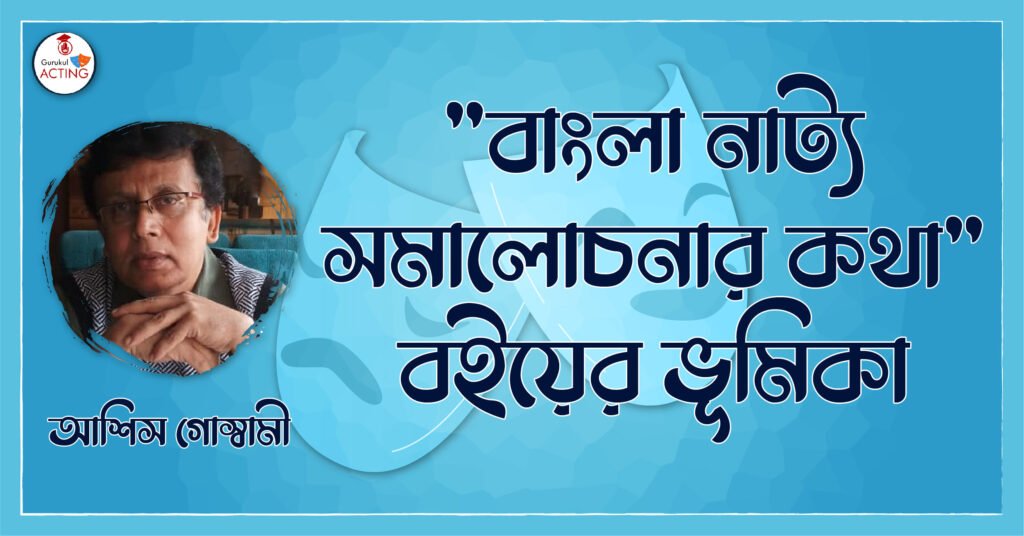
আমি নিজেই জানি আমার গবেষণাকর্মের কোথায় কতটুকু ফাঁক রয়ে গেছে। যেমন, ‘ভগ্নদূত’ পত্রিকার সময়কাল জানি কিন্তু কতগুলি সংখ্যা ঠিক কোন দিন থেকে কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হত জানি না। একই অবস্থা ‘রূপমঞ্চ’র ক্ষেত্রেও। প্রকাশক্ষণ জানি না। ‘প্রসেনিয়াম পত্রিকার প্রথম বর্ষের কোনো সংখ্যাই পাইনি। কেবলমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের বেশ কয়েকটি সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী অক্ষয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোডাউন থেকে খুঁজে পেয়েছিলাম।
সেই সংখ্যাগুলি থেকেই পত্রিকা সমালোচনার মোটিভকে ধরবার চেষ্টা করেছি। ড. বিষ্ণু বসু ‘গণনাট্য’ পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশনাগুলি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও সলিল চৌধুরী সম্পাদিত ‘গণনাট্য’ পত্রিকার সন্ধান মেলেনি। তবে ওই সময়ের দু-একটি সমালোচনা অন্যত্র খুঁজে পেয়েছি। ‘গন্ধব’র সমালোচনাগুলি দিয়েছেন ‘গন্ধব’র তৎকালীন সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা। এভাবেই আমার আলোচনার পথকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছি।
এই সমস্ত পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কারও সঙ্গে হয়তো আলোচনা করেছি কিন্তু এই বইয়ে লিখিত অথবা মুদ্রিত বিষয়ের ওপরেই জোর দিয়েছি। আমার মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি বলা-কথার ভিত্তিতে নয়, প্রামাণ্য বিষয়ের ভিত্তিতে। সেই কারণেই দৈনিক পত্রিকা বা সাময়িক পত্রিকাগুলির যে সংখ্যা গুলি হাতে পেয়েছি কেবলমাত্র সেই সংখ্যাগুলির সমালোচনার ভিত্তিতেই তার ঐতিহাসিকতা খুঁজবার চেষ্টা করেছি।
আমার এই প্রচেষ্টা কতখানি সঠিক এবং প্রয়োজনীয় তা বিচারের ভার, যিনি পাঠক তাঁরই। তবে তাঁর কাছে আমার বিনীত নিবেদন, অনেক ফাঁক-ফোকরের সন্ধান তিনি পাবেন কিন্তু বাংলায় এ ধরনের আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে না পাওয়াটাকে যেন ক্ষমাশীল মনে মেনে নেন। আমি সতত সচেষ্ট থাকব একে সম্পূর্ণতা দানে—এ অঙ্গীকার রাখছি।
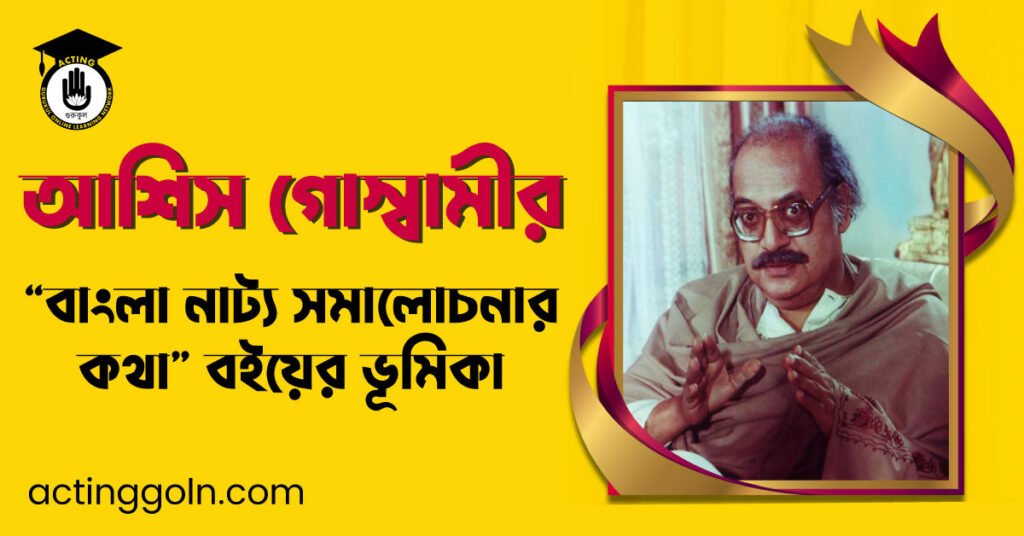
আমার কৃতজ্ঞতার তালিকার প্রথম নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বাংলা বিভাগের প্রধান, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়েব—তিনিই প্রথম ‘এরকম কাজ হয়নি, অথচ হওয়া দরকার’—এ কথা যেমন বুঝিয়েছিলেন; তেমনি আমার মতো অনুল্লেখিত ছাত্রকে এই বজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কোনো শব্দই যথেষ্ট নয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে। যেমন জানি না, প্রখ্যাত নট-নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তকে, কোন্ শব্দে শ্রদ্ধা জানাব? এখন সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি।
এই ধরনের কাজে সবচেয়ে উৎসাহী আর একজন মানুষের কাছেও ঋণী—তিনি নৃপেন্দ্র সাহা। তাঁর ভাবনার বহু প্রতিফলন আছে আমার কাজে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকার সম্পাদক নৃপেন্দ্রদা গোটা কাজের পিছনে অনবরত তাগাদা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ আলোর কবি শ্রী তাপস সেনের কাছেও। অনেক অনুসন্ধান তাঁরই মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। তবে এসব কথা আজ থেকে অনেক বছর আগের। বর্তমানে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন, কাজ করছেন। সমবেত চেষ্টার একটা সঠিক অর্থ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।
কৃতজ্ঞ দুই বাংলার প্রিয় মানুষ হায়াৎ মামুদ আর পরমাত্মীয় রহমত আলী ও ওয়াহিদা মল্লিক জলির প্রতি। কৃতজ্ঞ ড. বিষ্ণু বসুর কাছে। এ কাজের নানা কৌতূহল নিরসন করেছেন তিনিই। এ ছাড়া বন্ধু অনীত রায় ও স্কুলের সহকর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বীজেশ সাহা আমার অনেকদিনের বন্ধু। প্রতিভাস থেকে এই প্রকাশনায় ওর সহযোগিতা আজীবন মনে থাকবে।
এই কাজের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ এবং নাট্যশোধ সংস্থার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। যতটুকু তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা এদেরই সহায়তায়। আমার সহধর্মিনী সুমিত্রা বহু লাইব্রেরির কাজ করে দিয়েছে। আর বাবা, এবং দীপের কথাও বলতে হয়।

শেষে বলি, মায়ের কথা। মা কতকাল আগে থেকে এমন একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, উঁচু পাহাড় ডিঙোনোর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন এখনও যেমন তিনি লালন করেন, আমাকেও লালিত করার নিয়ত চেষ্টারই ফসল এই গবেষণাটি। তাই এ সবটুকুই তাঁর জন্য রইল। সকলের কাছে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।
আশিস গোস্বামী
[ ১৫-১২-২০১০ ]
আশিস গোস্বামীর “বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা” বইয়ের ভূমিকা -১ – বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমের আদলে বাংলা নাট্যরচনা ও নাট্যমঞ্চায়নের ইতিহাস দীর্ঘকালের নয়। লেবেদয় এক বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এদেশে। প্রাগাধুনিক কালে যাত্রা বা কথকতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন মাধ্যম সেকালের রসিকেরা। কিন্তু মঞ্চের তিনদিকে আব্রু টেনে দিয়ে মঞ্চ নির্মাণের যে-কৌশল তা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগকে দিল এক ভিন্ন মাত্রা। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে নাট্যরস-পিপাসা মেটানোর জন্যে বাঙালি রসিক যে-মাধ্যমের সাহায্য নিত তার আমূল পরিবর্তন যখন ঘটল তখন নাটক যেমন আবৃত্তি নামক কলা মাধ্যমে বদ্ধ রইল না, তেমনি কথা ও গানের মাধ্যমে নিতান্তই ‘পালা’-ও রইল না।
সংলাপ, সংগীত, সময় নামক নির্দিষ্ট পরিমাপক, দৃষ্টির অগোচরে ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং আরও কিছু নিয়ে মঞ্চমায়ায় আচ্ছন্ন নতুন শিল্পরূপ আমাদের কাছে অভিনবত্ব নিয়ে উপস্থিত হওয়ামাত্র আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম ভরতের নাট্যশাস্রোক্ত নির্দেশনার বিশ্ব থেকে এবং অবশ্যই লোকনাট্যের সংরূপগত বৈশিষ্ট্যের জগৎ থেকে। এই উত্তরণকে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী করার জন্য নতুন নাট্যরচনা যেমন অনিবার্য হয়ে উঠল, তেমনি সত্য হয়ে দেখা দিল সৃষ্টির সঙ্গে রস সম্ভোগ তথা সমালোচনা।
ড. আশিস গোস্বামী যে-গবেষণা সন্দর্ভটি রচনা করেছেন ‘নাট্য সমালোচনার কথা নামে, নাট্যরসিকদের কাছে তার আবেদন অজ্ঞাত তথ্যের উন্মুক্ত আলোকিত সম্ভার উপস্থিত করার প্রতিশ্রুতিগর্ভ। কাব্য এবং উপন্যাস রচনায় আমাদের ভাষা সফল ও গরিমাময়। স্বীকার করা অনুচিত হবে যে নাট্যরচনায় মধুসূদন দত্তের আক্ষেপই সত্য হয়ে রয়ে গিয়েছে দীর্ঘকাল। আবার রচনায় যদি ঋদ্ধির অভাব ঘটে তাহলে সমালোচকের তীর্থযাত্রা সফল হবে কি করে? সুতরাং নাট্যসমালোচনার কথা-র লেখক যে সহজ কর্মে ব্রতী নন তা অকপটে স্বীকার করা উচিত।
বাঙলা নাটকের বা চলচ্চিত্রের সমালোচনা আমরা একালে যেমন দৈনিক সংবাদপত্রে তেমনি সাময়িক পত্রেও পাই। শুধু তাই নয় অনেককাল ধরে নাট্য সমালোচনার জন্য পৃথক পত্র-পত্রিকাও জন্ম নিয়েছে। বলাবাহুল্য, নাটক যেমন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অবলম্বনে লেখা হয়েছে তেমনি তার উপস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে এবং পত্র-পত্রিকাগুলিও তাদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সেইসব নাট্য-সমালোচনাকে আশ্রয় দিয়েছে।
ড. আশিস গোস্বামী তাঁর আলোচনাকে দুটি অংশে ভাগ করে নিয়েছেন :
১. প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় একটি স্তবকে আবদ্ধ। এই স্তবকে আছে—
(ক) নাট্য সমালোচনার লক্ষ্য।
(খ) এদেশীয় নাট্য-সমালোচনার অতীত।
(গ) আধুনিক নাট্য সমালোচনার বৈশিষ্ট্য।
(ঘ) সমান্তরাল নাট্যধারার নাট্যসমালোচনা।
(ঙ) সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্য সমালোচনা।
২. দ্বিতীয় অংশে রয়েছে নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার (১৯৪৪-১৯৭৮)। এই অংশে আছে পনেরোটি নাটকের প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রসঙ্গ। সৎ সমালোচকের সমুচিত কথা আশিস ভূমিকাংশে যেভাবে জানিয়েছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হয়।
আশিস বলছেন, ‘আমি নিজেই জানি আমার গবেষণাকর্মের কোথায় কতটুকু ফাঁক রয়ে গেছে, যেমন ‘ভগ্নদূত’ পত্রিকার সময়কাল জানি কিন্তু কতগুলি সংখ্যা ঠিক কোন দিন থেকে কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হত জানি না। একই অবস্থা ‘রূপমঞ্চ’র ক্ষেত্রেও। প্রকাশক্ষণ জানি না। ‘প্রসেনিয়াম’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের কোনো সংখ্যাই পাইনি। ড. বিষ্ণু বসু ‘গণনাট্য’ পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশনাগুলি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও সলিল চৌধুরী সম্পাদিত ‘গণনাট্য’ পত্রিকার সন্ধান মেলেনি। তবে ওই সময়ের দু-একটি সমালোচনা অন্যত্র খুঁজে পেয়েছি।
‘গন্ধব’র সমালোচনাগুলি দিয়েছেন তৎকালীন সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা। সুতরাং তাঁর ত্রুটি স্বীকারে ও পরিগ্রহণের সত্য উচ্চারণে অকপট। পরস্ব অপহরণে অনেক গবেষক অকুতোভয় কিন্তু তিনি আত্মকৃতকর্মের ত্রুটি যেভাবে সন্ধান করেছেন তা পাঠকের মনে তাঁর কাছ থেকে আর একখানি গবেষণাধর্মী রচনার প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। সমালোচক হিসেবে তিনি প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই জানিয়ে দিয়েছেন, Irving Wardle-এর এই কথা তিনি স্মরণে রেখেছেন যে, একজন সমালোচক যেমন এখনকার দর্শক তেমনি আগামী দিনের ইতিহাস রচয়িতাও। অর্থাৎ রস সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচককে হতে হবে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক।
কিছু পরেই আশিস ১৩৫৪-এর পৌষ মাসের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় জনৈক লেখকের দেওয়া কয়েকটি পত্র স্মরণ করেছেন। তিনটি সূত্রের শেষেরটি অবশ্যই স্মরণীয়—’যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ঠিক ততটুকু দিতে হবে। তার কমও নয়, আবার বেশিও নয়, অর্থাৎ একদিকে ‘দারুণ হয়েছে’ নীতিটিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে, অপরদিকে তেমনি সেটা যাতে আর নিছক চাটুকারিতায় পর্যবসিত না হয়ে পড়ে তাও দেখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমালোচকের মধ্যে ব্যাপক সুন্দর সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
শুধু নাটক কেন, কাব্য-উপন্যাস প্রবন্ধ এমনকি স্থাপত্য-ভাস্কর্য তথা যা কিছু মানুষের প্রাণাবেগ থেকে সৃষ্ট তার মূল্যায়নে পাঠককে হতে হবে যথার্থ সহযোগী। সহযোগিতা সমালোচকের সৃজন ক্ষমতার পরিচায়ক। সমালোচক তো দ্বিতীয় স্রষ্টা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘এ দেশীয় নাট্য সমালোচনার অতীত আলোচনায় তিনি ইন্ডিয়া গেজেট’, ‘এনকোয়ার’, ‘হিন্দু পাইওনিয়ার’ থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। ১৮৩৫-এর ২২ অক্টোবরে ‘হিন্দু পাইওনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত নবীন চন্দ্র বসু’র বাড়িতে অভিনীত ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাট্যপালার সমালোচনার অংশবিশেষ এবং সতুবাবুর বাড়িতে প্রথম নাটক ‘শকুন্তলা’র অভিনয় প্রসঙ্গে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর মন্তব্য উদ্ধার করেছেন।
তারপর ১৮৭২-এ অমৃতবাজার পত্রিকার ১২ ডিসেম্বর সংখ্যায় ‘নীলদর্পণ’-এর প্রথম অভিনয়ের কথা জানিয়েছেন। ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ ও ‘ওরিয়েন্টাল থিয়েটার’-এ অভিনীত নাটকের কথাও বলেছেন তিনি। লক্ষ করা যায়, অভিনীত নাটকগুলি সমকালে লেখা— দীনবন্ধু মিত্র-র ‘জামাইবারিক’, মধুসূদন দত্ত-র ‘শর্মিষ্ঠা’, রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘মালতীমাধব’ ইত্যাদি। অর্থাৎ নাটকগুলি যখন লেখা হয় প্রায় সেই সময়েই নাটকগুলির অভিনয় ও অভিনয়ের সমালোচনা করা হয়েছে। আমরা মনে করি, রচিত নাটক মঞ্চস্থ হওয়া এক ধরনের সমালোচনা, আবার সেই মঞ্চাভিনীত নাটকের সংবাদপত্রে সমালোচনা দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনা।
প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই অবলম্বনটি হল মৌলিকতার দাবিদার। তা ছাড়া নাট্যকারের জীবদ্দশায় তাঁর নাটকের অভিনয় এবং সেই অভিনয়ের সমালোচনা শুধুমাত্র অভিনয়ের দল বা অভিনেতাদের সমালোচনা নয়, মূল নাটকেরও সমালোচনা হওয়ার ফলে যেমন নাট্যগোষ্ঠী তেমনি নাট্যকার দু-পক্ষেরই সংশোধিত হওয়ার অবকাশ থাকে।
আশিস, নৃপেন্দ্রনাথ সাহা নামক নাট্যোদ্যমী ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে ‘বেঙ্গ ল গেজেট (১৭৮১) থেকে ‘এশিয়াটিক জার্নাল’ (১৮৩২) পর্যন্ত সাঁইত্রিশটি পত্রিকার কোন্ কোন্ সংখ্যায় নাট্যবিষয়ক সংবাদ ও আলোচনা থাকত তার একটি তালিকা প্রস্তুত, করেছেন, যদিও এই তালিকার আগে তিনি ১৮৭০-এর হিন্দু পেটরিয়ট’ ও ১৮৭৪-এর ‘ইংলিশ ম্যান’ কাগজে যেসব থিয়েটারের সমালোচনা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমালোচক নাটক বা সাহিত্যের যে-কোনো শাখারই হোন তাঁকে বিশেষ কোনো দৃষ্টি অবলম্বন করতেই হয়।

এই দৃষ্টি অনুসারেই সমালোচনার এক একটি শাখার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হয়েছে। আশিস যদি এই ধরনের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণের হদিস দিতে পারতেন তাহলে নাট্য-সমালোচনার ইতিহাস না হয়ে গ্রন্থটি ইতিহাসের ইতিবৃত্তের একটি চমৎকার সমালোচনা গ্রন্থ হিসেবে মান্য হত। সমালোচক হিসেবে তাঁরও একটি attitude আছে। তিনি অবশ্যই নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু নিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ এই নয়, যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মর্যাদা থাকবে না।
তৃতীয় অধ্যায়ে আশিস পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রঙ্গালয়’ থেকে ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘প্রাণের হাসি’ নাটকের ‘নাচঘর’, ‘সচিত্রশিশির’ এবং ‘ধূমকেতু’ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, ‘এর পর থেকে থিয়েটারের সামাজিক ভূমিকাও বদলে যায়। ফলে সমালোচনার ভাষা, সমালোচনার প্রয়োজন অপ্রয়োজনীয়তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা দিতে শুরু করে।
চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় আসে ‘সমান্তরাল নাট্যধারার নাট্য সমালোচনা’র প্রসঙ্গ। ‘লোকনাট্য’, ‘গণনাট্য’, ‘গন্ধর্ব’, ‘প্রসেনিয়াম’, ‘রক্তকরবী’, ‘এপিক থিয়েটার’, ‘শৌভনিক’ এইরকম কিছু নাট্যপত্রের সম্পাদকের নাম ও প্রকাশকালসহ একটি সারণি উপস্থাপিত করেছেন গবেষক।
আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, ‘চল্লিশের দশক নতুন নাটককালের দশক, নতুন ভাবনার দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষও বিচলিত। সারা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এদেশও গলা মিলিয়েছিল। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দল তৈরি হয়েছে এখানেও। তারই ছত্রছায়ায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখন এই পটভূমিতে নাট্য আন্দোলন নতুন ভূমিকা নিল। পেশাদার নাট্যচর্চার পরিবর্তে নতুন এক নাট্যধারার সূচনা হল।
পেশাদারি নাট্যচর্চার সাংগঠনিক ও দর্শনগত দিক থেকে ভিন্নতর এক পথ— অপেশাদার কিন্তু গভীরভাবে সমাজমনস্ক এক কমিটেড নাট্যধারা’। এই রকম বেশ কিছুটা দিক্ নির্দেশক মূল্যবান মন্তব্যসমৃদ্ধ ভূমিকাসহ ‘বহুরূপী’, ‘গণনাট্য’, ‘গন্ধব’, ‘থিয়েটার’ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত সেকালের অনেকগুলি নাটকের প্রযোজনার সমালোচনা করেছেন গবেষক।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ প্রমুখের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় “থিয়েটার’ পত্রিকায়। ‘চক্র’, ‘দাবী’, ‘বেগম মেরী বিশ্বাস’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি নাটকের প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয় ‘রূপমঞ্চ’ পত্রিকায়। খুব উপভোগ্য একটি আলোচনা পড়া গিয়েছিল ‘পাদপ্রদীপ’-এ প্রকাশিত ‘বহুরূপী ও রক্তকরবী’ নামে লেখা উৎপল দত্তের একটি প্রবন্ধ। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘পাদপ্রদীপের আলোকে আরোগ্য নিকেতন’ প্রবন্ধটি।
গবেষকের সঙ্গে উৎপল দত্তের সম্পর্কটা ছিল নিবিড়। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো রচনাতেই উৎপল দত্ত প্রযোজিত নাটকের প্রশংসা হয়নি—উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটারের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ভূমিকা আর কখনোই গড়ে ওঠেনি। ফলে আমৃত্যু উৎপল দত্তকে এই পত্রিকার সমালোচনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেই চলতে হয়েছে। বরং ‘বহুরূপী’র কাজকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল – যে গুরুত্ব তাদের অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল।
সেই সঙ্গে নান্দীকার এবং অন্যান্য দলের প্রযোজনাগুলিও নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে যেসব নাট্য প্রযোজিত হয়েছিল তার সমালোচনা ‘অমৃত’, ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ ও ‘রূপমঞ্চ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সে সবের আলোচনার শেষে ‘উপসংহার’ অংশে গবেষক যা বলেছেন তার সাম্প্রতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। আশিস ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ তাঁর স্থিতি থেকে চমৎকার নিবেদন করেছেন।
যেহেতু তাঁর গবেষণাগ্রন্থের শেষ অংশটুকু (‘নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার ১৯৪৪-১৯৭৮’) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নাট্য-সমালোচনা অংশের উদ্ধৃতি (অত্যন্ত মূল্যবান এই অংশ) তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের ‘উপসংহার’ টুকু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তিনি মনে করেন মানুষের গণতান্ত্রিক শুভ চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে থিয়েটার’কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। থিয়েটারের ধারা অব্যাহত রাখার সঙ্গে নাট্যপত্রগুলিকেও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।
আশিস তাঁর ‘বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা’ সন্দর্ভে প্রচুর তথ্য উদ্ধার করে যেমন অনালোকিত ও অনালোচিত অংশ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন তেমনি সমালোচকের কর্ম সফল করে তোলার জন্য যে বিভিন্ন নাট্যপত্রকেও সজীব ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে এই বার্তা জ্ঞাপন করে তাঁর গবেষণাকর্মকে সার্থক করে তুলেছেন। সমগ্র গ্রন্থখানিতে লেখক তাঁর নাট্যপ্রীতির প্রমাণ রেখেছেন অনেক অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করে। তাঁর এই সন্দর্ভ অবশ্যই ভবিষ্যতের নাট্য-সাহিত্যপ্রেমীকে নতুন করে চিন্তা করতে উদ্দীপিত করবে।
ভাবাবেগতাড়িত বাঙালির জীবনে নাটক রচনা, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্যপত্রিকা প্রকাশনার তাগিদ অনুভূত হয় না ততটা, যতটা দেখা যায় কাব্য-কবিতা-গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি ও সে বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায়। আশিসের শ্রমসাধ্য গবেষণা আগামী দিনের রচয়িতা-প্রযোজক-অভিনেতা অভিনেত্রী সকলকেই উজ্জীবিত করবে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীতে প্রশ্রয় লাভের জন্য।
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
